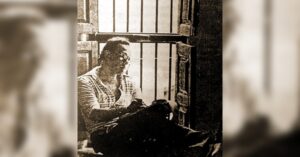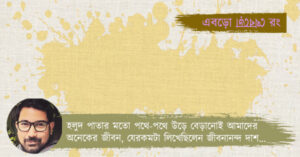খাস কলকাতার বুকে হাট, তাও আবার ফিলাটেলি অর্থাৎ ডাকটিকিট সম্পর্কিত? জোড়া অবিশ্বাসের মতন লাগছে না কথাটা? হ্যাঁ, অবাক হলেও সত্যি। ফি শনিবার এই হাট বসে ডালহৌসির জিপিও চত্বরে। জিপিও-র বড়ঘড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়ালে আপনার বাম হাতে সৌধটির যে-দালান, এক সময়ে সেটাই ছিল হাটের কেন্দ্রস্থল। গ্যালারির মতন যে টানা লম্বা সিঁড়ি উঠে গেছে, সেখানে বসেই চলত বিকিকিনি। গত শতকের নয়ের দশকের মাঝামাঝি এমন কিছু ঘটনা ঘটে সেই হাটে আসা ক্রেতা-বিক্রেতা, ক্রেতায়-ক্রেতায় এবং/অথবা ডিলারে-ডিলারে, যাতে জিপিও কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন দালানচত্বরে বসে সমস্তরকমের বিনিময় বন্ধ করে দিতে। ও হ্যাঁ, বলা হয়নি, এই হাটের শুরু মোটামুটি গত শতকের আটের দশকের প্রথমার্ধে।
ফিরে আসি, আগের কথায়। কর্তৃপক্ষের বারণ অবিশ্যি বেশিদিন মান্যতা পায়নি হাটুরে আবেগের তোড়ে। কখন সে নিষেধের বাঁধ আলগা হয়ে গেছে। এককালে এই হাটে মুম্বই, আমেদাবাদ, চেন্নাই, কানপুর, লখনউ, পাটনা, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি জায়গা থেকে আসতেন ডাকটিকিটের ব্যাপারীরা। হাতের অ্যাটাচি, দু’কাঁধের ঝোলা ব্যাগ, পিঠব্যাগে আসত তাদের পসরা। তারপরেও থাকত হোটেলের ঘরে, কলকাতায় তাদের অস্থায়ী ঠিকানায়। মোটামুটি এগারোটা থেকে সন্ধে সাড়ে ছ-টা/সাতটা— এই হল হাটবারের সময়। এই বেচাকেনার রেশ থাকত তাদের হোটেলের ঘর পর্যন্ত। অনেকে হাটবারের দু’একদিন আগে এসে তার পরেও পরিস্থিতি বুঝে থাকতেন হোটেলে। সবটাই যে নগদ বেচাকেনা হয়, তা নয়। ধারবাকিও চলে। সেসবের আদায়-উসুল চলে পরিবর্ধিত থাকার সময়ে।
হাটসূত্রে পরিচয় হবার পর অনেক সম্পন্ন ক্রেতাই আর হাটে আসেন না। সরাসরি পৌঁছে যান ডিলারের হোটেলের চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে। কী সেই কেনাবেচা? দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম, বিশেষ ডাকমোহর, পুরনো দিনের চিঠিপত্রাদি, নানান ধরনের পোস্টাল স্টেশনারি (যেমন পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড লেটার, এয়ারোগ্রাম, ম্যাক্স কার্ড, মেঘদূত পোস্টকার্ড, এয়ারমেল পোস্টকার্ড ইত্যাদি), ডাকমোহর, বুকলেট প্রভৃতি। এ হল মুখ্য। ক্রমে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফিলুমেনি (ম্যাচবক্স লেবেল ও সেই সংক্রান্ত উপকরণাদি), নোটাফিলি (পেপার মানি), মুদ্রা, নানান রকমের টোকেন, সেকেলে দলিল-দস্তাবেজ ও পেপার কাটিংয়ের কারবারিরাও। তবে সেকাল থেকে একাল— হাটের মুখ্য আকর্ষণ ডাকটিকিট বেওং তৎসংক্রান্ত কেনাবেচা। টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ কখনও-কখনও কোটির ঘর ছুঁয়ে থাকে। হিসেবটা অবশ্য নগদ, বাকি ও অন্যান্য বিনিময়ের হিসেব ধরে।
হাটে আগত মানুষজনকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে তাদের প্রকৃতি বিচারে। প্রথম দলে আছেন বিক্রেতারা। এদের আবার তিনটে ভাগ— ১. পেশাদার ডিলার (যেমন সত্য সরকার, প্রয়াত অরুণ ভট্টাচার্য্য)। ২. আংশিক সময়ের ডিলার, অন্য পেশায় যুক্ত থাকার পাশাপাশি যাদের এই সূত্রেও আয়ের একটা অংশ আসে। মুম্বইয়ের এস. সিংঘানিয়া যেমন পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবার পাশাপাশি ফিলাটেলির ব্যবসাতেও ভালই হাত পাকিয়েছিলেন। ৩. সংগ্রাহক কাম বিক্রেতা। এই শেষোক্ত শ্রেণির লোকের সংখ্যাই ক্রমশ বাড়ছে। শখ মেটানোর পুরো বা বেশির ভাগ অর্থই এঁরা জোগাড় করেন সমজাতীয় শখের জিনিস অন্যকে বিক্রির মাধ্যমে। দ্বিতীয় দলে আছেন সংগ্রাহক থেকে হয়ে ওঠা ফিলাটেলির ডিলার। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও ভাল সংগ্রহের (থিমাটিক বা দেশভিত্তিক) অধিকারী হন। সম্ভবত সেই সম্পদের পেছনে নিজের শ্রম, নিষ্ঠা, সময় ব্যয়িত হয় না বলেই একটা সময়ের পর আর সংগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ-মালিকের আত্মিক যোগসূত্রটা কেটে যায়। বস্তুমূল্যই তাদের বিবেচনায় অগ্রাধিকার পায়। সেটা বিক্রি করতে-করতেই তাঁরা হয়ে ওঠেন ফিলাটেলি তথা ডাকটিকিটের কারবারি। প্রকৃত স্ট্যাম্প-ডিলার আর সংগ্রাহকদের মাঝে এঁদের অবস্থান কতকটা মধ্যস্বত্বভোগী পর্যায়ের। এঁদের পুঁজি কম, স্টকও সীমিত। সামান্য সংখ্যক বাঁধা ক্রেতা আর ফ্লোটিং কাস্টমারের ওপরে নির্ভর করে চলে এদের ব্যবসা। তৃতীয় দলের আছেন শুধুই ক্রেতা ওরফে সংগ্রাহক।
ফিলাটেলির দুনিয়ায় অঘোষিত বিপন্ন প্রজাতি, আপন বৈশিষ্ট্যের জন্য কেউ-কেউ একটা চরিত্র হয়ে ওঠেন। ‘ধুতি দত্ত’ যেমন। আমরা বলি, দত্তদা। আসল নাম জিজ্ঞেস করলে ক’জন বলতে পারবেন সন্দেহ আছে। ছিলেন অধুনালুপ্ত এক রেফ্রিজারেটর কোম্পানির কর্মী। অকৃতদার দত্তদার অসাধারণ সংগ্রহ ছিল সুইৎজারল্যান্ড ও গ্রেট ব্রিটেনের। শুনেছি, দামি ডাকটিকিটগুলো চিহ্নিত করে তাদের পাশে তারিখ-সহ বাজারমূল্য লিখে রেখেছেন। দত্তদার সংগ্রহের উত্তরাধিকারী হবেন তাঁর ভাইপো। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন সল্টলেকনিবাসী প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল পাখি বিষয়ক ডাকটিকিট সংগ্রহের জন্য। অবসরের পরেও জারি ছিল তাঁর সংগ্রহের প্রয়াস। পাশাপাশি সারাজীবনের সংগ্রহকে তিনি প্রজাতির ভিত্তিতে (নমুনা: জলচর,শিকারি পাখি প্রভৃতি) কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়েছেন অ্যালবামে। অপত্য-বিয়োগের মতন যন্ত্রণাকে সহ্য করার শক্তি তাঁকে জুগিয়েছিল তাঁর বিপুল সংগ্রহ।
সন্তান হারানোর কথায় মনে পড়ে উত্তরপাড়ানিবাসী প্রয়াত (বছর চারেক আগে) সমীরেন্দ্রনাথ সেনের কথা। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে চাকরি করতেন। সে-সময়ে তাঁর একমাত্র ছেলে কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যান। মাত্র ২৩ বছর বয়সে। প্রায় আড়াই বছর অক্লান্ত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি একমাত্র সন্তানকে। একটা পর্যায়ে দৈনিক চিকিৎসার খরচ ছিল প্রায় দশ হাজার টাকা। শেষের দিকে টানা কয়েকমাস এই ধারাবাহিক খরচার রসদ এসেছিল সেনদার অসামান্য সংগ্রহ বিক্রির টাকা থেকে। প্রসঙ্গত সেনদার অবিশ্বাস্য সংগ্রহে ছিল তাঁর সময়কার ২৫-টিরও বেশি দেশের প্রায় সব ডাকটিকিট। শুধু সংগ্রহ নয়, ফিলাটেলির নানা ধারায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল ঈর্ষণীয়। সন্তানের মৃত্যুর পরে চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নেন তিনি। প্রথমে গড়াবেতায়, তারপরে সেখানকার পাট চুকিয়ে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন উত্তরপাড়া রেলস্টেশনের কাছে এক ফ্ল্যাটে। আমৃত্যু ছিলেন সেখানেই। সেনদার সঙ্গে আমার পরিচয় ফিলাটেলির হাটেই। আমার ফিলাটেলির অনেককিছুই শেখা তাঁর কাছ থেকে। তিনি ও বউদি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। আমার বৈবাহিক জীবনের সূত্রপাতেও তাঁদের দু’জনের বড় ভূমিকা ছিল। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অন্যতম প্রিয় শিল্পী, এ-কথা জানার পর বউদি নিজে উদ্যোগ নিয়ে সম্পর্কে তাঁর পিসেমশাই রামানন্দবাবুর কাছে যান যাতে তিনি আমার বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের নকশা করে দেন। সানন্দে যথা সময়ে করে দিয়েছিলেন শিল্পী। এটা সম্ভব হওয়ার নেপথ্যেও ছিল ফিলাটেলির হাটের পরোক্ষ ভূমিকা।
সোমেশলাল মুখোপাধ্যায় উচ্চমাধ্যমিকে ছিলেন কলা বিভাগের ছাত্র। সব বিভাগ মিলিয়ে তৃতীয় হন। সিটি কলেজে (আমহার্স্ট স্ট্রিট) আমাদের রাশিবিজ্ঞানের ক্লাস নিতেন। মাঝে অনেকদিন কোনও যোগাযোগ ছিল না। তাঁর দেখা পেয়েছিলাম পুনরায় এই ফিলাটেলির হাটেই। তাঁর সবিশেষ আগ্রহ ছিল পেইন্টিং সংক্রান্ত ডাকটিকিট সংগ্রহের ব্যাপারে। বিষয়ভিত্তিক ডাকটিকিট সংগ্রহ যে কত বিচিত্র হতে পারে, তা এখানে মালুম হয়। কারও-কারও তো সংগ্রহের কারণেই তাঁদের নামের আগে যুক্ত হত উপাধিস্বররূপ সংগ্রহের বস্তুনামটি। যেমন: ‘ইউরোপা প্রশান্ত’ হলেন বাগুইআটি নিবাসী প্রশান্ত বিশ্বাস। এঁর স্পেশালাইজেশন ‘ইউরোপা’ এবং অলিম্পিকের আয়োজক দেশের ডাকটিকিট-সহ বিবিধ পোস্টাল স্টেশনারি সংগ্রহে;আমার ‘হকি গৌতম’ খেতাব প্রাপ্তি হয়েছিল ফিল্ড হকি বিষয়ক ফিলাটেলিক সংগ্রহের সৌজন্যে। ‘ফ্ল্যাগ শেখর’ হলেন শেখর চক্রবর্তী।
বেচাকেনার এই হাটে ছিল কিছু স্বতন্ত্র স্থানমাহাত্ম্যও। যেমন ‘বটতলা’, ‘চায়ের দোকান’, ‘গাছতলা’, ‘রেলনীড়’ ‘এটিএম’ নাম উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে হাটে নিয়মিত আগত মানুষটি বুঝে যেতেন সুনির্দিষ্টভাবে কোন জায়গার কথা বলতে চাইছেন বক্তা। এগুলো ছিল কোডনেমের মতন। ফ্রেমে হিরো থাকলে ভিলেন-ও থাকবেই। শনিবারের এই হাটেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এক ডাক্তার এবং এক উচ্চপদস্থ চাকুরে আসতেন। গাড়ি নিয়ে। এঁরা আসামাত্র ডিলারদের মধ্যে এক সাজো-সাজো রব পড়ে যেত। ‘কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান’-এর কায়দায় ধাবিত হতেন তাঁরা এই দুই মান্যবরের দিকে। আমার কেবলই মনে হত সহজে মুরগি করার সুযোগ কেউই ছাড়তে চাইতেন না। কারণ এঁরা দর-দস্তুর বিশেষ করতেন না। যে যা দেখাতেন, পছন্দ হলেই সেটায় তাঁর অধিকার নিষ্পন্ন হত। পকেট থেকে মুঠো-মুঠো টাকা বের করতেন এঁরা পেমেন্ট করার জন্য। কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকত। ক্ষণজন্মা মরশুমি পাখির মতন একটা সময়ের পর এঁদের আবির্ভাব হয়নি হাটে। সেটা সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ হারানোর দরুন না কি অন্য কারণে— তা অবিশ্যি জানা নেই এই কলমচির।
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অন্যতম প্রিয় শিল্পী, এ-কথা জানার পর বউদি নিজে উদ্যোগ নিয়ে সম্পর্কে তাঁর পিসেমশাই রামানন্দবাবুর কাছে যান যাতে তিনি আমার বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের নকশা করে দেন। সানন্দে যথা সময়ে করে দিয়েছিলেন শিল্পী। এটা সম্ভব হওয়ার নেপথ্যেও ছিল ফিলাটেলির হাটের পরোক্ষ ভূমিকা।
ডক্টরেট ডিগ্রিধারী পশ এরিয়ার এক বাসিন্দা আসতেন প্রায়ই। কর্কটরোগের গবেষক। যে-সময়ের কথা বলছি, তখন বাড়িতে কম্পিউটার বিরল। কর্মক্ষেত্রের কম্পিউটারটিকে পদাধিকার বলে অনেকটাই ব্যক্তিগত কাজে লাগাতেন। ই-মেল মারফততিনি বিভিন্ন দেশের ডাকবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁদের বোঝান, ক্যানসার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে তিনি কর্কট রোগ এবং রক্তবাহিত অসুখ সম্পর্কিত ডাকটিকিটের সংগ্রহশালা গড়তে চান। তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল অনেকটাই। তবে সেসব সংগ্রহের স্থান হয়েছিল ব্যক্তিগত সংগ্রহের অ্যালবামে। কর্মস্থলে কোনও সংগ্রহশালা গড়ে তোলেননি। এহেন ফাঁকিবাজি-চালাকির কথা গর্বভরে আমাকে শুনিয়েছিলেন খোদ সেই লোকটি তাঁর অফিসে বসে। তার আগে তাঁর মুখে সংগ্রহশালার কথা অনেকবার শুনেছিলাম। সেটা দেখতেই আমার যাওয়া তাঁর অফিসে। তারপর থেকে তাঁকে দেখলেই কেমন বিবমিষা হত আমার। অথচ সেই লোকটি ব্যক্তিগত সু-যোগাযোগের সূত্রে বছরের পর বছর দৈনিক পত্রিকায় ডাকটিকিটে ক্যানসার বিষয়ক নিম্নমানের লেখা লিখতেন। সামাজিক প্রতিপত্তির উৎস যে ক্ষমতা, তারই প্রতিফলিত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করতাম।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের এক অধ্যাপককে দেখেছিলাম, তাঁর ক্লাস সেভেনে পাঠরত পুত্রের জন্য এক ফড়ে সংগ্রাহকের দ্বারস্থ হতে। উদ্দেশ্য, রাজ্যস্তরে আয়োজিত ডাকটিকিট প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় ছেলের পদক জয় নিশ্চিত করা। লক্ষ্যে সফল হয়েছিলেন তিনি। এহেন অসততার নেপথ্য কারণ ছিল, ছেলের সিভি-র ওজন বৃদ্ধি! এই আপাত ‘তুশ্চু’ ঘটনা প্রমাণ করে, তথাকথিত শিক্ষিত কতটা ভণ্ড, আদর্শহীন হতে পারে! ফিলাটেলি নিছক ‘শখ’ নয়, তা মানুষও চেনায়।
দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে ওঠার পর চূড়ান্ত খেলার আগেই শ্রীলঙ্কার ছাপানো স্মারক ডাকটিকিট, যাতে লেখা ছিল ‘ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা’ (পরে ডাকটিকিট নষ্ট করে ফেলা হয়, ফাইনালে শ্রীলঙ্কা হেরে যাওয়ায়); কিংবা, গুরু গ্রন্থসাহিবের চারশো বছর পূর্তিতে মুদ্রিত ভারতের মিনিয়েচার শিট (যা ইস্যু করার আগেই বাতিল হয়েছিল)— সেসব দর্শনের অমূল্য সুযোগ করে দিয়েছিল এই হাট। বিশ্বের প্রথম রেকর্ড স্ট্যাম্প (ভুটান) এবং সিডি ডাকটিকিট (দক্ষিণ কোরিয়া), নানান অনিয়মিত এবং একাধিক সুগন্ধী স্মারক ডাকটিকিট সংগ্রহের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই হাটের সঙ্গে।
পড়ন্ত হাটের ডিলার-সংগ্রাহকদের কেউ-কেউ মেতে ওঠেন জিপিও-র উলটোদিকে একটা নির্দিষ্ট চায়ের আড্ডায়। বয়স সেখানে বাধা হয়নি কোনওদিন। অরুণ ভট্টাচার্য, সত্য পালের মতন ডিলাররা প্রয়াত হবার পর তাঁদের ছেলে যথাক্রমে অভিষেক ও স্বদেশ তাঁদের জীবিকা অর্জনের জন্য বেছে নিয়েছেন ডাকটিকিটের ব্যবসাকেই। রয়েছেন নতুন-পুরনোরাও। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, বিশেষত কোভিড-পরবর্তী সময়ে এখন ডাকটিকিট ব্যবসাও অনেকটাই অনলাইননির্ভর। আগের মতন ভিন রাজ্যের ক্রেতা-বিক্রেতারা আর এই হাটে আসেন না বললেই চলে। তাতে ফিকে হলেও আমাদের এই একমাত্র ডাকটিকিটের হাটের আকর্ষণ একেবারে মিইয়ে যায়নি। ফিলাটেলির দর্পণে মানুষ চেনার এ এক অনন্য ক্ষেত্র।