জলরঙের দরদ
একটা ১৭ বছরের মেয়ের গর্ভপাতের চেষ্টার কাহিনি নিয়ে ছবি ‘নেভার রেয়ারলি সামটাইমস অলওয়েজ’ (চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: এলাইজা হিটমান, ২০২০)। এই ধরনের ছবি সাধারণত হয় তীব্র বেদনাময়, বা প্রচারধর্মী, বা অন্তত তর্কপ্রসবী। কিন্তু এই ছবি দেখলে মনে হয়, মেয়েটার মতোই চুপচাপ এ যন্ত্রণা ও একাকিত্ব বহন করে চলেছে। সমাজ সম্পর্কে কথা আছে, কিন্তু তা সংক্ষিপ্ত এবং অপ্রকট। অধিকাংশ তথ্য দর্শককে দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করা হয় না। কে মেয়েটিকে গর্ভিণী করেছে, আমরা জানি না। তার এখন কোনও প্রেমের সম্পর্ক আমরা দেখি না। ছবির নাম দেখানোর সময়ই আমরা দেখি নায়িকা একটা স্কুলের বা পাড়ার ফাংশনে গান গাইছে, একটা দর্শক-ছোকরা তাকে ‘বেশ্যা’ বলে আওয়াজ দেয়। ফাংশনের পর খাওয়াদাওয়ার সময় মেয়েটার সৎ বাবা সরাসরিই মেয়েটার প্রতি তার বিরক্তি প্রকাশ করে, আর পরেও সেই সৎ বাবা বাড়ির সকলের সামনে তার পোষা কুকুরকে ‘আমার বেশ্যা, আমার বেশ্যা’ বলে আদর করতে থাকে, মা চুপ করিয়ে দেয়। আমরা আন্দাজ করি, মেয়েটার হয়তো অনেক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে একটা বদনাম আছে।
মেয়েটা থাকে আমেরিকার পেনসিলভানিয়ায়, সেখানে অপ্রাপ্তবয়স্কার গর্ভপাত করাতে গেলে অভিভাবকের অনুমতি দরকার, তাই এক তুতো-বোনের সঙ্গে (বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে) সে যায় নিউ ইয়র্ক-এ, সেখানে চট করে গর্ভপাত করিয়ে ফিরে যাবে। ছবির মূল অংশটা এই নায়িকা (অটাম) এবং তার বোনকে (স্কাইলার) অনুসরণ করে, তারা একটা ভারী সুটকেস টানতে টানতে নিউ ইয়র্কের পথেঘাটে, বাসে-ট্রেনে ঘোরে, এই বিরাট ও অচেনা শহরে কিছুটা থতমত খেয়ে থাকে। তাদের হোটেলের পয়সাও নেই, বাসস্টপ বা মেট্রো স্টেশনে বসে বা মেট্রোয় চড়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। নিজেদের মধ্যে কথা যে খুব বলে তা-ও নয়, কান্নাকাটিও ঘটে না, মূলত দু-জনেই ফোন দ্যাখে, বা বাসে ট্রেনে যেতে ঢুলে পড়ে। ভেবেছিল ব্যাপারটা একদিনেই মিটে যাবে, দেখা যায় তা নয়, বাড়তি প্রায় দু-দিন থাকতে হবে। ওদের টাকা খুব নেই, দু-জনেই একটা দোকানে কাজ করত, সেখান থেকে স্কাইলার কিছু টাকা চুরি করেছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। গর্ভপাতের খরচা দিয়ে বাকি থাকে এত কম, তাতে ওদের বাড়ি ফেরার বাস-টিকিটও হবে না। বাসে একটা ছেলের সঙ্গে স্কাইলারের আলাপ হয়েছিল, ছেলেটা স্পষ্টতই তার প্রতি আকৃষ্ট, মেসেজও করেছে কয়েকবার, স্কাইলার পাত্তা দিচ্ছিল না, শেষে তার সঙ্গে একটু ঘোরাঘুরি করতে হয় ও লজ্জার মাথা খেয়ে টাকা চাইতে হয়। গর্ভপাতটা হয়ে যাওয়ার পর যখন অটাম-কে স্কাইলার জিজ্ঞেস করে, খুব লেগেছে কি না, বা লোকগুলো ভাল ব্যবহার করেছে কি না, অটাম একটু কাটা-কাটা উত্তর দেয়। তারপর বাসে ফেরার সময় ছবি শেষ হয়ে যায়।
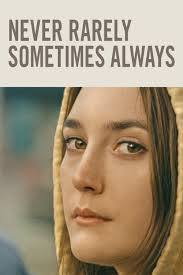

এমনিতে ছবির ভঙ্গিটা কেজো, যেন, যা হচ্ছে তা দেখাচ্ছি, ওরা কথা না বললে আমি তো আর সংলাপ তৈরি করে দিতে পারি না। চরিত্র দু-জনকে দেখানো হয় কোনও একটা দোকানে ঢুকে খাবার কিনছে, ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছে, কোনও খেলার দোকানে ঢুকে স্ক্রিনে একবার কাটাকুটি খেলল, ভারী সুটকেসটা স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে টানতে টানতে তুলছে, টিকিট নেই বলে মেট্রো রেলের গেটের তলা দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ছোট ছোট আঁচড়ে বহু কথা বলা হয়। বাথরুমে গিয়ে যোনি দিয়ে অল্প রক্ত বেরচ্ছে দেখার পর অটাম মা’কে একটা ফোন করে, কিন্তু মায়ের উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে কোনও কথা না বলে রেখে দেয়। নিজের শহরে অটাম যখন একটা ক্লিনিকে দেখাতে যায়, সেখানে এক মহিলা তাকে বলেন, তুমি কি অ্যাবর্শনের কথা ভাবছ, এই ভিডিওটা দ্যাখো। সেখানে আমরা দেখি গর্ভপাতের বিরুদ্ধে কথা বলা হচ্ছে। নিউ ইয়র্কে আবার বড় ক্লিনিকের সামনে ধর্মীয় একটা সমাবেশ, যারা, বোঝাই যাচ্ছে, গর্ভপাতকে অন্যায় বলে মনে করে। ফাঁকা মেট্রোয় খুব রাতে এরা যখন যাচ্ছে, এক কোট-টাই পরা লোক ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হস্তমৈথুন শুরু করে, ওরা তাড়াতাড়ি নেমে যায়। আবার নিজেদের শহরে দোকানে ওরা যখন কাজ করছিল, এক বয়স্ক লোক স্কাইলারের সঙ্গে জোর করে আলাপ জমিয়ে তাকে পার্টিতে ডাকার চেষ্টা করে।
দুই সুন্দরী তরুণীর জীবনে পুরুষদের গুঁতিয়ে ঢুকে পড়ার চেষ্টা বা রাষ্ট্রের ও সমাজের গর্ভপাত বিষয়ক শুচিবায়ুর কথা বলা হয়, তবে খুবই ছোট শটে, এবং দাগিয়ে দেওয়ার কোনও চেষ্টা থাকে না। অটামের সৎ বাবা যখন পোষা কুকুরের আদর কাড়া দেখে বলে, যাক, তবু আমায় এ-বাড়িতে কেউ ভালবাসে, এবং তারপরে কুকুরকে ‘আমার বেশ্যা’ বলে আদর করে, তার সঙ্গে অটামের প্রতি তার ধারাবাহিক দুর্ব্যবহার মিলিয়ে দেখে আমাদের মনে এই সন্দেহও উপস্থিত হতে পারে যে সে-ই এই অবাঞ্ছিত সন্তান-ঘটনার উৎস। কিন্তু সেটা নিতান্ত আন্দাজ। যখন ক্লিনিকে অটাম-কে কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয, যার উত্তর দিতে হবে ‘কক্ষনও না’ (Never), ‘খুবই কম’ (Rarely), ‘মাঝে মাঝে’ (Sometimes), অথবা ‘সবসময়’ (Always)— এর যে কোনও একটা ব্যবহার করে, তখন আমরা অটামের সঙ্গোপন জীবন সম্পর্কে সামান্য কথা জানতে পারি, যেমন, সে চোদ্দ বছর বয়স থেকে যৌনতা করছে, এখনও অবধি সে ছ-জনের সঙ্গে যৌনতা করেছে। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, তার কোনও প্রণয়সঙ্গী তাকে কখনও মেরেছে কি না, এবং (আরেক প্রশ্নে) তাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌনতায় বাধ্য করেছে কি না, তখন অটামের সদা-নির্বিকার মুখ ক্রমে ভেঙেচুরে যেতে থাকে, সে কেঁদে ফ্যালে এবং উত্তর দিতে পারে না, এই প্রথম আমরা তার বেদনার প্রকাশ প্রত্যক্ষ দেখি (এর আগে নিজের পেটে যখন সে সজোর ঘুসি মারছে ভ্রূণটাকে মেরে ফেলার জন্য, তার চোখে জল দেখেছিলাম, কিন্তু তা শারীরিক যন্ত্রণাতেও হতে পারে, আর ফাংশনে ‘বেশ্যা’ দর্শক-চিৎকার শোনার পর তার কান্না পেয়ে গেছিল কিন্তু সে তা সামলে গান শেষ করে)। এই ক্লিনিকে মাল্টিপল-চয়েস উত্তরের সময়টায় পরিচালিকা টানা শুধু অটামের মুখটাই ধরে রাখেন, সেই ফ্রেম এবং এই সরাসরি প্রশ্নাবলির খাঁচায় আটক হয়ে অটাম ছটফট করে, একবার বলেও, আমাকে কেন এসব জিজ্ঞেস করছেন, এবং তার দীর্ণ মুখচিত্রে আমরা বুঝতে পারি, কত অপমান, কত প্রহার, কত পরাজয় সে গোপন করে রেখেছে। বা, প্রসারিত অর্থে, কত মেয়েকে এই সমাজে কত অত্যাচারের কথা চেপেচুপে ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে বাহ্যিক টিপটপ ব্যবহারটা করে যেতে হয়। এবং ছবির শেষেও আমাদের মনে হয়, এই নিউ ইয়র্ক অভিযানের কথা হয়তো সে কোনওদিনই কাউকে বলবে না, হৃদয়ের একটা নিচু খোপে রেখে দেবে। ছেলেটার কাছে স্কাইলার যখন টাকা চায়, সে একটু অবাক হয়, তারপর বলে কাছের একটা এটিএম থেকে এনে দিচ্ছে, স্কাইলারকে সঙ্গে নিয়ে যায়, বিরাট সুটকেস নিয়ে অটাম একা থাকে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ স্কাইলার ফিরছে না দেখে এদিক-ওদিক খোঁজে, একবার স্টেশন থেকে বেরিয়েও যায়, ফের স্টেশনে ঢুকে একটা থামের আড়ালে দেখতে পায়, ছেলেটা স্কাইলারকে চুমু খাচ্ছে। অটাম তখন সেই থামের পিছনদিকে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, তারপর অল্প অল্প এগিয়ে স্কাইলারের একটা হাত ধরে। স্কাইলার তার হাত পিছনে বাড়িয়ে দেয়, তারা আঙুলে আঙুল জড়িয়ে নেয়। স্কাইলার যে টাকাটা পাওয়ার জন্য এই চুম্বন সহ্য করছে, তা বুঝে আরেক নারীর সহমর্মী হাত এসে তাকে কৃতজ্ঞতা ও ভগ্নিত্ব জ্ঞাপন করে। যখন ওরা বুঝেছিল ফেরার টাকা নেই, স্কাইলার অটামকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার মাকে ফোন করব? অটাম: না। তোর মাকে? না। তাহলে আমায় কী করতে বলিস? বেরিয়ে যা। তারপরেই যখন দেখি বাথরুমে স্কাইলার অটামকে সামান্য সাজিয়ে দিচ্ছে, চোখের তলায় একটু ক্রিম, ঠোঁটে লিপস্টিক (ওরা ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে যাবে), তখন এদের সখীত্ব আরও নিবিড় হয়ে ধরা দেয়।
তবু এই ছবিতে একটা-আধটা ক্ষেত্রে দর্শকের উদ্বেগ হয়, এবং সমস্যার সমাধান হবে কি না সেই প্রশ্নও জাগরূক, কিন্তু ‘গুড ওয়ান’ (চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: ইন্ডিয়া ডোনাল্ডসন, ২০২৪) ছবি যেন ঘটনাহীনতাকে সজোর আলিঙ্গন করে, আর কোনও অনুভূতিই এতটুকু উঁচু তারে প্রকাশিত হয় না। এক বাবা আর মেয়ে এবং বাবার এক বন্ধু হাইকিং-এ যাচ্ছে, মানে জঙ্গল-পাহাড়ে তিনদিন ধরে হাঁটাহাঁটি করে ফিরে আসবে, তাঁবুতে থাকবে। ছবি জুড়ে তারা তা-ই করে, অর্থাৎ হাঁটে, দাঁড়ায়, শোভা দ্যাখে। বাবা বেশ গম্ভীর ও দক্ষ ধরনের, বন্ধুটা উল্টো, অগোছালো, নিড়বিড়ে, আনাড়ি। সে মদ নিয়ে এসেছে, কিন্তু স্লিপিং ব্যাগ ফেলে এসেছে, ফলে তাকে মাটিতে শুতে হবে। এই দুই পুরুষেরই বয়স ষাটের কাছে, মেয়েটা কিশোরী। যদিও তার পিরিয়ড চলছে বলে প্রায়ই গাছের আড়ালে গিয়ে ট্যামপন পরে নিতে হচ্ছে, তবু দেখা যায় সে-ই জল ভরছে, রান্না করছে, ক্যাম্প খাটানোয় সাহায্য করছে। মেয়েটা মাঝে মাঝে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ফোনে কথা কথা বলে বা মেসেজ করে, কিন্তু আদ্ধেক সময় তো ফোনে সিগনালই নেই। তাই আমরা শুধু চরিত্রগুলোর যাওয়া-আসা, আর এমনি কথাবার্তা দেখি। মোটা বন্ধু একটু আমুদে, মেয়েটার সঙ্গে আলোচনা করে কী কী খাবার তাদের সবচেয়ে ভাল লাগে, আর এইসব গল্পের ফলে হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে দেখে বাবা একটু ক্ষুব্ধ হয়ে অপেক্ষা করে, সে কিছুটা এগিয়ে গেছে। মাঝখানে হাইকিং-এ আসা আরেকটা দলের সঙ্গে দেখা হয় (তিনটে ছেলে), তারা একদম ওদের পাশেই ক্যাম্প খাটাচ্ছে দেখে মেয়েটা বাবাকে বলে, ওরা কি এখানেই থাকবে না কি (অর্থাৎ, বারণ করো!), বাবা বলে, ও ঠিক আছে। একটা সময় এরা সবাই একসঙ্গে বসে গল্পটল্প করে, তাতে বোঝা যায়, এই বাবার সদ্য একটা বাচ্চা হয়েছে। টুকরো-টাকরা কথায় আমরা জেনেছি, দুই পুরুষই ডিভোর্সি, মেয়েটা বাবার আগের পক্ষের সন্তান, আর বন্ধুটার সন্তানেরা তার প্রতি ক্রুদ্ধ, ডিভোর্সের ফলে। পরে এক সন্ধ্যায়, মাতাল হয়ে বাবার বন্ধুটা বলে, সে হতে চেয়েছিল অভিনেতা, হয়েছে সেলসম্যান, তারপর একটা সেলসম্যানদের মিটিং-এ গিয়ে কোন মেয়ের সঙ্গে যৌনতা করেছিল, আরও কয়েকটা কারণে বউ তাকে ছেড়ে গেছে, কিন্তু সে বউকে খুব ভালবাসে। একটু কেঁদেও ফ্যালে। কিশোরী তখন কয়েকটা কথা বলে, যা তার বয়সের তুলনায় পরিণত। বন্ধু বেশ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়। সে যখন বলে, তাহলে বল তো আমার জীবনে এরপর কী হবে, মেয়েটা তখন বলে, সুন্দরী পঁচিশবর্ষীয়ার সঙ্গে আলাপ হবে আর ষাট বছরে গিয়ে বাচ্চা হবে, বোঝা যায় বাবার জীবন নিয়ে তার ক্ষোভ আছে। বাবা একটু বিরক্ত হয়ে শুতে চলে গেলে, মেয়েটা রসিকতার ঢঙে বলে, আগুনটা নিভিয়ে দেব, না কি তুমি এর পাশেই শোবে (কারণ স্লিপিং ব্যাগ আনেনি), বাবার বন্ধু তখন বলে, এক যদি না তুই আমায় গরম রাখার দায়িত্ব নিস। মেয়েটা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে, খুব ক্যাজুয়াল ঢঙে বন্ধুটা বলে, আমার তো হিংসে হয় তোর বাবাকে, কারণ তাঁবুতে তোর শরীরের উত্তাপটা আছে (যেন নিতান্ত পদার্থবিদ্যার প্রসঙ্গ তুলেছিল)। মেয়েটা কোনওমতে ‘জল আনতে যাচ্ছি’ বলে উঠে যায়। পরেরদিন যখন মেয়েটা বাবাকে বলে, ও আমাকে এমন একটা কথা বলেছে যেটা খুব অস্বস্তিকর, বাবা বলে, আরে ওর কথা ছাড়, মুখের কোনও আগল নেই, কোনও আক্কেল নেই, ওর কথা ধরতে আছে? মেয়েটা বলে, তা না, ও বলেছে, ওর তাঁবুতে আমি গিয়ে ওকে গরম রাখব কি না। বাবা বলে, তা ও যখন স্লিপিং ব্যাগ আনেনি, ওকেই ল্যাঠা সামলাতে হবে। মেয়ে বলে, কথাটা তা নয়। বাবা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, উফ, দিনটা কি আমরা ভাল করে কাটাতে পারি না? মেয়েটা কিছু না বলে বাবার সঙ্গে সাঁতার কাটে, আর পরে, বাবা ও তার বন্ধু যখন বিশ্রাম নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়েছে, ওদের ব্যাগে অনেকগুলো পাথর ঢুকিয়ে দিয়ে, একা বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গায় বসে কাঁদে, তারপর হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের গাড়িটার কাছে (হাইকিং শেষ হলে যেখানে আসতে হবে) যায়। বহুক্ষণ পরে বাবা ও বন্ধু আসে, বোঝাই যায় বাবা এই একলা চলে আসায় খুব ক্রুদ্ধ, কিন্তু মেয়েটা সেটাকে পাত্তাই দেয় না। তার ব্যবহারে বোঝা যায়, সেও কম ক্ষুব্ধ নয়। বাবা গাড়ি চালাতে বললে প্রথমে রাজি হয় না, পরে গাড়িতে ঢুকে কিছুক্ষণ দরজা লক করে রাখে, ওদের ঢুকতে দেয় না। তারপর ঢুকতে দিলে, বাবা ওর পাশে বসে কিছুক্ষণ ওর চোখ এড়ায়, তারপর একটা পাথর নিয়ে গাড়ির সামনের জায়গাটায় রাখে। ছবি শেষ।
এত অল্পভাষী ছবি প্রায় দেখা যায় না। ছবিতে একজন একটা মন্তব্য করেছে, যেটা নিগ্রহবাচক। এবং যার প্রতি করেছে, তার বাবা সেটা শুনেও কিছুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখায় না, কারণ সে বন্ধুর সঙ্গে সংঘাতে যাবে না। বাবার এই বিশ্বাসঘাতকতা মেয়েটাকে কতটা আঘাত করে, তা ওই একলা বেরিয়ে আসা, জঙ্গলে কান্না এবং ব্যাগে পাথর ভরে দেওয়ায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু সবকটাই এত অনুচ্চ, তার মধ্যে কোনও ফেটে পড়াই নেই। তার বাবা বন্ধুটার ম্যারাথন দৌড়নোর বা আরও ট্রেকিং করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অবজ্ঞাবাচক কথা বলতে বা বিদ্রুপবাচক হাসতে ছাড়ে না, আবার বন্ধুটা যখন রাত্রে তাঁবুর মধ্যে খাবার খেয়েছিল তখন প্রকাণ্ড রেগে বলে, ভাল্লুক বহুদূর থেকে খাবারের গন্ধ পায়, এখানে আমার মেয়ে আছে, তুই তাকে বিপন্ন করতে পারিস না। কিন্তু মেয়ে যখন বলে, সেই বন্ধু এমন কথা বলেছে, যা প্রবল অনুচিত ও অপমানজনক, তখন দেখা যায় তা নিয়ে বাবা সম্মুখ-সমরে যেতে খুব একটা উৎসাহী নয়। যদিও শেষ শটের এমন একটা মানে করা যায়: বাবা মেয়েটার প্রদত্ত শাস্তিটা বুঝতে পারে, ব্যাগে সে দেখেছে (হয়তো বন্ধুও) এই বাড়তি পাথরগুলো, এবং অন্তত একটা বয়ে এনেছে যাতে স্মারক হিসেবে সে রেখে দিতে পারে, যাতে নিজের কাছে ও মেয়েটার কাছে দোষটা স্বীকার করতে পারে। আবার এর মানে এও হতে পারে: বাবা এটাকে শাস্তি হিসেবে বোঝেইনি, ভেবেছে মেয়েটা অনেক পাথর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিয়ে আসতে চায়।
ছবি জুড়ে আমরা দেখেছি, মেয়েটার পিরিয়ড হয়েছে সেকথা দুই পুরুষ জানেও না এবং তার এই বারবার আড়ালে যাওয়া দেখে আন্দাজও করে না, বা অন্তত একবার জিজ্ঞেসও করে না, কী হয়েছে (বন্ধুটা একবার বলে, কী, প্রকৃতির কোলে হিসি হল?)। একেবারে পাশে পুরুষের দল এসে থেকে যাচ্ছে দেখে মেয়েটা যখন আপত্তি জানায়, বাবা সেটাকে পাত্তা দেয় না। বাবা ও বন্ধু তাদের গল্পে বহুকাল আগের এক এইরকম হাইকিং-এর কথা বলে, যেখানে কেন কে জানে তাদের এক সঙ্গিনী (ওই বন্ধুরই বান্ধবী) মাঝপথে হাইকিং ছেড়ে কাউকে কিছু না বলে চলে গেছিল। কেন আচমকা সে দল ছেড়ে চলে গেল, তাদেরই কোনও অসংবেদী আচরণে আঘাত পেয়ে কি না, তা নিয়ে এরা কোনওদিনই ভেবেছে মনে হয় না, বরং সে হাওয়াই চটি পরে হাইক করতে এসেছিল, তা নিয়ে এদের হাসি খুব। নারী সম্পর্কে (এমনকি সেই নারী নিজ সন্তান হলেও) দিব্যি অমনোযোগী থেকে ফুরফুরে জীবন কাটিয়ে যায় পুরুষেরা, আর নারীকে ভাল (গুড ওয়ান) হয়ে থেকে যেতে হয়, সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকেও, অপমান মেনে নেওয়ার দিক থেকেও। বাবাকে যখন মেয়ে গিয়ে নালিশ করে, বাবা মেয়েকে যা বলে, তার মর্মার্থ হল, একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে হইচই পাকিয়ে দিনটাকে (এবং আমাদের সফরটাকে, এবং আমাদের বন্ধুত্বটাকে) নষ্ট করে দিস না। মানে, দোষটা বন্ধুর যতটা, তিলকে তাল করার জন্য তার চেয়ে বেশি দোষ মেয়েটার। খুব আলগোছে, খুব আলতোভাবে প্রায়ই পুরুষেরা নারীবিদ্বেষ ও নারী-উপেক্ষা ছড়িয়ে যায়, অধিকাংশ সময় মেয়েরা তাতে যোগ দেয়, আর কেউ খ্যাচখ্যাচ করলে তাকে ডাকা হয়: বেরসিক। মেয়েটা বাবাকে কিছুই বলে না, অভিমানে ও অপমানে বেরিয়ে আসে এবং সম্ভবত বুঝতে পারে, ওই একটা বাক্য তাকে প্রাপ্তবয়স্কা করে দিয়েছে, যা পিরিয়ডের অভিজ্ঞতাও করতে পারেনি। এবার থেকে হয়তো মেনে নিয়ে নিয়ে দিন যাবে মেনে নিতে।
দুটো ছবিই নারী নিয়ে কথা বলে, আর তা করতে গিয়ে একবারও গলা চড়ায় না। দুটো ছবিই মেয়েটার মুখে ঝুঁকে থাকে আর বাকিদের ধারেপাশে রাখে, মন্তব্য হালকা জলরঙে করে, যা নজর এড়িয়ে যেতেই পারে। দুটো ছবিই আন্দোলন করতে ব্যস্ত নয়, চরিত্রদের কান্নার ঢোক গেলার ভঙ্গিটা ধরতে তন্ময়। ‘নেভার রেয়ারলি…’ শুরু হয় একটা গান দিয়ে (নায়িকা গাইছে), ‘He’s got the power’, যে প্রেমের গানের শুরুই হয়, ‘He makes me do things I don’t wanna do/ He makes me say things I don’t wanna say…’। মূল গানটা ‘দ্য এক্সাইটারস’ যে উত্তেজনাপূর্ণ ভাবে গেয়েছে, তা বদলে, এখানে প্রায় একটা দুঃখের গান হিসেবে গাওয়া হয়। আর ‘গুড ওয়ান’ শেষ হয় কনি কনভার্স-এর একটা গান দিয়ে, ‘Talking like you’, যা শুরু হয় এভাবে: ‘In between two tall mountains/ There’s a place they call Lonesome…’। এই বিষণ্ণ একাকিত্বের গান শেষ হতে একটা পুরুষকণ্ঠে প্রশ্ন শোনা যায়, এটা কবে লিখলে? হয়তো মেয়েটা বড় হয়ে কখনও নিঃসঙ্গতার গান লিখবে, যে বোধের শুরু এই সফরে।




