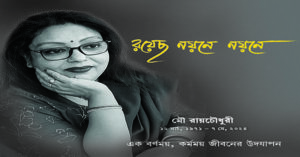পরিবহণের মাধ্যম যেমন, সেরকম বাহন-সংস্কৃতি তথা সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানও বটে হলুদ ট্যাক্সি। যার সঙ্গে যাত্রীর সম্পর্ক এবং ব্যবসায়িক চলন-বলনে ধরা পড়ে বিশেষ জীবনভঙ্গি। কলকাতার ‘ট্রান্সপোর্ট সিগনেচার’ হলুদ ট্যাক্সির পপুলেশন হাজারসাতেক। যার মধ্যে সামান্য কম-বেশি সাড়ে চার হাজারই বয়সজনিত কারণে বাতিল হবে ২০২৫-এ। বয়স ১৫ বছর হওয়ায় আদালত নির্দেশ দিয়েছেন, এদের বাধ্যতামূলক অবসর নিতে হবে। ফলে মুছে যাবে কলকাতার এক বিশেষ ঐতিহ্য। হারিয়ে যাবে চিরতরে, সেইসব হলুদ ট্যাক্সির গায়ে লেখা কথা ও ছবিরা। যাদের নাম দিয়েছি, যথাক্রমে বাহনলিপি ও বাহনচিত্র। প্রসঙ্গত, লোকসংস্কৃতির এই বিশেষ শাখার বহু নমুনা অবশ্য ইতিমধ্যেই আমরা হারিয়েছি যথার্থ সংরক্ষণের অভাবে। তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে আমাদের স্বভাবসিদ্ধ উদাসীনতা।
এমতাবস্থায় দেখা যাক, আমার ব্যক্তিগত প্রায় সাড়ে তিন দশক বয়সি ঝোলা থেকে অতঃপর কী কী বেরোয়।
কলকাতায় হলুদ ট্যাক্সি চালু হয়েছিল ১৯০৬ সাল নাগাদ। এই ক্লাসিক আইকনের গায়ে আমার জানা সবচেয়ে প্রাচীন লিপিটি ১৯৪৭ কি ’৪৮-এর হবে। এর সন্ধান পেয়েছিলাম আমার প্রয়াত বাবা মোহিনীমোহন দে-র কাছ থেকে। ভবানীপুরে তাঁর দেখা সেই লিপিটি ছিল জায়মান স্বাধীনতার জয়গানে মুখর: ‘আমরা স্বাধিন, নই কো মোরা ব্রিটিশের অধীন’। পাশে জাতীয় পতাকার ছবি। দীর্ঘ ‘ঈ’ হ্রস্ব রূপে হাজির ছিল— সেটা লিপিকারের অজ্ঞতা, না কি উত্তেজনাবশত— তা জানার অতীত।
আরও পড়ুন : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে গ্যালারির ভাষা!
লিখছেন জয়ন্ত চক্রবর্তী…
বাবার কাছ থেকে পাওয়া, নানা জায়গায় তাঁর দেখা আরও কিছু হলুদ ট্যাক্সিলিপির নমুনা: ‘পিতামাতার আশীর্বাদ ও দান’ (১৯৬৭); ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ (১৯৭১) বাংলা কবিতাচর্চার লোকায়ত প্রয়োগ; স্বাজাত্যাভিমান থেকে উৎসারিত ‘আমরা বাঙালী, দেশমাতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছি’ (১৯৬৯); দেশপ্রেম এবং/ অথবা রাজনৈতিক চেতনার চলমান লিপি ‘আমাদের দেশ আমরাই গড়বো’ (১৯৭৩); ভাষাপ্রেমের অমর ঘোষণা ‘বাঙলা আমার মায়ের ভাষা— আমি গর্বিত’ (১৯৭৫; পাশে রবীন্দ্রনাথের মুখাবয়ব, রেখাচিত্রে); মহানায়ক উত্তমকুমারের মুখের ছবি (১৯৭৬); ব্যক্তিবিশেষের পর্যবেক্ষণ ‘বড়লোক কখনো গরীবের বন্ধু হয়না’ (১৯৮৩) রাজনৈতিক শ্রেণিসচেতনতার কথা বলছে; মানুষের জয়গান ‘আমরা করবো জয় নিশ্চয়’ (১৯৯১)!
এছাড়া হলুদ ট্যাক্সি কারবারের সঙ্গে জড়িত-সহ বিভিন্ন জনের সঙ্গে নানা সময়ে এ-বিষয়ে কথোপকথনের সূত্রে পেয়েছি আরও কিছু হলুদ ট্যাক্সি লিপির খোঁজখবর। সেরকম কয়েকটি হারানো বার্তা; ‘পড়াশুনো শেখো কিন্তু আগে মানুষ হও’ (১৯৬৪)— একালের সমস্যা সেকালেই উপলব্ধির রেডারে ধরা পড়েছিল; ‘দেশকে ভালোবাসো’ (১৯৬৮); ‘মানুষ মানুষকে ভালোবাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে’ (১৯৭৮)— তৎকালীন অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ; ‘India Wins World Cup Cricket 1983’ (2008); বল পায়ে মারাদোনার ছবিটি ১৯৮৬ মেক্সিকো ওয়ার্ল্ড কাপের কয়েক মাস পরে; নেলসন ম্যান্ডেলার রেখাচিত্রের নিচে লেখা ‘অন্ধকার আফ্রিকার মুক্তিসূর্য’ (১৯৮৫)।
লক্ষ করলে দেখা যাবে, মানুষের স্মৃতিপটে থেকে যাওয়া লিপিগুলো মূলত দেশপ্রেম, রাজনীতি-কেন্দ্রিক। সঙ্গে ছিল কৃতজ্ঞতাবোধ ও জীবনের অভিজ্ঞান, আটের দশকে এসে তাতে ঠাঁই পেল ক্রিকেট-ফুটবল। এর মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে এসেছে রূপোলি পর্দার নায়ক। মোটামুটি এটাই ছিল, গত শতাব্দীর আটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হলুদ ট্যাক্সির গায়ে লেখা নাগরিক অনুভূতির চালচিত্র। লিপিগুলো প্রায় সবই লেখা হত বাংলায়। কারণ, কলকাতায় ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ছিল বাঙালি। মালিকও বেশিরভাগই বাঙালি।
গুরুগম্ভীর লিপিরও দেখা মিলবে হলুদ ট্যাক্সির গায়ে। এই যেমন, ‘পাগলা রে, আমার আমার করিস কেন, গোটা দুনিয়াটাই তো তোর’; ‘When passing the road, See others from a distance’; ‘U have right, Others do have their right’; ‘পাগোল, মা কী তোর একার?/ এটা কি প্রাইভেট প্রপার্টি’; ‘Man cannot live without mankind’; ‘Let Us Do Something’; ‘জোর খাটাইবেন না, ভালবাসুন’…
রোজগারপাতিও ভালই ছিল। কিন্তু সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। মাথায় বদবুদ্ধি চাপল। ক্রমে উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে নানান বদগুণ (যেমন, যখন খুশি কাজে না-আসা, ইচ্ছেমতো চালানো, যাত্রী প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি) প্রকাশ পেতে লাগল বাঙালি ট্যাক্সিচালকদের কথাবার্তা আর ব্যবহারে। সমস্যার সমাধান করতে শিখ ড্রাইভারদের আহ্বান জানাল মালিকপক্ষ, তাদের দক্ষতা, সততা ও পরিশ্রম করার ক্ষমতার জন্য। সময়টা গত শতকের ছয়ের দশকের শেষ দিক।
ক্রমে পাঞ্জাবি ড্রাইভারদের ওপর নির্ভরতা বাড়তে থাকল কলকাতার ট্যাক্সি মহলের। মালিকও গাড়ি সারানো থেকে রক্ষণাবেক্ষণ, কাগজেপত্রের দেখভাল— সবটা সংশ্লিষ্ট শিখ ড্রাইভারের ওপর নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিত। এই আবহে ট্যাক্সির ক্যানভাসে হিন্দিতে লেখার চল শুরু হল। কলকাতার সঙ্গে আত্মিক টানেই গুরুমুখীর বদলে হিন্দিতে লেখার কথা চালকদের মনে এসছিল। অবশ্যি সবটাই যে তাঁদের মর্জিমাফিক লেখানো হত, তা নয়।
আমার দেখা (১৯৮৯) হলুদ ট্যাক্সির গায়ে প্রথম কবিতাটি ছিল কবীরের বচন।
ডিকির ঢাকনায় দেবনাগরী হরফে
‘গুরুদেব বিন জীবকী কল্পনা ন মিটে।
গুরুদেব বিন জীবকা ভলা নাহী।’
অর্থ: গুরু ছাড়া জীব অর্থাৎ মানুষের কল্পনা অপূর্ণ থেকে যায়। গুরু ব্যতীত জীবের ভাল হয় না।

তখনও আমাদের প্রিয় শহর কলকাতার আকাশ-খিলানে, রংছুট বিকেলে গজল শোনাত পড়ন্ত বেলার গলা-রোদ। এমন মায়াবী আলোয় চঞ্চল মন প্রণোদিত হয়েছিল লিখতে, ‘ছেঁড়াফাটা শহরের টানে পড়ে আছি মনেপ্রাণে’, (বেলঘরিয়া, ১৯৯৪) এমনটা ভাবতে ভাল লাগে। চৌকোণা ইটের পাঁজরে, আকাশচুম্বী টাওয়ারের খাঁচায় হাঁসফাঁস, উদয়াস্ত খাটা হলুদ ট্যাক্সি-কর্মীর পথেই লেখা সম্ভব— ‘আমার গাড়ির রঙ দেখে— আমার বিচার করিবেন না স্যর’ (গড়িয়াহাট, ১৯৯০)। এমন লেখা আমাদের সমচৈতন্যে হাতুড়ির উপর্যুপরি ঘা মেরে মনে পড়ায়, শঙ্খবাবুর ভাষায়, ‘এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা’।
রাস্তায় পড়ে থাকা প্রাগৈতিহাসিক আবর্জনার স্তূপ দেখেই কেউ হয়তো নাগরিক সমাজের উদ্দেশে লিখেছিলেন: ‘আমাকে ভালোবাসলে তোমরা এটা করতে পারতে না’! (জোকা, ২০০০)। কারও বক্তব্য অলংকারবর্জিত। ‘শহর পরিষ্কার রাখুন’ (১৯৯৭), ‘KEEP CALCUTTA CLEAN’ (১৯৯৫), আরেকটু সচেতন মনের কথা: ‘Be Green, Keep Clean’ (২০০৪); ‘সবুজ রক্ষা করুন’ (২০০৬)। হলুদ ট্যাক্সিলিপিতে পরিবেশ সচেতনতার চলমান লক্ষণ।
শব্দদূষণ সম্পর্কে পেয়েছি দু’টি লেখা: ‘HIGH SOUND DESTROY US’ (২০০১) এবং, ‘শব্দদূষণ করিবেন না, ভাল থাকুন’ (২০০৮)। বনসৃজনের আহ্বান জানিয়ে লেখাটিও চমৎকার: ‘Plant Trees for U & Ur Child?’ (১৯৯৩)। শহর ঢুঁড়ে পাগলের মতো সবুজের খোঁজে: ‘শহরটা সবুজ হারিয়ে ফেলছে’ (২০০২)।
পিঠে বস্তা ময়লাবোঝাই এক কাগজ-কুড়ুনির রেখাচিত্র দেখেছিলাম, গোপালনগর থেকে হাজরা আসার পথে (১৯৯০)। অবশ্যই ব্যতিক্রমী বাহনচিত্র। সামাজিক হায়ারার্কিতে পেশায় কাগজ কুড়ুনির থেকে ট্যাক্সিমালিক বা চালকের অবস্থান অনেকটা উঁচুতে। এই বাহনচিত্র সেই প্রচলিত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে। এমন অসাড় মনের অধিকারীদের উদ্দেশেই হয়তো একদা লেখা হয়েছিল ট্যাক্সিপৃষ্ঠে: ‘ও রে পাগল, মনটা খোলসা কর রে’ (১৯৯১)। নিজেদের মস্তিতে শামিল করার আগে আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে ঘনীভূত লজ্জার মেঘ— এমন অমোঘ বার্তা ছড়িয়ে দেয় শেষোক্ত ট্যাক্সিলিপিটি।

‘বৃষ্টিতে আমায় পাবে না’ (১৯৯৭)— বহু অর্থবোধক এই লিপিটি পেয়েছিলাম বরানগরের কাছে। যদিও সেটা ছিল ডুবুডুবু কলকাতায় স্যাঁতসেতে আষাঢ়। বৃষ্টির প্রসঙ্গ এসেছে আরেকটি ট্যাক্সির সামনের বনেটের ওপর: ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান পাবি মেপে’ (১৯৮৮)। প্রচলিত লোকছড়ার লাইন বিশেষ উৎকলিত হলেও ‘দেব’ শব্দের জায়গায় ‘পারি’-র ব্যবহার যেখন কৌতূহলজনক, তেমনি এতে লিপিকারের ইনভলভমেন্টের ব্যাপারটিও লক্ষ্যণীয়।
‘Long Live Calcutta’ (১৯৯৩), ‘কলকাতা তুমি চিরদিনের’ (২০০৯), ‘অমর শহর কলকাতা’ (২০০৬)— এসবই কলকাতার প্রেমের চলমান বহিঃপ্রকাশ। এরপরে যখন দেখি কোনও হলুদ ট্যাক্সিচালক কিংবা তার সওয়ারি জানলার কার নামিয়ে টুক করে পিচকিরির আলপনা এঁকে দেয় প্রিয় শহরটার বুকে-মুখে; মুহূর্তে শান দেওয়া চপারের আঘাতে-আঘাতে স্মৃতিচ্ছিন্ন হয় স্নায়ু!
‘Please keep Safe Distance’; ‘দূরত্ব বজায় রাখুন’, ‘ট্রাফিক আইন মেনে চলুন’, ‘অযথা হরন বাজাইবেন না’, ‘Please use indicator’-এর মতো কেজো ট্যাক্সিলিপিগুলো মূলত দেখবেন পিছনদিকে ডিকির ঢাকনার গায়ে হাতলের ওপরের অংশে লেখা থাকে। পিছনের গাড়ির ড্রাইভারের উদ্দেশে। তাকে সজাগ করতেই, তার চেতনায় ঘা মারতেই এমন আয়োজন। কেন? উত্তরটা ট্যাক্সিলিপির ভাষাতেই দেওয়া যাক, ‘সাবধানের মার নেই’।
অন্যান্য বাহনলিপির মতো ট্যাক্সিলিপিতেও লিপিকারের স্খলন চোখে পড়বেই, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজেই বানানের যে হাল মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে, সেই তুলনায় এ তো কিছুই নয়। তবে বানানের চেহারা দেখে মাঝেমধ্যেই ইচ্ছে করে, তার রূপকারকে যদি একবার চোখের দেখাও দেখা যেত। এইসব ক্ষেত্রে যেমন— ‘কোল্কাতা’, ‘তাঁড়ে’ (দ্রষ্টব্য : ‘তাঁড়ে আমি চোখে দেখিনি’), ‘Pls’, ‘দুরুত্বো’, ‘Kip’ (অর্থাৎ, keep), ‘safe’ বোঝাত ‘Sef’, ‘distance’-এর জায়গায় ‘dhistance’— প্রতিভার বিস্মিত স্বাক্ষর এক-একটা। এবং হলুদ ট্যাক্সিলিপিই পারে এমন রং বিলোতে। মন্ত্রমুগ্ধ নিসর্গে জেগে থাকে ওরা শব্দেরই পিলসুজ হয়ে!
ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করার সময় যাত্রী মানসিকাতায় জাগরুক থাকে সাধারণত এই ভাব— ভাড়া দিয়ে ট্যাক্সি চড়ি। সুতরাং, অশ্রদ্ধা-অযত্নে নিজের ইচ্ছেমতো বন্ধ করা যায় ‘গাড়ির পাল্লা’। এজন্য ড্রাইভারের দিকেরটা বাদে বাকি তিনটে দরজায় বা তাদের কোনওটাতে লেখা থাকতে দেখে থাকবেন: ‘দরজা আস্তে ঠেলুন’ (বন্ধ করুন), ‘CLOSE DOOR SOFTLY’ কিংবা হিন্দিতে, ‘দরওয়াজা ধীরে সে বন্ধ করিয়ে’। তবে বলার ধরনের জন্য বিশেষভাবে মনে গেঁথে গেছে এই ট্যাক্সিলিপিটি, ‘দরজা বন্ধ করায় মানুষের পরিচয়’ (২০০০)।
লক্ষ্যণীয় বিষয়, ট্রাম, দোতলা বাস, রিকশা যতটা শিল্প-সাহিত্যে জায়গা পেয়েছে; তার ছিটেফোঁটাও জোটেনি হলুদ ট্যাক্সির কপালে। ব্যাপারটা ভাবার মতো। একটা কারণ হতে পারে, ট্যাক্সিচালকদের যাত্রী প্রত্যাখ্যান এবং মিটারের বদলে মর্জিমাফিক ভাড়া দাবি করার দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতি।
ট্যাক্সির সামনের অংশে বনেটের ওপর আঁকা থাকে নানান মজার ছবি। যেমন টিনটিন, নন্টে-ফন্টে, রকমারি ক্যারিকেচার। এসবই আসলে পথচলতি ফ্রি বিনোদন, মুহূর্তের হাসি-মশকরার ফুসকুড়ি। মা দুর্গা, মা কালী, গনেশ, শিবলিঙ্গ, শিবের সুখ, শিব-পার্বতী, রক্তজবা প্রকৃতিও আঁকা থাকতে দেখা যায়। এসব এখন ট্যাক্সির রিয়ার স্ক্রিনেও থাকে।
গুরুগম্ভীর লিপিরও দেখা মিলবে হলুদ ট্যাক্সির গায়ে। এই যেমন, ‘পাগলা রে, আমার আমার করিস কেন, গোটা দুনিয়াটাই তো তোর’; ‘When passing the road, See others from a distance’; ‘U have right, Others do have their right’; ‘পাগোল, মা কী তোর একার?/ এটা কি প্রাইভেট প্রপার্টি’; ‘Man cannot live without mankind’; ‘Let Us Do Something’; ‘জোর খাটাইবেন না, ভালবাসুন’; ‘হরি বোল! ফাঁকতালে করাল গোল!’; ‘যে যাইবার, সে যাইবে, আটকাইবার চেষ্টা বৃথা’; ‘Never play in unknown place’; ‘U cannot teach someone, if he don’t want to learn samething’; ‘পাবার হলে এমনি পাবে’।
পূর্বোক্ত লিপিগুলোর আপাত গাম্ভীর্য, ন্যারেশন, কৌতুকের (কিছু কিছুতে) মধ্যে রয়েছে গভীর জীবনবোধ, দর্শনের ছোঁয়া, শিল্পিত মনন ও ভাবনার চলন। এর অভিনবত্বে রয়েছে চিরন্তন মানুষের অতলান্তিক জীবনধর্ম। ডাগর সে লিপিসাগর!
লক্ষ্যণীয় বিষয়, ট্রাম, দোতলা বাস, রিকশা যতটা শিল্প-সাহিত্যে জায়গা পেয়েছে; তার ছিটেফোঁটাও জোটেনি হলুদ ট্যাক্সির কপালে। ব্যাপারটা ভাবার মতো। একটা কারণ হতে পারে, ট্যাক্সিচালকদের যাত্রী প্রত্যাখ্যান এবং মিটারের বদলে মর্জিমাফিক ভাড়া দাবি করার দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতি। নিজেদের টিকে থাকাটাই যখন বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন, তখনও এর অন্যথা হচ্ছে না। সেই সঙ্গে তো রয়েছেই দূরে যাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত অনীহা। বস্তুত হলুদ ট্যাক্সি আর ট্রমা সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই এই বিরূপ ইমেজ কালি-কলম-ইজেলের ডগায় আসার পথে— হলুদ ট্যাক্সির প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তবুও মানতে দ্বিধা নেই, হলুদ ট্যাক্সিলিপির মধ্যে রয়েছে বোধ, কল্পনা, আশাভঙ্গ, আকাঙ্ক্ষার যাপনচিত্র। ট্রাম সম্পর্কে জীবনানন্দ বলেছিলেন, ‘ফিলোজফার’স কার’; হলুদ ট্যাক্সিকে কলকাতার ভিস্যুয়াল আর্ট বলার মতো কেউ ছিলেন না, নেই। সে কী আমাদের ক্লীবতা? আমাদের অভিজ্ঞতার কেলাসিত ও শুদ্ধ রূপে একবিন্দু কলঙ্ক?
হলুদ ট্যাক্সির শৌর্যময় চলা আজ অতীত। তবুও অবলুপ্তির হাত থেকে তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে এ-রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। সময়ের ঘাত-প্রতিঘাত সামলে মূর্তিমান সহ্যের এই প্রতিমাই ভুল ইংরেজিতে হলেও লিখতে পারে— I love Kolkata, Kolkata love me. (2009)
এই অমোঘ লিখন এমন এক বাস্তব, অথচ অদৃ্শ্য মনোজাগতিক ভ্রমণের কথা বলে, যে ভ্রমণপ্রতিমার অবস্থান লোরকার সুররিয়ালিজম এবং র্যাঁবোর কল্পিত ভ্রমণের মাঝামাঝি।