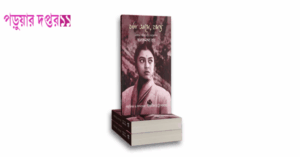সুভাষ মুখোপাধ্যায় পেশাগতভাবে ডাক্তার। এমবিবিএস পাস করেন কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে পিএইচডি—বিষয়, রিপ্রোডাকটিভ ফিজিওলজি। দ্বিতীয় পিএইচডি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, বিষয় রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রিনোলজি। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজি বিভাগে কাজ করার সময় তিনি গবেষণা শুরু করেন ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন নিয়ে। বলাই বাহুল্য, এ-দেশে এ-বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ।
রবার্ট এডওয়ার্ডস ও প্যাট্রিক স্টেপটোর হাতে প্রথম টেস্টটিউব বেবি জন্ম নেয় ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই। আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার ফসল টেস্টটিউব বেবি জন্ম নেয় ওই একই বছরের অক্টোবর মাসে— পৃথিবীর দ্বিতীয় টেস্টটিউব বেবি— এমন এক দেশে, যেখানে এ-বিষয়ে গবেষণার ঐতিহ্য, পরিবেশ, ধারণা কিংবা পরিকাঠামো, কিছুই ছিল না। ১৯৭৮ সাল, ৩ অক্টোবর— কলকাতা দূরদর্শনে দুপুর ১১:৪৪-এ ঘোষিত হয়েছিল প্রথম ভারতীয় টেস্টটিউব বেবির জন্মগ্রহণের খবর। কথাগুলো অনেকেই জানে।
সাফল্যের পরপরই মিডিয়া ঘোষণার পাশাপাশি তিনি সুসংবাদটি ভারতের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ মহলে জানালেন, উপস্থিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিশেষজ্ঞরা তাঁর সাফল্যে যৎপরোনাস্তি চমৎকৃতও হলেন— তবু, নিজের কর্মক্ষেত্রে এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের শেষে তাঁর বরাতে জুটল সম্মান বা স্বীকৃতির পরিবর্তে অবিশ্বাস। তদানীন্তন রাজ্য সরকার তাঁকে সম্মানিত করার পরিবর্তে বসাল তদন্ত কমিশন। এসবও সবাই জানে।
আরও পড়ুন : বিনোদিনীর সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন গিরিশচন্দ্রই…
তো সেই তদন্ত-কমিশনের বিচার্য—
১. ডাঃ মুখোপাধ্যায় দাবি করছেন, তিনি ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের মাধ্যমে দুর্গা নামক শিশুর কারিগর। এ কি সত্য?
২. তিনি দাবি করছেন, সাধারণ কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্যেই তিনি এত বড় যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তাঁর দাবি, মাতৃগর্ভে প্রতিস্থাপনের পূর্বে তিনি নিষিক্ত ডিম্বাণুটি রেখেছিলেন নিজের বাড়ির ফ্রিজে। এ কি আদৌ সম্ভব?
৩. সরকারি হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার হিসেবে তাঁর দায়িত্ব এমন আবিষ্কারের কথা সর্বাগ্রে সরকারকে জানানো— আমলাদের কাছে গবেষণার রিপোর্ট পেশ করা। তা না করে তিনি সরাসরি মিডিয়ার কাছে চলে গেলেন কেন?
৪. নিজের কার্যকলাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তিনি বারংবার নিজের গবেষণাকে সত্য বলে দাবি করেই চলেছেন। এ কি ঔদ্ধত্য নয়?

গবেষণার সত্যতা যাচাই করার জন্যে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি বসল, তার নেতৃত্বে ছিলেন এক রেডিওফিজিসিস্ট তথা অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট (ডাঃ মৃণালকুমার দাশগুপ্ত— পরবর্তীকালে, এই কমিশনের প্রধান হিসেবে কাজ করার জন্য তিনি লোকচক্ষে ভিলেন বনে গেলেও মানুষটি সত্যিই গুণী, নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার যোগ্য অথচ বঞ্চিত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অন্যতম)। কমিটিতে একজন স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ থাকলেও আইভিএফ-সংক্রান্ত গবেষণার ন্যূনতম অভিজ্ঞতা আছে, এমন কেউ-ই ছিলেন না। অবশ্য তেমন কাউকে পাওয়াও মুশকিল হত— কেননা, সেসময় এদেশে এমন গবেষণার কথা কেউ-ই ভাবেননি। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের বিচার করতে যাঁরা বসলেন, তাঁদের মধ্যে খুব কম জনই একটি মানব-ভ্রূণ ঠিক কেমন দেখতে হয়, সে-বিষয়ে অবহিত ছিলেন। অতএব, প্রশ্ন বলতে যা যা করা হয়েছিল, তা অত্যন্ত বোকা বোকা এবং শ্লেষপূর্ণ।
প্রত্যাশিতভাবেই ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ‘ভণ্ড’, ‘ধাপ্পাবাজ’ ও ‘মিথ্যেবাদী’ হিসেবে প্রমাণিত হন। কলকাতা থেকে দূরের বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে তাঁকে আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গবেষণা চলেছিল তার মধ্যেই। কিন্তু ধাপ্পাবাজ হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার পরে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়— ওই বছরেরই ২৮ ডিসেম্বর, যে-কোনও বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের আগাম অনুমতি গ্রহণ তাঁর জন্য আবশ্যক করা হয়।

১৯৭৯ সালের শুরুতে জাপানের কিয়োটো শহরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা বিষয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৬ ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন স্বাস্থ্য-অধিকর্তা তাঁর জাপানযাত্রার অনুমতির আর্জি নাকচ করেন— এবং এও জানান, কোনও কারণেই যেন ডাঃ মুখোপাধ্যায় দেশ ছাড়ার কথা না ভাবেন। এই আঘাত সামলাতে পারেননি তিনি— কিছুদিনের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। শারীরিক অসুস্থতার কারণে সরকারের কাছে বাড়ির কাছাকাছি বদলির আর্জি জানালেন, এবং কী আশ্চর্য, চটপট আর্জি মঞ্জুরও হয়ে গেল! কলকাতা মেডিকেল কলেজের পাশেই রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজি-র ইলেকট্রোফিজিওলজি-র প্রফেসর হিসেবে বদলির নির্দেশ এল।
দিনটা ১৯৮১ সালের ৫ জুন। আর পারছিলেন না তিনি। সব দরজা তাঁর সামনে বন্ধ হয়ে আসছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, তাঁর গবেষণার কথা তিনি আর কখনওই সকলের সামনে জানিয়ে উঠতে পারবেন না, কেননা সরকার তাঁকে কোনও বড়সড় সম্মেলনে যোগ দিতে দেবে না। এতদিন ধরে তেমন বড়মাপের কোনও জার্নালে তিনি নিজের গবেষণার কথা প্রকাশ করতে পারেননি, কেননা প্রথম সাফল্য খুব মিঠে হলেও গবেষণার ধাপগুলো আরেকবার পুনরাবৃত্তি করে না-দেখা অবধি সেটি বৈজ্ঞানিক নির্ভরযোগ্যতা পায় না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বুঝলেন, সে-সুযোগও তিনি আর পাবেন না, তাঁকে বদলি করা হয়েছে এমন এক বিভাগে, যেখানে বসে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব, সেই বিভাগ তাঁর গবেষণা থেকে বহু দূরের ব্যাপার এবং তাঁর আজীবন কাজের সঙ্গে এই নতুন কর্মক্ষেত্রর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

আর সত্যিই পারলেন না তিনি। ১৯৮১ সালের ১৯ জুলাই। বদলির অর্ডারের ৪৪ দিনের মাথায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় আত্মহত্যা করেন। সুইসাইড নোটে লেখা ছিল, কবে হৃদরোগ এসে আমায় মুক্তি দেবে, তার জন্য আর প্রতিদিন অপেক্ষা করে থাকতে পারলাম না। হ্যাঁ, এই আত্মহত্যার কথাও সকলেই জানেন— বিশেষত রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস ও তপন সিংহর অসামান্য চলচ্চিত্রের সুবাদে।
মৃত্যুর পর ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ভুলেই গিয়েছিলেন সবাই, শুধুমাত্র হাতে-গোনা কয়েকজন বাদে। যেমন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজির অধ্যাপক সুনীত মুখোপাধ্যায় এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ সরোজকান্তি ভট্টাচার্য (প্রথম টেস্টটিউব বেবির পিছনে এঁদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল)। ১৯৮৬ সালের ৬ আগস্ট আইসিএমআর এবং মুম্বই কেইএম হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে আইভিএফ পদ্ধতিতে জন্ম নেওয়া হর্ষকে দেশের প্রথম টেস্টটিউব বেবি এবং সেই টিমের নেতা ডাঃ আনন্দকুমার-কে পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে সেই সামূহিক বিস্মৃতিতে সিলমোহরও পড়েছিল।
১৯৯৭ সাল। ডাঃ আনন্দকুমার ততদিনে দেশের প্রথম টেস্টটিউব বেবির জনক হিসেবে স্বীকৃত, খ্যাতির শিখরে তিনি। কৃত্রিম গর্ভধারণ বিষয়ক জাতীয় সম্মেলনের আসর সে-বছর কলকাতাতেই। সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ বক্তা তিনি। উপস্থিত কয়েকজন প্রতিনিধি সেই সম্মেলনে একান্তে তাঁর হাতে তুলে দিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা-সংক্রান্ত ব্যক্তিগত নোটস। স্তম্ভিত এবং চমৎকৃত হয়ে গেলেন তিনি।
আর সত্যিই পারলেন না তিনি। ১৯৮১ সালের ১৯ জুলাই। বদলির অর্ডারের ৪৪ দিনের মাথায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় আত্মহত্যা করেন। সুইসাইড নোটে লেখা ছিল, কবে হৃদরোগ এসে আমায় মুক্তি দেবে, তার জন্য আর প্রতিদিন অপেক্ষা করে থাকতে পারলাম না। হ্যাঁ, এই আত্মহত্যার কথাও সকলেই জানেন— বিশেষত রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস ও তপন সিংহর অসামান্য চলচ্চিত্রের সুবাদে।
দেশকে আনন্দকুমারই জানালেন, এক বিস্মৃত বিজ্ঞানীর কথা৷ জানালেন, ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুধু বিশ্বের দ্বিতীয় টেস্টটিউব বেবি তথা দেশের প্রথম টেস্টটিউব বেবির জনকই নন, বেশ কিছু বিষয়ে সারা বিশ্বেই তিনি পথিকৃৎ।
১. পিতার শুক্রাণু কম হলেও কীভাবে আইভিএফ সম্ভব, সে-বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিকা জারি করার দু-বছর আগেই ঠিক একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন ডাঃ মুখোপাধ্যায়।
২. এডওয়ার্ডস-স্টেপটো ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করেছিলেন স্বাভাবিক ঋতুচক্রের সময় মেনে। ১৯৮১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা প্রথম ওভারিয়ান স্টিমুলেশন পদ্ধতি অনুসরণ করে আইভিএফ করেন, এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্ব জুড়ে সেই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়। জানা গেল, এ-বিষয়ে পথিকৃতের স্বীকৃতি প্রাপ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরই, কেননা বিশ্ব জুড়ে এখন যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়, সেই হরমোন দিয়ে ওভারিয়ান স্টিমুলেশন সর্বপ্রথম করেছিলেন তিনিই।
৩. এডওয়ার্ডস-স্টেপটো ডিম্বাণু সংগ্রহ করেছিলেন জটিলতর ল্যাপারোস্কোপির সাহায্যে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় অনুসরণ করেছিলেন সহজ পদ্ধতি— যোনিপথে ছোট ছিদ্র দিয়ে অনেক কম সময়ে সম্ভব কম জটিল সেই পদ্ধতি। সেই পদ্ধতি বিশ্ব জুড়ে জনপ্রিয় হয় অনেক পরে— যোনিপথে (ট্রান্সভ্যাজাইনাল) আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বহুল প্রচলিত হওয়ার পরে এখন ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয় যে-পদ্ধতিতে, সেটির সঙ্গে ডাঃ মুখোপাধ্যায় অনুসৃত পদ্ধতির হুবহু মিল।
৪. হরমোন দিয়ে ওভারিয়ান স্টিমুলেশন পদ্ধতিতে ডিম্বাণু সংগ্রহ করে বিশেষ দ্রবণের মধ্যে রাখা শুক্রাণুর সাহায্যে নিষেক ঘটানো— নিষিক্ত ডিম্বাণুটি প্রাথমিক দশার ভ্রূণে রুপান্তরিত হলে তাকে ফ্রিজে তুলে রাখা— পরবর্তী স্বাভাবিক ঋতুচক্রের উপযুক্ত সময়ে ফ্রিজ থেকে ডিম্বাণু বের করে সেটিকে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এনে গর্ভে প্রতিস্থাপিত করা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই পদ্ধতিই এখন অনুসৃত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র। হিমাঙ্কের নিচে ভ্রূণ সংরক্ষণ, হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা নামানোর জন্য উপযুক্ত যে রাসায়নিক উপাদান, প্রতিটির জন্যই কোনও না-কোনও বিজ্ঞানী দুনিয়া জুড়ে পথিকৃতের স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ডাঃ মুখোপাধ্যায় সেই কাজ করে গিয়েছেন তাঁদের ঢের আগে।
আনন্দকুমারের নিরন্তর প্রয়াসে ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় অন্তত মরণোত্তর স্বীকৃতিটুকু পেলেন। জাতীয় স্তরে, এবং পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীদের তালিকায় তাঁর নাম ইদানীং পরিগণিত হয়। একথাও মোটামুটি নিশ্চিত, সময়ে বিশ্বের দরবারে পেশ হলে রবার্ট এডওয়ার্ডসের সঙ্গে সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন আমাদের ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও, স্বাধীনোত্তর দেশের প্রথম বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার— কেননা, আইভিএফ বিষয়ে তাঁর গবেষণা চলছিল এডওয়ার্ডস-স্টেপটোর সঙ্গে একই সময়ে এবং তাঁর পদ্ধতি ছিল এডওয়ার্ডসদের চাইতে উন্নততর।
তবু কেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এমন করুণ পরিণতি? ক্ষমতাবানের ঔদ্ধত্য, সরকারি আমলাদের সবজান্তা মানসিকতা, সহকর্মীদের ঈর্ষা ইত্যাদি তো ছিলই— তার বাইরেও কিছু কথা রয়ে যায়।
বিজ্ঞানের আবিষ্কার আচমকা আকাশ থেকে পড়ে না। প্রদীপ জ্বলে ওঠার আগে সলতে পাকানোর পর্যায় থাকে, প্রদীপে তেল ঢালার পর্ব থাকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এই পর্বগুলো এতখানিই লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পন্ন হয়েছিল, প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল বিস্ময়, এবং সেখান থেকে অবিশ্বাস।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় গবেষণা বিষয়ে এমন গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিলেন কেন?
সময়টা মনে করুন। সে-সময় ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। বিশ্ব জুড়ে সব উন্নয়নশীল দেশেই তাই। ১৯৭৫ সালে সঞ্জয় গান্ধীর, জরুরি অবস্থার সুযোগে, বহুলনিন্দিত জোর করে ভ্যাসেকটমি করানোর কথা মনে করুন। সে-সময় গর্ভধারণ সংক্রান্ত যা গবেষণা চলছিল, তার প্রায় প্রতিটিরই লক্ষ্য ছিল, গর্ভধারণ বন্ধ করার পথ খোঁজা। অর্থাৎ, গবেষণা চলছিল নতুন গর্ভনিরোধকের সন্ধানে। এমতাবস্থায় বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা বা কৃত্রিম গর্ভধারণ সংক্রান্ত গবেষণা প্রায় রাষ্ট্রের লক্ষ্যের বিপ্রতীপ। স্বাভাবিকভাবেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়দের গবেষণা চলেছিল কিছুটা গোপনে। পরবর্তী ক্ষেত্রেও গবেষণার কিছু ধাপ আর-একবার খুঁটিয়ে দেখে আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করা অবধি ডাঃ মুখোপাধ্যায় নিজের গবেষণার যাবতীয় তথ্য সকলের সামনে আনতে চাননি। রাজ্য সরকারকে তিনি নিজের গবেষণার সারমর্ম জানিয়েছিলেন অবশ্যই। কিন্তু বিশদ তথ্য তৎক্ষণাৎ জানানোর ব্যাপারে কিছু অসুবিধের কথা জানিয়েছিলেন, যা শেষমেশ তাঁর বিষয়ে অবিশ্বাসকেই আরও গাঢ় করে তুলেছিল।
সুতরাং, সরকারি ঔদ্ধত্য, হৃদয়হীনতা, সবজান্তা মনোবৃত্তি এবং সহকর্মীদের তীব্র ঈর্ষা— এসবের পরেও কিছু ফ্যাক্টর ছিল, যা এক যুগন্ধর বিজ্ঞানীর স্বীকৃতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
তবু ভারতে বসে গবেষণা করে এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে যা অতি-বিরল (না কি নজিরবিহীন?) ঘটনা— তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ ভুলব কী করে? আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই পরিণতি যে কত তরুণ গবেষককে এ-দেশে গবেষণার ভবিষ্যৎ বিষয়ে সন্দিহান করে তুলল, কত প্রতিশ্রুতিবান তরুণ-তরুণীকে গবেষণার স্বপ্ন চোখে নিয়ে পশ্চিমমুখী করল— তার হিসেব কে রাখে!