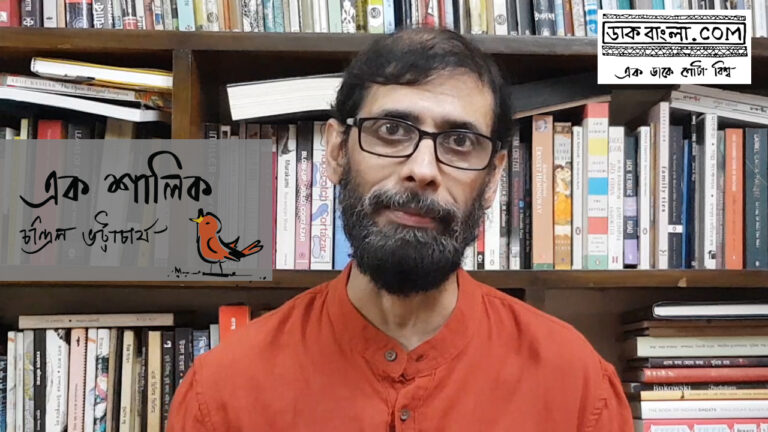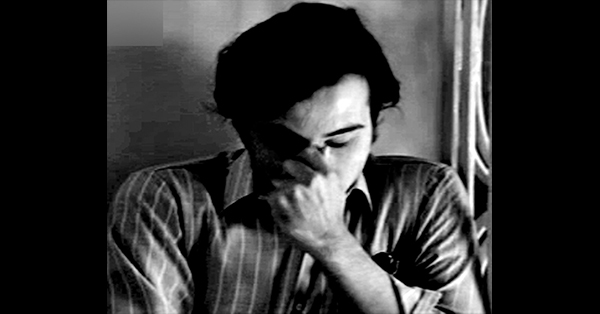ছায়াবাজি : পর্ব ৩৮

 চন্দ্রিল ভট্টাচার্য (May 23, 2025)
চন্দ্রিল ভট্টাচার্য (May 23, 2025)দুই নেকড়ে
একই থিমে এবং প্রায় একই নামে যখন অনেকগুলো ছবি তৈরি হয়, আমরা ভাবি, পরের ছবি আগের ছবির চেয়ে ভাল হবে। ধারণার কোনও ভিত্তি নেই, শুধু এই আশা ছাড়া: যত দিন যায়, মানুষ বুদ্ধিমান হয়, আগের ঠিক-ভুলগুলো খতিয়ে দেখে। কিন্তু এই বছরের ‘উলফ ম্যান’ ছবি (চিত্রনাট্য: লেই হোয়ানেল, করবেট টাক, পরিচালনা: লেই হোয়ানেল, ২০২৫) আবারও প্রমাণ করল, আগের লোকের চেয়ে পরের লোকের প্রতিভা বা বুদ্ধি বেশি হবে, মানে নেই।
এই ছবিতে, গল্পটা বলে ফেলার তীব্র তাড়াহুড়ো দেখে বিস্ময় ঘটে। হরর ফিল্মে পরিবেশটাকে গড়ে তুলতে হয়, এবং শুধু স্পেশাল এফেক্টের ওপর ভরসা না করে, চরিত্রগুলোকেও তৈরি করতে হয়। ভয়ের জিনিসটাকে হুড়মুড়িয়ে এনে ফেলে পেল্লায় তুর্কিনাচন গোড়া থেকেই লাগিয়ে দিতে হবে, এই দায় পরিচালকের কাঁধে কেউ ন্যস্ত করেনি। এমনিতে নিয়ম হল, একেবারে প্রথম দৃশ্যে একটা ভয়ানক কিছু ঘটাও, যাতে দর্শক চমকে ওঠে এবং সিধে হয়ে বসে, তারপর নাম-টাম দেখিয়ে ছবিটাকে ধরো, ধীরেসুস্থে ব্যাপারটা বলো, কীসে ভয়, কেন ভয়, মূল চরিত্ররা কে মুখচোরা, কে প্রেমলিপ্সু— তা-ও, তারপর আসল ভয়ের নাগরদোলাটা চালাতে শুরু করো।
কিন্তু এই ছবি কোনও ধৈর্য রাখায় বিশ্বাসই করে না। গোড়ায় দেখানো হয়, শিকার করতে বেরিয়ে এক বাবা তার ছেলেকে দু’বার বকাবকি করে। প্রথমবার ছেলেটা বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতার দিকে হাত বাড়াচ্ছিল এবং বাবার সতর্কীকরণ মন দিয়ে শুনছিল না। দ্বিতীয়বার, বাবার কাছছাড়া হয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল হরিণ মারার লোভে। দ্বিতীয় বকুনিটা একটু বেশিই ঝাঁঝালো, কিন্তু যেখানে ছেলে ভুল করলে একেবারে মরে যেতে পারে, বন্য জানোয়ারের কবলে পড়তে পারে (এবং অন্য এক ভয়াল মনস্টারেরও— নেকড়ে-মানুষ— যাকে নিয়ে এই ছবি), সেখানে বাবা তো উদ্বেগের চোটেই ছেলেকে বকবে। তবু এ-থেকে আমাদের বুঝে নিতে হবে, বাবা অত্যন্ত বদরাগী এবং ছেলে সদা-তটস্থ। দৃশ্যের শেষে নেকড়ে-মানুষ দু’জনকে প্রায় ধরে ফেলেছিল, পরের দৃশ্যে বাবা ঠিক করে, সে এই নেকড়ে-মানুষকে খুঁজে মারবে, নইলে তার ছেলে নিরাপদ নয়।

‘উলফ ম্যান’ ছবির দৃশ্য তারপরেই ছবিটা লাফিয়ে চলে যায় ৩০ বছর পরে, যখন ছেলেটা (তার নাম ব্লেক) বড় হয়ে গিয়েছে এবং সেও তার মেয়েকে বকছে, কারণ মেয়েটা রাস্তার ধারে একটা জায়গায় উঠে পড়েছে, সেখানে পথ-দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই বকুনি থেকে বুঝতে হবে, এর মধ্যেও প্রবল ক্রোধী মেজাজ প্রবাহিত হয়েছে। একটু পরে জানা যায়, ব্লেকের বাবা বহুদিন নিখোঁজ, এখন তার একটা মৃত্যু-সার্টিফিকেট এসেছে (এতদিন নিখোঁজ থাকলে ধরে নেওয়া হয়, সে মৃত), এইবার বউ-মেয়ে নিয়ে ব্লেক পুরনো বাড়িতে ফিরছে, বাবার জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্য। ব্লেকদের গাড়ি বাড়ি অবধি পৌঁছনোর আগেই সন্ধের ঝোঁকে নেকড়ে-মানুষ রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও ভয়াল ধুন্ধুমার চালু। এবং ‘উলফ ম্যান’-মার্কা ছবিগুলোর যা মূল ব্যাপার: নেকড়ে-মানুষ কামড়ে/আঁচড়ে দেওয়ার ফলে, ব্লেক-ও নেকড়ে-মানুষে পরিণত হতে শুরু করে।

‘উলফ ম্যান’ ছবির দৃশ্যে ক্রিস্টোফার অ্যাবট, জুলিয়া গার্নার ও মাটিলডা ফার্থ ফলে, ছবির প্রথম দ্বন্দ্ব হল: নিশুত রাতে পরিবারটাকে আক্রমণ করছে একটা নেকড়ে-মানুষ, আর তার খপ্পর থেকে নিজেকে ও বউ-মেয়েকে রক্ষা করতে চাইছে ব্লেক। আরেকটা দ্বন্দ্ব: ব্লেক নিজে নেকড়ে-মানুষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করছে মানুষের মতো থাকতে, ফলে তার নিজের ভেতরে নেকড়ে বনাম মানুষের লড়াই চলেছে। দ্বিতীয় লড়াইটাই মূল, কারণ ওটা হারলে তো এক নম্বর লড়াইটার অর্থই থাকে না। ব্লেককে নিজের ভেতরের নেকড়ে-সত্তাটাকে ঠেলে রেখে, মানুষ-সত্তাটাকে জাগিয়ে, বাইরের নেকড়ে-মানুষটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিবারকে বাঁচাতে হবে।
ক্রমে ব্লেকের মানুষের ভাষা বলার ক্ষমতা হারিয়ে যায়, ভাষা বোঝার ক্ষমতাটাও চলে যায়, দৃষ্টিশক্তি অন্যরকম হয়ে যায় (অন্ধকারেও দেখতে পায়), শ্রবণক্ষমতা অতি-প্রখর হয়ে ওঠে (মাকড়সার পদশব্দও হাতুড়ির আঘাতের মতো টের পায়), কিন্তু সে প্রাণপণ লড়ে নেকড়েত্ব দমন করে বাবা ও স্বামীর দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা চালায়। এক সময় তার ও নেকড়ে-মানুষের মুখোমুখি সংঘাত হয় এবং মারামারির শেষে নেকড়ে-মানুষের গলা কামড়ে-ছিঁড়ে সে বুঝতে পারে (মৃতের হাতের ট্যাটু দেখে), এই মনস্টারটা ছিল তার বাবা। মানে, বহুকাল আগে নেকড়ে-মানুষকে শিকার করতে বেরিয়ে, বাবা তার কামড় খেয়ে নিজেই নেকড়ে-মানুষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর ব্লেক হু-হু বদলে যেতে শুরু করে এবং বউ ও মেয়েকে ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকে, মা ও সন্তান হিংস্র, নৃশংস, রক্তকামী বাবার কাছে থেকে পালাতে থাকে। একসময় তারা মুখোমুখি হয়, ব্লেক তখন আক্রমণকারী, আর তার স্ত্রীর হাতে উদ্যত বন্দুক, আর ব্লেকের মেয়ে বলে, মা, বাবা চায় এসব শেষ হোক। মানে, ব্লেক নিজেকে এই পূর্ণ মনস্টার হিসেবে মেনে নিতে পারবে না। ব্লেক ঝাঁপায় ও আঁতকে উঠে স্ত্রী গুলি করে, ব্লেক মারা যায়। ভোর হয়ে যায় এবং মৃত মনস্টারের মাথায় হাত বুলিয়ে মা ও মেয়ে উপত্যকার সৌন্দর্যের দিকে হেঁটে যায়।
ছবিতে প্রচুর থরথর উত্তেজনা, অনেক ভয়, মার ও পাল্টা মার, আর অবশ্যই বহু বীভৎস কাণ্ড— একটা লোক জন্তুর মতো দেখতে হয়ে যাচ্ছে, তার চুল উঠে যাচ্ছে, নখ খসে পড়ছে, চোয়াল বেঁকে যাচ্ছে, সে রক্তবমি করছে, গরগর গর্জন করছে, নিজের হাত কামড়ে খাচ্ছে। ভেবে দেখতে হবে, ছবিতে দুটো প্রিয়জনহত্যা আছে। ছেলে বাবাকে খুন করছে, স্ত্রী স্বামীকে। আমরা ভেবেচিন্তে এই মানেও পড়ে নিতে পারি: রাগ দমন করতে না পেরে এক বাবা শুধু তিক্ত, ক্রোধময় হয়ে উঠেছিল, তার প্রকাণ্ড শাসনে ঘৃণা বোধ করে ছেলে তার সঙ্গ ত্যাগ করে এবং গোটা পরিবারে তার প্রভাব এসে পড়ার সম্ভাবনা দেখে একসময় তাকে চিরনির্বাসিত করে। কিন্তু ছেলে নিজেও জিন বা শৈশব-পরিবেশের ক্রিয়ায় ঠিক ওইরকমই ক্রোধসর্বস্ব ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে। পরিবারকে রক্ষা করার মানসিকতাই, তাদের জন্য নিরন্তর ভয় পাওয়ার প্রবণতাই তাকে উলটে নিপীড়নকারী করে তোলে, এবং স্ত্রী তখন মেয়ের প্রেরণায় তার সংশ্রব পুরোপুরি ত্যাগ করে। আবার এরকম মানে তৈরি না-করে নিয়ে, গল্পটা যা, সেভাবেও গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু যা-ই করি, মানতে হবে, গল্পটাকে যে ছবিতে স্রেফ একটা রাত্তিরের গল্প হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়, তাতে যে তাড়াহুড়ো ঘটে, ছবিটার সমস্ত মানবিক আবেদন মার খেয়ে যায়। একটা ছেলের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ভাল করে দেখানো না হলে, ‘যাকে হত্যা করলাম, সে আমার বাবা’ অনুভূতির ধাক্কাটাই বোঝানো যায় না। আর, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক দেখানোর কোনও সময়ই না পেলে, স্ত্রী স্বামীকে গুলি করে মারছে— সেই দৃশ্যের অভিঘাতও দর্শককে তেমন স্পর্শ করে না।
গোটা ছবি জুড়ে কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাচীন ইংল্যান্ড, পোড়ো প্রাসাদ, প্রাচীন বস্তু ডাঁই করা ও সিঁড়িতে মাকড়সার জাল জড়ানো মৃত আভিজাত্য, মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় আলোকিত অন্দর, চন্দ্রালোকিত গহন অরণ্য, ঘোড়ার উচ্চ হ্রেষা এমন পরিবেশ রচনা করে, ১৮৯১ সালের একটা পৃথিবী প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কাব্যের পটভূমি হয়ে ওঠে।
কিন্তু পাশাপাশি আমরা যদি দেখি ২০১০ সালের ‘দ্য উলফম্যান’ ছবিটাকে (চিত্রনাট্য: অ্যান্ড্রু কেভিন ওয়াকার, ডেভিড সেল্ফ, পরিচালনা: জো জনস্টন, ২০১০), তখন বুঝব, একই গল্প কী নিপুণভাবে বোনা যায়! যদিও সে ছবিটা একেবারে চলেনি ও পেল্লায় নিন্দিত হয়েছিল, কিন্তু তার গল্প এবং বলার স্টাইল— দুটোই রীতিমতো ভাল। সে ছবিতে, যুবক লরেন্স অভিনয় করে বেড়ায় কিন্তু ভাইয়ের নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে ফিরে আসে আদি বাড়িতে, যা এক জরাজীর্ণ প্রাসাদ। একরকমভাবে বলা যায়, তার বাবার সঙ্গে পুনর্মিলন হয়। ছোটবেলায়, এক পূর্ণিমার রাতে, বাইরে বেরিয়ে লরেন্স দেখেছিল, তার মা’র রক্তাক্ত দেহ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বাবা। এরপর মানসিকভাবে লরেন্স এমন অসুস্থ হযে পড়ে, বাবাকে মনস্টার ভাবতে শুরু করে, তাকে মানসিক হাসপাতালে দেওয়া হয়। তারপর তাকে মাসির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এতদিনে সে ফিরল। বাবার অনুগত ভৃত্য সিং (একজন ভারতীয় শিখ) এবং বাবা এই প্রাসাদে থাকে, সঙ্গে এখন আছে ভাইয়ের বাগদত্তা (যার চিঠি পেয়ে লরেন্স এসেছে)। ভাই অবশ্য এখন আর নিখোঁজ নয়, তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে, ভয়াবহ ছিন্নভিন্ন, কে তাকে মেরেছে, তা নিয়ে গ্রামবাসীরা আলোচনা করে। কেউ বলে, জিপসিরা আসার ক’দিনের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটল, তাদের পোষা ভাল্লুক দায়ী। কেউ বলে নেকড়ে-মানুষের গল্প। লরেন্স একদিন জিপসিদের তাঁবুতে যায়, সেই সময়েই অনেকে মিলে জিপসিদের ভাল্লুককে ধরে নিতে আসে, সেই গোলমালের মধ্যে একটা আশ্চর্য জীব হানা দেয়, অনেককে মারে, আর লরেন্স তার পিছন পিছন বন্দুক নিয়ে ধাওয়া করায় লরেন্সকেও কামড়ে দেয়, কিন্তু জিপসি বৃদ্ধা সেই ক্ষত সেলাই করে, ওষুধ লাগিয়ে বাঁচায়। একজন জিপসি রমণী বলে, একে তো মেরে ফেলা দরকার, কারণ এ অভিশপ্ত, কিন্তু জিপসি বৃদ্ধা বলে, শুধু যে ভালবাসে, সে-ই একে মুক্তি দিতে পারে। পরের পূর্ণিমায় লরেন্স নেকড়ে-মানুষ হয়ে যায়, কয়েকজনকে মারে (তারা মনস্টারকে শিকার করতে জঙ্গলে বেরিয়েছিল), শেষে তাকে গ্রেফতার করা হয়, কারণ পুলিশের মতে, যে লোককে বহুদিন আগেই মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্য হাসপাতালে দিতে হয়েছিল, তার পক্ষেই এরকম কাণ্ড করা স্বাভাবিক। তাকে ফের ওই হাসপাতালেই দেওয়া হয়, মন-চিকিৎসক তার ওপর বহু পাশবিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে, তারপর একদিন লরেন্সের বাবা দেখা করতে এসে লরেন্সকে বলে, আমি ভারতে গিয়ে এক আশ্চর্য বালকের দেখা পাই, যে আমাকে কামড়ে দেয়, তারপর থেকে আমি প্রতি পূর্ণিমায় নেকড়ে-মানুষ হয়ে যাই। তুমি ঠিকই দেখেছিলে, আমিই তোমার মাকে হত্যা করেছিলাম, আমিই মনস্টার। প্রতি পূর্ণিমারাতে আমার ভৃত্য আমাকে তালাবন্ধ ঘরে বন্দি রাখে, কিন্তু ক’দিন আগে আমি তাকে পর্যুদস্ত করে বেরিয়ে যাই। আসলে তোমার ভাই বলেছিল, তার বাগদত্তাকে নিয়ে সে আলাদা থাকবে। আমি তাকে হারাতে চাইনি, মেয়েটিকেও না (মেয়েটিকে অনেকটা লরেন্সের মা’র মতো দেখতে। লরেন্সের বাবা এও বলে, মেয়েটি উষ্ণ আর গনগনে, চাঁদের মুখের মতো। বোঝা যায়, মেয়েটির প্রতি তার কামনা রয়েছে)। বাবার কথা থেকে এও বোঝা যায়, লরেন্সের ভাইকেও সে-ই মেরেছে। এরপর সে লরেন্সকে একটা ছুরি দিয়ে যায়, আত্মহত্যা করার সুবিধের জন্য, যদি লরেন্সের এই প্রায়ই মনস্টারে পরিবর্তিত হওয়া জীবনকে অসহনীয় মনে হয়।

২০১০ সালের ‘দ্য উলফম্যান’ ছবির দৃশ্য তারপর অনেক কাণ্ড ঘটে, লরেন্সের সঙ্গে ভাইয়ের প্রেমিকার প্রেম হয়, লরেন্স সবার সামনে পূর্ণিমারাতে মনস্টার হয়ে যায়, এবং শেষে একরাতে বাবা ও ছেলের লড়াই ঘটে, দু’জনেই তখন আধা-নেকড়েতে রূপান্তরিত, লরেন্স বাবাকে হত্যা করে, তারপর যখন ভাইয়ের প্রেমিকাকেও আক্রমণ করে, সে কাতরভাবে বলে আমার দিকে তাকাও, তুমি আমাকে চেনো, এবং লরেন্সের চোখের মণিতে মেয়েটির ছবি ফুটে ওঠে (তার মানুষী সত্তা মেয়েটিকে চিনতে পারে, ভালবাসা অনুভব করে) এবং সে মেয়েটিকে হত্যা করে না। বিনিময়ে, মেয়েটি লরেন্সকে হত্যা করে। লরেন্স মরার আগে ধন্যবাদ দিয়ে যায়।
গোটা ছবি জুড়ে কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাচীন ইংল্যান্ড, পোড়ো প্রাসাদ, প্রাচীন বস্তু ডাঁই করা ও সিঁড়িতে মাকড়সার জাল জড়ানো মৃত আভিজাত্য, মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় আলোকিত অন্দর, চন্দ্রালোকিত গহন অরণ্য, ঘোড়ার উচ্চ হ্রেষা এমন পরিবেশ রচনা করে, ১৮৯১ সালের একটা পৃথিবী প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কাব্যের পটভূমি হয়ে ওঠে। পিছনের বাজনা ও ক্যামেরা মিলিয়ে সারাক্ষণ ছমছমে একটা বিশ্ব তৈরি হয়, যেখানে হলঘরে বিজ্ঞান-বক্তৃতা চলাকালীনই চেয়ারে-বাঁধা মানুষ ক্রমশ জন্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এবং এখানে সযত্নে দেখানো হয়, বাবা-ছেলের সম্পর্ক, যা প্রথমে মনে হচ্ছিল ছেলের ফিরে আসার ফলে সুন্দর ও স্নিগ্ধ, পরে বোঝা যায়, উন্মাদ বাবা ছেলের প্রতি অত সস্নেহ নয়। দেখানো হয়, ভাইয়ের বাগদত্তার প্রতি আকর্ষণ, যা অপরাধবোধ মিশ্রিত। এমনকী, পুরাতন ভৃত্যের আনুগত্য বুঝতেও তার ঘরে লরেন্স যায়, তাকে জিজ্ঞেস করে, কেন এতদিন সে এখানে পড়ে আছে (উত্তর পায় না)।
ছবিটা তার পরিবেশ, চরিত্র রচনায় সময় দেয় বলেই আমাদের চেনা লোক মনস্টার হয়ে গেলে আমাদের কষ্ট হয়, মনে হয়, যেমন করে হোক পরিত্রাণের উপায় বেরলে ভাল। যখন জিপসি বৃদ্ধা বলে, মুক্তির একমাত্র পথ লরেন্সকে মেরে ফেলা, আমরা বিষণ্ণ হয়ে পড়ি। একটা-দুটো দৃশ্যে একটা লোককে দেখিয়ে সহসা তাকে নেকড়ে করে দিলে তার প্রতি সমবেদনা জাগে না, এভাবে চরিত্রটাকে দর্শকের প্রিয় করে তুলতে হয়। গল্পের অর্থ-প্যাঁচগুলোও খেয়াল করা ভাল, এখানে বাবা তার বউকে নিগ্রহ করে শুধু নয়, খুন করে, তারপর তা আত্মহত্যা বলে চালায়। বালক সন্তান তা দেখে ফেলেছিল বলে তাকে পাগল হিসেবে পৃথিবীর কাছে পরিচয় দেয়, তাকে হাসপাতালে ভরে দেয়, পরে মাসির বাড়ি আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয় (নির্বাসন বলা চলে)। পরে অন্য প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে যখন সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করবে ভাবে এবং অন্যত্র সংসার পাতবে ঠিক করে, তাকে হত্যা করে। অন্য ছেলে অনুসন্ধান চালাচ্ছে দেখে তাকেও হত্যা করছিল, লোক এসে পড়ায় পারে না, পরে তার রূপান্তর দেখে বাইবেল উদ্ধৃত করে বলে, এ তো অনুতপ্ত সন্তান ফিরে এসেছে (মানে, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শেষ করে পুত্র এবার পিতার আদেশানুসারে চলবে মনস্থ করেছে)। ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, এ-জিনিসের (চাঁদের প্রভাবে অমিত শক্তিধর হয়ে ওঠার) মহিমাই আলাদা, তাই না? আর উত্তরে লরেন্স বলে, মহিমান্বিত অবস্থা তো নয়, এ তো নারকীয়!
ফলে, এই আদর্শের সংঘাত, ধর্মগ্রন্থ আওড়ানো আত্মবিশ্বাসী শয়তান বনাম থতমত প্রেমিক-শিল্পীর যুদ্ধ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। ক্ষমতাবান জন্তু হওয়া উপভোগ করব, না কি নিজেকে বিনাশ করে দিয়েও মানবিকতার জয় চাইব— এই ছবিতে সেই ধাঁধা অনেক বেশি দপদপে। এক নির্মম নীতিহীন বাবা— যে নিজের স্বার্থ চরিতার্থের জন্য যে কোনও নীচ কাজ করতে এতটুকু পিছপা নয়, স্বজনহত্যা যার কাছে অভীষ্ট লাভের একটা পদ্ধতি, এবং উল্টোদিকে এক সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন সন্তান— যে তার সদ্য-নিহত মা’কে দেখে টালমাটাল হয়ে পড়ে, শেক্সপিয়রের বিভিন্ন নায়কের চরিত্র অভিনয় করে বিখ্যাত হয়, নিজেকে বিপন্ন করেও ভাইয়ের মৃত্যুর রহস্যভেদ করতে চায়, এই দু’জনের দ্বন্দ্বই ছবির দ্বন্দ্ব: একজন মনস্টার হয়ে খুশি, অন্যজন মনস্টার হয়ে বাঁচার তুলনায় অবসান মেনে নিতে ইচ্ছুক। ছবিতে মৃতা মা’র (এবং ইডিপাস গ্যাঁড়াকলের) ভূমিকাও কম নয়। একই নারীর প্রতি নায়কের আকর্ষণ, নায়কের বাবার আকর্ষণ এবং নায়কের অন্য ভাইয়ের আকর্ষণ কি এই সুতোয় বাঁধা নয়— সেই নারী মৃতা মহিলার মতো দেখতে, যে বাবার স্ত্রী ও ভাই
দু’জনের মা? বাবার কাছ থেকে পালিয়ে মা’র কাছে আশ্রয় নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই হয়তো দুই ভাইকে এই নারীর কাছে টেনে এনেছিল। আর বাবার হয়তো পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল জৈবিক ছটফটানি। ছবির শেষে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লরেন্স যখন বাবাকে মেরে ফেলে, আগুন লেগে গোটা প্রাসাদই ধ্বংস হয়, মা’র তৈলচিত্রটা আলাদা করে দেখানো হয়, যেন তা প্রতিশোধে উদ্ভাসিত। একটা লোকের বিকৃত ও স্বৈরাচারী মানসিকতার ফলে একটা বংশ ধ্বংস হচ্ছে (চারপাশের বহু লোকও, অনুগত ভৃত্যকেও ছাড় দেয় না বৃদ্ধ জমিদার), তবু বঞ্চিত সন্তান এসে শাসকের শাস্তি দিয়ে যাচ্ছে— এই গোছের বার্তা এ-বছরের নেকড়ে-মানুষওলা ছবি থেকেও পড়া যায়, কিন্তু তা কাহিনি-সমর্থিত হয় না, খুঁটিনাটি এসে তাকে রক্ত ধমনী ও মাংস দেয় না, শুধু কাঠ-কাঠ গণিত পড়ে থাকে, আর কিছু চেয়ার-লাফানি আতঙ্ক।
হরর-ফিল্মও যে আগে ফিল্ম, পরে হরর, সে-কথা ভুললে, ঘোড়ার গোড়ায় গাড়ি জুতে দেওয়া হবে।
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook