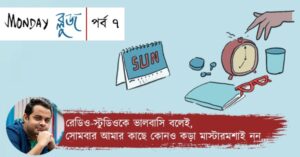পৃথিবীর সমস্ত ‘সৎ’ আন্দোলনই একটা শ্রেয়তর পৃথিবীর কামনায়। এই শ্রেয়তর পৃথিবীর সংজ্ঞা এবং উপাদান হয়তো বদলে যায় এক আন্দোলন থেকে আর-এক আন্দোলনে। দক্ষিণপন্থীরাও যদি সৎভাবে কোনও আন্দোলনে নামেন, সেই আন্দোলনের পিছনে থাকে তাঁদের চোখে যা আরও ‘ভাল’, আরও সমুচিত এমন কোনও দাবি। বামপন্থীরা তো বটেই। সুখের কথা এই যে, পৃথিবীর সিংহভাগেরও বেশি আন্দোলনই শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের দ্বারা অথবা তাঁদের জন্য সংগঠিত আন্দোলন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তরুণরাই যেহেতু যে কোনও প্রতিবাদ আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি, তাই তারুণ্যের সৃষ্টিশীলতাও স্বভাবতই প্রতিফলিত হয় আন্দোলনের ময়দানে। বিশেষত, একুশ শতকের পৃথিবীতে যেখানে মূল প্রতিযোগিতা মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা নিয়ে, পথের প্রতিবাদ আন্দোলনও যুগের দাবি মেনে প্রতিদিনই হয়ে উঠছে আরও রঙিন, আরও অভিনব, আরও চিত্তাকর্ষক। বাম, ডান, মধ্য— সব পন্থার আন্দোলনেই।
সম্প্রতি তুরস্কের এরদোগান-বিরোধী আন্দোলনে মিষ্টি হলদেরঙা পিকাচুর বেশে রাস্তায় নেমেছিলেন কেউ একজন। সেই ভিডিওর সত্যতা নিয়ে তোলপাড় হয়েছে সামাজিক মাধ্যম। তবে এ তো নতুন কিছু নয়৷ তুরস্কের ঘটনার অনেক আগেই ২০১৯ সালে চিলিতে দেখা গিয়েছে পিকাচু-আন্টিকে। পিকাচু ছাড়াও অন্যান্য এনিমে চরিত্র সেজেও রাস্তায় নেমেছেন আন্দোলনকারীরা। চোখে পড়েছে এনিমে এবং মাঙ্গার চরিত্র ও সংলাপ সংবলিত ব্যানারও।
আরও পড়ুন : ইলন মাস্কের স্বার্থবিরোধী প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না গ্রক! লিখছেন প্রতীক…
জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, এবং চীনের পপ কালচারের বেশ কিছু চরিত্র বা উপাদান জনপ্রিয়তার গুণে জায়গা করে নিচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন গণআন্দোলনে। যেহেতু এখনকার তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পপ কালচার— বিশেষত, জাপানি এনিমে, মাঙ্গা, ও দক্ষিণ কোরিয়ার কে-পপ খুবই জনপ্রিয়— এই উপাদানগুলির ব্যবহার কমবয়সিদের আবেগের কাছে আবেদন করছে সহজেই। এগুলি তরুণ প্রজন্মের আপাতভাবে রাজনীতি-বিমুখ অংশকেও আন্দোলনে টেনে আনতে সক্ষম হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ায় রাস্তার আন্দোলন থেকে নির্বাচনী প্রচার, সর্বত্রই দেখা গেছে কে-পপের লাইট-স্টিক। থাইল্যান্ড ও হংকংয়ের ওপর বেইজিংয়ের ‘কর্তৃত্ব’-র বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার ক্ষেত্রে যেসব বিচিত্র মিম বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে, তার মধ্যে রয়েছে সিধেসাধা দুধ-চা-র ওপর এক মিম— ‘ইন মিল্ক-টি উই ট্রাস্ট’। গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে নির্দিষ্ট নেতৃত্ববিহীন প্রতিষ্ঠান-বিরোধী আন্দোলনের একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে এই দুধ-চা। দুঃখের বিষয় হল, দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল এবং পাকিস্তানে বিভিন্ন ধারার গণআন্দোলনের রাজনীতি সুদীর্ঘকাল ধরে শক্তিশালী হলেও এগুলি এখনও আলোচনার পরিসরে উঠে আসে না। শ্রীলঙ্কা কিছুটা ব্যতিক্রম।

২০২০ সালে ব্যাংককের ডিমোক্রেসি মনুমেন্টের জমায়েতে কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে, হামতারো নামের এক ঝিকিমিকি চোখওয়ালা হ্যামস্টার। আসলে, জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যমের পরিচয় পেরিয়ে ন্যায়বিচার, অন্যায়ের প্রতিবাদ, ঐক্য, দারিদ্র্যমুক্তির সামাজিক দাবিগুলোর সঙ্গে মাঙ্গা ও এনিমের কাহিনিগুলোর সংযোগ পরিবর্তনকামী মানুষকে উদ্দীপিত করে তুলছে। এগুলি একুশ শতকের গণআন্দোলনের ভাষা৷ এই নতুন ভাষাকে পড়তে পারা জরুরি।

২০২০ সালে হংকংয়ের আন্দোলনে শামিল হয় পেপে নামের এক বিরসবদন সবুজ ব্যাঙও। সে কিন্তু কোনও এনিমে চরিত্র নয়। বরং সে পশ্চিমি বিশ্বের একটি মিম, যা ২০১৫ সাল নাগাদ দক্ষিণপন্থী শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদীদের একটি পছন্দের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। কার্টুনিস্ট ম্যাট ফিউরি, যিনি পেপে-র জনক, তাঁর অবশ্য এতে সায় ছিল না। হংকংয়ের আন্দোলনে পেপের ব্যবহার বরং তাঁকে সান্ত্বনা দেয়। এই ধরনের আশ্চর্য অর্ন্তঘাতও ঘটিয়ে ফেলছে সমকালীন গণআন্দোলনগুলি।
সিনেমা বা উপন্যাসের নানা চরিত্রও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে জ্বালানি জুগিয়েছে। ভিন্নধর্মী, সমকামী, অভিবাসীদের প্রতি নির্যাতন নামিয়ে আনা প্রোপাগান্ডিস্ট, ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জনপ্রিয় চিহ্ন গাই ফকের মুখোশ। ‘ভি ফর ভেন্দাত্তা’ ছবির শেষ দৃশ্যে পার্লামেন্ট বিস্ফোরণের মুহূর্তে শত শত মানুষের মুখ যখন বেরিয়ে আসছে সেই মুখোশের নিচ থেকে, সকলের বিস্মিত চোখে মূর্ত প্রশ্ন, কে ভাঙল এই স্বৈরাচারের ইমারত? উত্তর দিচ্ছে অন্তিম সংলাপ— সে আমার বাবা, আমার মা, আমার ভাই, আমার বন্ধু, সে তুমি, সে আমি। আজও যে-কোনও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এই মুখোশের উপস্থিতি চোখে পড়বেই।
বছরপাঁচেক আগে ট্রাম্পের অ্যান্টি-অ্যাবরশন বিলের প্রতিবাদে আমেরিকার মহিলারা রাস্তায় নেমেছিলেন মার্গারেট অ্যাটউডের হ্যান্ডমেইড’স টেইলের লাল লাল আলখাল্লায়। নারীর শরীর এবং যৌনতার ওপর সিস্টেমের অসহ্য দখলদারি বোঝাতে এই প্রতীকী পরিচ্ছদ বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা। তারও আগে হেলথকেয়ার বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেও এই সাজে নেমেছিলেন মহিলারা। ফ্রান্সে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গাত্মক প্রতিবাদ দেখাতে পুলিশের কস্টিউমের ওপর স্টার ওয়ারের স্টর্মট্রুপারদের মতো হেলমেট পরে মিছিল করেছিলেন প্রতিবাদকারীরা।
জনপ্রিয় টিভি সিরিজ ‘হাঙ্গার গেমস’-এর ভেতরে আছে অর্থনৈতিক বৈষম্যের গল্প। ২০১৪ সালে আমেরিকায় হ্যারি পটার অ্যালায়েন্স নামে পরিচিত এক সংস্থার সদস্যরা ওয়ালমার্ট, ম্যাকডোনাল্ডস প্রভৃতি বাণিজ্যিক সংস্থার কর্মীদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য ‘হাঙ্গার গেমস’-এর কায়দায় তিন আঙুলের স্যালুট করেছিলেন। দেশের সরকারের প্রতি অনাস্থা বোঝাতে এই একই মুদ্রার ব্যবহার বেছে নিয়েছিলেন থাইল্যান্ডের শিশু-কিশোররা।
২০১৯-এ লেবাননে অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে আন্দোলনকারীরা ব্যাটম্যান সিরিজের জোকার চরিত্রের মতো করে মুখ রং করে প্রতিবাদ করেছিলেন। গল্পের গথাম সিটিতে দুর্নীতি, অপরাধ আর মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে সমস্ত অর্থ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিল, আর তা বাধ্য করেছিল একজন ক্ষমতাহীন সৎ নাগরিককে নিষ্ঠুর জোকার হয়ে উঠতে। জোকার চরিত্রের বিশেষত্ব এখানে এই যে, মুখে রং না থাকলে জোকারকে কেউ গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু নিজের মুখের বীভৎসতা তাকে মানুষের চোখে আতঙ্কের বিষয় করে তোলে, যা তাকে দেয় মানুষের ওপর কর্তৃত্বের শক্তি। সরকারের জনবিমুখ রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তাই এই চরিত্রটিকে বেছে নিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। আবার এই রঙের নিচে প্রতিবাদকারীরা নিজেদের পরিচয়ও গোপন রাখতে পেরেছিলেন।
সিনেমা বা উপন্যাসের নানা চরিত্রও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে জ্বালানি জুগিয়েছে। ভিন্নধর্মী, সমকামী, অভিবাসীদের প্রতি নির্যাতন নামিয়ে আনা প্রোপাগান্ডিস্ট, ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জনপ্রিয় চিহ্ন গাই ফকের মুখোশ। ‘ভি ফর ভেন্দাত্তা’ ছবির শেষ দৃশ্যে পার্লামেন্ট বিস্ফোরণের মুহূর্তে শত শত মানুষের মুখ যখন বেরিয়ে আসছে সেই মুখোশের নিচ থেকে, সকলের বিস্মিত চোখে মূর্ত প্রশ্ন, কে ভাঙল এই স্বৈরাচারের ইমারত?
সম্প্রতি সুইডেনে প্যালেস্টাইনের সমর্থনে সংগঠিত মিছিলে ট্রাম্প আর নেতানিয়াহু সেজে হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলেন দু’জন। বাস্তবের ট্রাম্পও তো যেন কার্টুন জগতের থেকে জীবন্ত হয়ে ওঠা একটা খলচরিত্রই। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সংগঠিত করা ছাড়াও আসলে গণআন্দোলনের একটা অন্য ভূমিকা থাকে— তা হল অন্ধকার সময়ে মানুষকে নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা করে দেওয়া। আর সেজন্যই একটা শ্রেয়তর পৃথিবীর গল্প-বলা চরিত্ররা হয়ে উঠছেন আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
একুশ শতকের গণআন্দোলন, এমনকী, গণঅভ্যুত্থানের ভাষা বিশ শতকের থেকে পৃথক। যে ভাষায় কথা বলছে এই শতকের গণআন্দোলন, তার নিবিড় পাঠ ব্যতিরেকে এই সময়কে বোঝা কঠিন৷ বিশ শতকেই আমরা শুনেছিলাম, বিপ্লব বা গণঅভ্যুত্থান আদতে জনতার উৎসব৷ কিন্তু সেই উৎসবের ধরন সময় এবং স্থানভেদে বদলে বদলে যায়৷ একুশ শতকের গণআন্দোলনগুলি কথা বলছে নিজেদের ভাষায়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এই শতকের আন্দোলনের বিশেষ চরিত্র। বিশ শতকের চশমায় তাকে দেখতে চাওয়া ভুল-ই হবে।