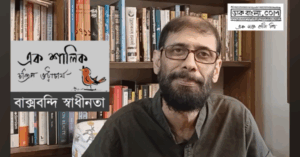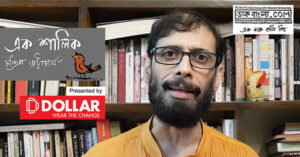এবার কাণ্ড ত্রিনিদাদে
অক্স টেল! বলে কী! অক্স টাং শুনেছি খুব উপাদেয় খাদ্য, খাইনি যদিও কখনও। এখানে টেবিলে সাজানো ছোট ছোট ওয়াইন গ্লাসে মহার্থ সুরায় ডোবানো ষাঁড়ের লেজের টুকরো। আর সেটা খেতে বলছেন কে? ব্রায়ান লারা!
না, এরকম পেট গরমের স্বপ্ন আমি দেখিনি। এটা সত্যি ঘটেছিল ২০০৭ সালের জানুয়ারির এক দুপুরে, পোর্ট অফ স্পেনে, স্বয়ং লারার বাড়িতে। সৌজন্যে অবশ্যই সফরসঙ্গী নামী ক্রীড়া সাংবাদিক, যাঁর দৌলতে ভিভ রিচার্ডস থেকে শুরু করে ব্রায়ান লারার বাড়ির দরজা আমাদের জন্য এক নিমেষে চিচিং ফাঁক! শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপের কার্টেন রেজার ‘ক্যারিবিয়ান ডায়েরি’ টিভি শোয়ের জন্য এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার থেকে একান্ত অন্দরমহল পর্যন্ত, যেখানে খুশি দাপিয়ে বেড়ায় ক্যামেরা। আপাতত আমরা রয়েছি প্রিন্স অফ পোর্ট অফ স্পেন-এর ডাইনিং টেবিলে। আদর করে এই নামেই তাঁকে ডাকে নিজের দেশ ত্রিনিদাদ তো বটেই, গোটা
ক্যারিবিয়ান্স।
যে টিলার ওপরে এই বাড়িটা, সেটা নাকি প্রাইভেট। সরকার তাঁকে সম্মান জানিয়েছে টিলাসমেত দোতলা প্রাসাদ উপহার দিয়ে। মনে পড়ে গেল, বেকার যুবক নীললোহিতের সাধ ছিল বান্ধবীকে টিলা উপহার দেবে! এই বাড়ির সামনের রাস্তাটা শহর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেছে আটলান্টিকের দিকে। কাছেই থাকেন দেশের প্রেসিডেন্ট আর প্রধানমন্ত্রী।
তপশ্রী গুপ্তর কলমে পড়ুন ‘ডেটলাইন’-এর আগের পর্ব…
এই প্রাসাদে লারা থাকেন, আবার থাকেনও না। নিজেই বলেন, ‘আই অ্যাম ভেরি কমফর্টেবল অ্যাট মাই ওন্ড রেসিডেন্স ইন দ্য সাবার্ব। মোস্টলি আই প্রেফার টু স্টে দেয়ার।’ আসলে উডব্রুক শহরতলিতে পৈতৃক বাড়িতে ১৪ বছর বয়স থেকে কেটেছে, সেলিব্রিটি হয়ে ওঠার পরও পুরোপুরি শিকড়টা ওপড়াননি সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন, এই মহাতারকা। কিন্তু তা বলে ভাববেন না, খুব সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত লারা।
যে বাড়িতে আমরা বসে আছি, সেটার সাজসজ্জা দেখলেই মালুম হয় কতটা শৌখিন এর মালিক। বাড়ির একটা অংশে মিউজিয়াম, লারার মেডেল, ট্রফি, ছবি, ব্যাট, বল, ক্রিকেট গিয়ার দিয়ে সাজানো, অন্যদিকটা বসবাসের জন্য। সাধারণ মানুষ ঢুকতে পারেন মিউজিয়াম দেখতে, আবার আর-একটা অংশ শুনলাম উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য খুলে দেওয়া হয়। লারার ম্যানেজার ঘুরে দেখালেন শোওয়ার ঘর পর্যন্ত। বাকিংহাম প্যালেসের থেকে কোনও অংশে কম মনে হল না। আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম, টেস্ট আর প্রথম শ্রেণি, দু’ধরনের ক্রিকেটেই রেকর্ডধারী মাচো হিরো ভদ্রলোকটি কতখানি উচ্ছ্বসিত নিচে পার্ক করা নতুন লাল টুকটুকে জাগুয়ার ই-পেস (তাঁর সব গাড়ির নম্বর প্লেটে লাকি জার্সির ৯ থাকতেই হবে) নিয়ে, পরমুহূর্তেই গদগদ গলায় বলছেন, মেয়ে সিডনি (তখনও ছোট মেয়ে হয়নি) এ-বাড়িতে আসার জন্য কীরকম বায়না করে।

ভাবছিলাম, সবারই তাহলে মুখোশের আড়ালে একটা মুখ থাকে, সময়সুযোগ এলে অজান্তেই শেষ বিকেলের নরম রোদ পড়ে অন্যরকম হয়ে ওঠে রক্তমাংসের মুখটা। হয়তো খুব অল্প সময়ের জন্য, তবু তো হয়। যেমন এখন হল এই গোধূলিবেলার রাজপ্রাসাদে। সবাই জানে, মাঠে লারা কতখানি মেজাজি, বেপরোয়া, আক্রমণাত্মক ব্যাটিং তাঁর ইউএসপি। মাঠের বাইরে কেমন, জানার সুযোগ হত না ত্রিনিদাদ পর্যন্ত না এলে। স্টিভ ওয়া তাঁর আত্মজীবনীতে লারা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, ‘হি ইজ চার্মিং, ভালনারেবল, এনডেয়ারিং, মুডি অ্যান্ড ইমপসিবল টু ওয়ার্ক আউট অ্যাট টাইমস অ্যান্ড এন্ডলেসলি ফ্যাসিনেটিং।’ পোর্ট অফ স্পেনে ইন্ডিপেন্ডেন্স স্কোয়ারের একটা দিকের নাম ব্রায়ান লারা প্রোমেনাড, সেখানে প্রচুর মানুষ যান বেড়াতে, কিন্তু তারুবা বলে একটা জায়গায়, ২০০৭ বিশ্বকাপের আগেই তাঁর নামে স্টেডিয়াম তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত একটা ম্যাচও আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।
মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন, লেখার শুরুতে অক্স টেল-এর গল্পটা। ভাবছেন, শেষ পর্যন্ত কি গলা দিয়ে নেমেছিল ওই আশ্চর্য বস্তুটি? সত্যি বলছি, স্বয়ং ক্রিকেট-সম্রাটের আপ্যায়নে আপ্লুত আমি হাতে ধরেছিলাম কাটগ্লাসের (না কি ক্রিস্টাল?) পাত্রটি, সামান্য চুমুকও দিয়েছিলাম রক্তাভ ওয়াইনে, কিন্তু খুব সাবধানে, যাতে ষাঁড়ের লেজের টুকরোটুকু কোনওভাবেই মুখে না ঢোকে। সংস্কারে নয়, অজানার আতঙ্কে। দেখলাম, গভীর আলোচনার অজুহাতে বিষয়টা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন নামী সাংবাদিক, আর ক্যামেরাম্যানের তো সবসময়ই দুটো হাত ব্যস্ত!
কথায় বলে, প্রয়োজন হল আবিষ্কারের জননী। কিন্তু বিদ্রোহ শিল্পের জননী, এমন কথা কেউ বলে না কেন? এই যে ভুবনজয়ী ক্যালিপসো মিউজিক, তা তো আসলে কৃষ্ণাঙ্গ দাসেদের মর্মবেদনার গান। ত্রিনিদাদের আখের ক্ষেতে কাজ করতে আসা ক্রীতদাসদের জীবনে কোনও আলো-বাতাসের জানালা ছিল না। এমনকী, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত বারণ ছিল। অন্যথা হলে পিঠে পড়ত চাবুকের ঘা। তারা তাই লুকিয়েচুরিয়ে গাইত ফেলে আসা দেশের গান, মাটির গন্ধমাখা সুরে খুঁজে পেতে চাইত হারানো আপনজনদের। পরে সেই সুর কণ্ঠে তুলে নিয়ে দুনিয়া জয় করেছেন হ্যারি বেলাফন্টে, মাইটি স্প্যারো।
আর কথা বলা বারণ তো কী? সসপ্যানের ঢাকনা বাজিয়ে একে-অন্যের সঙ্গে ইশারায় ভাব বিনিময় করত তারা। সেই থেকে জন্ম স্টিলপ্যানের। একে তো বলা যায় ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের জাতীয় বাদ্যযন্ত্র, ক্যালিপসো বা সোকা কনসাটের স্টেজ আলো করে থাকে যে সার দেওয়া ঝকঝকে স্টিলের প্লেটের মতো ইনস্ট্রুমেন্ট। ত্রিনিদাদের বিখ্যাত কার্নিভালের মাসখানেক আগে পোর্ট অফ স্পেনে যাওয়ার সুবাদে বেশ কয়েকটা রিহার্সাল দেখার সুযোগ হয়েছিল। গিটার বলুন কি ড্রামস, সবকিছুকে ম্লান করে দেয় স্টিলপ্যানের ঝংকার। ‘দুঃখ-সুখ দিবসরজনী/ মন্ত্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধুনি/ শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে/ ওরা কাজ করে।’
ভদ্রলোকের নামটা আজ আর মনে নেই। কিংবদন্তি গাভাসকরের প্রাণের বন্ধু। এবং গাভাসকরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হওয়ার সুবাদে আমাদের টিমলিডার তারকা সাংবাদিকের চেনা। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ত্রিনিদাদের মানুষটি নিপাট ভালমানুষ, আমাদের এক মুহূর্ত চোখের আড়াল না-করাটাকে তাঁর পবিত্র কর্তব্য বলে মেনেছেন। তিনি আমাদের জন্য যে হোটেলটা ঠিক করেছেন, সেটা আমার দেখা আশ্চর্যতম বাড়ি। আমি রিপ্লে-র বিলিভ ইট অর নট মার্কা উল্টো, তেড়াব্যাঁকা, হেলে পড়া মজাদার বাড়ির কথা বলছি না, থাকার যোগ্য বাড়ির কথা বলছি। দেশে-বিদেশে, কাজ অথবা নিছক বেড়ানোর কারণে অনেক ছোট-বড় হোটেলে থেকেছি। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা এখনও পর্যন্ত একবারই হয়েছে যেখানে লিফটে মাইনাস সেভেন বোতাম টিপতে হল। এয়ারপোর্টে আমাদের নিতে এসে ভদ্রলোক যখন হোটেলের নাম বললেন, আমরা ভিরমি খেলাম। খুবই নাম করা আন্তর্জাতিক চেন। ফিসফিস করে বলাবলি করলাম, ‘উনি কি আমাদের গাভাসকারের সমগোত্রীয় ভেবেছেন নাকি? এই হোটেল তো আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।’ লিডার গম্ভীরভাবে বললেন, ‘গিয়ে দেখাই যাক না ব্যাপারটা কেমন।’ গাভাসকার বিষয়ে একটি বই লিখেছেন তাঁর বন্ধু, গাড়িতেই সেটি দিলেন সাংবাদিক দাদাকে। উনিও সময় নষ্ট না করে বলে ফেললেন, ‘আমরা কিন্তু বাজেট হোটেলে থাকতে চাই।’ অল্প হাসলেন ভদ্রলোক, বললেন, ‘কমেই হবে।’ ঝাঁ-চকচকে হোটেলের রিসেপশনে দাঁড়িয়েও ভাবছিলাম, কোন ম্যাজিকে কম হবে ঘরভাড়া? ডিসকাউন্ট দিলেও সেটা আমাদের সাধ্যের মধ্যে হতে পারে কীভাবে? ভাবতে ভাবতেই শুনলাম উনি বলছেন, ‘সেভেন্থ ফ্লোরে দুটো রুম দেবেন।’
কথায় বলে, প্রয়োজন হল আবিষ্কারের জননী। কিন্তু বিদ্রোহ শিল্পের জননী, এমন কথা কেউ বলে না কেন? এই যে ভুবনজয়ী ক্যালিপসো মিউজিক, তা তো আসলে কৃষ্ণাঙ্গ দাসেদের মর্মবেদনার গান। ত্রিনিদাদের আখের ক্ষেতে কাজ করতে আসা ক্রীতদাসদের জীবনে কোনও আলো-বাতাসের জানালা ছিল না। এমনকী, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত বারণ ছিল। অন্যথা হলে পিঠে পড়ত চাবুকের ঘা।
লিফটে উঠে কেন মাইনাস সেভেন যেতে হল, সেটা বুঝলাম পরে। এই হোটেলটায় ন’টা ফ্লোর আছে। সবচেয়ে নিচের তলাটা নয় নম্বর। একটা পাহাড়ের গায়ে এমনভাবে তৈরি হোটেলটা যে তার প্রথম তলাটা শুধু মাথা বার করে আছে সুইমিং পুল, লন, ব্যাঙ্কোয়েট, লবিসমেত। বাকিটা মনে হবে যেন মাটির নিচে। আসলে কিন্তু পাহাড়ের ঢালে। জানালার পর্দা সরালে নিরেট পাহাড়ের দেওয়াল। যত নিচে নামবেন, তত দাম কম ঘরের। তাই দমবন্ধ লাগলেও (আসলে পুরোটাই মানসিক), বাজেটের মধ্যে হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।
সকালে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে মন ভাল হয়ে গেল। বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। মাসখানেক পরই ফেব্রুয়ারিতে ত্রিনিদাদের সবচেয়ে বড় পরব কার্নিভাল। তারই কার্টেন রেজার বলা যায়। সে যে কী রঙিন, কী ঝলমলে, কী চমকদার, কী বলব! হুতোম যদি ব্রাজিল বা ত্রিনিদাদের কার্নিভাল দেখতেন, কী আমোদই না পেতেন! কলকেতার রাজপথে চড়ক সংক্রান্তিতে জেলেপাড়ার সং-এর যে বর্ণনা আছে ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-য়, তাকে হাজার দিয়ে গুণ করলেও বোধহয় এর ধারেপাশে পৌঁছনো যাবে না। তাও তো আমরা আসল কার্নিভাল দেখার সুযোগ পাইনি, তার মুখবন্ধটুকু দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।
কতরকম পাখির পালক মাথায়, মুখে কত কিসিমের মুখোশ, আর পোশাক তো তাবড় স্টাইল স্টেটমেন্টকে তছনছ করে দেওয়া। এরকম কয়েকশো নারী-পুরুষের মিছিলে একদিকে রঙের বন্যা, অন্যদিকে শব্দের। স্টিলপ্যান থেকে ভুভুজেলা, বাজছে গমগম করে, সঙ্গে গান আর উদ্দাম নৃত্য। সেই জনস্রোত থেকে হাত বাড়িয়ে এক কৃষ্ণকলি আমাকে উপহার দিলেন বিশাল একটা পালক। পরে জেনেছিলাম, আগুনরঙা সেই পালকটি উটপাখির। ইচ্ছেমতো রং করে নিয়েছে। আমি যত্ন করে স্যুটকেসে ভরে সেই উপহার দেশে নিয়ে এসেছিলাম। বহুদিন ছিল সে কাপড়ের ভাঁজে। একসময় বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় ফেলে দিই। পরে আমাদের লোকাল গার্জিয়ান ভদ্রলোককে ধরে এক কার্নিভাল ম্যানেজারের ওয়ার্কশপে গেছিলাম। বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে দেখলাম, তৈরি হচ্ছে মুখোশ, কস্টিউম, প্রপস। মুখোশ দেখে পুরুলিয়ার চড়িদা গ্রামের কথা মনে পড়ল। ঘরে ঘরে ছৌ-এর মুখোশ তৈরিতে ব্যস্ত বাচ্চা, বুড়ো সবাই। সেগুলোও তো কম ঝলমলে নয়।
মাসক্যারেড, অর্থাৎ মুখোশধারীদের মিছিল। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ধরে। আঠারো শতকের শেষদিকে ক্যারিবিয়ান্সের ফরাসি-শাসিত দ্বীপগুলো থেকে দলে দলে লোক চলে আসে ত্রিনিদাদ-টোব্যাগোয়। তাদের মধ্যে যেমন ছিল আখ ক্ষেতের শ্বেতাঙ্গ মালিক, তেমনই ছিল নানা দেশের, বিশেষ করে আফ্রিকার ক্রীতদাসরা। গুড ফ্রাইডের আগে মাসখানেকের সংযম শুরুর আগেই সাহেবরা আয়োজন করে ফেলত মাসক্যারেড, সংক্ষেপে, মাস আর বল-এর। সেই নাচাগানা, খানাপিনার মোচ্ছবে অবশ্যই ব্রাত্য ছিল কৃষ্ণাঙ্গ দাসের দল। তারা নিজেদের মতো করে ছোট ছোট কার্নিভাল করত, যাতে আফ্রিকার লোকসংস্কৃতির ছাপ থাকত, যেমন ক্যালিপসো গান বা লাঠির লড়াই। সাহেবদের অনুকরণে মুখোশ পরার চলও ছিল। পরে যখন ব্রিটিশরা দাসপ্রথা তুলে দিল, মুক্তির আনন্দে জমকালো কার্নিভাল শুরু হল। আখের ক্ষেতের দুঃস্বপ্ন ভুলতে কার্নিভালের শুরুতেই আখ পোড়ানোর প্রথা চালু হল। আমাদের দোলের আগের সন্ধের ন্যাড়াপোড়ার মতো ত্রিনিদাদে কার্নিভালের আগের দিন এখনও হয় ‘বার্নট কেন’। তবে একসময় যেমন গায়ে তেল, কাদা, পাউডার মেখে সং হাঁটত মিছিলে, এখন আর তেমন দেখা যায় না। বদলে এসেছে ব্যঙ্গাত্মক বা কমেডি চরিত্রের সাজ, আর মেয়েদের পছন্দ জরি-চুমকি বসানো টু-পিস। মুখোশ কিন্তু রয়ে গেছে তার নিজের জায়গাতেই। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুখোশ এঁটে হাঁটছে, গাইছে, নাচছে মিছিলে। আর কে না জানে, প্রতিটা মুখের মতোই প্রতিটা মুখোশের গল্পও আলাদা!
সনাতন ধর্ম মহাসভা। রিপাবলিক অফ ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্যাগো-র সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সংগঠন। ভারত থেকে এসেছি শুনে সেখান থেকে আমন্ত্রণ এলেও, যাইনি আমরা। আসলে এই দেশে এত বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের বাস আর তাঁরা হিন্দুত্ব নিয়ে এত গর্বিত যে, মাঝে মাঝে শিকড়ের সঙ্গে দূরত্বটা ভুলে যান। এঁরা কীভাবে এলেন এই প্রবাসে? যখন ব্রিটিশ মুক্তি দিল আফ্রিকার দাসেদের, তারা আর কাজ করতে চাইল না আখের ক্ষেতে। বিপদে পড়ে ভারত থেকে আমদানি করতে হল শ্রমিকের দল। দালালেরা বলত, ‘চিনিদাত থেকে ডাক এসেছে, চিনির দেশে পয়সা কামানোর এই সুযোগ হাতছাড়া কোরো না।’
উনিশ শতকে ঝাঁকে ঝাঁকে ভারতীয় এল ত্রিনিদাদে। ফেরার টিকিটের বদলে চালাক শ্বেতাঙ্গ প্রভু তাদের প্রস্তাব দিল, জমি দিচ্ছি, থেকে যাও। এবং বেশিরভাগ ভারতীয় ত্রিনিদাদকেই স্বভূমি বানিয়ে থেকে গেল। পোর্ট অফ স্পেনে চারপাশে তাই হিন্দি শুনবেন, বলিউড সিনেমার পোস্টার দেখবেন, ক্যাবে উঠলে এফএম-এ বাজবে হিট ফিল্মি গানা। আর পথ-খাবারের স্টলে দাঁড়ালে জিগ্যেস করবে, কী খাবেন, ডাবলস্ না বস আপ শাট? ঘাবড়াবেন না। প্রথম আইটেমটা হল দক্ষিণি বড়া, সঙ্গে চানা, আর দ্বিতীয়টা তো ঘরের খাবার, পরোটা।