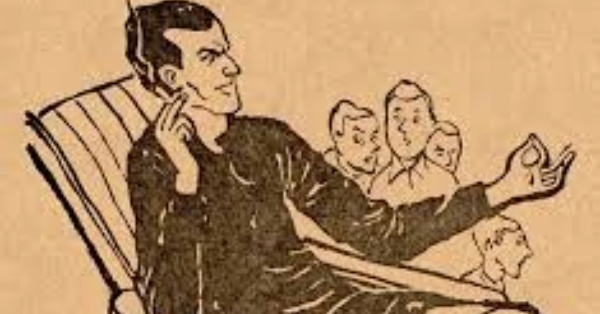ঘনাদার সঙ্গে যখন আমার প্রথম আলাপ, সে-সময়ে আমার বয়স নেহাতই কম। বয়স বছর তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ অথবা পঁয়তাল্লিশ হলেও, তাকে দাদা বলতে বাধা ছিল না, কারণ ঘনাদার আসল বয়স অনুমান করার চেষ্টা বৃথা। সময়টা ছিল গল্প বলার, গল্প শোনার। গল্প ছাড়া আর তেমন কিছুই ছিল না সেসময়ে। পাড়ার লাইব্রেরি ছিল রোজকার যাতায়াতের জায়গা। আর ছিল রেডিওতে শ্রুতিনাটক, গান, খবর, খেলার ধারাবিবরণী, ‘বিবিধ ভারতী’, ‘শনিবারের বারবেলা’, ‘বিশ্বরুপা থিয়েটার’-এর ‘শনি-রবি ও ছুটির দিন’-এর নাটকের বিজ্ঞাপন। আমার জীবনে তিন দাদার আবির্ভাব ওই একই সময়ে— টেনিদা, ফেলুদা আর ঘনাদা। আর প্রোফেসর শঙ্কু। ঠিক দাদা না হলেও, শঙ্কুর সঙ্গে অনেক মিল পেতাম ওঁর উত্তরসূরি ঘনাদার। তবে ঘনাদার মতো অবাক করা, তাক-লাগানো গল্প বলার ধরন ছিল না শঙ্কুর। শঙ্কু ডায়েরি লিখছেন, ঘনাদা স্মৃতি থেকে বলছেন নানা সময়ে, বিশ্বজুড়ে তাঁর নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প। অবাক হয়ে শুনেছে, ৭২ বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির বাসিন্দা শিবু, শিশির, গৌর আর সুধীর। আর আমাদের মতো অবাক হয়ে থাকা পাঠকরা। যারা সারাদিন গল্পের আশায় বসে আছি হাঁ করে।
গত দুশো বছর ধরে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই, যেখানে তিনি যাননি, হেন ঘটনা ঘটেনি, যার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই। সেই ঘনাদার গল্প। গল্প না গুল্প, সেটা বিচার করার কোনও তাগিদ নেই আমাদের। হোক না ‘টল টেলস’, আমাদের কাছে সবই বিশ্বাসযোগ্য। তাকলাগানো গল্প হলেই হল। আর সেই গল্প শুনে, পড়ে যদি বাঙালি বিশ্বভ্রমণ করতে পারে মনে মনে, জানতে পারে অনেক না-জানা বিজ্ঞানভিত্তিক, ভৌগোলিক তথ্য আর ঐতিহাসিক ঘটনা, ক্ষতি কী? তবে আজকের প্রজন্মর মুঠোফোনের বন্দিদশা ঘুচলেই ঢুকতে পারা যাবে সেই আড্ডা আর গল্প শোনার, গল্প বলার দুনিয়াতে। না হলেই মুশকিল।
আরও পড়ুন : রামায়ণ-মহাভারত শুধু কাহিনির জোরেই ধর্মগ্রন্থ হল না, হয়ে উঠল মহাকাব্য! লিখছেন জয়া মিত্র…
প্রেমেন্দ্র মিত্র-র পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কের সুবাদে তাঁর লেখা সম্বন্ধে জেনেছি অনেক অজানা কথা। যেমন, ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক’ পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তিনি। ঘনাদার বিশ্বপরিক্রমার অনেকটাই লেখা হয়েছে তাঁর নিয়মিত ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক’ পত্রিকা পড়ার অভ্যাস থেকে। সব জায়গায় সশরীরে উপস্থিত থেকে নয়। যদিও নানা সময়ে, বিশ্বের নানা দেশ ঘুরেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, কিন্তু সব দেশে যাননি। এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প মনে পড়ে। সম্ভবত, সাহিত্যিক সমরেশ বসুর একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে থাকার কথা বেশ কিছুদিন। তিনি এলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র-র কাছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁকে আমেরিকার কোন জায়গায়, কোন রাস্তার মোড়ে কোন দোকান আছে, সেখানে কোন জিনিসের দাম কীরকম, কোন বাড়িতে ভাড়া থাকা যেতে পারে ইত্যাদি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে দিয়েছিলেন, যেন তিনি সেখানে থেকেছেন বহুদিন। আসলে আমেরিকা গেলেও, সেই বিশেষ জায়গায় কখনও, কোনওদিনই যাননি তিনি। সমস্তটাই বই আর পত্র-পত্রিকা পড়ে মনে রেখে দেওয়া। আর প্রয়োজনে ব্যবহার করা। এছাড়া ঘনাদার গল্পের সমস্ত ভৌগোলিক আর বৈজ্ঞানিক তথ্য একেবারে প্রমাণিত সত্য। আবার পরবর্তীকালে পৃথিবী জুড়ে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে, যার হদিশ পাওয়া যায় এত বছর আগে লেখা ঘনাদার গল্পে।
৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির বাসিন্দা শিবু, শিশির, গৌর আর সুধীর আসলে শিবু, মানে বন্ধু, সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী। শিশির, বাংলা ছবির প্রযোজক ও অভিনেতা, ‘বসুমতী চিত্র প্রতিষ্ঠান’-এর সহ প্রতিষ্ঠাতা শিশির মিত্র। গৌর, অভিনেত্রী কাবেরী বসুর দাদা গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। তিনিও ‘বসুমতী চিত্র প্রতিষ্ঠান’-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা আর সুধীর, স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্র-র ডাকনাম। প্রেমেন্দ্র মিত্র থাকতেন কালীঘাটের উল্টোদিকে ভবানীপুরের ৫৭ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট-এ (এখন প্রেমেন্দ্র মিত্র সরণি)। পাশেই সরু গলি গোবিন্দ ঘোষাল লেন। সেখানেই এক সময়ে একটি বাড়িতে থাকতেন বিমল ঘোষ বা ‘টেনদা’। প্রেমেন্দ্র মিত্র-র পরিচিত এই বিমল ঘোষের আদলেই তৈরি হয়েছিল ঘনাদা। আর গোবিন্দ ঘোষাল লেনের নাম গল্পে হয়ে যায় কল্পনার বনমালী নস্কর লেন। ঘনাদার বেশিরভাগ গল্পের সূত্রপাত এখান থেকেই। বেশিরভাগ গল্পের নাম দুই অক্ষরের।
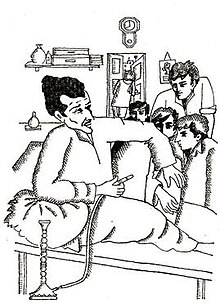
শুনেছি, একটা কি দুটো গল্প প্রকাশের পর ঘনাদার গল্প লেখা থামিয়ে দেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু পাঠকদের আবদারে কলম ধরেন আবার। অন্যান্য লেখার সঙ্গে সঙ্গে লিখতে থাকেন একটার পর একটা ঘনাদার গল্পও।
আমাদের বয়স বাড়লেও, গল্পের এই দাদাদের বয়স বাড়ে না কোনওদিন। কোনওদিনই তাঁরা জেঠু, কাকু, মেসো, বা দাদু হয়ে ওঠেন না। তাঁরা চিরনবীন, চিরকিশোর। বইয়ের পাতায় পাতায় আজও দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন আসমুদ্র হিমালয় আর সাত সমুদ্র তেরোনদীর পার। কখনও শাখালীন তো কখনও গ্যালাপ্যাগস দ্বীপ। কল্পনার জগতে, বইয়ের পাতায় পাতায়ই তাঁদের জীবন। সেখানেই তাঁদের জন্ম-কর্ম। সিনেমার পর্দায় নয়। ‘ওটিটি’ অথবা মুঠোফোনের মধ্যে তাদের ধরে ফেলা দুষ্কর। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে যখন ছবি তৈরি হচ্ছে মূলত ‘বই’ থেকেই, তখন একরকম কালের চাহিদা আর নিয়মের ফাঁদে পড়ে তাঁদেরও বইয়ের পাতা থেকে অবতরণ করতে হয় ছবিতে। ফিল্মের নায়ক হিসেবে। আর সেখানেই হয় মুশকিল। কল্পনার জগতের উন্মুক্ত ‘কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা’ থেকে ধরে-বেঁধে তাঁদের হাজির করা হয়, পরিচালক-নির্ধারিত খাঁচার মধ্যে। গল্পের লেখক কোনওদিন তাঁদের সিনেমার কথা ভেবে তৈরি করেন না, তাঁদের জন্ম বইয়ের পাতায় বিচরণের জন্যই। কথা আর বর্ণনার জাদুর মধ্য থেকেই তাঁদের অক্সিজেনের জোগাড়। পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি বা ছবির সম্পাদকের কম্পিউটারের মনিটর-কীবোর্ড-মাউস থেকে নয়। আর সে-জন্যই বোধহয় একটা সময় পাঠক-দর্শকের মনে দ্বিধা জাগে তাঁদের নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই তুলনা হয় গল্প আর ছবির মধ্যে মিল আর অমিলের। এতদিনের কল্পনার বাইরে বেরিয়ে চোখের সামনে এসে পাঠককে দোটানার মধ্যে ফেলে দেন তাঁরা। ফিল্মকে আজও অনেক বাঙালি ‘বই’ বললেও, বইকে ফিল্ম বলেন না কখনও। গল্পের বইয়ের প্রচ্ছদ বা অলংকরণের কারণে পাঠকের কল্পনায় তাঁরা একরকম। কিন্তু ফিল্মের নায়কের চরিত্রে? রবিনসন ক্রুসো, গালিভার বা ঘনাদা যদি ছবির চরিত্র হয়ে যান হঠাৎ? মেনে নিতে পারবেন তো, পাঠক-দর্শক?
৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির বাসিন্দা শিবু, শিশির, গৌর আর সুধীর আসলে শিবু, মানে বন্ধু, সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী। শিশির, বাংলা ছবির প্রযোজক ও অভিনেতা, ‘বসুমতী চিত্র প্রতিষ্ঠান’-এর সহ প্রতিষ্ঠাতা শিশির মিত্র। গৌর, অভিনেত্রী কাবেরী বসুর দাদা গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। তিনিও ‘বসুমতী চিত্র প্রতিষ্ঠান’-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা আর সুধীর, স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্র-র ডাকনাম।
প্রেমেন্দ্র মিত্র-র নানা গল্প থেকে একাধিক ছবি তৈরি হয়েছে বাংলা এবং হিন্দিতে। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, পূর্ণেন্দু পত্রী, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার— এঁরা সকলেই ছবি তৈরি করেছেন তাঁর নানা গল্প থেকে। প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেও চিত্রনাট্য লিখেছেন, ছবি তৈরি করেছেন অনেক। বিমল রায়ের অনুরোধে বম্বে গিয়েও থেকেছেন বহুদিন। বিনামূল্যে পাওয়া ‘পালি হিলস’-এর বাংলোয় থেকে, চিত্রনাট্য লিখেছেন ছবির জন্য। ভাল না লাগায় সব ছেড়েছুড়ে ফিরে এসেছেন কলকাতায়। বাড়িতেই ফিল্ম প্রোডাকশন কোম্পানি তৈরি করেছেন ‘মিত্রানি’ নাম দিয়ে। এই কোম্পানিতেই একসময়ে সকলকে চা-জলখাবার পরিবেশন করেছেন পরবর্তীকালে বাংলা ছবির সফল অভিনেতা-নির্দেশক সুখেন দাস। প্রেমেন্দ্র মিত্র-র নানা গল্প থেকে ছবি তৈরি হয়ে থাকলেও ঘনাদা নিয়ে ছবি তৈরির কথা তাঁরও কল্পনার বাইরে। নানা সময়ে বিভিন্ন পরিচালক তাঁদের সুবিধেমতো ঘনাদার কিছু গল্প অদলবদল করে নিয়ে বাংলায় ছবি করতে চাইলে, পরিবারের তরফ থেকে তাঁদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে সংগত কারণেই।
এক সময়ে আমি নিজে ঘনাদার কিছু গল্প নিয়ে ছবি করার কথা ভাবি। সেটাও দ্বিমাত্রিক সাদা-কালো অ্যানিমেশনের সাহায্যে। কথাও এগয় পোল্যান্ডের কিছু বিশেষ অ্যানিমেশন চিত্রশিল্পীর সঙ্গে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। নানা কারণে সেই ছবির কাজ আর এগয় না। এর অনেক বছর পর, বিশ্বের প্রথম সারির একটি ‘ওটিটি’ কোম্পানি পরিকল্পনা করে আমার এবং আরও কিছু নামী পরিচালকের পরিচালনায় ‘ওটিটি’-র জন্য এক-একটি ঘন্টাখানেকের এপিসোড করে ‘সিজন’-এ ভাগ করে বেশ কয়েকটি ছবি তৈরি করবে ঘনাদা সিরিজের। পরিকল্পনামাফিক গল্প বলার আসরের শুটিং হবে কলকাতায়। বাকি সমস্ত শুটিং হবে মূল গল্প অনুযায়ী বিশ্বের নানা জায়গায়। যেহেতু ঘনাদার বয়সের ইয়ত্তা নেই, তাই এই সময়ের কথা মাথায় রেখে মেসবাড়ির জায়গায় গল্পের আসর বসবে ঘনাদার বাড়ির আধুনিক সময়ের বসার ঘরে। সর্বভারতীয় দর্শকের কথা ভেবেই ছবির ভাষা হবে হিন্দি। বিদেশিরা সংলাপ বলবেন তাঁদের নিজস্ব ভাষায়। ‘সাবটাইটল’ থাকবে সেগুলোর সঙ্গে। তা ছাড়া, ঘনাদাও বুঝিয়ে দেবেন সেই সংলাপের সারমর্ম। এই ধরনের ছবি তৈরির খরচ বিস্তর। এত বড় প্রোডাকশন সামলানোও সহজ নয়। এইসব জেনেও এগিয়ে আসেন সেই ‘ওটিটি’ কোম্পানি। কারণ একটাই – এই ধরনের বিচিত্র ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান-বিষয়ক গল্প তাঁরা শোনেননি বা পড়েননি কখনও।
নানা কারণে সেই সিরিজ তৈরি হয়নি। কিন্তু তৈরি হলে, তা কীরকম হত, তাঁর মধ্যে বাঙালির নির্ভেজাল আড্ডা আর গল্প বলার মেজাজ কতটা অক্ষুণ্ণ থাকত, তা ভাবার বিষয়। সারা পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে অভিনেতাদের নিয়ে এই বিশাল চিত্রাভিযানও চাট্টিখানি কথা নয়। আবার বাংলার বাইরে নানা-দেশি এবং বিদেশি ভাষায় ঘনাদা অনুবাদ হয়ে থাকলেও, আজকের প্রজন্মর ক’জন ঘনাদা পড়েছে, বা পড়লেও সমস্ত গল্প মনে রেখেছে, সেটাও ভাববার বিষয়। আর যদি গল্প না-ও পড়ে থাকে, ছবির অ্যাডভেঞ্চারের জাদু তাকে বশ করতে পারবে তো?
একটা অত্যন্ত জরুরি কথা ভুললে চলবে না, লেখক কিন্তু গল্প লিখেছেন পড়ে কল্পনা করার জন্য। ছবি দেখে নয়। এখানেই ‘টিনটিন’ বা ‘অ্যাসটেরিক্স’-এর সঙ্গে ঘনাদার গল্পের তফাত। ঘনাদার গল্প কল্পনা করা যায়, চোখে দেখা যায় না। দেখে ফেললেই কল্পনার শেষ। কারণ কল্পনা তো একমাত্রিক নয়, বিভিন্ন পাঠকের কল্পনা তাঁর একান্ত নিজের। সমান নয় একেবারেই। সেই নানা পাঠকের নানা রকমের কল্পনার মধ্যেই বেঁচে থাকবেন ঘনাদা। বেঁচে থাকবে তাঁর বিভিন্ন অভিযান আর অ্যাডভেঞ্চার। বেঁচে থাকবে ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির বাসিন্দা শিবু, শিশির, গৌর আর সুধীরও। কোনও সিনেমা বা সময়কালের মধ্যে ধরা পড়বেন না তিনি। ধরা পড়বেন শুধু পাঠকের কাছে, তাঁর গল্প পড়ার মধ্য দিয়েই। কাগজের পাতায়, ছাপার অক্ষরে অথবা কম্পিউটারের পর্দায় বা ‘কিন্ডল’-এ। যতদিন বই পড়া হবে, ততদিন।