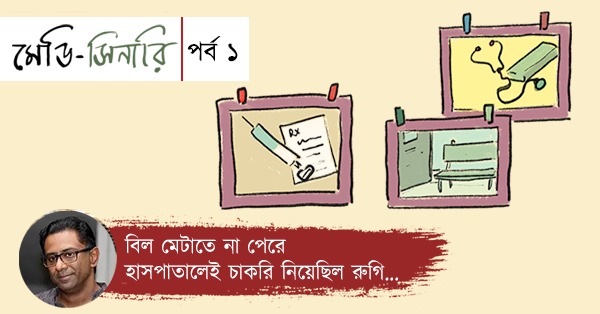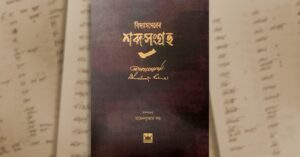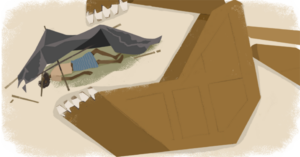চেনা চেম্বারের বাইরে
একটা ভারতের মধ্যে আসলে দুটো ভারত রয়েছে, যে কোনও বিভক্ত সমাজে যেমন হয়— একদল ওপরতলার মানুষ, আরেকদল নিচের তলার মানুষ। একজন ডাক্তার হিসেবে এই দুটো জায়গাতেই কাজের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।
একটি অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রর। হাসপাতালের নাম করছি না। এটা ছিল ঠিক সীমান্তের পাশে। সেখানে আমি চুক্তিভিত্তিক চাকরি করতে যাই, সে প্রায় চব্বিশ বছর আগে। ডাক্তারিতে সকলকেই কিছু যন্ত্রপাতি বহন করতে হয়। নিজস্ব কিছু ইনস্ট্রুমেন্টস থাকেই। আমার মনে আছে, চাকরির প্রথমদিন আউটডোরে যাওয়ার সময়, একটা স্টেথো, একটা বিপি ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা হ্যামার, একটা টর্চ— এই চারটি যন্ত্র নিয়ে যাচ্ছিলাম। খেয়াল করলাম, সহকর্মী অন্যান্য ডাক্তাররা বেশ মজা পেলেন। নার্সিং স্টাফ, ওয়ার্ড বয়রাও হাসাহাসি শুরু করলেন। এর কারণটা যদিও বুঝে উঠতে পারছিলাম না। একজন প্রশ্ন করলেন, এইসব সরঞ্জাম নিয়ে গিয়ে কি আদতে কোনও লাভ আছে? আমি স্বভাবতই উত্তর দিলাম, যা ডাক্তারি শিখেছি, তাতে এই চারটি যন্ত্র তো অন্তত আবশ্যক।
আরও পড়ুন : রবিবারের ছুটি আর সোমবারের কাজ কি লেখকের জীবনেও একই রুটিন মেনে আসে? লিখলেন প্রচেত গুপ্ত…
আউটডোরে গিয়ে বুঝতে পারলাম এই হাসিঠাট্টার আসল কারণটা। আবিষ্কার করলাম, তিন ঘণ্টায় আমাকে সাড়ে চারশো রুগি দেখতে হবে। আমরা এমনিতে যা জানি, ঠিক করে চিকিৎসা করতে গেলে অন্তত আধঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিট এক-একজনের জন্য ব্যায় করা উচিত। কিন্তু সেই আউটডোরে পৌঁছে বোঝা গেল, এখানে রুগিপিছু সময় দেওয়া সম্ভব তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড। তার কারণ, ওই রুগির দীর্ঘ লাইনের সকলকেই দেখতে হবে ওই সময়ের মধ্যে, এবং ওই তিন ঘণ্টার সময়সীমা বাড়ানোও সম্ভব নয়, হাসপাতালের নিজস্ব আইনকানুনের কারণে।
রুগি দেখা শুরু করলাম। প্রথম দু-একজনের ক্ষেত্রে যাহবা স্টেথো বা স্ফিগমোম্যানোমিটার ব্যবহারের সুযোগ পেলাম, কিন্তু তারপর একটা সময় এল, যখন বোঝা গেল, আর যন্ত্র ব্যবহার করে সময়সাপেক্ষ ডাক্তারিটা করা সম্ভব নয়। তারপর আরও একটা সময় এল, যখন আর রুগির মুখটাও দেখার সুযোগ পেলাম না। রুগির সমস্যাটুকু শুনেই প্রেসক্রিপশন লিখে দিতে হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ পাবেন রুগিরা, সরকারি ব্যবস্থামাফিক।
এই ঘটনাটা চলতে শুরু করল। একদিন দেখলাম, আমারও অভ্যেস হয়ে গেছে, তিন ঘণ্টায় সাড়ে চারশো রুগি দেখা।
তখন যেটা খুব ভাবিয়েছিল, এই ধরনের প্রত্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রুগির এই চাপ এবং সময়ের এই সংকটের মোকাবিলা কীভাবে সম্ভব? একটা সময় এই সব ভাবনাই সরিয়ে রেখে চিকিৎসা করতে শুরু করলাম। সেইসব রুগি আদৌ সুস্থ হয়েছিলেন কি না, আমরা সত্যিই জানি না। ওষুধপত্রর জোগান কম ছিল, যে পুষ্টি দরকার সুস্থভাবে বাঁচতে, তা পাওয়া সম্ভব ছিল না ওই গ্রামীণ বাস্তবতায়।
একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছিল ওই আউটডোরেই। এক রুগি প্রায় ছ-সাত কিলোমিটার দূর থেকে এসেছিলেন, ‘ফ্র্যাকচার্ড হিপ’ নিয়ে। অন্য দু-জনের কাঁধে ভর দিয়ে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে। দুঃখের যেটা, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁর চিকিৎসা কিন্তু সম্ভব নয়। তাঁকে আবার রেফার করতে হত সদর হাসপাতালে। ফলে, গ্রামের রুগিরা ক্রমশ শহরমুখী হতে শুরু করল। ডাক্তার-রুগি অনুপাতেও চরম বৈষম্য দেখা দিয়েছে ওইভাবেই, ভারতে সর্বত্রই। তখন মনে আছে, এক ডাক্তারপিছু রুগির অনুপাত ছিল ৪২ জন। এখন পরিসংখ্যানটা কোথায় দাঁড়িয়েছে, জানা নেই যদিও।
রুগি দেখা শুরু করলাম। প্রথম দু-একজনের ক্ষেত্রে যাহবা স্টেথো বা স্ফিগমোম্যানোমিটার ব্যবহারের সুযোগ পেলাম, কিন্তু তারপর একটা সময় এল, যখন বোঝা গেল, আর যন্ত্র ব্যবহার করে সময়সাপেক্ষ ডাক্তারিটা করা সম্ভব নয়। তারপর আরও একটা সময় এল, যখন আর রুগির মুখটাও দেখার সুযোগ পেলাম না।
এর বিপ্রতীপ মেরুতে এসে আবার একটা আশ্চর্য, নতুন অভিজ্ঞতা হল। ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থার একেবারে দুটো ভিন্ন চিত্র পাওয়া যাবে সেক্ষেত্রে।
সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আমার চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমি শহরে এসে যোগ দিয়েছিলাম একটি ভীষণ নামজাদা হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট বা আইসিইউ-তে। সেখানে সুযোগসুবিধার কোনও অভাব নেই। চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মী সকলেই করিৎকর্মা, দক্ষ। সেখানে এক রুগি একদিন ভর্তি হলেন, পাইরেশিয়া অফ আননোন অরিজিন বা পিইউও নিয়ে। প্রাথমিকভাবে তাঁর জ্বর আসতে শুরু করল তাড়সে। কী কারণে জ্বর, তখনও বোঝা যাচ্ছে না। তারপর চিকিৎসা শুরু হল, ডায়গোনসিস হল, ওষুধ পড়ল। ভদ্রলোক সুস্থ হলেন।
সুস্থ হওয়ার পর, যেদিন বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে তাঁকে, সেদিন সেই রুগি বলে বসলেন, আমি বাড়ি যাব না।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিস্মিত!
কেন যাবেন না, প্রশ্ন করায় জানা গেল, বাড়ি যেতে গেলে তাঁকে বিল মেটাতে হবে, যে সামর্থ তাঁর নেই। ফলে, তিনি চান পরিশ্রম করে উপার্জন করে বিল মিটিয়ে বাড়ি যেতে। এবং সেই কারণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর কাছে চাকরি চেয়ে বসলেন তিনি!
প্রথমে সকলেই খুব অবাক হয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষত কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরি দিল, গ্রুপ ডি স্টাফ হিসেবে।
বিল তিনি মেটাতে পেরেছিলেন কি না জানি না, তবে এটা জানি, এখনও তিনি সেই হাসপাতালে চাকরি করে চলেছেন।
দুই মেরুর স্বাস্থ্যব্যবস্থার এই ছবি একটা জিনিসই বোঝায়, আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়ন কতটা প্রয়োজনীয়!