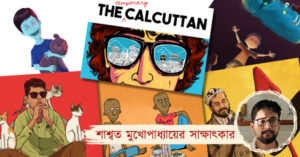তখন রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালার মতো অনেক খুচরো প্রযোজকই টালিগঞ্জ স্টুডিওপাড়ায় ঘুরঘুর করতেন। কিন্তু তাঁদের সব্বার ঋত্বিক ঘটকের এক গেলাসের ইয়ার হওয়ার সুযোগ ছিল না। রাধেশ্যামের সেটা ছিল। আর ওরকমই কোনও রঙিন আড্ডায় রাধেশ্যাম ঋত্বিককে এক লাইনের একটা গল্প শোনান। এক ভাই আর বোনের করুণ, নিষ্ঠুর গল্প। ‘ধরুন সময়ের ঘূর্ণিতে হারিয়ে তলিয়ে যাওয়া কোনও বোনের ঘরে এক রাত্রে খদ্দের হয়ে হাজির তার আপন দাদা। পারবেন এমন একটা গল্প নিয়ে ছবি করতে?’ হালকা চালে ঋত্বিককে প্রায় চ্যালেঞ্জই ছুঁড়ে দিয়েছিলেন রাধেশ্যাম। ঋত্বিক কথা দিয়েছিলেন, এই গল্প নিয়েই ছবি করবেন। গেলাস-ভর্তি তরল আগুন ছুঁয়ে বলা সে কথা তিনি রেখেওছিলেন। ‘সুবর্ণরেখা’র ক্রেডিটে সহ-কাহিনিকার হিসেবে ঋত্বিকের সঙ্গে রাধেশ্যামের নামও গিয়েছিল। যদিও তাঁর ‘কৃতিত্ব’ ওই এক লাইনের আইডিয়াটুকুই। ঋত্বিক সেটাকেই পদ্মাপাড় থেকে সুবর্ণরেখার তীর অবধি মস্ত ক্যানভাসে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সিনেমার পণ্ডিতরা এই ছবিটাকে ঋত্বিকের দেশভাগ ট্রিলজির তিন নম্বর পর্ব হিসেবেই দেখেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু যুবক ঈশ্বর তার বাপ-মা মরা ছোট্ট বোন সীতাকে বুকে আগলে প্রায় মেয়ের মতোই মানুষ করেছে। আর সীতার সঙ্গেই বড় হয়েছে উদ্বাস্তু কলোনি থেকেই কুড়িয়ে পাওয়া দলিত বালক অভিরাম।
রুজিরুটির টানে উদ্বাস্তু কলোনি ছেড়ে দুই বালক-বালিকার হাত ধরে ঈশ্বর চলে আসে ঘাটশিলার কাছে এক অনামা শহরে। সেখানে সুবর্ণরেখার সোনালি বালুকাবেলায়, মালভূমির খয়েরি-ধূসর-রুক্ষ-উদার প্রকৃতির বুকের ভেতর কখন যে ব্রাহ্মণকন্যা সীতা আর ‘ছোট জাতের ছেলে’ অভিরামের প্রেম হয়ে যায়, ঈশ্বর টেরই পায় না। যখন জানতে পারছে, তখন সীতাকে ‘তুই মরে যা’ বলার চেয়ে কঠিন কোনও অভিসম্পাত তার মনে পড়ে না। সেই একরত্তি বোন, যাকে দেশছাড়ার সময় থেকেই ঈশ্বর ‘নতুন বাড়ি’র মরীচিকা দেখিয়ে আসছে, সে কিন্তু মরে যাওয়ার জন্য নয়, অভিরামের সঙ্গে নতুন করে বাঁচার স্বপ্নেই দাদার বাড়ি ছাড়ে। তবে অভিরামও তাকে কোনও নতুন বাড়ি দিতে পারে না। বরং সংসার চালাতে হয়রান হয়ে সীতাকে দাদার কাছেই হাত পাততে বলে। সীতাও সাফ জানিয়ে দেয়, সে মরে যাবে, কিন্তু দাদার কাছে ভিক্ষে চাইতে পারবে না! কথার কথাই, তবু ঈশ্বর আর সীতার সম্পর্কের মাঝখানে আরও একবার কিন্তু মৃত্যুর মেঘ একচিলতে ছায়া ফেলে যায়। সরকারি দোতলা বাসের ড্রাইভার অভিরাম রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করে। ক্রুদ্ধ পাবলিক বাস জ্বালিয়ে তাকে পিটিয়ে মেরে ফ্যালে। সীতা এবার সত্যি সত্যিই পথে বসে। বা পথে বসে না, বরং তার বয়সি মেয়েরা অনেকেই এই অবস্থায় যেখানে গিয়ে ওঠে, ছোট্ট মিনুর হাত ধরে সেই পাড়াতেই তাকে ঘর নিতে হয়।
সীতার সেই নতুন পাড়ার নতুন বাড়িতেই এক রাতে আসে তার একদা ভগবানের মতো দাদামণি ঈশ্বর। সে তখন বেহেড মাতাল। উদ্বাস্তু কলোনির পুরনো সাথী হরপ্রসাদের উস্কানিতে নগর কলকাতায় ফুর্তির পাতাললোকের উদ্দাম যাত্রী। রেসের মাঠ থেকে পানশালা হয়ে তারা এবার নারীমাংসের গন্ধে গন্ধে অ্যাদ্দূর! পয়সা খরচ করে এ শহরে যতটা মস্তি কিনতে পাওয়া যায়, তার সবটা ঢকঢকিয়ে গিলে তবে তাদের শান্তি। তাই সদ্য লাইনে নামা সীতার ঘরে ঈশ্বরই প্রথম খদ্দের। ভাইফোঁটায় বাংলার বোনেরা যখন ঘরে ঘরে ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে তাদের চিরকালের সুরক্ষা বাব্লে মুড়ে রাখতে চায়, তখন এই বোন নিজেকেই যম-দুয়ারে পাঠিয়ে ভাইয়ের পাপের পথে কাঁটা বিছোয়। ঈশ্বর তাকে চিনে ফেলবার আগেই সীতা হাত বাড়িয়ে ঘরের কোনে রাখা আঁশবঁটিটা তুলে নেয়। ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোঁটা ঈশ্বরের সাদা পাঞ্জাবিতে ছিটকে লাগে। প্রথমে একটু। তারপরে অনেকটা। বোনের রক্তের অঞ্জলিতে দাদার নেশালু দুচোখের কুয়াশা ঘুচে যায়। আবছা ঘরের মেঝেয় সীতার মৃত মুখখানি জুঁইফুলের মতো ফুটে থাকে।
ঋত্বিকের মৃত্যুর পর তাঁর শোকবার্তায় সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ও আমাদের সব্বার চেয়ে অনেক বেশি বাঙালি ছিল। মুণ্ডমালা গলায় খাঁড়া হাতে কালী সাজা বহুরূপীর আচমকা আবির্ভাবে ছোট্ট সীতার ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া,মাতৃত্বের আর্কিটাইপ, ইয়ুং-এর তত্ত্ব, সীতা-ঈশ্বর এসব নামের পৌরাণিক তাৎপর্য পেরিয়ে, বাঙালি ঋত্বিক বাঙালি ভাইবোনের আখ্যানকে এখানে কোথাও গ্রিক ট্র্যাজেডির অচেনা রোমাঞ্চকর কোনও মোড়ে এনে দাঁড় করালেন কি না, তাই নিয়ে সিনে-তাত্ত্বিকরা যত খুশি তর্ক করুন। আমরা শুধু দেখতে পাচ্ছি, ঋত্বিকের ছবিতে ভাইবোনের সম্পর্কে কোথায় যেন রক্তের দাগ একটু লেগেই থাকে। ‘সুবর্ণরেখা’র ক’বছর আগে দেশভাগ-ত্রয়ীর পয়লা ছবি ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় নীতা যখন তার যক্ষ্মা রোগের প্রথম রক্তপাত রুমালের আড়ালে লুকোতে চায়, সেটা দাদা শঙ্করেরই চোখে পড়ে যায়। হালকা খুনসুটির ভঙ্গিতে ‘এই বয়সে প্রেমপত্র? দেখি দেখি’ বলে সে যখন গোপন জিনিসটা কেড়ে নিতে যাচ্ছে, তখনই দেখা যায় সাদা রুমালের গায়ে নকশার মতো বিন্দু বিন্দু রক্তের রেখা। মা-বাবা-ভাই-বোন-দাদার বিরাট সংসারের মস্ত চাকাটাকে একার দায়িত্বে বছরের পর বছর চালু রাখতে গিয়ে সত্যি সত্যিই নীতার মুখে রক্ত উঠে এসেছিল।
আমরা শুধু দেখতে পাচ্ছি, ঋত্বিকের ছবিতে ভাইবোনের সম্পর্কে কোথায় যেন রক্তের দাগ একটু লেগেই থাকে। ‘সুবর্ণরেখা’র ক’বছর আগে দেশভাগ-ত্রয়ীর পয়লা ছবি ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় নীতা যখন তার যক্ষ্মা রোগের প্রথম রক্তপাত রুমালের আড়ালে লুকোতে চায়, সেটা দাদা শঙ্করেরই চোখে পড়ে যায়। হালকা খুনসুটির ভঙ্গিতে ‘এই বয়সে প্রেমপত্র? দেখি দেখি’ বলে সে যখন গোপন জিনিসটা কেড়ে নিতে যাচ্ছে, তখনই দেখা যায় সাদা রুমালের গায়ে নকশার মতো বিন্দু বিন্দু রক্তের রেখা।
উদ্বাস্তু কলোনির দরমার ঘরে, গরমে-গুমোটে, আধপেটা খেয়ে সে তার সাধ্যমতো বাড়ির সব্বার মুখে হাসি, সব মনে শান্তি, সমস্ত হৃদয়ে সুখ আর স্বপ্নের রসদ জুগিয়ে গেছে। কোনওদিন একটুও অনুযোগ করেনি, মুখ ফুটে একবারও প্রতিবাদ করেনি, তরণ মাস্টারের এই ‘শান্ত মাইয়াটা’। তাই পরিবারের সবাই তাকে সময়-সুযোগ মতো ব্যবহার করে গেছে। এমনকী শঙ্করও। মস্ত গাইয়ে হওয়ার সাধনায় সে এলেবেলে কোনও চাকরিতে ঢোকেনি। দাড়ি কামানোর জন্য সামান্য কটা পয়সা চেয়ে চাকুরে ছোট ভাইয়ের মুখঝামটা খাওয়ার পর সেই নীতার কাছেই এসে হাত পাততে হয়েছে। ছেঁড়া চপ্পলে সেফটিপিন লাগিয়ে সংসারের জোয়াল টেনে চলা নীতার কষ্টটা সে দেখেও দেখেনি। বা দেখতে চায়নি, নিজের স্বার্থের জন্যই। তবে নীতার প্রেমিক সনৎ যখন তার জন্য অপেক্ষা না করে তাদেরই বোন গীতাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল আর গোটা পরিবার এই ‘অবিচার’টা নিয়ে উৎসবে মেতে উঠল, তখন আর শঙ্কর সহ্য করতে পারেনি। সে ‘অন প্রোটেস্ট’ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়! আর চলে যাওয়ার আগের রাত্তিরে ছোট বোনটাকে গান তোলাতে বসে। নীতাই শিখতে চেয়েছিল দাদার কাছে। নিজের প্রেমিকের সঙ্গে নিজেরই ছোটবোনের বিয়ের বাসরে গাইতে হবে তো। বোনের সর্বনাশের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দাদা গান ধরে ‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে’। বোন গলা মেলায়। আবছা অন্ধকার ঘরে ছিটে-বেড়ার ফাঁক গলে কয়েক কুচি আলো ভাইবোনের মুখের ওপর খেলা করে।
ক্যামেরা ঘরের বাইরে একবারও যায় না। তবু রুদ্ধ কান্নার মতো সেই গান যেন দুজনের বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, দরমার ঘর ফাটিয়ে, বাইরের কালো আঁধার পৃথিবীর মর্মে গিয়ে বাজে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঙ্গীত পরিচালনায় এই গানের ইন্টারল্যুডে আরও একবার ছবির সেই বিখ্যাত চাবুকের আওয়াজটা ফিরে আসে। ভাই-বোনের দুঃখ-রাতের গানের শরীরে সেই কশাঘাতের নীলচে-লাল কালশিটেগুলোও যেন আঙুল ছুঁয়ে টের পাওয়া যায়।
নীতা তার শ্রম দিয়ে একদা শঙ্করের স্বপ্নকে আগলে রেখেছিল। ভারত-বিখ্যাত গায়ক হয়ে ফিরে আসা শঙ্করও অসুস্থ বোনকে শিলং পাহাড়ে যক্ষ্মা রোগীদের স্যানেটোরিয়ামে নিয়ে যায়। এখানে বোনের প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্যের পাশাপাশি কোথাও হয়তো ঋণশোধের একটা জায়গাও ছিল। এটা হয়তো ঠিক লেনদেন নয়। কিন্তু বিবেকের একটা খোঁচাখুঁচির ব্যাপার তো বটেই। সেই কর্তব্য, বিবেক আর হৃদয়ের জটিল রসায়নেই শঙ্কর সময় করে স্যানেটোরিয়ামে আসত। আর এভাবেই ‘মেঘে ঢাকা তারা’র ক্লাইম্যাক্সে বাংলা তথা ভারতীয়, হয়তো বিশ্ব-সিনেমারও সেই আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনাটা ঘটে যায়।
স্যানেটোরিয়ামের বাগানে নীতাকে খুঁজতে খুঁজতে শঙ্কর তাকে একটু নিরালা একটা কোণে দেখতে পায়। নীতার ভাল লাগবে বলে সে তাকে বাড়ির গল্প শোনাতে থাকে। গীতার ছেলের কথাও ওঠে। দু’বছরের ছোট্ট বাচ্চাটা কী দস্যি দামাল! আর কী অফুরান প্রাণ! আর তখনই শঙ্কর এবং ছবির দর্শক কাউকে এতটুকু কোনও প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে নীতা শঙ্করের দুহাত ধরে আচমকা চিৎকার করে ওঠে, ‘দাদা আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম! দাদা আমি বাঁচব! দাদা আমি বাঁচব!’ উন্মত্ত সেই আর্তি যেন হঠাৎ বিস্ফোরণে ভাঙা গ্লেসিয়ারের মতো দর্শকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।নীতার আকুল ইচ্ছের ডাক এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়-চুড়োয় ধাক্কা খেতে খেতে ফেরে। ক্যামেরার প্যানোরামিক চলনেও যেন হিস্টিরিয়া-গ্রস্তের বিকার। মেলোড্রামা ততক্ষণে তার শিল্পের এভারেস্ট ছুঁয়ে ফেলেছে। মেধাবী চিন্তার, সাজানো যুক্তির সব শান কান্নায় ভোঁতা করে, সংযমের সব শৃঙ্খলা আবেগে তছনছ করে, আমাদের মগজের মধ্যেও তার প্রতিধ্বনি বেজেই চলে! দর্শকও তখন শঙ্করের মতোই একই রকম বিব্রত, বিপন্ন, বিষণ্ণ।
পুণে ফিল্ম ইন্সটিটিউটে নাকি অনেক বছর ধরেই একটা প্রিয় খেলা চালু আছে। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ দেখে শিলং পাহাড়ে নীতা আর শঙ্করের ওই দৃশ্যটায় একেবারে স্বাভাবিক থাকতে হবে। অনেকে একশো দুশো আড়াইশোবার ছবিটা দেখেছেন। ওই অমোঘ মুহূর্তটা আসার আগে অবধি মন শক্ত করে বসে থেকেছেন। না, এবার কিছুতেই ঋত্বিক আর তাঁর নীতাকে জিততে দেব না। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁদের হৃদয়ের ডিফেন্স ভেঙে চুরমার করে নীতা তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কবেকার কুমার সাহনিদের আমল থেকে সঞ্জয় লীলা বনশালিদের ব্যাচ অবধি, বা তার অনেক পরেও, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। সংযমের পরীক্ষায় কেউ উতরোতে পারেননি।
‘পথের পাঁচালী’কে নিয়ে এরকম কোনও পরীক্ষা প্রতিযোগিতার কথা শোনা যায়নি। ঋত্বিকের সিনেমায় যেমন সমাপতন সার বেঁধে আসে— মেলোড্রামা সিরিয়াল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলে, ‘মেঘে ঢাকা তারা’র পাঁচ বছর আগের ‘পথের পাঁচালী’তে তেমন কিছু ঘটে না। ঘটার সুযোগও নেই।
নিশ্চিন্দিপুরের মতো ভীষণ সাদামাটা ঘটনাবিহীন একটা গ্রাম। সেই গ্রামেরও একধারে প্রায় জঙ্গলের ভেতরে একটা ভাঙা পোড়ো ভিটেয় সর্বজয়া দুর্গা আর অপুকে নিয়ে থাকে। দুর্গার বাবা হরিহর আর তার সৎদিদি ইন্দির ঠাকুরণ সেখানে মরশুমি অতিথির মতো আসা-যাওয়া করে। সর্বজয়া কীভাবে তাঁর ভাঙা রান্নাঘরের চুলোয় আগুনটা জ্বলিয়ে রাখে, সারা বছর হরিহর তার কতটুকু খোঁজ নেয়? সেখানেই শিশু দুর্গা কিশোরী হয়। কাপড়ের দোলনায় শোওয়া অপুরও পাঠশালায় যাওয়ার সময় চলে আসে।
সারা পৃথিবীর সিনেমার ইতিহাস যে আইকনিক ভাইবোনকে নিত্যনতুন ভাবে আবিষ্কার করে চলেছে, তাদের আমরা ওই পাঠশালায় যাওয়ার সকালবেলাতেই প্রথম দেখি। অপু কিছুতেই ঘুম থেকে উঠছে না। সর্বজয়া দুর্গাকে বলে ওকে ডেকে দিতে। দুর্গা অপুকে ঝাঁকায়। সে চাদর মুড়ি দিয়ে মটকা মেরে থাকে। তারপরেই বিশ্ব সিনেমার সেই চির-ক্লাসিক শট। দুর্গা অপুর মুখের একপাশ থেকে চাদরটা সরিয়ে নেয়। বন্ধ চোখটা টেনে খুলে দেয়। অপু পৃথিবীর দিকে প্রথমবার তাকায়।
সারা পৃথিবীর সিনেমার ইতিহাস যে আইকনিক ভাইবোনকে নিত্যনতুন ভাবে আবিষ্কার করে চলেছে, তাদের আমরা ওই পাঠশালায় যাওয়ার সকালবেলাতেই প্রথম দেখি। অপু কিছুতেই ঘুম থেকে উঠছে না। সর্বজয়া দুর্গাকে বলে ওকে ডেকে দিতে। দুর্গা অপুকে ঝাঁকায়। সে চাদর মুড়ি দিয়ে মটকা মেরে থাকে। তারপরেই বিশ্ব সিনেমার সেই চির-ক্লাসিক শট। দুর্গা অপুর মুখের একপাশ থেকে চাদরটা সরিয়ে নেয়। বন্ধ চোখটা টেনে খুলে দেয়। অপু পৃথিবীর দিকে প্রথমবার তাকায়। তারপর কাতুকুতু। অপুর ধড়মড়িয়ে উঠে পড়া। পুকুরপাড়ে দাঁতমাজা। মুখ ধোওয়া। দিদির যত্ন করে ভাইয়ের চুল আঁচড়ে দেওয়া। অপুর দুধের বাটিতে চুমুক। দুর্গার মুখ মুছিয়ে দেওয়া। সর্বজয়ার আদরমাখা ঝলমলে হাসি মুখ। গোটা ছবিতে খুব কম সময়ই যা দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এমন ভরন্ত, গার্হস্থ্য সুখের মুহূর্তও তো তাদের জীবনে তেমন একটা আসে না! তবু অপু আর দুর্গা অভাবের আঁচে রোজ শুকিয়ে যাওয়া জীবন ছেনেই তাদের শৈশবের রসটুকু নিংড়ে নিতে চায়। মায়ের রান্নাঘর থেকে হিসেবের তেল একটুখানি চুরি করে এনে লুকিয়ে কাঁচা আম মাখা খাওয়া—খেতে খেতে অপু হুশহাশ শব্দ করায় দুর্গার আদরের চড়— অপুর গালে আমতেলে মাখামাখি দিদির আঙুলের ছোপ ভালবাসার তিলকফোঁটা হয়ে লেগে থাকে।
এমনই ছোটখাট প্রাত্যহিকী দিয়েই অপুর সঙ্গে দুর্গার, তাদের দুজনের সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামটার সেখানকার পুকুর-ডোবা-জলফড়িং-গাছ-পাখি-ঝোপঝাড়-ক্ষেত-মাঠ-কাশবনের জানাশোনা মেলামেশা চলতেই থাকে। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসটা ছিল অপুর পাঁচালি। অসম্ভব কল্পনাপ্রবণ মনের এক বালকশিশু নিশ্চিন্দিপুর গ্রামটাকেই তার স্বপ্নের পৃথিবী বানিয়ে নিয়েছিল। সত্যজিতের সিনেমায় কিন্তু দুর্গাই নায়িকা। গোটা নিশ্চিন্দিপুরই তার লীলাভূমি। এখানকার শস্য-ফল-আকাশ-বৃষ্টি সবের ওপরেই তার অবাধ অধিকার। সে এখানকার প্রকৃতিরাজ্যের রাজকন্যে। পুজোর সময় যাত্রা দেখে, দুর্গার পুতুলের বাক্স ঘেঁটে রাংতা দিয়ে মুকুট বানিয়ে রাজা সাজলেও, আসলে অপু তার খাসতালুকের আদরের প্রজা। দুর্গাই তাকে সঙ্গে করে নিজের রাজপাট চেনায়। দিদির পিছুপিছুই সে গ্রামের সীমানায় টেলিগ্রাফের খুঁটি, ট্রেন-লাইনের কাছ-বরাবর পৌঁছে যায়।
আবার দুর্গার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতেই সে নিজেদের অভাব, অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া অপমানও চিনতে শেখে। চিনিবাস ময়রার পিছু ধরে রানুদের বাড়ি অবধি চলে যাওয়া আর অবাঞ্ছিত অতিথির মতো সে-বাড়ির দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কাঙালপনা দেখতে দেখতে প্রত্যেকবার একটা ভীষণ কষ্ট গলার ভেতর দলা পাকাতে থাকে। চোখের ভেতর জ্বালা করে।
অপু তার দিদিকে প্রথম বৃষ্টির উৎসবে তুমুল আনন্দে চুল ভেজাতে দেখে। দুর্গাকে তখন অহংকারী রাজকন্যার মতো লাগছিল। একটু পরেই যে এসে গাছতলায় ঠান্ডায় কাঁপতে থাকা ভিতু ভাইটাকে ভিজে আঁচলের আদরে আশ্বাসে জড়িয়ে নেবে। আবার ওই দিদিটাকেই অপু মায়ের হাতে চোরের মার খেতে দ্যাখে। ইশারা করে পালাতে বলেও অপু সে-যাত্রায় দুর্গাকে বাঁচাতে পারেনি। আর যে পুঁতির হারটা নিয়ে এত কাণ্ড, দুর্গা মারা যাওয়ার পরে সেটাকেই সে একটা পুরনো নারকেলের মালার মধ্যে খুঁজে পায়। কাউকে কিচ্ছু না বলে পাশের পানাপুকুরে সে হারটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পুকুরের কচুরিপানাগুলো একটু সরে যায়, আবার সবটা ঢেকে ফ্যালে। দুর্গার খিদে, কষ্ট, অনেক কিছু না পাওয়া—দুর্গার ছোট ছোট সুখ, ছেলেমানুষি আনন্দ—দুর্গার বোকার মতো লোভ—নিশ্চিন্দিপুরের পুরনো পুকুর—সবটা তার বুকের ভেতর লুকিয়ে ফ্যালে। অপু পুরোটা দাঁড়িয়ে দেখে। সে একা একা এবার বড় হয়ে গেল। দুর্গাকে ছাড়া তাদের নিশ্চিন্দিপুরে থাকার আর কোনও মানেই হয় না।
দুর্গা পুণ্যিপুকুর ব্রত করে। তাদের গ্রামে দুর্গাপুজো আসে, চলে যায়। কিন্তু ভাইফোঁটার কথা কিছু শোনা যায় না। ‘পথের পাঁচালী’র পরে সত্যজিতের আর কোনও ছবিতে সেভাবে ভাইবোনের গল্প আসেনি। ‘চারুলতা’য় উমাপদ ভাইয়ের চেয়েও ভিলেন অনেক বেশি। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’তে বেকার সিদ্ধার্থ কোথাও চাকুরে ছোটবোনকে একটু হিংসেও করে। বোনের বসের বউ বাড়ি বয়ে এসে বোনের সম্পর্কে নোংরা কথা শুনিয়ে গেলে অবশ্য তার মানে লাগে। পৌরুষেও। কিন্তু কড়া কথা শোনাবে বলে বসের বাড়িতে গিয়েও সে কেঁচোর মতো পালিয়ে আসে। বোন অবশ্য দাদাকে পাত্তা না দিলেও বন্ধুই ভাবে। অনেক রাতে তাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে নতুন শেখা নাচ দেখায়। পার্টি ড্যান্স। তার মডেলিং করার ইচ্ছের কথাও জানায়। কিন্তু সে নীতা নয়। হতেও চায় না। যে পাখির ডাকটার সঙ্গে সিদ্ধার্থর ছোটবেলার স্বপ্ন স্মৃতি জড়িয়ে আছে, সেখানে বালিকা বোন ছিল। কিন্তু চাকরির জন্য বালুরঘাটে গিয়ে সে যখন সত্যি সত্যি ওই পাখিটার ডাক আবার শুনতে পায়, সেখানে কোনওভাবেই বোনের কোনও জায়গা থাকে না।
পুনশ্চ: হিন্দি সিনেমায় ‘রক্ষা বন্ধন’ বা রাখির রিচুয়াল যেমন ঘুরে ফিরে আসে, বাংলা সিনেমার মূল ধারায় কিন্তু ভাইফোঁটা সেভাবে দেখতে পাই না। অকিঞ্চিৎকর এক-আধটা সিনেমায় হয়তো ‘ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা’ গোছের গান শোনা যায়। কিন্তু ওই অবধিই। উত্তমকুমারের মহানায়ক হওয়ায় ইউএসপি-তে বড়ভাই ইমেজ একটা অন্যতম ফ্যাক্টর। কিন্তু তিনি কোনও সিনেমায় মেঝেতে বাবু হয়ে জমিয়ে বসে ভাইফোঁটা নিচ্ছেন, এমন দৃশ্য চট করে মনে পড়ে কি? বাংলা মেগা অবশ্য বড় পর্দার সেই অভাব সুদে-আসলে উশুল করে দিয়েছে। আগামী সপ্তাহখানেক বিভিন্ন সিরিয়ালের ট্র্যাকে তার অনেক নমুনাও পাবেন। কিন্তু কে না জানে, বাংলা সিরিয়াল আসলে বাঙালিই নয়।