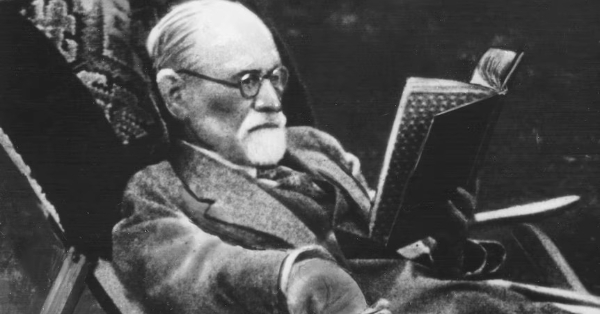হর এক পল কা শায়র

 জাভেদ আখতার (Javed Akhtar) (March 31, 2023)
জাভেদ আখতার (Javed Akhtar) (March 31, 2023)১৯২১ সালে, লুধিয়ানার কাছাকাছি, ফজল মহম্মদ নামে এক ধনী জায়গিরদারের একটি ছেলে জন্মায়। অবশ্য বলা উচিত, মা সর্দার বেগমের একটি ছেলে জন্মায়, কারণ ফজলের ১১জন স্ত্রী ছিলেন, এবং সর্দার বেগম তাঁর ছেলেকে প্রায় একাই মানুষ করে তোলেন।
এই ছেলেটির জীবনে প্রথম সঙ্কট আসে ১৯৩০-এ, যখন তার বাবা ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ছেলে এসে তাঁর জায়গিরের উত্তরাধিকার গ্রহণ করুক। সর্দার বেগম বলেন, তিনি ছেলেকে ছাড়বেন না। শর্ত দেন, স্ত্রী হিসেবে তাঁকে সঙ্গে রাখতে রাজি হলে, তবেই ফজল মহম্মদ ছেলেটিকে পাবেন। ফজল রাজি হন না। কে ছেলেকে পাবেন, এই ব্যাপারটা তিক্ত যুদ্ধে পরিণত হয়। মীমাংসা হয় তখনই, যখন নাবালক সাহির, ধনী পিতার উত্তরাধিকার এবং প্রাচুর্যময় জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে, দুঃস্থ মায়ের সান্নিধ্য বেছে নেয়। ‘সাহির’ শব্দের অর্থ জাদুকর। ওই দিনেই এই জাদুকরের প্রকৃত জন্ম হয়, কারণ মায়ের প্রতি আনুগত্য আর ভালবাসার মধ্যে দিয়ে, সে মূল্যবোধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁকে জীবনে অভাব এবং বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু এই সময়টাকে সাহির কখনও ভুলে যাননি। সর্দার বেগমের প্রভাব বহু ক্ষেত্রে সাহিরের গীতিরচনায় এবং কবিতায় সুস্পষ্ট, যেখানে মাতৃস্নেহ এবং সমাজে মহিলাদের অবস্থান ও মর্যাদার কথা বারেবারে উঠে এসেছে। সাহির চিরকাল মায়ের স্নেহময় সন্তান ছিলেন।
ছোট থেকেই জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে বেড়ে ওঠা সাহির স্বপ্ন দেখেছিলেন এক সুন্দর ভবিষ্যতের, নিজের ক্ষেত্রেও, গোটা সমাজের ক্ষেত্রেও। এটাই বোধহয় একজন শিল্পী এবং একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য। শিল্পী উপলব্ধি করেন যে তাঁর দুঃখ তাঁর একার নয়, বরং সমগ্র মানবজাতি তার শরিক। আর যখন তিনি এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা শুধু নিজের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা গোটা পৃথিবীর ভাল-চাওয়ায় চারিয়ে যায়।
১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে, তাঁর যুবা-বয়সে, সাহির লাহৌরে এক পত্রিকায় কাজ করতে শুরু করেন। ১৯৪৫-এ তাঁর নজম এবং গজল প্রকাশিত হয় ‘তালখিঁয়া’ নামক একটি সঙ্কলনে। শব্দটির অর্থ ‘তিক্ততা’। প্রথম বইয়ের এই নাম থেকেই বোঝা যায়, অল্প বয়সেই জীবনযুদ্ধের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে কত যন্ত্রণা এবং অপমান সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। এই ‘তালখিঁয়া’ বোধহয় তাঁর জীবন থেকে কখনওই মুছে যায়নি; মায়ের যন্ত্রণা এবং নিজের বেড়ে ওঠার কষ্টকর অভিজ্ঞতা যেন তাঁর অন্যতম উত্তরাধিকার। ভবিষ্যতে তাঁর জীবনে বহু সম্পর্কের উপর এর বিরূপ প্রভাব দেখা যায়।
সাহির ছিলেন প্রগতিশীল, সংস্কারমুক্ত, মুক্ত চিন্তাধারা-সম্পন্ন যুবক, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত খোলাখুলি ভাবে জানাতেন। ধর্মীয় মৌলবাদ ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে ‘সাভেরা’ নামক পত্রিকায় লিখেছিলেন, যার ফলে অচিরেই তাঁর নামে ফতোয়া এবং গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি হয়। সাহির পালিয়ে দিল্লি চলে আসেন এবং ছোটখাটো কাজ করে দিন গুজরান করেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে কবি অমৃতা প্রীতম-এর আলাপ হয়; যে আলাপ ও সম্পর্ক বিষয়ে অমৃতা লিখে গেছেন।
সাহিরের প্রতি আনুগত্যে এবং প্রেমে অমৃতা অকৃপণ ছিলেন। এমনকী সাহিরের একটা আধা-খাওয়া সিগারেটের বর্জিতাংশও অমৃতার কাছে মহা মূল্যবান ছিল, কারণ তা সাহিরের ঠোঁট ছুঁয়ে গেছে। সাহির কি অমৃতাকে একই ভাবে ভালবাসতেন, সমান আকুলতা নিয়ে? বলা কঠিন, কিন্তু এ কথা পরিষ্কার ছিল যে তিনি শুধুমাত্র প্রেমের স্বপ্ন দেখতেন না, জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতা তাঁর কাছে জরুরি ছিল। একই সঙ্গে, শুধু নিজের প্রেমের ঘোরে বিভোর না থেকে, ভালবাসা ও নিষ্ঠা সহ মানুষের দুর্দশা দূর করার কাজ তাঁর কাছে সমান গুরুত্ব দাবি করত। আর্থিক নিরাপত্তার খোঁজেই সাহির বম্বে আসেন, এবং গীতিকার হিসাবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যোগ দেন। সাফল্য আসে প্রায় তৎক্ষণাৎ, ইন্ডাস্ট্রিতে যুবক সাহিরের লেখা গানে এবং কবিতায় নতুন ভাব ও চিন্তাধারার জয়জয়কার ওঠে।আমার সৌভাগ্য যে আমার সঙ্গে সাহির লুধিয়ানভীর খুবই ভাল আলাপ ছিল। আমার সৌভাগ্য যে আমি ওঁর নিজের মুখে শুনেছি, ওঁর কবিতা, ওঁর বিশ্বাস এবং ওঁর গজলের নিখুঁত প্রকরণ সম্পর্কে কথাবার্তা। আমি ওঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলাম, উনি আমার বাবা (জান নিসার আখতার) এবং মামার (মেজাজ) বন্ধু ছিলেন। আমি ওঁকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতাম, কেন উনি সহজ উর্দু লেখার চলটাকে ভেঙে মাঝে মাঝেই অত্যন্ত কঠিন বাক্যাংশ গঠন করতেন, যেমন ‘বরসাত কি রাত’-এর কাওয়ালিতে। ওই বিখ্যাত কাওয়ালিতে এই কাপলেট-টা আছে:
‘না তো কারভাঁ কি তালাশ হ্যায় না তো হমসফর কি তালাশ হ্যায়,
মেরে শৌকে-খা-আ-খারাক কো তেরি রেহগুজর কি তালাশ হ্যায়।’সাহির সবসময় উত্তর দিতেন, বিষয়টা ভারসাম্যের। শ্রোতা যদি কাপলেট-এর একটা লাইন বুঝতে পারেন, অন্য লাইনে কঠিন কথা থাকলে ক্ষতি হয় না। তাই যদি প্রথম লাইন সহজ, শ্রোতার কাছে স্পষ্ট হয়, একটু কঠিন দ্বিতীয় লাইন পদ্যে সাহিত্যগুণ এবং গভীরতা আনতে পারে। এই বিশ্বাসেই সাহির তৎকালীন হিন্দি গীতিরচনার চলনকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন। আজকের যুগের মতোই, ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে, গান ও কবিতা লেখার মান পড়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। ‘সানডে কে সানডে’ গোছের হাল্কা, ফুরফুরে কিছু গানই তখন জনপ্রিয়। এই সময়ই সাহির নিয়ে আসেন এক নতুন ‘জুবাঁ’, সিনেমার গানের ভাষায় এক নতুন শুদ্ধতা।
তাঁর ভাষার নিখাদ কাব্যগুণ ছাড়াও, সাহিরের গান-লেখা স্বতন্ত্র হয়ে উঠত, যখন তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ ব্যবহার করতেন, নরনারীর প্রেম বোঝাতে। মনে হত, সমগ্র প্রকৃতি যেন প্রাণ দিয়ে চাইছে ও চেষ্টা করছে, এক পুরুষ ও এক নারীর প্রেম পূর্ণতা পাক।
‘ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনি তুম কঁহা
সুন যা দিল কি দাস্তাঁ’— গানটি এর এক উজ্জ্বল উদাহরণ।প্রভূত খ্যাতি, যশ এবং সাফল্য পেলেও, মানুষ হিসাবে সাহির তিক্ততা বর্জন করতে পারেননি। তাঁর ব্যবহারের জন্য তাঁর সঙ্গে বহু মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি তাঁর সঙ্গে এক গায়িকার বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। গায়িকা দাবি করেছিলেন, গানে মূল ভূমিকা গায়কের, মোটেই গীতিকারের নয়। সাহির বললেন, যদি তা-ই হয়, তিনি গান লেখা বন্ধ করে পানের দোকান খুলবেন। এই সময় সাহিরের হাতে এগারোটা ছবি ছিল; এই বিরোধ যখন চরমে উঠল, তখন চরমে পড়ে থাকল মাত্র দুটো— ‘নয়া দৌড়’ (যাতে ছিল আশা ভোঁসলের কন্ঠে গান) এবং ‘পিয়াসা’ (যাতে গেয়েছিলেন গীতা দত্ত)। দুটো ছবিই ১৯৫৭ সালে মুক্তি পায়, এবং বিস্ময়কর সাফল্য পায়। দুঃখের বিষয়, এই সাফল্যের অল্প সময়ের মধ্যেই সাহির ‘নয়া দৌড়’-এর সঙ্গীত পরিচালক ও.পি. নায়ার এবং ‘পিয়াসা’-র সঙ্গীত পরিচালক শচীন দেববর্মণ-এর সান্নিধ্য থেকে সরে আসেন। কথা ছড়িয়ে পড়ে যে সাহিরের সঙ্গে কাজ করা কঠিন, এবং একটা সময় আসে যখন এন. দত্ত, রোশন এবং খাইয়াম ছাড়া, অন্য কোনও সঙ্গীত পরিচালক সাহিরের সঙ্গে কাজ করতে রাজি ছিলেন না।
সাফল্যের শিখর এবং ভঙ্গুর সম্পর্কের খাদ— এই দুইয়ের মাঝে, মা ছিলেন সাহিরের জীবনে এক অটল, সর্বব্যাপী উপস্থিতি। মায়ের প্রতি ভক্তি ভারতীয়দের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সাহিরের নিষ্ঠা ছিল আশ্চর্য, এবং বলা যায়, অত্যধিক। মা ছিলেন সাহিরের সর্বক্ষণের সঙ্গী, সে সাহির কোনও মুশায়রাতেই যান, বা পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে। জীবনে যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মা-ই ছিলেন তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা— সর্দার বেগম ছিলেন সাহিরের কম্পাসের দৃঢ়, ধ্রুব উত্তরদিক। কিন্তু সময় ও বয়স থেমে থাকে না, সর্দার বেগম মারা যান, এবং পুত্র সাহির হয়ে পড়েন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, দীর্ণ, দিশাহীন। যে সাহির ছিলেন লড়াকু ও উদ্যমী, আর নিজের বিশ্বাসে একেবারে অটল, যিনি নির্ভীক ভাবে টক্কর নিয়েছিলেন তৎকালীন গায়ক, সঙ্গীত পরিচালক, তারকা, এমনকী সরকারের সঙ্গে, মায়ের মৃত্যুর পর তিনি হয়ে দাঁড়ালেন নোঙরহীন, আগের সাহিরের একটা নিতান্ত ছায়া। মাতৃবিয়োগে তিনি এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে নিজের ঘরে পর্যন্ত ঘুমোতেন না, বসার ঘরের সোফায় শুয়ে রাত কাটাতেন।
তা ছাড়া, এক দিকে যখন সম্মানের বন্যা বইছে— ১৯৭১-এ পদ্মশ্রী পাচ্ছেন, সাহিরের নামে নামকরণ হচ্ছে এক প্রজাতির গোলাপের, লুধিয়ানায় একটা পার্কের এবং ভারতীয় সেনার একটা চক-এর, তখনই আবার ঘটে যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে একের পর এক বন্ধুর ছাড়াছাড়ি।
১৯৮০ সালে সাহিরের মৃত্যু হয়, নিঃসঙ্গ মৃত্যু। খবর পেয়ে ওঁর বাড়িতে যখন ছুটে যাই, ওঁর দুই বোন সমেত সেখানে হাজির ছিলেন মাত্র চারজন। চিকিৎসক আমাকে বললেন, ওঁর হাত দুটো সোজা করে দিতে। করলাম, আর তখন হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, কী পরিমাণ ক্ষমতা এবং কাব্য ওই হাত থেকে প্রবাহিত হয়েছে; কত নজম, গজল, দ্বিপদী এবং অলীক জাদু সৃষ্টি করেছে এই হাত, যা এখন নিথর, প্রাণহীন। বহু বছর আগে ওই হাত আমাকেও আশীর্বাদ উপহার দিয়ে গিয়েছিল।
আমার পিতা এবং মামার সৌজন্যে আমার ওই প্রজন্মের বেশ কিছু বিখ্যাত লেখক এবং কবির সঙ্গে আলাপ ছিল— সাহির, কৃষন চন্দর, ইসমাত চুঘতাই, নরিন্দর বেদী, মজরুহ সুলতানপুরী এবং কাইফি সবাই একটি দল ছিলেন, একটি ‘কাবিলা’, একটি সম্প্রদায়, যার সঙ্গে আমি ছেলেবয়স থেকেই পরিচিত। প্রথম বম্বে আসার পর আমার বাবার থেকে আমি দূরে সরে আসি, বোধহয় সাহির আমার মধ্যে নিজের অল্প বয়স এবং সংগ্রামের একটা ছবি দেখতে পান। আমার কোনও থাকার জায়গা ছিল না, পরের বেলার খাবার কীভাবে জুটবে জানতাম না। মাত্র ২১ বছর বয়স ছিল আমার, কিন্তু আমি কবিতাপ্রেমী ছিলাম, এবং বেশ কিছু কবির লেখাপত্র খুব ভাল পড়া ছিল। সাহির আমাকে ‘নওজওয়ান’ নামে ডাকতেন, বলতেন: ‘নওজওয়ান, শোনো আমি কী লিখেছি।’ উনি আমার মতামতকে সম্মান দিতেন, এবং আমি ওঁর বাড়ি গেলে আমার সঙ্গে সুরাপান ও নৈশভোজ উপভোগ করতেন।
মাসিক এই সান্ধ্য সাক্ষাতের ধারা ভাঙে ১৯৬৭-এ, যখন আমি একদিন সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমার হাতে কোনও কাজ ছিল না, এবং আমি ওঁর কাছে অনুনয় করি, একটা ফিল্ম সেট-এ, সহকারীর কাজের জন্য যদি আমার নামটা একটু সুপারিশ করে দেন। উনি বলেন, প্রত্যেক যুবককেই এই ধরনের সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, শিগগিরই এই দুঃসময় কেটে যাবে। উনি আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দেন, এবং আমি বেরিয়ে আসি। বেরিয়ে দেখি, আমার হাতে দুশো টাকা— আমার দু’মাসের খরচ চলার পক্ষে যথেষ্ট, যাকে বলে একটা রাজকীয় অঙ্ক।
তারপর একটা সময়ে, কাজ সত্যিই আসে, এবং কখনও কখনও একই ছবিতে আমি ও সাহির কাজ করতে শুরু করি, উনি গীতিকার হিসেবে, আমি চিত্রনাট্যকার হিসেবে। ‘দিওয়ার’, ‘ত্রিশূল’ এমনই দুটো ছবি। আমাদের মাঝে মাঝে কিছু পার্টিতেও দেখা হত। তখন আমাদের মধ্যে যে মশকরাটা চলতেই থাকত, তা হল, আমার কাছে সাহিরের দুশো টাকা পাওনা রয়েছে, কিন্তু আমি তা কক্ষনও ফেরত দেব না। সাহির মজা করে প্রতিবাদ করতেন আর বলতেন, ওই টাকা আদায় করেই তিনি ছাড়বেন।
ওঁর মৃত্যুর পরের দিন, কিছু বন্ধু এবং আত্মীয়ের উপস্থিতিতে সাহিরকে কবর দেওয়া হয়। কবরস্থান থেকে বেরোচ্ছি, এমন সময় এক পরিচিত মানুষ আমাকে থামান। বলেন, যে-লোকটি কবর খুঁড়েছিলেন, তাঁর দুশো টাকা পাওনা আছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই টাকা চুকিয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠি।
এর কিছু পরে বুঝি, এই পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার কাজটা নিয়তি-নির্দিষ্ট। আমার একজন গুরু, এক বয়োজ্যেষ্ঠ পরামর্শদাতা, এক কিংবদন্তির কাছে আমার দেনা এভাবে মেটানো গেল। সাহির বোধহয় নিজের মশকরাটাকে এভাবেই সত্যি করে নিলেন।
আমরা এখন সাহিরের শতবর্ষ উদযাপন করছি। আমি করছি আমার স্মৃতির সাহায্যে, অগণিত মানুষ করছেন তাঁর কবিতাকে সঙ্গে নিয়ে। সাহির, শতবর্ষের শুভেচ্ছা জানাই, আপনার কবিতা যেন ভবিষ্যতের বহু শতাব্দী জুড়ে বেঁচে থাকে।
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook