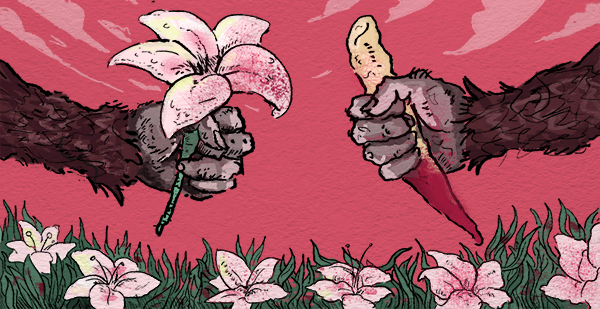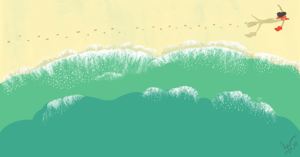জানি জানি, বন্ধু, জানি—
তোমার আছে তো হাতখানি॥
‘হাত! সেবার এই হাতের জোরেই হোমিনিনরা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। নইলে, মানুষের ইতিহাস যে ঠিক কোন খাতে বইত, সে-কথা কে-ই বা নিশ্চিত করে বলতে পারে?’
যদি এটা ঘনাদার গল্প বা তার প্যাস্টিশ হত, তাহলে বোধহয় ঠিক এমনই লাগসই ভাবে শুরু হয়ে যেতে পারত এই লেখাটি, সঙ্গে থাকত বনোয়ারির গরমাগরম ভেজে-আনা কচুরি আর শিশিরের টিন থেকে নির্বিবাদে হাতিয়ে নেওয়া সিগ্রেটের ধূম্রজাল। তারপর, বিস্তর অনুরোধ-উপরোধের বেড়া টপকে, লম্বা ভণিতা আর রূদ্ধশ্বাস সাসপেন্সের পর, আমরা জানতে পারতাম, কীভাবে নিছক হাতের জোরে একদল হোমিনিন (মনুষ্যজাতীয় আদিম দ্বিপদ প্রাণী— ঘনাদা তাঁর করুণাঘন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জানিয়ে দিতেন, গৌর, শিশির, শিবুদের বেকুব মুখের দিকে চেয়ে) বিবর্তনের দৌড়ে অন্য প্রাইমেটদের ওপর টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর সেক্ষেত্রে, ঘনাদার যে-কোনও গল্পের মতোই, এই গল্পটিকেও বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক থেকে শতকরা একশোভাগ নির্ভুল বলে ধরে নিতে আমাদের কোনও অসুবিধা হত না।
বস্তুত, প্রাইমেট থেকে হোমিনিডে বিবর্তনের ক্ষেত্রে, হাতের শারীরবৃত্তীয় গঠন ও অঙ্গসংস্থানের যে একটা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে, সে-কথা আজ স্বীকৃত ও প্রমাণিত। মানুষের হাতে রয়েছে পূর্ণত বিপরীতমুখী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ (বিজ্ঞানের পরিভাষায় ulnar opposition বা fully opposable thumb), যার ফলে আমরা অনায়াসে বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে কড়ে আঙুল-সহ অন্য সমস্ত আঙুলের ডগা ও গোড়া স্পর্শ করতে পারি। শিম্পাঞ্জি, গোরিলা-সহ অন্যান্য প্রাইমেটদেরও বিপরীতমুখী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রয়েছে, কিন্তু তাদের বুড়ো আঙুলের দৈর্ঘ্য বাকি আঙুলগুলির তুলনায় যথেষ্ট ছোট। হাতের চারটে আঙুল আকারে লম্বা ও নমনীয় হওয়ার ফলে, গাছের ডাল বেয়ে ওঠানামা করা তাদের পক্ষে ঢের সহজসাধ্য হয়েছে, কিন্তু সূক্ষ্ম কাজের জন্য যে-দক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রয়োজন, তা তারা আয়ত্ত করতে পারেনি। অন্যদিকে, মানুষের বুড়ো আঙুলের দৈর্ঘ্য বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য আঙুলগুলি আকারে খর্বকায় হয়েছে, ফলে পাথর বা গাছের ডালকে হাতের মুঠোয় ধরে, তাকে অস্ত্র বা যন্ত্র (tool) হিসেবে ব্যবহার করার কৌশল তারা শিখে নিতে পেরেছে সহজেই।

কেউ-কেউ নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন, পরিচালক স্ট্যানলি কুব্রিক তাঁর ১৯৬৮ সালে নির্মিত ছবি ‘২০০১: আ স্পেস ওডিসি’-তে কী অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন বিবর্তনের এই গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদলটি। সিনেমার শুরুতে আমরা দেখি, আফ্রিকার ভেল্ড অঞ্চলে, একটি পানীয় জলের প্রস্রবণ দখল করে নিয়েছে একদল হোমিনিন, এবং অন্য হোমিনিনদের তারা সেই জলের ধারেকাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। শেষে, অন্য দলের একজন আবিষ্কার করে ফেলে কীভাবে হাতের মুঠোয় শক্ত করে পাকড়ে ধরতে হয় মৃত পশুর হাড়, আর তার ফলে, কীভাবে তা এক অতীব কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত হয়। হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরা সেই হাড় দিয়ে সে পিটিয়ে মেরে ফেলে বিরোধীদলের এক সদস্যকে। বিরোধীরা ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে, প্রস্রবণের ওপর সে অনায়াসে কায়েম করে নিজের কর্তৃত্ব। এবং, এক-অর্থে, সেখান থেকেই সূচনা হয় মানুষের সভ্যতার। পরবর্তীকালে, এই হাতের জোরেই সে পাথর দিয়ে অস্ত্র বানাবে, পাথরে পাথর ঘষে শিখে নেবে আগুন জ্বালাতে, শুরু হবে চাষবাস, এবং মানুষের যন্ত্রসভ্যতা ক্রমশ অপ্রতিহত বেগে অগ্রসর হতে থাকবে। ‘২০০১: আ স্পেস ওডিসি’-র প্রথম পর্বের শেষে আমরা দেখব, শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া সেই হাড়টিকে, একটি অবিস্মরণীয় ম্যাচিং কাটের মাধ্যমে, কৃত্রিম উপগ্রহের ছবি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করবেন কুব্রিক। আদিম হোমিনিন, এভাবেই, ক্রমশ পরিণত হবে হোমো ফাবের বা যন্ত্রনির্মাণকারী প্রজাতিতে।
মানুষের সভ্যতার উন্মেষমুহূর্তটিকে চিহ্নিত করার জন্য কুব্রিক যে এমন একটি হিংস্র ও নৃশংস ঘটনাকেই বেছে নিলেন, তার একটা গভীরতর তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে হয় আমার। মানুষের উদ্ভাবনীশক্তি একদিকে যেমন তাকে প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার সামর্থ্য জুগিয়েছে, তেমনই তা, অন্যদিকে, সূচিত করেছে পারস্পরিক হানাহানি ও হিংসার এক অনিঃশেষ ঐতিহ্যের। মানুষের ইতিহাস ক্রমশ পরিণত হয়েছে আত্মধ্বংস ও আত্মঅবমাননার ধারাবাহিক প্রতিবেদনে। কুব্রিক কি ঠারেঠোরে সে-কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন?
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন প’ড়ে আছে
যন্ত্রসভ্যতার কৃত্রিমতায় বিচলিত হয়ে, আমরা প্রায়শই প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবি; ছুটি পেলেই বেড়িয়ে পড়ি পাহাড়, জঙ্গল কিংবা সমুদ্রের উদ্দেশ্যে, হয়তো-বা প্রকৃতির টানেই। শুধু আমরা নই, পাশ্চাত্যের রোম্যান্টিক কবিকুল থেকে আরম্ভ করে, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, বিভূতিভূষণ, কিংবা এমার্সন ও থরোর মতো মার্কিন স্বজ্ঞাবাদী দার্শনিকরাও, প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থানের শতেক গুণগান গেয়েছেন তাঁদের লেখালিখির মাধ্যমে। থরো তো জঙ্গলের মধ্যে কুটির বানিয়ে, এক-দু’দিন নয়, টানা দু’বছর কাটিয়ে দিলেন প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যে। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা ও তজ্জনিত আত্মোপলব্ধি নিয়ে লেখা বই ‘ওয়ালডেন’ আজও রীতিমতো সমাদৃত।
তবে, প্রকৃতির এই শান্ত, সমাহিত রূপের উল্টোপিঠে, তার যে একটা ভয়াবহ ও ক্রূর চেহারাও বিদ্যমান, সে-কথাও কেউ-কেউ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন বইকি! রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে, কোলরিজ এবং এডগার অ্যালান পো, তাঁদের লেখায়, প্রকৃতির এই তামস রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন অসামান্য নৈপুণ্যে। আবার, এ হয়তো নিছক কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, রোম্যান্টিক ভাবান্দোলনের প্রায় সমসময়েই, ইওরোপে জন্ম নেবে গথিক সাহিত্য— প্রকৃতির ভয়াল, রহস্যময় ও ব্যাখ্যাতীত রূপই যার প্রধান চালিকাশক্তি।
মোদ্দা ব্যাপার হল, প্রকৃতির কোলে জীবনযাপনের চিন্তাটা আমাদের মেদুর, ভাবালু ও বাষ্পাকুল চোখে যতই লোভনীয় ঠেকুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে তা বোধহয় ততখানি সুখপ্রদ নয়; সহজসাধ্য তো নয়ই! যোগ্যতমের উদ্বর্তন যে কতটা নির্মম ও ক্ষমাহীন হতে পারে, প্রকৃতিকে একটু বেশি কাছ থেকে দেখতে গেলেই সে-কথা হাতেনাতে টের পাওয়া যায়। হোমিনিনরা যে শেষ অবধি টিকে যেতে পেরেছিল, এবং আস্তে-আস্তে গোটা পৃথিবীজুড়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান কারণ, প্রকৃতি ও পশুজগতের সঙ্গে ক্রমাগত প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের ধারাবাহিক জয়লাভ। শুধু তাই নয়, অস্তিত্বরক্ষার খাতিরে তাকে তার স্বজাতির সঙ্গেও লড়াই করতে হয়েছে। প্রতিযোগিতায় হেরে, হোমো সেপিয়েন্সদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে নিয়ান্ডারথালরা, যদিও, আমাদের ডিএনএ-র নকশায়, আমরা আজও তাদের চিহ্ন বহন করে চলেছি।
এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, অস্তিত্বরক্ষার লড়াইটুকু মানুষের ক্ষেত্রে সত্যি হলেও শেষ সত্যি নয়, এবং সেখানেই অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে তার প্রধান পার্থক্য। একদিক থেকে দেখলে, মানুষের যাত্রাপথের অনেকটাই তৈরি হয়েছে প্রকৃতির উল্টোবাগে হেঁটে। মানুষের সভ্যতার যা-কিছু মহান— তার নীতি, ধর্ম (রিলিজন অর্থে নয়), ন্যায়, সাম্য ইত্যাদির ধারণা, তার বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প— সমস্তই আদতে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে একের পর এক সোচ্চার বিদ্রোহের নিশান। এতদ্সত্ত্বেও, হিংসা, হানাহানি ও রক্তপাত মানুষের পিছু ছাড়েনি।
ফ্রয়েড বলেছিলেন, মানুষের চেতনায় মৃত্যুকাম (ডেথ ড্রাইভ, থানাটোস) আর জিজীবিষা (ইরোস) পাশাপাশি বিদ্যমান। মানুষের যাবতীয় ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ— যুদ্ধ, হত্যা, খুনোখুনি— এসবের জন্য দায়ী তার মৃত্যুকাম। আর অপরদিকে, জিজীবিষা তাকে ঠেলে দেয় সৃষ্টিশীলতার দিকে— তার যৌনতা, প্রেম, শিল্প, এই সমস্তই সেই উদগ্র জীবনতৃষ্ণা থেকে উৎসারিত। ফলে, যে-হাত দাঙ্গার সময়ে পড়শির দোকানে আগুন লাগায়, বা অস্ত্রের কোপে তাকে হত্যা করতেও পিছপা হয় না, সেই হাতই পরম স্নেহে নিজের সন্তানের মুখে খাদ্য তুলে দেয়, হয়তো-বা প্রেমিকাকে স্পর্শ করে সপ্রেমে। যে-হাত নিয়ত গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃতির গোপন রহস্যকে বুদ্ধির গোচরে আনতে চায়, সেই হাতই আবার তাকে ব্যবহার করে ভয়াবহ মারণাস্ত্র হিসেবে। যদি বলি, ডেথ ড্রাইভ আর ইরোস, পর্যায়ক্রমে, মানুষের হাতকে সচল রাখে, এবং তাকে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ার করে তোলে, তাহলে বোধহয় সত্যের খুব একটা অপলাপ হবে না।
এই প্রসঙ্গে, হলোকস্টের পটভূমিকায় লেখা, জনাথান লিটেলের ‘দয়ালু মানুষজন’ (Les Bienveillantes) উপন্যাসটির কথা মনে পড়ল। ২০০৬ সালে, প্রি গ্যঁকুর এবং গ্রাঁ প্রি দু রোমাঁ-র মতো দু-দুখানা জাঁদরেল পুরস্কার পাওয়ার পর, প্রশংসার পাশাপাশি প্রভূত নিন্দামন্দও জুটেছিল বইটির কপালে। কেননা, উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল একজন অনুশোচনারহিত প্রাক্তন নাৎজির দৃষ্টিকোণ থেকে, যে আবার একইসঙ্গে উভকামী এবং অজাচারী; ফলে, বইয়ের মধ্যে বীভৎসরসের পরিমাণ কিছু বেশি ছিল, যা অনেকেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। বইয়ের নায়কের জবানিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন লিটেল—যদি ভাবি, এই গোটা হলোকস্টটাই আসলে হিটলার, হিমলার, আইখমানের মতো কয়েকজন বিকৃতমস্তিষ্ক দানবের চিন্তাপ্রসূত, এবং কেবলমাত্র তাদের উদ্যোগেই এতবড় একটা কাণ্ড সংঘটিত হতে পেরেছিল, তাহলে মস্ত বড় ভুল করব আমরা। যে-পয়েন্টসম্যানরা ইহুদী-বোঝাই ট্রেনগুলোকে নির্বিঘ্নে পাস করিয়ে দিত, নির্বিকারমুখে সবুজ ঝাণ্ডা দোলাত যে-গার্ডরা, যে-হাজার হাজার কেরানি দপ্তরের ফাইলে হিসেব রাখত এইসব কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের জমাখরচ আর উৎপাদনের, তারা কি নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে? হতে পারে, সমস্ত ঘটনা তারা জানত না, তারা জানত না কাঁটাতারের আড়ালে ঠিক কী কী ঘটছে এইসব ক্যাম্পগুলোতে, জানত না ‘ফাইনাল সলিউশন’-এর কথা। কিন্তু, নিজের অজান্তে বা আধা-জ্ঞানে, এবং সর্বোপরি বিনা-প্রশ্নে, তারাই এই বিরাট ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রেখেছিল; রাষ্ট্রের ওপর, রাষ্ট্রনায়ক ও নেতাদের ওপর তাদের বিশ্বাস আগাগোড়া অটুট ছিল। কোথাও কোনো গণ-অভ্যুত্থান হয়নি, কোনো বিদ্রোহও নয়। যে-শ্যুটজস্টাফেল এবং এস এস কমান্ডোবাহিনী ক্যাম্পগুলোকে পাহারা দিত, তারা তো জানত ক্যাম্পের ভেতর কী অবর্ণনীয় অমানবিকতার উদযাপন ঘটছে প্রত্যেকদিন, তবু তারা নিজেদের কর্তব্যপালনে এতটুকু গাফিলতি দেখায়নি কখনও। ব্যক্তিগত জীবনে তাদের পরিবার-পরিজন ছিল, প্রেমিকাও ছিল নিশ্চয়ই। তারা নিশ্চয়ই বাড়িতে চিঠি লিখত, আর তাতে উপচে উঠত নিকটজনের প্রতি তাদের নিখাদ স্নেহ, প্রেম, মমতা। আবার তারাই সেই অসহায় মানুষগুলোকে লাইন করে নিয়ে যেত গ্যাসচেম্বারের দিকে, এবং ভেতর থেকে ভেসে-আসা চিৎকার শুনতে-শুনতে সিগারেট ধরাত, হয়তো হাসিঠাট্টাও চলত নিজেদের মধ্যে।

বস্তুত, লিটেল দেখাতে চাইছিলেন, রাষ্ট্র একটা বিরাট ঘূর্ণ্যমান যন্ত্র, আর আমরা তার কলকবজা, নাটবল্টুমাত্র। এই বিপুল যন্ত্রের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি আমাদের দৃষ্টি-বুদ্ধির গোচর হয় না বলেই, আমরা তাকে সচল রাখি, আমাদের ব্যক্তিগত আদর্শ ও মানবিকতার সঙ্গে কোনোরকম সংঘাত ছাড়াই। অথচ খানিকটা তলিয়ে ভাবলে, এমনটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, আমাদের এইসব ছোটখাটো কাজকর্মগুলোই আদতে রাষ্ট্রের যাবতীয় অন্যায় ও অবিচারের ভিত তৈরি করছে, এবং একটু-একটু করে তাদের মান্যতা দিচ্ছে; ফলত, ব্যক্তিগত আদর্শ বা বিবেকের দোহাই দিয়ে, আমরা যদি সেইসব কুকর্মের পিছনে আমাদের সমস্ত দায় অস্বীকার করে হাত ধুয়ে ফেলতে চাই, তবে তা এক হাস্যকর দ্বিচারিতায় পর্যবসিত হবে।
আমি কখনও আউশভিৎজে যাইনি। তবে শুনেছি, গ্যাসচেম্বারের কালচে ছোপধরা দেওয়ালগুলোর গায়ে না কি অসংখ্য লম্বা-লম্বা দাগ রয়েছে, নখের আঁচড়ের। জাইক্লোন বি-এর বিষক্রিয়ায় যখন ভেতরের মানুষগুলোর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, ফুসফুস ভরে উঠছে নিজের বমিতে, তখনও তারা হাতের ভরে, কোনোমতে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ওপরে উঠতে চাইছে। অবর্ণনীয় যন্ত্রণায়, আতঙ্কে, নখ দিয়ে আঁচড়ে ক্ষতবক্ষত করে তুলছে দেওয়াল; ভাবছে, এভাবেই বুঝি তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলা যাবে। একদল মানুষের হাতে তৈরি দেওয়ালের গায়ে আরেকদল মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণার এই শ্বাসরোধী চিহ্ন যেন মৃত্যুকামের বিরুদ্ধে তার সমবেত জিজীবিষার অন্তিম স্বাক্ষর হয়ে উঠেছে।

একটি স্মৃতি অন্য স্মৃতিকে টেনে আনে। ব্যক্তিগত স্মৃতির ওপর, এভাবেই আস্তে-আস্তে জমা হতে থাকে সমবেত স্মৃতির ভার, অন্য মানুষের, সমষ্টির। আমার মনে পড়ে যাবে, ২০০২ সালে, ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র প্রথম পাতায়, তিন বা চার কলাম জুড়ে ছাপা হয়েছিল এক যুবকের ছবি। হাতজোড় করে ক্ষমাভিক্ষা করছিল সে। তার চোখে, জলের চেয়েও যেটা আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেটা হল ভয়; এক অবিমিশ্র আতঙ্কের ছায়া। জেনেছিলাম, লোকটা গুজরাতের এক অখ্যাত, নিম্নবিত্ত ওস্তাগর, এবং ধর্মপরিচয়ে মুসলমান। সেখানে তখন গর্ভবতী মেয়েদের পেটে ত্রিশূল ঢুকিয়ে বের করে আনা হচ্ছিল জীবন্ত ভ্রূণ। দেখেছিলাম, পেছনে আগুন জ্বলছে, আর তার সামনে তরোয়াল হাতে জয়ধ্বনি দিচ্ছে একজন মানুষ। সেই একই মোটিফ— মৃত্যুকামের সামনে ভিক্ষাপ্রার্থী মানুষের জীবনতৃষ্ণা, তার বেঁচে থাকার উদগ্র আগ্রহ।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক তারা নব নব
জীবন আর মৃত্যুর কথা তো অনেক হল। এইবার, অন্য একজোড়া হাতের কথা বলি বরং। নীল হ্যান্ডমেড কাগজের ওপর কালি-কলমে আঁকা পুরুষের হাত, প্রার্থনার ভঙ্গিতে স্থির। কালো কালির সরু-সরু আঁচড়ে আশ্চর্যরকমের জীবন্ত হয়ে উঠেছে হাতদুটি, তাদের বলিরেখা এবং শিরা-উপশিরার নিখুঁত আঁকিবুকিসমেত। সামনে থেকে আলো এসে, তেরছা হয়ে, বাঁ-হাতের কনিষ্ঠার ওপর আর কবজির কাছে গোটানো জামার হাতায় পড়েছে। যেন সমস্ত অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত কোনো আলোর জন্যেই এই প্রার্থনা, এই বিনিদ্র প্রতীক্ষা তার। শুধুমাত্র রেখার টানটোনে, আলো-ছায়ার খেলাটি এত বাস্তবোচিতভাবে পরিস্ফূট হয়েছে, যে শিল্পীর দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহের আর কোনো অবকাশই থাকে না।
ছবিটি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বিখ্যাত জার্মান শিল্পী আলব্রেখট ড্যুরারের আঁকা। শোনা যায়, ফ্রাংকফুর্টের কোনো চার্চের অল্টারপিসের জন্য ফরমায়েশি এক ট্রিপটিকের (তিনভাগে বিভক্ত ছবি, তিনটে প্যানেলে আলাদা-আলাদা করে এঁকে, কবজা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়) প্রস্তুতি হিসেবে এই স্টাডিটি এঁকেছিলেন ড্যুরার। আবার অনেকে মনে করেন, হাতে তৈরি বিরল নীল কাগজের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্যেই ছবিটি আঁকা। সে যা-ই হোক, মানুষের সমর্পণের এই ভঙ্গিটি, তার পর থেকেই, দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে, কীভাবে যেন সর্বজনীন হয়ে উঠেছে।

আসলে, আস্তিক হোক বা নাস্তিক, অথবা অজ্ঞেয়বাদী, বিপুল ও সীমাহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে মহাবিশ্বের রহস্যে বিস্মিত হয়নি, এমন মানুষ বিরল। মানুষের অধ্যাত্মচিন্তা, দর্শন এবং বিজ্ঞান—সমস্ত যাত্রার সূচনাবিন্দুতেই রয়ে গেছে এই বিস্ময়ের বোধ। প্রকৃতি ও অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচনের লক্ষ্যে তার ধারাবাহিক যাত্রাটি কবে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হবে, বা আদৌ শেষ হবে কি না, সে-কথা বলা দুষ্কর। ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যায়, নিউটন থেকে শুরু করে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ পর্যন্ত, যে-নৈর্ব্যক্তিক ও নিয়মানুবর্তী মহাবিশ্বের ধারণার সঙ্গে আমরা ক্রমশ পরিচিত হয়ে উঠছিলাম, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এসে তার মূল ধরে টান দিল। নৈর্ব্যক্তিক ও দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ জগতের পরিবর্তে, আমরা পেলাম এমন এক জগত, যেখানে পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি প্রভাবিত করে পারমাণবিক ঘটনাবলীকে, এবং সম্ভাব্য অসংখ্য পরিণতির মধ্যে থেকে একটিমাত্র পরিণতিকে বাস্তবায়িত হতে বাধ্য করে। এভাবেই, নৈর্ব্যক্তিকতার পরিবর্তে, বিজ্ঞানের জগতেও ঢুকে পড়ল সাবজেক্টিভিটি বা প্রাতিস্বিকতা। এখানে পর্যবেক্ষক বা দর্শক বলতে অবিশ্যি শুধু মানুষ নয়, মানুষ অথবা যন্ত্র (যেমন ক্যামেরা, আলোকসংবেদী পর্দা ইত্যাদি) অথবা এই দুইয়ের সমবায়ে নির্মিত যেকোনো যৌগিক ব্যবস্থাকেই বোঝানো হয়ে থাকে।
জগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের এই অনিবার্য সীমাবদ্ধতার সূত্র ধরে আরেকটি বিষয়ও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—বিপুল ও সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের সাপেক্ষে মানুষের, তথা তার সভ্যতার, নির্বিশেষ ক্ষুদ্রতা ও সামান্যতাটুকু। অথচ, কী অনায়াসে সে-কথা ভুলে থাকি আমরা, এবং কী বিপুল অভিমানে, নিজেদের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের লক্ষ্যে, অর্থহীন বিগ্রহে ও যুদ্ধে ক্রমাগত খরচ করে ফেলতে থাকি আমাদের যাবতীয় উদ্যম, আমাদের প্রাণশক্তি ও আয়ু, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। অন্যের হাতের ওপর হাত রেখে, আরো বেঁধে-বেঁধে থাকার পরিবর্তে, পারস্পরিক দ্বেষ আর কৃত্রিম বিভাজনই আমাদের সভ্যতার অভিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়।
মানুষের চিন্তার জগতে এই ঘটনার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। ইন্দ্রিয় ও চেতনাধৃত প্রাতিস্বিকতার বাইরে বেরিয়ে, জগতকে তার সার্বিক পরিপূর্ণতায়, এবং এক নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব থেকে ব্যাখ্যা করার যে-প্রকল্প এতদিন যাবৎ আমাদের বিজ্ঞানভাবনার মূল চালিকাশক্তি ছিল, প্রশ্নায়িত হল তার কার্যকারিতা, এবং তার পুনর্মূল্যায়ণ জরুরি হয়ে দাঁড়াল। ব্যাপারটা কতকটা এইরকম— বাড়ির ভেতরে বসে, আমরা তার বাইরের আকার-আকৃতি বা দেয়ালের রং সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো ধারণা করতে পারি না, তার জন্য বাইরে থেকে বাড়িটিকে অবলোকন করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তেমনই, জগৎ-সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য, আমাদের প্রয়োজন হয় একটি god’s eye view। কিন্তু, আমরা নিজেরাই যদি এই জগতের অংশ হই, এবং আমাদের অংশগ্রহণ যদি প্রতিমুহূর্তে তার নকশাকে খানিকটা করে বদলে দিতে থাকে, তাহলে কি ঈশ্বরের চোখ দিয়ে জগতকে দেখা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর? না কি যেভাবে, জলের প্রতিসরণের ক্রিয়ায়, মাছের চোখে ধরা পড়ে এক কৌণিক, শঙ্কু-আকৃতির পৃথিবীর ছবি, সেভাবেই, আমরাও এক গভীর প্রমাদের শিকার, জন্মাবধি? কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিখ্যাত গবেষক কার্লো রোভেল্লি তাঁর বইতে লিখেছেন— জগত ঠিক কীরকম, এ-কথা নিশ্চিত করে বলা হয়তো সম্ভব নয়। শুধু, বিভিন্ন ঘটনার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, এক স্বতশ্চল, ধারাবাহিক পরিবর্তনের ছবিই আমাদের চোখে ধরা পড়ে, আর তাকেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি আমরা। বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণবাদের সঙ্গে এর সাদৃশ্যের কথাও তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না।
জগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের এই অনিবার্য সীমাবদ্ধতার সূত্র ধরে আরেকটি বিষয়ও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—বিপুল ও সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের সাপেক্ষে মানুষের, তথা তার সভ্যতার, নির্বিশেষ ক্ষুদ্রতা ও সামান্যতাটুকু। অথচ, কী অনায়াসে সে-কথা ভুলে থাকি আমরা, এবং কী বিপুল অভিমানে, নিজেদের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের লক্ষ্যে, অর্থহীন বিগ্রহে ও যুদ্ধে ক্রমাগত খরচ করে ফেলতে থাকি আমাদের যাবতীয় উদ্যম, আমাদের প্রাণশক্তি ও আয়ু, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। অন্যের হাতের ওপর হাত রেখে, আরো বেঁধে-বেঁধে থাকার পরিবর্তে, পারস্পরিক দ্বেষ আর কৃত্রিম বিভাজনই আমাদের সভ্যতার অভিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। আর তখনই, আলব্রেখট ড্যুরারের আঁকা ওই হাতদুটির কথা মনে পড়ে আমার—সভ্যতার তাবৎ আস্ফালনের বিপরীতে, নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা ও আত্মসমর্পণের ওই ভঙ্গিটি যেন ক্রমশ আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে, আরো তাৎপর্যপূর্ণও।
ছবি এঁকেছেন অনুষ্টুপ সেন