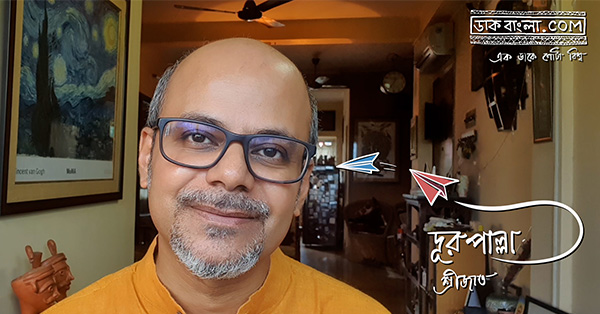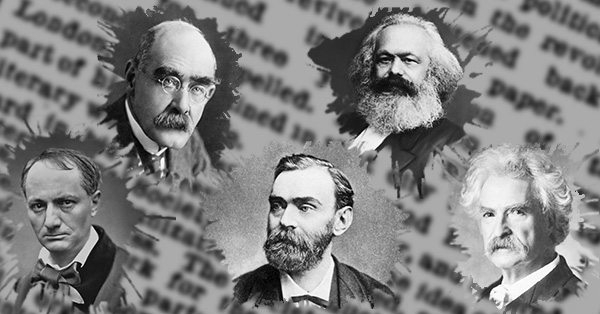থালা-বাটি-সমাজ

 শান্তনু চক্রবর্তী (January 1, 2022)
শান্তনু চক্রবর্তী (January 1, 2022)এখনও অবধি দুনিয়ায় একটা মাত্র যুদ্ধই স্রেফ মিষ্টি বিলিয়ে থামিয়ে দেওয়া গেছে! সবাই জানেন সেটা ‘গুপী গাইন ও বাঘা বাইন’-এ হাল্লা বনাম শুন্ডির যুদ্ধ। ঘোড়া-উট, তলোয়ার-বল্লম, বর্মে-চর্মে সাজগোজ করা সেনাবাহিনী দেখে পাবলিক চিরকাল বাস্রে বলে পালাবার পথ দেখেছে। হাল্লা রাজার সেনা দেখে গুপী-বাঘার ভয়টা অন্য রকম: ‘আধপেটা খেয়ে বুঝি মরে/ যত বেটা চলেছে সমরে’! গানের কথায় ‘সমরে’-র সঙ্গে অর্ধাহারে মরে যাওয়ার এমন চমকদার অন্ত্যমিলেই মালুম যুদ্ধবিরতি পদ্ধতিটা কী হতে যাচ্ছে! এরপরেই গুপী আর বাঘার এর-হাতে-ওর-হাতে-মিলে-তালি! আর তারপরেই আকাশ থেকে হাঁড়ি-হাঁড়ি ‘মিহিদানা পুলিপিঠে/ জিভেগজা মিঠে মিঠে/ আরও কত আছে মিষ্টি’ সব বৃষ্টির মতো নেমে আসে। এবং গাল-চোপসানো, কণ্ঠার হাড় বের করা রোগা ডিগডিগে হাল্লা-বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র, উটফুট ছেড়ে, বরফির জাদু আর মিলিটারি-শৃঙ্খলা চুলোর দুয়ারে পাঠিয়ে ওই মিষ্টির হাঁড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যস, গুপী-বাঘার কাম ফতে! যুদ্ধটুদ্ধ সব মাথায়! সেনাবাহিনীর খিদের ঢেউয়ের সামনে মন্ত্রী-সেনাপতি-ক্ষমতা-সিংহাসন সব হুড়মুড়িয়ে ভেসে যায়!


‘গুপী গাইন ও বাঘা বাইন’-এ হাল্লা বনাম শুন্ডির যুদ্ধ স্রেফ মিষ্টি বিলিয়ে থামিয়ে দেওয়া গেছে সত্যজিৎ ‘একেই বলে শুটিং’-এ লিখেছেন, উটওয়ালাদের কস্টিউম-টস্টিউম পরিয়ে হাতে অস্ত্রশস্ত্র গুঁজে দিয়ে সৈন্য সাজালেও তারা ‘অনেকদিন আধপেটা খেয়ে হঠাৎ আকাশ থেকে পড়া অফুরন্ত মিষ্টি দেখে... দিশেহারা হয়ে হা-ভাতের মতো খাওয়ার’ অভিনয়টা করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাই কামু মুখোপাধ্যায়-সহ ইউনিটের কয়েকজন খাদ্যরসিক অভিনেতাদের ঝটপট সেনার মেক-আপ কস্টিউম পরিয়ে দৃশ্যের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ফলে ছবিতে যাঁদের ক্লোজআপ-এ হাঁড়ি বাগিয়ে গোগ্রাসে মিষ্টি সাবড়াতে দেখা গেছে, তাঁরা প্রায় সবাই পেশাদার অভিনেতা। তার মানে যুদ্ধবিরতির একটা মেসেজ দেওয়ার পাশাপাশি খিদের রাজনীতিটাও সত্যজিতের মাথায় ছিল। আর সেটা কিন্তু গুপী-বাঘা হাল্লা যাওয়ার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে। কারা বেশি খাবে আর কারা কম— কাদের রাজভোগ নিশ্চিন্ত, আর কাদের অনশন অনিবার্য— ক্ষমতার দাঁড়িপাল্লায় তার মাপজোখ কীভাবে হয়, মার্কসবাদী না হয়েও সত্যজিৎ সেটা জানতেন।
তাই আমলকি গাঁয়ের রাজামশাই সাতসকালে দুধের বাটিতে আয়েশি শেষ চুমুকটুকু দিয়ে, মুখটা মুছেই গরিব দোকানদারের ছেলে গুপীকে গাঁ-ছাড়া করে। জঙ্গলে গিয়ে ভূতের রাজার দেওয়া বরের দৌলতে যা-চাই-খুশি খেতে পাওয়ার গ্যারান্টি পেল বলেই তো গুপী-বাঘা ক্ষমতার চোখে চোখ রেখে বলতে পারল ‘ও মন্ত্রীমশাই, ষড়যন্ত্রীমশাই’। মন্ত্রীর ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে শাসাতে পারল: ‘পড়লে ফাঁদেতে চুপসিয়ে যাবে ঢাক, জয়ঢাক!’ এই মন্ত্রীই হাল্লার রাজ্যসুদ্ধ লোককে না খাইয়ে শুকিয়ে মারে! প্যাংলাপনা গুপ্তচরের খিদের করুণ চোখের সামনে মুরগির ঠ্যাং চিবোতে-চিবোতে জ্ঞান ঝাড়ে: ‘তোমরা দিনরাত এত খাইখাই করো কেন বলো তো?’
এই মন্ত্রীই তো ঠিক করে দেয়, ক্ষমতার মাপে হাল্লার রাজ্যে কে কতটা খেতে পাবে। নীচের তলার সেপাই-গুপ্তচর খালিপেটে কোমরবন্ধ আরও আঁটো করে ঝোপ-ঝাড়-পাহাড়-নদী তোলপাড় করে দেশের শত্রু খুঁজে বেড়াবে। আর গোলগাল, নাদুসনুদুস সেনাপতি কিচ্ছুটি না করে দিনরাত কিছু-না-কিছু চিবিয়েই চলবে। রাজা বা মন্ত্রীমশাই ডাকলে, কাপড় সামলাতে-সামলাতে মুখভর্তি খাবারদাবার নিয়েই ছুটে আসবে! আসলে সেও তো ভয়ে-ভয়ে থাকে, এই বুঝি চাকরিটা গেল। আর চাকরি গেলে এই চর্ব্যচোষ্যও জুটবে না। মন্ত্রী তো একবার খিঁচিয়েও ওঠে— ‘আচ্ছা সেনাপতি, বেশি খেতে দিয়ে তোমার বুদ্ধিটা কি একদম লোপ পাইয়ে দিলাম?’ রাজ্যসুদ্ধ লোকের পেটবাঁধা মন্ত্রীমশাইয়ের মুঠোয়— তবে খাবারের রাজনীতিটা সবচেয়ে ভাল ফুটে ওঠে জেলখানার সিকোয়েন্সে। খুব পেটুক না হলেও ভূতের দয়ায় রোজ রাজভোগ খেয়ে-খেয়ে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে গুপী-বাঘার নজরটা এখন বেশ উঁচু। হাল্লা জেলের লপসি তাই তাদের মুখে রোচে না। তাই গারদের মধ্যেই তারা গালা-ডিনারের বন্দোবস্ত করে ফেলে।
একটু আগেও চিমসে, হাড়গিলে মার্কা যে-কারারক্ষীটা নাকের ভেতর ঘড়ঘড় শব্দ তুলে বেঘোরে ঘুমোচ্ছিল, মাংস-পোলাও-পায়েসের গন্ধে সে ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠে। তারপর তার সে কী লম্ফঝম্ফ! অননুকরণীয় অভিনয়ে এই দৃশ্যে নৃপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর আস্ত শরীরটাকেই কয়েক জন্মের খিদে বানিয়ে ফেলেছিলেন। আর সেই শরীরভরা খিদের ঠিকরে আসা চোখের সামনে গুপী আর বাঘা একটার পর একটা সুখাদ্যের ডেমো দিতে থাকে— এটা মাংস, এটা পোনামাছ ইত্যাদি ইত্যাদি। খাদ্য কূটনীতির, যাকে বলে, মাস্টারস্ট্রোক।
ফল যা হওয়ার, তা-ই হয়। কারারক্ষী তালা খুলে গারদে ঢুকে গুপী-বাঘার এঁটো পাতের ওপরেই লাফিয়ে পড়ে। বন্দিরা ‘আমরা তবে যাই’ বলে নিশ্চিন্তে কেটে পড়ে। রক্ষীও হাত নেড়ে তাদের টাটা করে দেয়। জয় হয় খিদের। এই স্ট্র্যাটেজি এবার ময়দান-এ-জঙ অবধি পৌঁছে যায়। হাল্লা রাজার হাড়-জিরজিরে বাহিনীর মাথার ওপর আকাশ থেকে ‘রসবৃষ্টি মধুবৃষ্টি’! সেই মিষ্টি-মধুর বৃষ্টিতেই সেনা বিদ্রোহের সৃষ্টি। আর সেই বুভুক্ষু বিদ্রোহী সৈন্যদের এলোমেলো পায়ের নীচেই ষড়যন্ত্রীমশাইয়ের শুন্ডি দখলের গ্র্যান্ড মিশনটা তার আঁকড়ে ধরা মিষ্টির হাঁড়িটার মতোই চেপ্টে, চটকে, ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।
‘গুপী গাইন ও বাঘা বাইন’-এর মতো ঠিক এভাবে না হলেও, সেই ‘পথের পাঁচালী’ থেকে ‘আগন্তুক’ অবধি সত্যজিতের লম্বা সিনে-সফরে খিদে, খাবার আর খাবারের রাজনীতিটা নানা ভাবে এ-কোণ সে-কোণ দিয়ে বারবারই ঢুকে পড়েছে। সত্যজিৎ জানতেন, রান্নার ধরন, কী রান্না হচ্ছে, সেই রান্না করা খাবার কীভাবে পরিবেশন হচ্ছে, এবং বিভিন্ন চরিত্র সে খাবার কীভাবে খাচ্ছে, এ-ব্যাপারগুলো একটা গোটা অঞ্চল, সেই অঞ্চলের জীবন-যাপন-সংস্কৃতির পরিষ্কার ছবি তুলে ধরে। সকাল, দুপুর, রাতের খাওয়ার তফাত, গ্রাম আর শহরের মেনুর ফারাক, ন্যারেটিভ-এর স্থান-কাল চেনায়।
একজন খাবারটা কীভাবে খাচ্ছে, সেটা দিয়েও একটা চরিত্রের মনের অবস্থা, আর্থ-সামাজিক মইয়ের কোন ধাপে সে আছে, সেসব বোঝা যায়। কাঁটা-চামচ ধরতে কতটা স্বচ্ছন্দ, খাওয়ার সময় ঠোঁটটা কতটা ফাঁক হচ্ছে, চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে চুকচুক-হুশহাস শব্দ করছে কি না, এগুলো তো টেবিল ম্যানার্সের দিক। তারপরেও তো বাঘারা থেকে যায়। শুন্ডির রাজপ্রাসাদে ঘরের মধ্যে কলা খেয়ে তার খোসাটা বেমালুম ফোয়ারার ভেতর ফেলে দিলেও বাঘা কিন্তু প্রতিবার খাওয়ার আগে হাতটা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে চায়। এমনকী হাল্লার জেলখানাতেও। 
‘পথের পাঁচালী’-তে ইন্দির ঠাকরুন যখন শেষবারের মতো ঘর ছেড়ে চলে যায়, সর্বজয়া তখন দুপুরে ভাত খাচ্ছে খাওয়ার সময় আসলে মানুষের আবেগ, সেন্টিমেন্টগুলো খুব নরম-তুলতুলে-স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। খেতে বসে খাওয়ার খোঁটা তাই সবচেয়ে বেশি গায়ে লাগে! যে-কোনও লোকের। এমনকী ইন্দির ঠাকরুনেরও। এমনিতে ইন্দির ‘পথের পাঁচালী’র সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে অসহায়, সবচেয়ে বেশি পরের দয়ায় বেঁচে থাকা একটা চরিত্র। তবু সর্বজয়া খাওয়া তুলে কথা বললে সেও ডাঁট দেখিয়ে, ছেঁড়া মাদুর আর তেলচিটে, নোংরা বোঁচকা বগলে বারবার ঘর ছাড়ে। সর্বজয়ার সঙ্গে তার তরজাটাও রান্নাঘর আর ভাঁড়ার নিয়েই। ইন্দির সর্বজয়ার রান্নাঘর থেকে প্রায়ই তেলটা, নুনটা, আনাজটা না বলে সরায়। দুর্গা এ-বাগান সে-বাগান থেকে যেসব ফলমূল কুড়িয়ে আনে, সেটাও ইন্দিরেরই ভোগে লাগে। সর্বজয়াকে সেজন্য লোকের কথা শুনতে হয়। তার আত্মসম্মানে লাগে। টানাটানির সংসারে ভাঁড়ারের হিসেবের জিনিস এদিক-ওদিক হয়ে গেলেও গৃহিণীর সমস্যা বাড়ে। ‘পথের পাঁচালী’ তো আসলে ব্রিটিশ-বাংলার একটা অজপাড়াগাঁয়ের অভাবের, খিদের, আর সেসবের সঙ্গে নানা রকম গেরিলা কায়দায় লড়াই চালিয়ে যাবার করুণ, বিষণ্ণ পাঁচালি। সেখানে ফলের বাগান বাঁধা দিয়ে সংসার খরচের টাকা আসে! সে-টাকা ফুরোলে, তোরঙ্গ খুলে সাবেকি বাসন বাঁধা দিয়ে উনুনে হাঁড়িটুকু চড়াবার চাল আসে। তাও ফুরোলে প্রতিবেশিনীর দয়া-দাক্ষিণ্যই ভরসা। গাছের ফল, ক্ষেতের আখ কিশোরী দুর্গার বাড়ন্ত শরীরে যথেষ্ট পুষ্টি জোগাতে পারে না। জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনা শাকপাতা সর্বজয়ার ভাঙা রান্নাঘরের দীনতা ঢাকতে পারে না। জমিদারি সেরেস্তার আট টাকা মাইনের কেরানি হরিহর স্বপ্নে পোলাও-কালিয়া রান্না করে। তিন মাসের বাকি-পড়া মাইনে এরিয়ার পাওয়ার খুশিতে আস্ত মাছ ঝুলিয়ে বাড়ি ফেরে। কর্তার মুখে তৃপ্তি আর গর্বের হাসি, মেয়ের মুখে একদিন একটু ভাল খেতে পাওয়ার হঠাৎ সুখ, তবু গিন্নির মুখে গুমোট-আঁধার কাটেই না। আসলে সর্বজয়া তো জানে, একদিনের ভরপেট মাছ-ভাতের উৎসবে তাদের বারোমাসের খিদের পাঁচালি শেষ হবে না। তার খিদে, ইন্দিরের খিদে, দুর্গার খিদে, আর তাদের সবার খিদে জমিয়ে অপুকে খিদের গ্রাস থেকে যতটা সম্ভব আড়াল রাখার চেষ্টাটা চলতেই থাকবে। অপুই তাই একমাত্র খিদে পেলে মুখ ফুটে বলে। সে পায়েস খেতে চাইলে অভাবের সংসারেও দুর্গাকে দোকান থেকে নতুন গুড় আনার হুকুম দেওয়া হয়। তবে অপুও যে খিদে চাপতে শিখে যাচ্ছে, শুকনো মুড়ি চিবিয়ে পাঠশালায় যাচ্ছে, সেটাও সর্বজয়ার সংলাপেই আমাদের জানা হয়ে যায়। ‘পথের পাঁচালী’র খিদের পাঁচালি তো সর্বজয়ার চোখেই আমাদের দেখা হয়ে যায়। ইন্দির ঠাকরুন যখন শেষবারের মতো ঘর ছেড়ে চলে যায়, সর্বজয়া তখন দুপুরে ভাত খাচ্ছে। রোদে তেতেপুড়ে আসা ইন্দিরকে সে জিরোতে অবধি না দিয়ে পত্রপাঠ বিদেয় করে। তার খাওয়া হয়েছে কি না, সেটা অবধি একবারও জানতে চায় না। ফ্রেমের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ইন্দির অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে তার বাপ-পিতেমোর ভিটের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। সেই চোখে কোথাও কি একটু মায়া লেগে থাকে? ইন্দির যতক্ষণ চোখের সামনে থাকে, সর্বজয়া দুধের বাটিটা মুখের কাছে তুলেও তাতে চুমুক দিতে পারে না। চলে যাওয়ার পরেই সে নিশ্চিন্তে খাওয়া শেষ করে। কিন্তু খুব নিশ্চিন্তে কি? তার চোখে কোথাও কি ঘন হয়ে থাকে খানিকটা অপরাধবোধ? ইন্দির কি চলে যেতে-যেতে এক গণ্ডগ্রামের হদ্দ গরিব পরিবারের ভাঙা নগণ্য রান্নাঘরের দখল নিয়ে অকারণ যুদ্ধে একতরফা সাদা পতাকা উড়িয়ে দিয়ে গেল? সর্বজয়ার খিদের পৃথিবীটা এরপর থেকে তো আর একটু লবণহীন হয়ে যাবে।
জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনা শাকপাতা সর্বজয়ার ভাঙা রান্নাঘরের দীনতা ঢাকতে পারে না। জমিদারি সেরেস্তার আট টাকা মাইনের কেরানি হরিহর স্বপ্নে পোলাও-কালিয়া রান্না করে। তিন মাসের বাকি-পড়া মাইনে এরিয়ার পাওয়ার খুশিতে আস্ত মাছ ঝুলিয়ে বাড়ি ফেরে। কর্তার মুখে তৃপ্তি আর গর্বের হাসি, মেয়ের মুখে একদিন একটু ভাল খেতে পাওয়ার হঠাৎ সুখ, তবু গিন্নির মুখে গুমোট-আঁধার কাটেই না। আসলে সর্বজয়া তো জানে, একদিনের ভরপেট মাছ-ভাতের উৎসবে তাদের বারোমাসের খিদের পাঁচালি শেষ হবে না। তার খিদে, ইন্দিরের খিদে, দুর্গার খিদে, আর তাদের সবার খিদে জমিয়ে অপুকে খিদের গ্রাস থেকে যতটা সম্ভব আড়াল রাখার চেষ্টাটা চলতেই থাকবে। অপুই তাই একমাত্র খিদে পেলে মুখ ফুটে বলে।
অপু-ত্রয়ীর বাকি দুটো ছবিতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা ততটা গুরুত্ব পায় না। ‘অপরাজিত’-তে তবু কাশীতে সর্বজয়ার ঘরকন্নার খানিকটা হদিশ মেলে। হরিহরকেও সেখানকার মোটা-সরওয়ালা-ঘন দুধ তৃপ্তির সঙ্গে খেতে দেখি। অপুও হিন্দিভাষী বন্ধুর ঘর থেকে ‘লাড্ডু অউর সামোসা’ খেয়ে আসে। কিন্তু এই নতুন খাদ্য-সংস্কৃতিটাকে সত্যজিৎ খুব একটা ‘এক্সপ্লোর’ করতে পারছেন না। কারণ হরিহরের মৃত্যুর পর সর্বজয়া অপুকে নিয়ে আবার বাংলাদেশেই ফিরে আসছে। দশাশ্বমেধ ঘাটে কথকতা করা হরিহরের চেনা বুড়ো মানুষটি অপুকে সঙ্গে নিয়ে কোনও এক রাজবাড়িতে যে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, সেটাও অপ্রয়োজনীয় বলেই সত্যজিৎ ছবিতে বাদ দিয়েছেন।
‘অপরাজিত’ উপন্যাসে বিভূতিভূষণ অবশ্য সেই ‘রাজকীয়’ ভোজের ভারি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছিলেন। পড়তে-পড়তে ওই একলা অসহায় বয়স্ক মানুষটা— সারা বছর যার দু’বেলা ভাল করে খাওয়াই জোটে না— তার জন্য বুকের ভেতর একটা তিরতিরে কষ্ট হবে।
একই রকম কষ্টটা ‘অপুর সংসার’-এ অপুর জন্যও একবার হয়। যখন বন্ধু পুলুর দৌলতে ‘সধবার একাদশী’ দেখে রেস্তোরাঁয় খেয়ে, রাস্তার পাহারাওয়ালাকে নিমচাঁদের ডায়ালগ শুনিয়ে অপুর ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ, তখন সে একবার শুধু বলে ফেলে, ‘আজকে একটু উত্তেজিত বোধ করছি। কদ্দিন পর পেটভরে খেলাম বল তো?’ এই অপুর পায়েস খাওয়ার জন্য গুড়, খিচুড়ি খাওয়ার বায়না মেটানোর জন্য মুগডাল জোগাড় করার কেউ নেই! এই অপু খিদের রাজ্যে একদম একা। তার খিদে আড়াল করার জন্যও কেউ কোত্থাও নেই। ছবিতে তো বাজে না— কিন্তু দর্শকের অন্তরমহলে তখুনি কি অলোকনাথ দে’র বাঁশিতে আকুল বেজে ওঠে ‘পথের পাঁচালী’র সেই আশ্চর্য থিম-সঙ্গীত?
‘অশনি সংকেত’-এ অবশ্য খাবার বা খিদে নিয়ে এত দুঃখ-স্মৃতি বিলাসের সময় নেই। চালের দর সেখানে কাগজের হেডলাইন থেকে গেরস্থের হাঁড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আকাশে যুদ্ধবিমানের চক্কর, গাঁয়ের মুদি-দোকান থেকে সরষের তেল উধাও হয়ে যাওয়া, একইসঙ্গে ঘটছে! আমাদের ছবির নায়ক একাধারে কৃষকপ্রধান গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত, কিছু ছাত্রের গুরুমশাই, আবার পার্টটাইম কবিরাজও। ছবির গোড়ায় জেলেদের কাছ থেকে ভেট পাওয়া আস্ত রুইমাছ হাতে দুলিয়ে বাড়ি ফিরলেও (‘পথের পাঁচালী’-র পর আর একবার সত্যজিতের ছবিতে বাঙালির চিরকেলে মৎস্যপ্রীতির ফিল্মি প্রমাণ মেলে), ক’দিন পরেই গঞ্জের দোকানে চাল কিনতে এসে গলাধাক্কা খায়। মানুষের পেটে ভাত নেই, মহাজনের গোলায় ধান নেই। যুদ্ধ আর মজুতদারির সাঁড়াশি-চাপে গ্রামবাংলার খাদ্যব্যবস্থা তছনছ হয়ে যায়।
সর্বজয়ার সংসারে বারোমাসই অভাব আর খিদে লেগেই থাকত। কিন্তু ১৯৪৩-এ বাংলা জুড়ে যেটা ঘটল, সেটা মহামন্বন্তর। আর সেটার প্রাথমিক ধাক্কাটা সংসারে মেয়েদের গায়েই সরাসরি আগে লাগল। দুর্ভিক্ষের গোড়ায় হয়তো কৃষকবধূ ছুটকিদের মতো বামুন পণ্ডিতের বউ সুশনি শাক আর গেঁড়িগুগলি খুঁজতে বেরোয়নি। কিন্তু রোজই যখন চাল বাড়ন্ত, সবার সঙ্গে সেও তখন জঙ্গলে মেটে আলু তুলতে যায়। খিদের জ্বালা উঁচুজাত-ছোটজাতের বেড়া মানে না। জঙ্গলে প্রথমদিন ছুটকিরাই ধর্ষকের হাত থেকে তাদের বামুনদিদির ইজ্জত বাঁচায়। কিন্তু দু’মুঠো চালের জন্য ছুটকি নিজেই তার শরীর আব্রু বেচে দেয় ইটভাঁটার মুখপোড়া লোকটার কাছে। দুর্ভিক্ষের সময় খিদের দাবি যে ওসব সমাজ-নীতি-নৈতিকতার ধার ধারে না, ’৪৩-এর মন্বন্তরের আগে বাঙালি এটা সেভাবে বোধহয় বোঝেনি।
একটা গ্রামের একটা পরিবারের গল্প বলতে বসে সত্যজিৎ বাংলাজোড়া ভুখা মানুষের মৃত্যু-মিছিলের আখ্যান তৈরি করে নেন। আর তার মধ্যেও গেরস্থ বাঙালির রোজকার ঘরোয়া খাদ্যসংস্কৃতি আর দাম্পত্য প্রেমের ভীষণ মানবিক দৃশ্য রচনা করে ফেলেন। চালের খোঁজে সাত ক্রোশ দূরের অন্য এক গ্রামের মহাজনের বাড়ি গেছে ছবির যুবক পুরোহিত। মহাজন তাকে চাল বিক্রি না করলেও, গৃহস্থের যাতে অকল্যাণ না হয়, তাই দুপুরবেলা বাড়ি বয়ে আসা ব্রাহ্মণের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করেন। গ্রামবাংলার গেরস্থ খাদ্যসংস্কৃতির এটাও কিন্তু একটা অঙ্গ। ক্ষেতের চালের ভাত, বাড়ির পুকুরের সদ্যধরা মাছ, আর বাড়ির উঠোনেই দোয়ানো গরুর দুধ দিয়ে অতিথি সৎকার।
কিন্তু আমাদের চেনা বামুনঠাকুরটি স্বপাক রান্নার পর একথালা ভাতের ওপর মাছের ঝোলের বাটিটা উপুড় করেও আর মেখে উঠতে পারছে না! থালার পাশেই রাখা দুধের পাত্রটাও দেখা যাচ্ছে। আয়োজনেও কোনও ত্রুটি নেই। তাহলে? আসলে ঠাকুরমশাইয়ের তখনই বাড়িতে গিন্নির অভুক্ত মুখটা মনে পড়ে যায়— নিজে না খেয়েও যে ঘরে যেটুকু যা আছে সেটা স্বামীর পাতেই তুলে দেয়! আমাদের, মানে দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্যসংস্কৃতির, এটাই দস্তুর বা রীতিরেওয়াজ। কিন্তু সত্যজিৎ তার উল্টো একটা মুহূর্ত তৈরি করেন। সেখানে অনেকদিন পর পেটভরে দু’মুঠো খাবার সুযোগ এলেও ক্ষুধার্ত স্ত্রীর কথা ভেবে স্বামীর হাতের গ্রাস আর মুখ অবধি পৌঁছতে চায় না! খিদের কবিতা ভালবাসায় ভরে ওঠে।
তবে খাদ্যসংস্কৃতির রিমোট যে মেয়েদের হাতেই মানায়, সত্যজিতের ছবিতে নানা ভাবেই সেটা ঘুরেফিরে এসেছে। বাড়ির ঘরোয়া ডিনার থেকে জমাটি পিকনিক, রান্না আর পরিবেশনের ভারটা মেয়েদেরই। তাদের তরিবত, আর কুশলতার ছোঁয়াতেই খাওয়া-দাওয়া স্রেফ পেট ভরানোর চেয়েও বেশি কিছু হয়ে ওঠে। খেয়ে আর তারিফ করেই ধন্য পুরুষমানুষরা খাদ্যসংস্কৃতির এত কিছু সূক্ষ্মতার তারতম্য বোঝে না— তাদের সে যোগ্যতাই নেই। মেয়েরা সামনে বসে খাওয়াবে— এটা খাও, ওটা নাও বলে জোরজার করবে— এ সাবেকিয়ানার প্রতি সত্যজিতের নিজেরও বোধহয় একটা পক্ষপাত ছিল। এমনকী তাঁর অলটার ইগো, ‘আগন্তুক’-এর মনোমহন মিত্র, এত বছর তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে, ঘোর জঙ্গলে আদিবাসী মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করে এসেও, ভাগ্নির খাঁটি মধ্যবিত্ত বাঙালি গৃহিণীপনায় মুগ্ধ হয়ে যান। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।
বাড়ির বউটি রাঁধাবাড়ায় তাই দাম্পত্য আবহাওয়ার ওঠা-পড়া ঝড়বাদলও টের পাওয়া যায়।
‘ঘরে বাইরে’-য় সন্দীপ যখন স্বদেশি প্রচারে নিখিলেশের জমিদারিতে প্রথমবার এল, তার বক্তৃতা আর ব্যক্তিত্বে বিমলার বুকের ভেতর সবে একটু দোলা লাগল। তখনও নিখিলেশের রাতের খাওয়ার সময় তার থালার পাশে পঞ্চব্যঞ্জন-পরমান্নের বাটি সাজিয়ে বিমলাও থাকে। ফুলকো লুচির শরীর ছিঁড়ে চিংড়ি মাছের মালাইকারির ঘন ঝোলে ডুবিয়ে মুখে পুরতে-পুরতেই নিখিলেশ সন্দীপের উগ্র স্বদেশিবাদ, তার গা-জোয়ারিপনার বিপদ নিয়ে আলোচনা করে। বিমলাও তার সঙ্গে তর্ক জোড়ে। তখনও অবধি নিখিলেশই তার সমস্ত পৃথিবী।
ফুলকো লুচির শরীর ছিঁড়ে চিংড়ি মাছের মালাইকারির ঘন ঝোলে ডুবিয়ে মুখে পুরতে-পুরতেই নিখিলেশ সন্দীপের উগ্র স্বদেশিবাদ, তার গা-জোয়ারিপনার বিপদ নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু তারপর যখন সন্দীপের আহ্বান দেশের ডাকের চেয়েও বেশি করে বিমলার মনের আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলল, তখন এসব রান্নাবান্না-ঘরকন্নায় সে যেন থেকেও নেই! বাড়ির কাজের মেয়েটি যখন জানতে আসে, কইমাছ কী করে রান্না হবে— আর সে একটুও না ভেবে খানিকটা হেলাফেলা, খানিকটা যান্ত্রিক অভ্যেসের মতো করে বলে দেয় ‘সরষেবাটা দিয়ে’— তখন তার বলার ভঙ্গিতেই বোঝা যায়, ওই রান্না বা তার রেসিপি নিয়ে সে আসলে একটুও মাথা ঘামাচ্ছে না।
আবার ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’-তে খাদ্য আর দাম্পত্য উদাসীনতার একটা উল্টো কিস্সা দেখি। লখনউ-এর দুই জায়গিরদার মীর আর মির্জা সাহেব অনন্ত দাবা খেলে চলে। বিকেল গড়িয়ে, সন্ধে পেরিয়ে, রাতের খাবার সময়ও বয়ে যায়। মির্জার বাবর্চিখানা— মানে হেঁশেল থেকে দুজনের জন্য বিরিয়ানি আসে। খেলতে-খেলতেই খাওয়া, তারপর হাত ধুয়েমুছে আবার খেলা! অন্দরমহল থেকে মির্জার তরুণী বেগম ডাক পাঠায়। মেয়েটির শরীর তখন আদরের জন্য ছটফট করছে। মির্জার কোনও হুঁশ নেই। তাগিদও নেই। সে বরং মীরের সামনেই বউকে ভেঙিয়ে বলে: বিবিদের নিয়ে এই সমস্যা। কোনও কাজ নেই— ‘বিরিয়ানি আচ্ছি থি’ এটুকু জানতেই নাকি বেগমের এত ডাকাডাকি! স্পষ্ট উপেক্ষা!
আসলে আওয়াধি বিরিয়ানি, লখনউ-এর পরোটা-কাবাব, বেগমের যুবতী শরীর, দেশের পালটে যাওয়া রাজনীতি— শতরঞ্জ-এর নেশার পাশে পার্থিব আর কোনও কিছুতেই মীর-মির্জার আসক্তি নেই। এভাবেই সত্যজিৎ লখনউ-এর খাদ্যসংস্কৃতি, তার আভিজাত্য-তমিজ-তেহ্জিব: এসবের আভাস দেন! কিন্তু মীর-মির্জা সেসব সুখাদ্যের ভোক্তা হলেও, সেটা তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করার যোগ্যতা যে তাদের নেই, সেটাও বুঝিয়ে দেন।
আওয়াধি বিরিয়ানি, লখনউ-এর পরোটা-কাবাব, বেগমের যুবতী শরীর, দেশের পালটে যাওয়া রাজনীতি— শতরঞ্জ-এর নেশার পাশে পার্থিব আর কোনও কিছুতেই মীর-মির্জার আসক্তি নেই এভাবেই খাবার, তার অভাব এবং প্রাচুর্য, তাকে ঘিরে মানুষের মন, সে-মনের লোভ, চাহিদা, খুশি, নিরাসক্তি, তার নীতি, রাজনীতি, নানা ভাবে সত্যজিতের ছবিতে ঘুরেফিরে এসেছে। ‘সোনার কেল্লা’য় মন্দার বোস যখন সার্কিট হাউসে তোপসেকে ডেকে, তার হাত থেকে লাঞ্চ প্যাকেটটা চেয়ে নিয়ে, একবার ভাল করে নিঃশ্বাস ভরে গন্ধ শুঁকে নিয়ে ফেরত দেয়, তখনই তার ভেতরের লোভী, পেটুক, এটা-ওটা দু’নম্বরি উঞ্ছবৃত্তি করে চলা একটা বেচারা-অভাবী লোক উঁকি দিয়ে যায়। একটু পরেই সে আবার পুরোদস্তুর ভিলেন হয়ে যাবে— কিন্তু তক্ষুনি মিনিটখানেকের জন্য সে নেহাতই একটা সাধারণ লোক। ‘জয়বাবা ফেলুনাথ’-এ ল্যাজা থেকে মুড়ো অবধি ঘোর মধ্যবিত্ত ক্যালকাটা লজ-এ যে ফেলুদা অ্যান্ড কোং হোটেলের নতুন কুকের হাতে রান্না করা মাছের ঝোল ভাত তৃপ্তি করে খায়, তাদের সঙ্গে ওই লোকটার অনেক তফাত।
খাওয়াটা সত্যজিতের ছবিতে স্রেফ ‘বিজনেস’ নয়, খাবারগুলোও নেহাত ‘প্রপস’ নয়। চিত্রনাট্যের সঙ্গেই সেগুলো ‘অর্গানিক’, প্রাণবান হয়ে ওঠে। ‘সদ্গতি’-তে দুখি চামার খালপেটে সারাদিন ভয়ানক শক্ত কাঠের গুঁড়িটা কাটার জন্য মরিয়া চেষ্টা করে চলে, আর ব্রাহ্মণ ভরপেট খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে উঠে ঢেঁকুর তোলে— ওই খাওয়াটা তখন শুধু অপরাধ নয়, ওটা পৈশাচিক, নৃশংসও।
‘শাখাপ্রশাখা’-য় খাবার টেবিলে অন্য ভাইরা আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি সাজাতে গিয়ে বিশ্রী ঝগড়া করে তেমনই ‘শাখাপ্রশাখা’-য় খাবার টেবিলে অন্য ভাইরা যখন যে যার একনম্বরি-দু’নম্বরি কাজ-কারবার নিয়ে কথা বলে, আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি সাজাতে গিয়ে বিশ্রী ঝগড়া করে, তখন স্কিৎজোফ্রেনিক মেজভাইটি প্লেট-বাটি-জলের গ্লাস কাঁপিয়ে জোরে-জোরে টেবিল চাপড়াতে থাকে। এটা কিন্তু টেবিল ম্যানার্সের দফারফা নয়— বরং সব রকম অনৈতিকতার বিরুদ্ধে একজন সৎ, শুদ্ধ মানুষের রাগি পবিত্র প্রতিবাদ।

প্রথমদিন দুপুরে ভাতের পাতে মেদিনীপুরের গয়নাবড়ি দেখে মুগ্ধ মনমোহন রায় দেন— ‘আহারের এত বাহার, এ শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব‘ অনেকেই বলেন, সত্যজিতের সারা জীবনের সিনেমাকর্মে যা-যা কথা বলা বাকি ছিল, তার সবটাই তিনি ‘আগন্তুক’-এর মনমোহন মিত্রকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। এ যেন রবীন্দ্রনাথের ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধের সেলুলয়েড-সংস্করণ। মনমোহন এখানে বারেবারেই আদিবাসী মানুষের প্রকৃতির আশীর্বাদধন্য খাদ্যসংস্কৃতিকে সভ্য মানুষের রান্না করা কৃত্রিম খাওয়া-দাওয়ার অভ্যেসের উল্টোদিকে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও সত্যজিৎ মনমোহনকে দিয়ে গেরস্থ বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতির সপক্ষে একটা মস্ত সার্টিফিকেট আদায় করে নিয়েছেন। প্রথমদিন দুপুরে ভাতের পাতে মেদিনীপুরের গয়নাবড়ি দেখে মুগ্ধ মনমোহন রায় দেন— আহারের এত বাহার, এ শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব। সত্যজিতের সারাজীবনের সিনেমাপঞ্জিও যেন সেই বাঙালি আহারের বাহারেরই একটা ধারাবাহিক চিত্রভাষ্য, যার খুশবু সময় পেরিয়ে আরও যেন খোলতাই হয়ে যায়।
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook