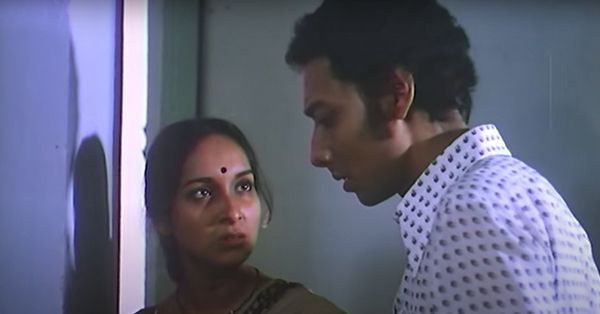আমাদের দেশে প্রায়ই ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হয়। নেতার ছেলে নেতা। ক্রিকেটারের ছেলে ক্রিকেটার, বলিউড তারকাদের ছেলেমেয়েরা অবশ্যই তারকা। এমনকী মাঝেমধ্যে কবির ছেলে কবিও! সেই হিসেবে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর ডাক্তার হওয়ার কথা ছিল। তাঁর প্রিয়তম পরিচালক আন্দ্রেই তারকভস্কির বাবা আর্সেনি ছিলেন কবি। ছেলে কবিতা না লিখলেও সিনেমার পর্দায় যেসব কাণ্ড ঘটালেন, পৃথিবীর অজস্র কবিতা সেই দৃশ্যপ্রবাহের সামনে তাদের সব শব্দ, প্রতীক, চিত্রকল্প, এমনকী নৈঃশব্দ্য সুদ্ধ হাঁটু মুড়ে বসে!বুদ্ধদেবের বাবা ডাক্তার হলেও ছিলেন সরকারি চাকুরে। বদলির চাকরি। ফলে মাঝারি, ছোট বা প্রায় মফস্সল শহরে বুদ্ধদেব শিশু থেকে বালক, বালক থেকে কিশোর হয়েছেন। এই বড় হওয়ার সময়টায় তাঁকে ঘিরে থেকেছে ছোট ছোট পাহাড়, টিলা— সেইসব পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা আচমকা ঝর্না— গোড়ালি অবধি ভিজিয়ে দেওয়া এক-চিলতে নদী— আর যতদূর চোখ যায়, দিগন্ত অবধি ছড়িয়ে থাকা এক আদিম ভূখণ্ড। সেখানে ঢেউ-খেলানো সবুজ, খয়েরি, লাল গায়ে-গায়ে। রুক্ষতা আর কোমলতা পাশাপাশি। সেই সঙ্গে সেখানকার মানুষজন। তারা একই সঙ্গে সরল-অসহায়-গরিব-প্রান্তিক। আবার মনের অন্দরে বীর-সাহসী-দার্শনিক-কবি!
এই প্রকৃতি আর মানুষদের সঙ্গে বড় হতে হতেই বুদ্ধদেব কলকাতায় আসেন। ডাক্তারের ছেলে ততদিনে নেশায় কবি। আর কেতাবি লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে পেশায় অর্থনীতির অধ্যাপক। ক্লাসে যাঁকে মূলত পড়াতে হয় ইকনোমেট্রিক্স। যেখানে নানা রকম আঁক কষে, গাণিতিক মডেলে অর্থনীতির তত্ত্বকে প্রমাণ আর প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। ফলে দেশের উন্নতি আর দুর্গতির ছবিটা সংখ্যা সেজে তাঁর চোখের সামনে, নখের ডগায় নড়েচড়ে, ঘুরেফিরে বেড়াত। ষাটের দশকের গোড়ায় তিনি যখন এই মহানগরে আসছেন, তখন সেখানেও অনেক ডামাডোল, ঝড়-তুফান। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেড়-দু’দশকের সরকারি অপকর্মের ক্ষার-সাবানে কেচে কেচে ফিকে। সাবেকি বুলি কপচে কংগ্রেস আর ক্ষমতা ধরে রাখতে পারছে না। ওদিকে দিন-বদল আনবে যে প্রাতিষ্ঠানিক বামেরা, তাদের সদর দপ্তরেও কামান দাগছে নকশালবাড়ি। সেই ‘বসন্তের বজ্রনির্ঘোষে’ ভেঙে পড়ছে, পাল্টে যাচ্ছে অনেক কিছুই। পঞ্চাশের বাংলা কবিতাতেও যে সুললিত, সুখশ্রাব্য, লিরিকাল মায়া— মানিক চক্রবর্তী, শামসের আনোয়াররা তার উল্টোদিকে ‘অ্যান্টি পোয়েট্রি’ বা ‘না-কবিতা’র রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছেন। বুদ্ধদেবও সেই লাইনেই কবিতার শরীর থেকে ছন্দ, অলঙ্কার, সব শাস্ত্রীয় কাব্যিপনা ছাড়াতে লেগে গেলেন। সেখানে আলমারির ‘ভেতর থেকে এসে শার্টের লম্বা হাত’ জড়িয়ে ধরে আলমারির ভেতরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ‘এবং নানা রঙের জামারা’ শেখায় ‘কী করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, এক জন্ম থেকে আর এক জন্ম ঝুলে থাকা যায় শুধুমাত্র একটা হ্যাঙার ধরে...’।
রাজনীতি, অর্থনীতি ও কবিতা বা না-কবিতা চর্চার পাশাপাশিই এই মহানগর, তার ফিল্ম সোসাইটিগুলো, আর সেখানে নিরন্তর বয়ে যাওয়া সারা পৃথিবীর সিনেমা-কর্মের অনন্ত স্রোত— স্বল্প সময়ের রাজনৈতিক কর্মী, পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক, এবং সময়-অসময়ের কবি বুদ্ধদেবকে অন্য এক সিদ্ধান্তের দিকে ক্রমশ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি টের পাচ্ছিলেন, সিনেমার ভাইরাস ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর চেতনায়, বোধে, অনুভবে। হয়তো অবচেতনেও। তারপর যখন বোঝা গেল সংক্রমণ সম্পূর্ণ, আরোগ্য অসম্ভব, তখন অধ্যাপনার চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া ‘আক্রান্ত’ বুদ্ধদেবের আর কোনও উপায় থাকল না।
তাঁকে নিয়ে যে একাধিক তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে, বা নিজে যেসব সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, সেখানে তাঁর ছবিতে স্বপ্ন, পরাবাস্তবতা, বা চেনা বাস্তবতার লৌকিক চলনের এক লহমায় অলৌকিক উড়ানে বদলে যাওয়ার শিকড় খুঁজতে সব সফরই শেষ অবধি পৌঁছে যায় রাঢ়-বাংলায় তাঁর শৈশবে। যেন সেখানে স্মৃতির শিশির আর কুয়াশা মেখে এতদিন অপেক্ষায় ছিল তাঁর সেই সিল্যুয়েটেড লং শট আর ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্সের নরম পেলব মায়া! হ্যাঁ, ‘লাল দরজার’-র ওই ছড়াটা: ‘ছোটি মোটি পিপড়া বটি... লাল দরজা খোল দো’, বা ‘বাঘ বাহাদুর’-এর ওই তীব্র প্রবল বাঘ-নাচ বুদ্ধদেবের ছোটবেলায় শোনা, দেখা। কিংবা ‘উত্তরা’-র ওই গাছের গায়ে ঝোলানো ডাকবাক্সে কান লাগিয়ে অন্দরের চিঠিগুলোর অন্তরের কথা শোনার খেলাটাও তাঁরা ছেলেবেলায় খেলছেন।

চিত্রগ্রাহক: স্বরূপ দত্ত
কিন্তু শতায়ু ঢোলশিল্পী ক্ষীরোদ নট্টকে নিয়ে ‘ঢোলের রাজা’-র মতো তথ্যচিত্র দিয়ে হাত পাকিয়ে বুদ্ধদেব যখন প্রথম কাহিনিচিত্র করতে আসছেন, তখন তো সে ছবির সারা গায়ে সত্তরের ঝোড়ো, রাগী, বিষণ্ণ সময়ের ছাই-ধুলো মাখামাখি। ১৯৭৮-এ ‘দূরত্ব’ তৈরির সময় ঋত্বিক আর নেই। কলকাতা-ট্রিলজির পর সত্যজিৎ ফিরে গেছেন সিপাহি বিদ্রোহের একটু আগের আওয়াধ আর তার রাজধানী লক্ষ্ণৌ-এ। এদিকে মৃণাল সেন তখনও চারপাশের সময়টাকে ধরবার যথার্থ সিনেম্যাটিক ভাষা খুঁজে ফিরছেন। ‘দূরত্ব’-তে অবশ্য মাঝেমধ্যেই মৃণাল আছেন। ভঙ্গিতে, মেজাজেও। কিন্তু মৃণালের সিনেমায় কখনও মধ্যবিত্তের সেই আত্মসমালোচনার পর্বটা শুরু হয়নি। অথচ প্রথম ছবিতেই বুদ্ধদেব মধ্যবিত্ত বাঙালি মেধাজীবীর ভদ্র ভণ্ডামি, আত্মপ্রবঞ্চনার নেকুপনাকে তীক্ষ্ণ তীব্র বিঁধলেন।
ছবির শুরুতেই কথক, এ কাহিনির নায়ক আর নায়িকা মন্দার আর অঞ্জলির সঙ্গে দর্শকদের আলাপ করিয়ে দেন, ভূমিকাভিনেতা এবং অভিনেত্রীর নামসুদ্ধ। যাঁরা মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ দেখেছেন, তাঁদের হয়তো সেই ছবিতে প্রোটাগনিস্ট রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে দর্শকের পয়লা মোলাকাতের ব্যাপারটা খানিকটা মনে পড়ে যেতে পারে। খানিকটাই। তবে ‘দূরত্ব’য় ন্যারেটর হিসেবে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের কথনের ভঙ্গিতে গোড়া থেকেই একটা শ্লেষ আর কৌতুকের স্বর সাপটে ছিল। আমাদের মনেই হচ্ছিল এই মন্দার লোকটাকে চিত্রনাট্যে পুরোপুরি ক্লিনচিট দেওয়া হবে না। তার অতীতটা খুঁড়ে দেখা হবে।

ছবি ঋণ: সম্বিত বসু
মন্দার সম্পর্কে ছবির গোড়াতেই আমরা দুটো হিন্ট পেয়ে যাচ্ছি। সে একটা কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ায় এবং অঞ্জলির সঙ্গে তার বছর দুয়েক আগে বিয়ে হয়েছিল। যে বিয়েটা টেকেনি। প্রথম দৃশ্যে মন্দারকে ক্লাসঘরে বসে রোল কল করতে দেখা যায়। সেই ক্লাসঘরের ব্ল্যাকবোর্ডে সেদিনের পাঠ্য বিষয়টা লেখা আছে আর সাদা দেওয়ালে কালো হরফে অস্পষ্ট কিছু রাজনৈতিক গ্রাফিত্তি। রাজ্যে কয়েক বছর আগের উত্তাল রাজনীতির স্মৃতিচিহ্নের মতো।
এই রাজনীতির প্রসঙ্গ ছবিতে ঘুরেফিরেই এসেছে। কখনও কথকতায়, কখনও সংলাপে। কথক জানাচ্ছেন, রাষ্ট্র ও তার পোষা আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসবাহিনী ‘হাতে হাত মিলিয়ে’ যাবতীয় বিপ্লবী অ্যাডভেঞ্চার ঠান্ডা করে দিয়েছে। রক্তের দাগ মুছে কলকাতা এখন ‘কল্লোলিনী তিলোত্তমা’ হচ্ছে। আবর্জনা ও যাবতীয় রাজনৈতিক বিরোধীদের সেখান থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হচ্ছে... টিং টং! আমরা এটাও জেনে যাই মন্দারও একদা ওই বিপ্লবের দলে ছিল। মাঝরাস্তায় গা বাঁচিয়ে সরে এসেছে। তবু পুরনো কমরেডরা এখনও কোনও ফেরারি পার্টি কর্মীর শেল্টারের ব্যবস্থা করার জন্য তাকে অনুরোধ করে। আর মন্দার এটা-ওটা অজুহাতে পাশ কাটায়। অঞ্জলি যখন অন্য কারও সন্তান গর্ভে নিয়ে মন্দারকে এই ভরসায় বিয়ে করে যে সে তার সমস্যাটা ঠিক বুঝবে, আর মন্দার নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে বিয়েটা ভেঙে দেয় বা অন্তত সেটাকে বাঁচানোর কোনও চেষ্টাই করে না— তখনও তো সে আসলে পাশই কাটায়! দায়ই এড়ায়। পুরুষের ইগোর কাছে ব়্যাডিকাল রাজনীতির মহান সব তত্ত্ব, আদর্শ— স্রেফ কেতাবি বুলি হয়েই থেকে যায়।
আমাদের তথাকথিত রাজনৈতিক ছবিতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের অজস্র ফাঁক-ফোকরগুলোকে এভাবে হাট করে খুলে দেখানোর ব্যাপারটা বোধহয় এর আগে ঘটেনি। কংগ্রেস পার্টিতে পিতৃতন্ত্রের একচেটিয়া ডান্ডাবাজি নিয়ে আজকাল অনেক কথা শোনা যায়। তবে সেই ১৯৭৮-এর ছবিতে অঞ্জলি বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরের দিন মন্দার যখন কলেজের ক্লাসে মেয়েদেরকে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে ফেলার বিষয়ে এঙ্গেলস-এর তত্ত্ব আওড়ায়, তখন মতাদর্শের ফক্কিবাজির বেহায়াপনাটা ধক করে বুকে লাগে। ছবির একেবারে শেষের অংশে মন্দার আবার অঞ্জলির বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায়। স্বামিত্বের দাবি নিয়ে নয়— বন্ধু হওয়ার কুণ্ঠিত আবেদন নিয়ে। কথকের গলায় তখন শ্লেষের বদলে চাপা আবেগ। তিনি জানান, অঞ্জলির ছেলেকে একটা পরিচয় দেওয়া আর ফেরারি রাজনৈতিক কর্মীর জন্য একটা আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করা এখন আর দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মানে কোথাও এক বর্ষার সন্ধ্যায় মন্দারের সঙ্গেই আদর্শ-বিপ্লবের স্বপ্নরাও ঘরে ফেরে। দুর্মর আশারাও আবার কোথাও আড়মোড়া ভাঙে। কিন্তু এটাও কোথাও বিহ্বল, বিভ্রান্ত, দুর্বল, অস্থিরচিত্ত, মেধাজীবী মধ্যবিত্তের নতুন কোনও আত্মপ্রবঞ্চনা নয় তো? বুদ্ধদেব চান বা না চান, ‘দূরত্ব’-র গড়নে-গঠনে কোথাও এই জরুরি সংশয়টা জেগে থাকে।

পরের ছবি ‘নিম অন্নপূর্ণা’য় তিনি আরও কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন। কারণ এ ছবির কাহিনিকারের নাম বাবু কমলকুমার মজুমদার। তাঁর আশ্চর্য ডিটেল-এর বর্ণনায় সেখানে অবশ্যই সিনেমার বীজ আছে। সিনেমাকারকে ‘দেখি কেমন পারো’ গোছের উস্কানি দেওয়া আছে। তারপর নিশির ডাকের মতোই অলৌকিক ভাষার কুহক-মায়ায় টেনে বার করে, গল্পের এক অসম্ভব ক্ল্যাইম্যাক্সের মোড়ে এনে পথ ভুলিয়ে দেওয়া আছে। এই ‘নিম অন্নমপূর্ণা’র টেক্সটাই তো এই কলকাতার পেটের ভেতর আর একটা কলকাতা আর সেখানকার বাসিন্দাদের বেঁচে থাকা নিয়ে এক ভয়ঙ্কর ন্যারেটিভ। গোটা আখ্যানটা জুড়েই হা-হা খিদে। পেটের এবং শরীরের। গল্পের অন্দরের সেই নিঃশব্দ ভায়োলেন্সের আঁচটা গোটা ছবি জুড়ে অনেকদূর ছড়িয়ে রাখতে পেরেছেন বুদ্ধদেব।
সেখানে এক বালিকা, যূথী, খিদের জ্বালায় পাশের বাড়ির পোষা টিয়াপাখিটার দাঁড় থেকে ছোলা চুরি করে খেতে গিয়ে পাখির ঠোক্করে রক্তাক্ত হয়। আর ছবির শেষে যূথীর মা প্রীতিলতা এক বুড়ো ভিখিরির চালের বস্তা চুরি করতে গিয়ে তাকে খুনই করে ফেলে। এর মাঝখানে যূথী আর তার দিদি লতি, খাওয়া-খাওয়া খেলা খ্যালে। কল্পনার সমস্ত সুখাদ্য তারা সশব্দে চিবিয়ে, চুষে, চেটেপুটে খায়। আর মেয়েদের সেই বিনিপয়সায় মিছিমিছি ভোজের আয়োজন প্রীতিলতার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মাথায় আগুন, পেটে আগুন, শরীরে আগুন— শুধু বাড়ির উনুনটাতেই আঁচ নেই। পরিবারের কর্তা, প্লুরিসিতে ভোগা কেশো রুগি ব্রজ, রোজই বাড়ি থেকে বেরোয় চাল নিয়ে ফিরবে বলে। কিন্তু রোজই তাকে ফেরত আসতে হয় খালি হাতে। অন্নহীনতা, অন্নের লোভ এবং না-পেয়ে না-পেয়ে সেই লোভ-খিদে সব হজম করে বসা অসহায় শরীরের নিষ্ঠুর কাহিনিটা বুদ্ধদেব পর্দায় বলেছেন একই রকম মমতাহীনতায়। দর্শকের জন্য প্রায় কোথাও এতটুকু স্বস্তি বা জিরোবার জায়গা না রেখেই।

ঘোর নাগরিক ‘দূরত্ব’ বা ‘নিম অন্নপূর্ণা’য় স্বপ্ন বা জাদুবাস্তবতার কোনও ঠাঁই ছিল না। ক্যামেরা খুব কাছে গিয়ে বা মাঝামাঝি দূরে থেকেই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত ওইসব জীবনযাপন আর চরিত্রগুলোকে দেখবার, বুঝবার চেষ্টা করেছে। দর্শকের চোখকে জুড়োবার, আরাম পাওয়ার স্পেস দেওয়া হয়নি। এখানে যেন না-কবিতার কবি বুদ্ধদেব জীবনের খড়খড়ে, আটপৌরে, অস্বস্তিকর জায়গাগুলোয় হাত বোলাচ্ছেন। ‘দূরত্ব’য় যে রাজনীতিটা একটু দূরে, অপ্রত্যক্ষ, কেবল তর্ক বা আলোচনায় ছিল, তাঁর তিন নম্বর ছবি ‘গৃহযুদ্ধ’-য় সেটাই অনেকটা গায়ের ওপর এসে পড়ল। ‘দূরত্ব’-এ ন্যারেটর যে রাষ্ট্র-পোষিত গুন্ডাবাহিনীর কথা বলেছিলেন, গৃহযুদ্ধে তারাই ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে দল বেঁধে খুন করে। তার বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে। বুড়ো বাবাকে ধাক্কা মারে। যুবতী বোনের হাত ধরে টানাটানি করে।
এই ছবির মূল অবলম্বন দিব্যেন্দু পালিতের গল্প ‘মাছ’। অনুপ্রেরণায় কোথাও হয়তো থেকে যায় কোস্তা গাভরাস-এর ‘জেড’ ছবিটা। এখানেও এক মস্ত কর্পোরেট সংস্থা তাদের সমস্ত দু’নম্বরি কারবার যেমন করেই হোক ধামাচাপা দিতে চায়। সরকার, পুলিশ, মাফিয়া— সব তাদের পকেটে। যারাই তাদের সম্পর্কে একটু বেশি জেনে ফেলছে, সবাইকেই তারা দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়। সৎ লেবার অফিসার, লড়াকু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বা বামঘেঁষা কমিটেড সাংবাদিক, এমনকী যার হাত দিয়ে আগের খুনগুলো করানো হয়, সেই ভাড়াটে খুনি— কাউকেই বাঁচতে দেওয়া হয় না। আর যারা বেঁচে থাকে, যেমন লেবার অফিসারের স্ত্রী বা ট্রেড ইউনিয়ন নেতার বোন— কোম্পানি তাদের আপোসগুলো নগদ পয়সায় কিনে নেয়। কারও ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। কাউকে চাকরি দেয়।

ছবি ঋণ: গৌতম মিত্র
খুব ঠান্ডা, স্মার্ট, ছিপছিপে, টানটান থ্রিলারের ধরনে গল্পটা বলেছেন বুদ্ধদেব। এরপরে আর কোনও ছবিতে এভাবে তিনি গল্প বলেননি। প্রায় চার দশক পরে ‘আনোয়ার কা আজব কিসসা’য় তিনি আবার কিছুটা থ্রিলারের রাস্তায় হাঁটলেন বটে, কিন্তু সেই তদন্তের মুখ তো মানুষের অন্তরমহলে। সেখানে এক কাহিনি অনেক দিকে গড়াচ্ছে। সময় যেন রবারের মতো। ‘গৃহযুদ্ধ’ ছবিতে, মূল প্লটের ভরকেন্দ্র থেকে না-সরেও, আরও কিছু কিছু প্রসঙ্গ এসেছে। কোনও মন্তব্য ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গের শ্রমের বাজার আর সেই বাজারের পণ্য শ্রমিকদের অসহায়তার স্পষ্ট ছবি ফুটেছে। এ ছবিতে আদর্শ আর দায়বদ্ধতার দিকটায় একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে সাংবাদিক সন্দীপন ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতার বোন নিরুপমা। আর আপোসের দিকটায় আছে নিহত নেতার প্রাক্তন কমরেড, তার বোনের প্রেমিক তথা লড়াইয়ের ময়দান থেকে মাঝপথে পালিয়ে যাওয়া বিজন। বিজন আবার ফিরে এসে নিরুপমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়। সে নিরুপমাকে তার নতুন ফ্ল্যাট, তাদের ভবিষ্যতের লাল-নীল সংসার দেখাতে নিয়ে যায়। কিন্তু নিরুপমার ভাল লাগে না। সে বিজনকে পেতে চায় তার সেই পুরনো, আপোসহীন, আদর্শবাদী অবতারে। বিপ্লবের অনুষঙ্গ বা মোটিভ হয়ে ওঠে বিজনের মাউথ অর্গানে বাজানো ‘উই শ্যাল ওভারকাম’-এর সুর।

সরলীকরণ? না কিন্তু। যে শীতল দাস ময়দানে প্রথম ডিভিশনে ফুটবল খেলে আর ব্যারাকপুরে কোম্পানির হয়ে খুন করে, তারও একটা নিজস্ব শোষণের গল্প আছে। বাংলা ছবির গড়পড়তা আদর্শবাদী গুন্ডাদের গল্প থেকে সেটা অনেক আলাদা, আর সন্দীপন যেভাবে খুন হয়ে যায়, রেড রোডের ধারে উল্টে যাওয়া মোটর বাইকের পাশে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া যায়, অবিকল সেভাবেই তো এই ক’দিন আগে (১৩ জুন, ২০২১) খুন হয়ে গেছেন উত্তরপ্রদেশের এক সাংবাদিক। অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন লেখায় যাঁর সুনাম ছিল। চার দশক আগের ‘গৃহযুদ্ধ’ তাই এখনও তার প্রাসঙ্গিকাতা হারায় না। বরং ‘গৃহযুদ্ধ’-র পর থেকে বুদ্ধদেবের ছবির ধরনই পাল্টে যায়।
‘ফেরা’-তেই এই বাঁক নেওয়ার চিহ্ন প্রথম চোখে পড়ে। নাগরিক জীবনের ইট-কাঠ-পাথর-কংক্রিটের জঙ্গল ছেড়ে বুদ্ধদেবের ছবির সেই যে বেরিয়ে আসা, তিনি তারপরে আর সেভাবে নগরে ফেরত যাননি। ‘ফেরা’-য় আমরা কিছুটা ‘জলসাঘর’-এর বিশ্বম্ভর রায়ের মতোই একটা চরিত্র দেখি। অবশ্যই বিশ্বম্ভরের চেয়ে অনেক জটিল এবং তাঁর চেয়ে অনেক বেশি ‘ইমমরাল’! কিন্তু সে তার শখের ধ্রুপদী যাত্রাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সর্বস্ব পণ করে বসে। যেমন ‘বাঘ বাহাদুর’-এর বাঘ-নাচিয়ে ঘনুরাম। কারও কারও মনে হয়েছে, বুদ্ধদেব এই লম্বা সময়টা জুড়ে যেন একটাই ছবি বানিয়ে গেছেন বিভিন্ন পর্বে। সিনেমার হাড়ে-মাংসে, মানে ফর্ম আর কনটেন্টে এভাবে আমূল পাল্টে যাওয়ারও অবশ্যই একটা দর্শন আছে। শুধুই প্রকৃতি, পরিবেশ, স্মৃতি আর প্রান্তিক জীবন দিয়ে যাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই রূপান্তর নিয়েও আলাদা করে কখনও আলোচনা করা যেতে পারে। পরবর্তী কোনও মোলাকাতে।