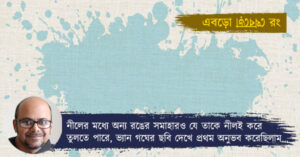বর্ষার সন্ধে ও আশ্চর্য মুড়ি মাখা
সে এক আশ্চর্য মুড়ি মাখা হত, সন্ধে নেমে এলে। এখনকার সন্ধে নয়, আমাদের ছোটবেলার সন্ধে। সেসব সন্ধেও ছিল আশ্চর্য, সুতরাং মুড়িমাখাও যে তেমনই হবে, তাতে আর অবাক কথা কী। কিন্তু এই যে বারবার ‘আশ্চর্য’ বলছি, তার মানে তো আর এই নয় যে, দুর্লভ সমস্ত উপকরণ দিয়ে মাখা হত বিরল প্রজাতির মুড়ি। কক্ষনওই তা নয়। তবু, কীভাবে আশ্চর্য হয়ে উঠত সেই মুড়িমাখা?
তখন, ছোটখাটো মধ্যবিত্ত সাধারণ পাড়াগুলোয় সন্ধে নামত ভারি ধীরে, তার কোনও তাড়া ছিল না কোথাও। মানুষজনেরও তাড়া ছিল না কোনও। তারা আস্তে আস্তে কাজে যেত, ধীরে-সুস্থে কাজ থেকে ফিরত, হাতে অনেক সময় নিয়ে আড্ডা মারত বা দাবা খেলত। যেন আজকের পৃথিবী থেকে খুব অন্যরকম একখানা গ্রহে তখন বাস করতাম আমরা। সে-গ্রহের অবশ্য নামও আছে একটা। ছোটবেলা। তা সেই ছোটবেলা নামের গ্রহে সন্ধে নেমে এলে বাড়িতে মুড়ি মাখা হত। বিশেষ করে বর্ষার সন্ধেয় তো অবশ্যই। এমন বলছি যেন, অন্যান্য সময়ে সান্ধ্য জলখাবারের পঁচিশটা রকমফের থাকত। তা তো নয়, আমাদের মতো সাধারণ বাড়িতে হয় মুড়ি, নয় পাঁউরুটি সেঁকা, নাহয় দই-চিঁড়ে, এসবই চলত। তারই মধ্যে কোনও একদিন আরামবাগের পিসিমা আসছেন, তাই ডিম দিয়ে চাউমিন হল। বা কখনও হঠাৎ এসে পড়েছেন বাবা’র কোনও বন্ধু, রান্নাঘর থেকে ভেসে এল সর্ষের তেলে ডিম ভাজার গন্ধ। দু’খানা ডিমের অমলেট হল সেদিন। সেসবের ভাগ বাড়ির ভেতরকার লোকজন কখনও পেতাম, কখনও সেসব চোখের সামনে দিয়ে ভেসে বেরিয়ে যেত। কিন্তু সাধারণ জলখাবারের মধ্যেও মুড়িমাখার আকর্ষণ কোনওদিন ফিকে হয়ে যায়নি। কেননা তার স্বাদ প্রত্যেকবার নতুন মনে হত।
হয়তো দিনতিনেক ধরে টানা বৃষ্টি চলছে। কখনও ঝমঝম, কখনও ঝিরঝির। কিন্তু থামার নাম নেই। পাড়ার ভাঙাচোরা রাস্তাঘাটে এদিক-ওদিক জল জমেছে, স্কুল থেকে ফেরার পথে সেসবে ঝুপ্পুস লাফ দিয়ে কাদায় ইউনিফর্ম ভিজিয়ে বাড়িতে বকাঝকা। এই চলছে লাগাতার। বিকেলের খেলা ফুরোচ্ছে তাড়াতাড়ি, কেননা জলের মধ্যে অন্ধকারের ছায়া পড়ে না। ফিরেই এক রাক্ষুসে খিদে। হোমটাস্ক আছে কোনওদিন, কখনও বাড়িতে টিউশন পড়াতে আসবেন স্যার, তার আগে খেয়ে নিতে হবে। বর্ষার কারণেই হয়তো, থমথমে হয়ে থাকত পাড়ার সমস্ত আকাশ। যেন সেও আমাদেরই মতো মধ্যবিত্ত। আর সূর্য ডোবার পর পর এক কমলা-বেগনি রঙে ভরে উঠত তার শরীর, যেন সস্তার বেনারসিতে বিয়ে সারছে কেউ।
এরই মধ্যে মুড়ি মাখার একটা তোড়জোড় শুরু হত। সেটা বুঝতাম, কারণ খেলে ফেরার পর কাদাপায়েই মা দোকানে পাঠাত, হাতে দু’টাকার নোট। ‘ও কাকু, আড়াইশো চানাচুর দাও না’— এই বাক্য যে একদিন প্রায় অচল হতে বসবে জীবনে, সেই ছোটবেলায় তা বুঝতে পারিনি। তখন বাড়িতে চানাচুরের প্যাকেট ব্যাপারটা ঢোকেনি, যখন যেমন লাগত, দোকান থেকে খুচরো কিনে আনা, এই ছিল চল। ‘কী নেবে, পাপড়ি না ঝাল?’ এই ছিল দোকান-কাকুর নিত্য প্রশ্ন। আমি নিজেও খাব যেহেতু, পাপড়িটাই বেশি নিতাম। তারপর লাফাতে লাফাতে বাড়ি। লাফানোটা অবশ্য অন্য আনন্দে। ওই দু’টাকা থেকেই চার আনা বাঁচিয়ে হজমি কিনেছি, মুড়ির পর লুকিয়ে সাবাড় করব বলে। তার জন্য লাফানোর কমে কিছু সাব্যস্ত ছিল না তখন।
বর্ষার কারণেই হয়তো, থমথমে হয়ে থাকত পাড়ার সমস্ত আকাশ। যেন সেও আমাদেরই মতো মধ্যবিত্ত। আর সূর্য ডোবার পর পর এক কমলা-বেগনি রঙে ভরে উঠত তার শরীর, যেন সস্তার বেনারসিতে বিয়ে সারছে কেউ।
বাবা হয়তো ফিরে এসেছে এরই মধ্যে বাড়ি, যা সচরাচর বড় একটা হত না। খবরের কাগজের লোক, রাতবিরেতে বা ভোরের আগে বাড়িতে তাকে পাওয়াই দায় ছিল। কিন্তু কোনওদিন হয়তো বর্ষার সন্ধের শ্লথ ট্রামে চেপে পাঞ্জাবির হাতা ভিজিয়ে ফিরেও এসেছে বাড়ি। সুতরাং, মুড়ি একটু বেশিই ঢালা হবে আজ। সে অবশ্য কখনও কম হত না এমনিতেও, এটা আমি দেখেছি। বা ফুরিয়ে এলেও কোনও জাদুবলে তিন মিনিটের মধ্যে রান্নাঘর থেকে আরেক দফা একই রকম মুড়ি মাখা হাজির হয়ে যেত। আমার কেবলই মনে হত, আমাদের এই ছোট, সাধারণ, মেপে চলা জীবনের এক প্রাচুর্য হল মুড়ি, কৃপণতা যেখানে তার জমিদারি কায়েম করতে পারেনি।
তা যা হোক, বাবা তাড়াতাড়ি ফিরে আসায় একটা গোল বাঁধত, এই মুড়ি মাখা নিয়ে। কেননা বাবা মুড়ি মাখতে চাইত। এমনিতে বাবা রান্নাবান্নায় খুবই পটু মানুষ ছিল, আর সেসব তরিবত করে পেশ করতে ভালও বাসত খুব। ছুটির দিনে গামছা কাঁধে বাবাকে দেখেছি কতদিন, রান্নাঘরেই বেলা বইয়ে দিতে। কিন্তু এই একটি বিষয়ে মা রান্নাঘরের দখল ছাড়তে চাইত না। আর সেটা হল, মুড়ি। কেন, বলি তাহলে। বাবা ছিলেন কট্টর এই দেশীয় মানুষ, পুরুলিয়ায় বড় হওয়া ঘটিবাড়ির ছেলে। ফলে হয়েছিল কী, বাবার মুড়ি-ধারণা মায়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এবং মুড়ি দিয়ে মেখে খাওয়া যায় না, এমন জিনিস পৃথিবীতে নেই, এই বোধ নিয়েই বাবা বড় হয়েছিল। যা, স্বাভাবিক ভাবেই, ফরিদপুর থেকে উঠে আসা মা’দের বাঙাল পরিবারের সংস্কৃতি-বহির্ভূত একটা ব্যাপার। বাবা সিঙাড়া দিয়ে মুড়ি মেখে খেতে পারে যেমন, তেমনই গতকালের কুমড়ো-আলুর ছক্কা দিয়েও মুড়ি মেখে খেতে পারে। শুধু তাই নয়, দু’দিনের পুরনো মাংসের ঝোল আর আলু দিয়েও মুড়ি মেখে খেতে দেখেছি বাবাকে। এবং সঙ্গে অবশ্যই দু’আঁজলা জলের ছিটে। সে তুমি যা দিয়েই মুড়ি মাখো না কেন, জল দিতেই হবে। বলা বাহুল্য, এ-জিনিস ছোট থেকে না পেলে বড় হয়ে মানিয়ে নেওয়া মুশকিল। মা তাই মুড়ি মাখার ব্যাপারটা বাবা’র হাতে ছাড়তে চাইত না কিছুতেই। কেননা, আমরা জানতাম, বাবা এমনিতে ভারি সৎ মানুষ হলেও, মুড়িতে জল মেশাবেই মেশাবে।
এই যে মুড়ি মাখা হচ্ছে রান্নাঘরে, পরতে পরতে তার গন্ধ আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ত সারা বাড়ি জুড়ে। বাড়ি মানে তো ভাড়া বাড়ি, সারা মানে সাকুল্যে আড়াইখানা ঘর আর একফালি বারান্দা। কিন্তু খুব সামান্য ওই আয়োজন, ওই মুড়ি মাখার তোড়জোড় ছিল আমাদের প্রায়দিনের উৎসব। যেন কী না কী হয়ে যাচ্ছে বাড়িতে। আমি তখন ভেতরঘরে বসে, বাধ্য হয়ে বই খুলে সামনে রেখেছি। কিন্তু জীববিজ্ঞানে বসানোর মতো মন তখন নেই। মাঝে মাঝেই উঠে রান্নাঘরে গিয়ে দেখে আসছি, কতদূর কী হল। মুড়ি খাওয়া হবে, সে যতখানি না আনন্দের, তার চেয়ে খাওয়ার জন্য এই প্রস্তুতি যেন ছিল বেশি সুখের।
কী কী পড়ত সেই মুড়িতে? তেমন কিছুই নয় বিশেষ। কোনওদিন হাতে বেশি সময় থাকল তো ছোট ছোট ডুমো করে আলুসেদ্ধ বা কুচো করা টোম্যাটো, সে হত উপরি পাওনা। কিন্তু বেশিরভাগ দিনই অত কিছু হত না। দোকান থেকে কিনে আনা সেই চানাচুর, বাড়িতে ভেজানো ছোলা, পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা কুচি, সর্ষের তেল আর বাড়িতে বানানো ভাজা মশলা। ব্যাস। কিন্তু এই সামান্য উপকরণ দিয়ে মাখার পর যে-জিনিসটা দাঁড়াত, তাকে আর সামান্য বলা চলত না। কোনও-কোনওদিন জুটে যেত শশা কুচি, যাকে আজকের ভাষায় বলে এক্সট্রা টপিং, সেদিনটা বেশ বিলাসী মনে হত নিজেদের। আর যেদিন সাধারণ সর্ষের তেলের বদলে পুরনো আম আচারের তেল পড়ত, সেদিন সম্ভবত পাশের তিন-চারখানা বাড়ি পর্যন্ত ছেয়ে যেত আমাদের বাড়ির মুড়ি মাখার সেই গন্ধ।
আজ বুঝি, মুড়ি মাখার আসল উপকরণটাই সেদিন বুঝতে পারিনি। ছোটবেলা দিয়ে মাখা হত সেই মুড়ি। মধ্যবিত্ত, সাধারণ ছোটবেলা দিয়ে। তাই সে আজ এত আশ্চর্য হয়ে ফুটে আছে ভাবনায়। তাকে আর ফেরানো যাবে না কিছুতেই…
মনে আছে, পেল্লায় এক গামলায় ঢালা হত সেই মুড়ি, তারপর সেই গামলা নামিয়ে রাখা হত মেঝেতে। মেঝে মানে যে-সে মেঝে নয়, তখনকার দিনের লাল মেঝে, কালো বর্ডার দেওয়া। বাড়ির ইউনিফর্ম যেন সে। হোক ফাটল ধরা, হোক পায়ের ধুলো লাগা, সেই লালের মধ্যে কোনও লজ্জা বা বিপ্লব ছিল না। কী যে ছিল, কে জানে। তো সেই লাল মেঝেতে গামলা যখন নেমে আসত উড়ন্ত চাকতির মতো, আগ্রহী আমরাও গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যেতাম সেদিকে। কখনও হয়তো স্যার অঙ্ক করাবেন বলে এসে পড়েছেন ততক্ষণে, কোনওদিন হয়তো পাড়ার কোনও এক মাসিমা এসেছেন মা’র সঙ্গে গপ্পো জুড়বেন বলে, ছোট ছোট স্টিলের বাটিতে তুলে তাঁদেরও দেওয়া হত সেই মুড়ির ভাগ। কিন্তু তাতেও মুড়ি কখনও কম পড়ত না আমাদের। আর যেদিন বাইরের কেউ থাকতেন না, আমাদের তিনজনের তিনখানা মুঠো নেমে পড়ত সেই বিশাল গামলায়, মুড়ির মধ্যে। কেউ তুলে আনত বাদামগুচ্ছ, কেউ পেত বেশি শশার কুচি, কারও বা কাঁচালঙ্কা অতিরিক্ত। কিন্তু সেই অলীক বৃষ্টি-থামা কমলা-বেগনি সন্ধেবেলাগুলোয় আমরা ওই এক গামলা সমুদ্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বসে থাকতাম, আর তুলে তুলে আনতাম নুড়ি-পাথর-ঝিনুক।
তারপর, সমুদ্র শুকিয়ে যখন তার তল দেখা যেত, যখন পড়িয়ে ফিরে যেতেন স্যার, যখন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ত গোটা পাড়া, আমি নাকের কাছে হাতের পাতা এনে রাখতাম। তাতে লেগে থাকা আম-তেলের গন্ধ, ভাজা মশলার গন্ধ, কাঁচা পেয়াজ আর লঙ্কার ঝাঁঝ আমাকে জাগিয়ে রাখত অনেক, অনেকক্ষণ। তারপর তো কত বছর গেল। মুড়ি মাখার জন্য দু’তিনজন বাঁধা দোকানদার খুঁজে পেলাম কলকাতায়, তাঁদের হাত অনবদ্য। নিজেও বাড়িতে সময় পেলেই মুড়ি মাখি ইদানীং। বর্ষার অলস সন্ধেবেলায় সেই মুড়ি মাখার আয়োজনই হয়ে ওঠে আমার উৎসব, আজও। কিন্তু কিছুতেই সেই স্বাদ, সেই গন্ধ আর ফিরিয়ে আনতে পারি না। ফিরিয়ে আনতে পারি না সেই লাল মেঝে আর তার ফাটল, ফিরিয়ে আনতে পারি না পুরনো পাড়ার সেই টিমটিমে দোকানের চানাচুর, ফিরিয়ে আনতে পারি না রেডিওয় বাজতে থাকা অনুরোধের গান বা রহস্য নাটিকা। ফেরাতে পারি না কিছুই। একা সেই মুড়ি কীভাবে আর পথ চিনে ফিরে আসবে। আজ বুঝি, মুড়ি মাখার আসল উপকরণটাই সেদিন বুঝতে পারিনি। ছোটবেলা দিয়ে মাখা হত সেই মুড়ি। মধ্যবিত্ত, সাধারণ ছোটবেলা দিয়ে। তাই সে আজ এত আশ্চর্য হয়ে ফুটে আছে ভাবনায়। তাকে আর ফেরানো যাবে না কিছুতেই…
ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র