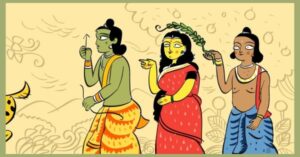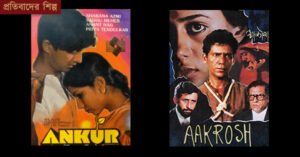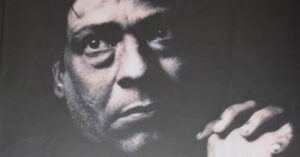ক্লাস সেভেনে রবার্ট লুই স্টিভেন্সনের ‘ফ্রম রেলওয়ে ক্যারেজ’ কবিতাটা পড়ে ব্যাপারটা আমিও চেষ্টা করেছিলাম। ঘর ঝাঁট দেওয়ার ঝাঁটাটাকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ধরে, তার ওপরে চেপে ওড়ার চেষ্টা। ‘ফাস্টার দ্যান ফেয়ারিজ, ফাস্টার দ্যান উইচেজ’— স্টিভেন্সন যেমন লিখেছিলেন। আর তার পাশের প্রচ্ছদে ঢাউস বাঁকানাকা টুপি পড়া, লম্বা ঝাঁটার ওপর যে উড়ন্ত ডাইনি…ঠিক তার মতো।
আমার বিশ্বাস, উড়তে আমি ঠিকই পারতাম, যদি না আমায় দুটো উটকো ঝামেলার মুখে পড়তে হত। প্রথম ঝামেলাটা ছিল- উড়ানযান। স্টিভেন্সনের ডাইনিদের মতো খ্যাংরাকাঠি ওড়ার ঝাঁটা, যা কিনা গোটা কলকাতা শহরে কেবলমাত্র কর্পোরেশনের ড্রেন পরিষ্কারের কাজে লাগে, বলা বাহুল্য, তা আমার নেই। আমার নাগালে থাকা গেরস্ত ঘরের পেলব ঝাঁটাটি, যা কিনা পেলবতর নাম নিয়ে সংসারে ‘ফুলঝাড়ু’ বলে পরিচিত; আমার মতে যা ঘর পরিস্কারের বদলে সুড়সুড়ি দেওয়ার কাজে বেশি জাস্টিফায়েড, তাতে চেপে যে আকাশ বেড়ানো যাবে না, সে তো বলা বাহুল্য।
আর দ্বিতীয় কারণটি হল আমার মা, কিংবা বলা ভাল যে কোনও বাঙালি মায়ের সঙ্গে স্টিভেন্সনের মায়ের মুলগত পার্থক্য। অমন পেলব ঝাঁটার মালিকরা যে এমন কঠিনচিত্ত হতে পারেন, তা ঝাঁটা-রকেট তৈরি করতে গিয়ে খুন্তির মার না খেলে মালুম হয় না। আমি নিশ্চিত, পশ্চিমী সন্তান স্টিভেন্সনকে এসব ফেস করতে হয়নি বলেই, সে এরকম উড়ুক্কু কাব্য লিখতে পেরেছিল। কিন্তু আমার ব্যর্থ উড়ানের পেছনে এর বাইরেও যে একটা তৃতীয় কারণ ছিল, যা কিনা এক অত্যাশ্চর্য মলম, সে কথা তখন কে জানত?
সে-কথা জানলাম আরও কয়েক বছর পর, কলেজ জীবনে। তখন নেশা আর রাজনীতিতে সদ্য হাতেখড়ি হয়েছে। আমরা দুটোই করি এক্কেবারে একইরকমভাবে। দিনের বেলায় অদৃশ্য কোনও এক এন্টিটির থেকে, ‘জবাব চাই, জবাব দাও’— এর পোস্টারের ওপর পোস্টার মেরে কলেজ দেওয়ালের গাঁথনি মজবুত করতে-করতে স্বপ্ন দেখি বিপ্লব জাস্ট এল বলে। আর রাতের বেলা দু’টি হাফ পেগ বিদেশি মদ খেতে-খেতে ভাবি, এই যে আমার মাতাল না হওয়ার এহেন ঐশ্বরিক ক্ষমতা, এই যে আমার জগদ্দল স্থিরচিত্ত— যা কিনা সংসারে দু’টি নেই; তার জোরে একদিন আমি সংসারের সবচেয়ে কঠিন নেশাটি করব। আর তারপর কলেজে গিয়ে এক্কেরে স্বাভাবিকভাবে ক্লাস করে অত্যাচারী সিনিয়রদের চোখে সর্ষেফুল নাচাব।
সে না হয় হবে। কিন্তু তার আগে জানতে হবে যে, বিশ্বের সবচেয়ে সাংঘাতিক নেশার বস্তুটি কী? এক্কেবারে নেশা না করে ফুল কন্সেন্ট্রেশনে কদিন বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করে আবিষ্কার করলাম যে, তা একপ্রকার সুদীর্ঘ প্রাচীন মলম। আর এ হল গিয়ে সেই মলম, যা ছিল বলেই, আগেকারদিনের ডাইনিরা ঝাঁটা চেপে, মেজাজে ফ্লাই করতে পারতেন আকাশে। ভাবা যায়!
আসলে ঝাঁটাফাটা কিস্যু নয়। সেকালের ডাইনীদেবীদের সফল উড়ানের একমাত্র কার্যকরী উপাদানই ছিল ‘ফ্লাইং অয়েনমেন্ট’ নামের এক হ্যালুসিনেটিং মলম। বাকি সবই ওই ম্যাজিক শোয়ের প্রপের ভূমিকার মতো। বিষাক্ত কিছু গাছের পাতা, ফুল ও বীজের সঙ্গে চর্বি মিশিয়ে এই অত্যাশ্চর্য বস্তুটি বহুযুগ আগে বানানো হয়েছিল মূলত মাদকদ্রব্য হিসেবে। যা সহজে অ্যাবজর্বড হবে, শরীরের এমন কয়েকটি নার্ভ পয়েন্টে লাগালে খোলা আকাশে ওড়ার অনুভূতি জাগাবে। শুধু তাই নয়, এই মলমের ক্ষমতা এমনই তুখোড় যে ব্যবহারকারীকে যে গল্প বলা হবে, যে চিত্রকল্পের বর্ণনা দেওয়া হবে, মলমের এফেক্ট থাকা অবধি চোখের সামনে সেটাই দেখতে পাবেন তিনি, অনুভব করতে পারবেন একেবারে বাস্তবের মত।
কী সাংঘাতিক! কিন্তু তার থেকেও সাংঘাতিক কথা হল, এই মলমের তত্ত্বে বিশ্বাস করার মানে, ছোটবেলার উড়ন্ত ডাইনির ধারণাটা আগাপাশতলা বাতিল করা। আসল নায়ক হল, উড়ছি-উড়ছি ফিলিং জাগানো এক আয়ুর্বেদিক মলম। এ কি মানা যায়? মোটেই না। বিশেষ করে আমরা বাঙালিরা যারা ধারাবাহিকতায় অতুলনীয়, যারা দশকের পর দশক— একই পার্টির করসেবা করে আজও ঠেকে শিখিনি, যারা তিরানব্বই বছর ধরে বোরোলীন ব্যতীত কোনও মলমকেই শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ভরসা করে বঙ্গজীবনের অঙ্গে ধারণ করতে পারিনি, তাদের পক্ষে তো একটা মলমের উপর নির্ভর করে উড়ন্ত ডাইনির ফ্যান্টাসি ভেঙে ফেলাটা এক্কেবারে অসম্ভব কাজ।
‘মলম’ শব্দের মূল উদ্দেশ্যই সকলের জীবনে এই স্নেহের পরত বিছিয়ে দেওয়া। এমনকী ‘আলফা মেল’দের জীবনেও। সেজন্যেই তো বছর দুই আগে মুক্তিপ্রাপ্ত সুপারহিট ‘অ্যানিম্যাল’ সিনেমার নায়ক, যার বুকের ছাতিতে লোহার বুলেট রিফ্লক্ট করে বেরিয়ে যায়, সেও কিনা প্রেমিকার স্পর্শের আকাঙ্খায় পাহাড়ে-পাহাড়ে মলমের গান গেয়ে বেড়ায়— ‘মারহাম মারহাম দিল পে লাগা।’
এর মানে কিন্তু এই নয় যে, আমি বাঙালিদের গালমন্দ করছি। একেবারেই না। আমার মতে, বাঙালিদের মতো কল্পনাশক্তিতে প্রতিভাবান জাতি খুব কমই আছে। নইলে যে-কোনও মলম, যুগে-যুগে যার একটিমাত্র সর্বজনীন উপাদান— ফ্যাট, তার বাংলা তর্জমা কি কেউ ‘স্নেহ পদার্থ’ করতে পারে? যিনি করেছিলেন, তিনি তো আর মলমের আরাম দেওয়ার ক্ষমতার দিকটি ভেবে এই তর্জমা করেননি। অথচ কি জিনিয়াস আইডিয়া ভাবুন, যে মলমের মূল কাজই হল ব্যথা, জ্বালা প্রদাহের উপশম; এই একটিমাত্র তর্জমা তাতে মিশিয়ে দিল ‘স্নেহ’ শব্দটি। সত্যিই তো। আমার কষ্টের নিষ্কৃতি দেবে যে, তার যত গুণই থাকুক, খানিক স্নেহ না হলে কি চলে?
চলে না। কারোরই চলে না। হয়তো সে-জন্যেই ফার্সি শব্দ ‘মারহাম’ থেকে আসা ‘মলম’ শব্দের মূল উদ্দেশ্যই সকলের জীবনে এই স্নেহের পরত বিছিয়ে দেওয়া। এমনকী ‘আলফা মেল’দের জীবনেও। সেজন্যেই তো বছর দুই আগে মুক্তিপ্রাপ্ত সুপারহিট ‘অ্যানিম্যাল’ সিনেমার নায়ক, যার বুকের ছাতিতে লোহার বুলেট রিফ্লক্ট করে বেরিয়ে যায়, সেও কিনা প্রেমিকার স্পর্শের আকাঙ্খায় পাহাড়ে-পাহাড়ে মলমের গান গেয়ে বেড়ায়— ‘মারহাম মারহাম দিল পে লাগা।’
এমন অভিজ্ঞতা অবশ্য আমাদের সকলেরই হয়েছে। বিশেষ করে সেই বয়সে, যখন ব্যর্থ প্রেমের মতো দুঃসহ ব্যথার মাধুর্য উপভোগ করার ম্যাচিওরিটি জন্মায়নি। তখন সকলেই ভেবেছি, হা ঈশ্বর! আর যে পারিনা। মনের এই দুঃসহ ব্যথা কমানোর একটা অন্তত মলম দাও সংসারে। খানিক দম নিয়ে বাঁচি। এখনও যে ভাবি না তা নয়। বস্তুত ব্যথার মলমের ডিমান্ডটা এখনও একইরকম আছে, কারণটা খানিক বদলে বদলে গেছে। যেমন এখন আমরা ভাবি, কেন যে তখন মনের ব্যথা কমানোর একটা জুতসই মলম পেলাম না ছাই! তাহলে আজকের ম্যাক্সির ওপর গামছা জড়ানো টেঁপির মা, কিংবা ভুড়ির নীচে লুঙ্গি বাঁধা পল্টুর বাপের জন্যে সেদিন দিনদাহারে অমন আছাড়ি-পিছাড়ি না কেঁদে, মাধ্যমিকের টেস্টপেপার সল্ভ করে লেটার বাগাতে পারতাম।
যাইহোক, এসব আজেবাজে বকবক শেষ করব একটা সিরিয়াস কথা দিয়ে। সেটা হচ্ছে এই যে, ভারতে ব্যথা কমানোর পরেই যে মলমের চাহিদা সবচেয়ে বেশি, তা হল মহিলাদের ফর্সা হওয়ার মলম। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজও এই ফর্সা হওয়ার মলমের বাজার, টাকার অঙ্কে বছরে প্রায় পাঁচ থেকে দশ হাজার কোটি।
এসব শুনলে একটা কথাই মনে হয় যে, অন্য কিচ্ছু নয়, আসলে মলম একখানা এমন আবিষ্কার হওয়া উচিত, যা আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ আর মনটাকে খানিক ফর্সা করতে পারবে। ব্যস, আর কিচ্ছুটি নয়।