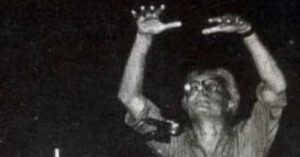১২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে চুরানব্বই বছরে পা রাখলেন শ্রুতকীর্তি ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব। বয়সের কারণে স্বাভাবিকভাবেই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক ইরফান সাহেব এখন আগের মতো ইতিহাস-চর্চার টানে যত্রতত্র চলাচল করেন না। কিন্তু তাঁর মন সজাগ, সতেজ; ইতিহাস-আলোচনায় কোথাও খামতি নেই। এই তো সবেমাত্র পয়লা আগস্ট তাঁর ভিডিও-বার্তাতে শুনলাম তাঁর প্রায় সমবয়সি অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী মশাই-এর সদ্য-প্রকাশিত ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষি-অর্থনীতি বিষয়ক বিশালায়তন বইটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ মন্তব্য। ভারত-ইতিহাসের— বিশেষত ১৩০০ থেকে ১৮ শতক অবধি কালপর্বের— তথ্যে ভরপুর, মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ মৌলিক গবেষণার জন্য গত শতকের ছয়ের দশক থেকে ইরফান হাবিব যে জগৎ-জোড়া মান্যতা এবং খ্যাতির অধিকারী, তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার দরকার লাগে না। আর, সেই বিষয়ে আমার কিছু বলা মোটেই সাজে না। ভারত-ইতিহাসের যে পর্বের (১৩০০-১৮০০) গবেষণার ব্যাপারে তিনি স্বক্ষেত্রে সম্রাট, সেই কাল সম্বন্ধে আমার ধারণা যৎসামান্য। তা সত্ত্বেও এই নিবন্ধ যে লিখছি, তার রসদ হল,অধ্যাপক হাবিবের সঙ্গে নানা সময়ে আমার আলাপচারিতা এবং ওঁর কাজকর্ম তথা কাজের পদ্ধতি কাছ থেকে দেখার সুযোগ ।
হাবিব সাহেবের মুঘলকালীন কৃষিব্যবস্থা নিয়ে যুগান্তকারী গ্রন্থটির (১৯৬৩) ব্যাপারে অবশ্যই অবহিত ছিলাম গত শতকের সাতের দশকের শেষ ভাগ থেকে; মার্ক্সবাদী তত্ত্ব ও পদ্ধতি ধরে অতীত-ব্যাখ্যাতে তাঁর আগ্রহ এবং দক্ষতা, তাও তো সুবিদিত। প্রথম দেখলাম ওঁকে, ১৯৮১ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বোধগয়া-র অধিবেশনে । অব্যবস্থার চূড়ান্ত সেখানে; গোলমেলে আর্থিক কারবারের অভিযোগও কানে এসেছিল। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন সহকর্মী এবং অনেক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে, অধিবেশনের বহু আগে যাবতীয় কাগজপত্র এবং টাকাকড়ি আগাম পাঠিয়ে দেওয়া হলেও, থাকাখাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না বোধগয়ার মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইরফান হাবিব প্রতিবাদে গয়া রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শেষ-ডিসেম্বরের প্রচণ্ড ঠান্ডায় সদলে ঠায় বসেছিলেন। কর্তাব্যক্তিরা প্রমাদ গুণে তাঁকে প্রাথমিক তুষ্ট করার বাসনায় ইরফান সাহেবের জন্যে সব ব্যবস্থা যে পাকা, এই বলে ওঁকে রেল স্টেশন থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য সক্রিয় হন। অধ্যাপক হাবিব সাফ বলে দেন, আলিগড় থেকে আসা সবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না হওয়া অবধি তিনি গয়া রেলস্টেশনের চত্বর থেকে এক পা-ও নড়বেন না । তিনি বুঝিয়ে দেন, তিনি দলটির নেতা বটে, কিন্তু সহযাত্রী, সহমর্মী এবং সমদর্শী এক বিরল ব্যক্তিত্ব।
আরও পড়ুন : আরবি-ফারসি ছাড়া বাংলা ভাষা হয় না, মনে করতেন প্রমথ চৌধুরী!
লিখছেন অনল পাল…

কুরুক্ষেত্রে ইতিহাস কংগ্রেসের ১৯৮২ অধিবেশনে তিনি প্রধান সভাপতি; সভাপতির ভাষণে তিনি তুলে ধরেছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিতে কৃষকদের অবস্থান এবং পরিস্থিতি কীরূপ। সে এক বিস্ময়কর সিংহাবলোকন। প্রাচীন ভারত তাঁর চর্চার প্রাথমিক এলাকা না হলেও, প্রকাশিত গ্রন্থ-প্রবন্ধাদির (যাকে সেকেন্ডারি সোর্স বলা হয়) নিপুণ বিশ্লেষণ দিয়ে সুদূর অতীতের কৃষি-ব্যবস্থার জটিলতা নিয়ে তাঁর উপস্থাপন দেখে ও পড়ে অবাক বনে যাই। চতুর্দশ থেকে আঠারো শতকের পরিসরে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষিত দর্শানোতে তিনি তো প্রায় তুলনাতীত।
সরাসরি, মুখোমুখি পরিচয় এবং অমূল্য সাহচর্য-র শুরুয়াত ১৯৮৫-’৮৬ থেকে। আমার স্ত্রী ওই সময়ে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে চক্ষু-চিকিৎসার উচ্চতর পাঠ নিচ্ছেন। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের গরম, পুজো আর বড়দিনের ছুটিতে চলে যেতাম আলিগড়ে। ইতিহাস বিভাগের নিজস্ব গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অনুমতি চাইলাম হাবিব সাহেবের কাছে; তিনি তখন বিভাগীয় প্রধান। হেসে জানালেন, আমাকে তিনি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহকর্মী বলেই দেখেন। তাই লিখিত অনুমতি নিষ্প্রয়োজন; আমি অন্য সবাকার মতো গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারি। তবে বই ধার করে বাইরে নেওয়া যাবে না।
ওই গ্রন্থাগারটি যে কী সমৃদ্ধ ছিল! প্রাণভরে উপভোগ করেছি ওই সময়কার রাশি রাশি টাটকাতম গবেষণা-প্রবন্ধ। সবচেয়ে উপকৃত হলাম প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বাইরের বইপত্র পড়ে। ইরফান সাহেব আজও বোধ হয় জানেন না, কীভাবে আমার চোখ উনি খুলেছিলেন। ততদিনে জেনেছি, ইতিহাসাশ্রয়ী মানচিত্র প্রণয়নে ওঁর গভীর আগ্রহ এবং বিশাল অবদান। মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক পরিচয় মূর্ত হয়েছে অধ্যাপক হাবিবের ‘অ্যাটলাস অব দি মুঘল এম্পায়ার: পলিটিকাল এন্ড ইকনমিক ম্যাপস উইথ ডি্টেইল্ড নোটস’ (১৯৮২)-এ। একদিন ওঁকে একটু একলা পেয়ে বলে ফেললাম, আপনার মানচিত্র-নির্মাণ নিয়ে আমাকে একটু বোঝাবেন? স্মিত মুখে এককথায় রাজি হয়ে জানালেন, তিনদিন পর রবিবার সকাল ন’টায় বিভাগে এসো। আমি ইতস্তত করে বললাম, রবিবার ছুটির দিন— আপনি ওই দিন সাতসকালে বিভাগে আসবেন?

সুরসিক মানুষটি জবাব দিলেন, সারা হপ্তা তো কাজ করি না, তাই রবিবারও কাজ থাকে। বিভাগীয় ভবনের তিনতলায় নিজের হাতে অন্তত পাঁচটি তালা খুলে (কোনও সহায়ক ধারেকাছে নেই) আমাকে নিয়ে গেলেন এক বিশাল কামরায়। সেখানে মানচিত্রের প্রায় মেলা বসেছে। সেইগুলিকে নিয়ে আমাকে মানচিত্র বানানোর পদ্ধতি, তার কৃৎকৌশলের পাঠ দিতে লাগলেন অবিরাম। সেই কথা শুনলে মনে হবে, মানচিত্র তৈরির এক অতি দক্ষ পেশাদার। আমার প্রায় মাথা ঘোরার জোগাড়; মানচিত্র প্রণয়নের অত জটিলতা জীবনে কখনও শুনিনি। একটু বাদে মিউ মিউ করে বলেই ফেললাম, আমি একেবারে আনাড়ি। আপনি যেসব ম্যাপ তৈরি করান, সেইগুলি কি একবার দেখাবেন? বলামাত্র একের পর এক দেরাজ খুলে অন্তত একশো ম্যাপের খসড়া দেখাতে শুরু করলেন— ব্যাখ্যাসমেত। ট্রেসিং কাগজে আঁকা ম্যাপগুলি প্রায় তৈরি; সেগুলিকে শুধু ছাপার অপেক্ষা; প্রতিটির পাশে পেনসিল দিয়ে লেখা হাবিব সাহেবের অনুপুঙ্খসহ সংশধোনী মন্তব্য।
আচমকা একটি খসড়া ম্যাপ হাতে দিয়ে বললেন, তুমি তো প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে আগ্রহী; এই মৌর্যকালীন ম্যাপটি একবার দেখবে? অতি যত্নে বানানো সেই মানচিত্র; আকর তথ্যসূত্র অনুসারে রং-এর রকমফের দিয়ে চিহ্নিত নানাবিধ উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের এলাকা; সমকালীন মুদ্রার প্রাপ্তিস্থল; স্থলপথের সর্বভারতীয় বিন্যাস এবং সম্ভাব্য বন্দরের হদিশ। আমি একটি বাড়তি তথ্য জুড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিই। আমার শিক্ষক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অশোকের আরামীয় এবং গ্রিক লেখগুলির ওপর বিখ্যাত বইয়ে (১৯৮৪) আফগানিস্তানের লাঘমান থেকে আবিষ্কৃত দুইটি অনুশাসনে রাষ্ট্রিক উদ্যোগে তৈরি এক রাজপথের উল্লেখ আছে; তার দ্বারা মধ্য এবং পশ্চিম এশীয় এলাকার সঙ্গে আফগানিস্তান হয়ে স্থলপথে যোগাযোগ প্রমাণ করা সম্ভব। জানতে চাইলেন, কোথা থেকে এই তথ্য আমি পেয়েছি। ব্রতীনবাবুর বইটির নাম শোনামাত্র আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে দোতলায় গিয়ে গ্রন্থাগারিককে বলে দিলেন, আমার কাছ থেকে প্রকাশনাটির সব খবর নিয়ে তিন হপ্তার মধ্যে বই যেন বিভাগীয় গ্রন্থাগারে চলে আসে। ব্রতীনবাবুকে যোগাযোগ করার সব খবরও নিলেন আমার কাছে।

ছবি সৌজন্য : লেখক
এর ছ’মাস বাদে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত এক পাঠচক্রে যোগ দিয়ে দেখি, বিভাগের তৈরি ম্যাপগুলি নিয়ে এক প্রদর্শনী করা হয়েছে। সেই মৌর্যকালীন মানচিত্রটিও আছে; আমার দেখা খসড়া মানচিত্রে ছয় মাসের ব্যবধানে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে অশোক-এর আরামীয় অনুশাসন দুইটির প্রাসঙ্গিক তথ্য। একমেবাদ্বিতীয়ম এই অভিজ্ঞতা! কলকাতায় ফেরার পর জানলাম, ব্রতীনবাবুকে ফোন করে প্রভূত প্রশংসা জানিয়ে বলেছিলেন, ‘ভারতে বসে এই বই আপনি লিখলেন কী করে?’ ১৯৮৬ থেকে ব্রতীনবাবুর সঙ্গে ইরফান সাহেবের যে ইতিহাস-চর্চার সেতুবন্ধন হল, তা অটুট থাকবে ২০১৩-তে ব্রতীনবাবুর জীবনাবসান পর্যন্ত ।
১৯৮৬-তে আরও এক প্রগাঢ় বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল। রাষ্ট্রকূট রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণর দশম শতকীয় একটি প্রত্নলেখে দীপাবলির উল্লেখ দেখে চমকে যাই, কারণ সেখানে আর্থিক লেনদেনের কথা এসেছিল, যা ঘটবে দীপাবলির পরের দিন। বাংলায় দীপাবলিতে প্রধানত কালীপুজো হয়, যদিও ভারতের বহু এলাকায় ওই দিনটিতে লক্ষ্মীর আরাধনা চলে মহা ধুমধামে। বাংলায় পয়লা বৈশাখে হালখাতা চালু করার মতো উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে দীপাবলির পরের দিনটি সাবেক বণিক-সমাজে নতুন আর্থিক সালের সূচক। আমার নিজের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল, দীপাবলির সঙ্গে নতুন আর্থিক বছরকে জুড়ে দেওয়ার এটি কি সবচেয়ে পুরাতন নজির—অন্তত প্রত্নলেখের নিরিখে?
একদিন জানতে চাইলাম ইরফান সাহেবের কাছে— মধ্যযুগে এই প্রথার কোনও নির্দিষ্ট তথ্য আছে কি? দুই দিন পর, দুপুর একটা নাগাদ— প্রবল ব্যস্ততার মাঝে— হঠাৎ ডেকে নিলেন আমাকে; প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য জানালেন। তারপর জানতে চাইলেন, আমি ফার্সি জানি কি না। আমার অজ্ঞতা হাবিব সাহেবকে জানাতে বললেন, তিনি আমাকে আঠারো শতকের প্রথম ভাগের একটি ফার্সি অভিধান (‘বাহার-ই-আজম’; লেখক দিল্লিবাসী টেক চন্দ) থেকে মুখে মুখে চটজলদি ইংরেজি তর্জমা করে দেবেন। আমি লিখে চলেছি সেই বিবরণ: দিওয়ালির রাত্রে উৎসব, নতুন পোশাক পরিধান, ব্যবসার নতুন খাতা শুরু করার রীতিনীতি ইত্যাদি। বিবরণটি অনুসারে, দিওয়ালির পরদিন কোনও বানিয়া/ব্যবসায়ী যদি প্রকাশ্য দিবালোকে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ রেখে একটি প্রদীপ জ্বেলে দেন, এই প্রতীকী কাজের দ্বারা তিনি নিজেকে সর্বস্বান্ত বলে চিহ্নিত করেন; তাঁর অভিধা হয়ে যায় দিওয়ালিয়া।
ইতিহাস-আশ্রয়ী ভূগোল এবং তার ভিত্তিতে মানচিত্র প্রণয়নে হাবিব সাহেবের আগ্রহ কিন্তু নিছক মুঘল আমলে আটকে নেই। গত দশকের অন্তিম বছরগুলি থেকে নতুন শতকের প্রথম দশ বছর তিনি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে নিয়মিতভাবে পেশ করে চলেছিলেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-নির্ভর মানচিত্র রচনা-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি; সঙ্গে প্রস্তাবিত
মানচিত্রগুলিও দেখাতেন।
আমি লিখতে লিখতে লাফিয়ে উঠি। ইরফান সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? আমি বলেছিলাম, আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না; বাংলায় নিঃস্ব কথার প্রতিশব্দ, দেউলিয়া। এই শব্দটির উৎস যে দীপাবলিতে নিহিত, আপনার অনুবাদে তা ধরা দিল (দীপাবলিয়া— দিওয়ালিয়া—দেউলিয়া— দেউলে)। আর, আমার যে প্রাথমিক আন্দাজ, দীপাবলি মূলত ব্যবসায়ীদের উৎসব; বার্ষিক হিসেব-নিকেশের পুরাতন খাতা বন্ধ করা এবং আর নতুন খোলার সঙ্গে তার নিবিড় যোগ— সেই ধারণা শক্তপোক্ত তথ্যের জমি পেল ইরফান সাহেবের আনুকূল্যে।
এইসব কারণেই অশীন দাশগুপ্ত ইরফান হাবিবের ‘অ্যাটলাস অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার’ বই-এর সমীক্ষা আরম্ভ করেন এই বলে— ভারত-ইতিহাসের চর্চায় যদি মার্ক ব্লকের মতো কাউকে খুঁজতে হয়, তিনি ইরফান হাবিব। অশীনদা কিন্তু পুরোদস্তুর অ-মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ। তাতে হাবিব সাহেবের থেকে তিনি অনেক সময় ভিন্ন মত নিলেও ইরফান হাবিবের পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাতে তিলেক দ্বিধা করেননি; এই দুই ইতিহাসবিদের গভীর বন্ধুতাও অজানা নয়। তবে, ওই সমীক্ষাতে অশীনদা কয়েকটি বিরুদ্ধ এবং বিকল্প বক্তব্যও লিখেছিলেন। সমীক্ষার শেষ বাক্যটি চমকপ্রদ, মুঘল মনসবদার, যাকে ইরফান হাবিবের থেকে বেশি ভাল কেউ জানেন না, সেই মনসবদারের মতোই হাবিব সমুদ্রের নোনা বাতাস লাগলে স্বস্তিতে থাকেন না। ঈষৎ বাঁকা মন্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য, ওই যুগান্তকারী বইতে ইরফান সাহেব শুধু ডাঙাকেই দেখেন, ভারত সাগরের কথা তাঁর মননে ও মানচিত্রে প্রায় অধরা। কথাটি হাবিব সাহেব মনে রেখেছিলেন।
২০২০-তে আমার সমুদ্র-ইতিহাস সংক্রান্ত একটি নতুন বই বেরোল। বইটি উৎসর্গ করেছিলাম অধ্যাপিকা রোমিলা থাপারকে। করোনাকালে বই তাঁর হাতে নিজে দিতে পারিনি বলে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার আশ্রয় নিতেই হল। সেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক অধ্যাপক হাবিব। আমার বহু সুকৃতির ফসল। উনি সঞ্চালকের বক্তব্য শুরু করেছিলেন অশীনদার সেই সমালোচনাটি দিয়ে। খানিক স্মিত হেসে তারপর বললেন, জাহাজ বা নৌকোর পাল কিন্তু কাপড়ের তৈরি; আর সেই কাপড় বোনা হবে, যদি আগে জমিতে কার্পাস ফলানো যায়। কোনও ঝাঁজ নেই, প্রয়াত বন্ধুর সঙ্গে মতদ্বৈধ মনে রেখেই রসিকতার আশ্রয়ে কথাগুলি বলেছিলেন।
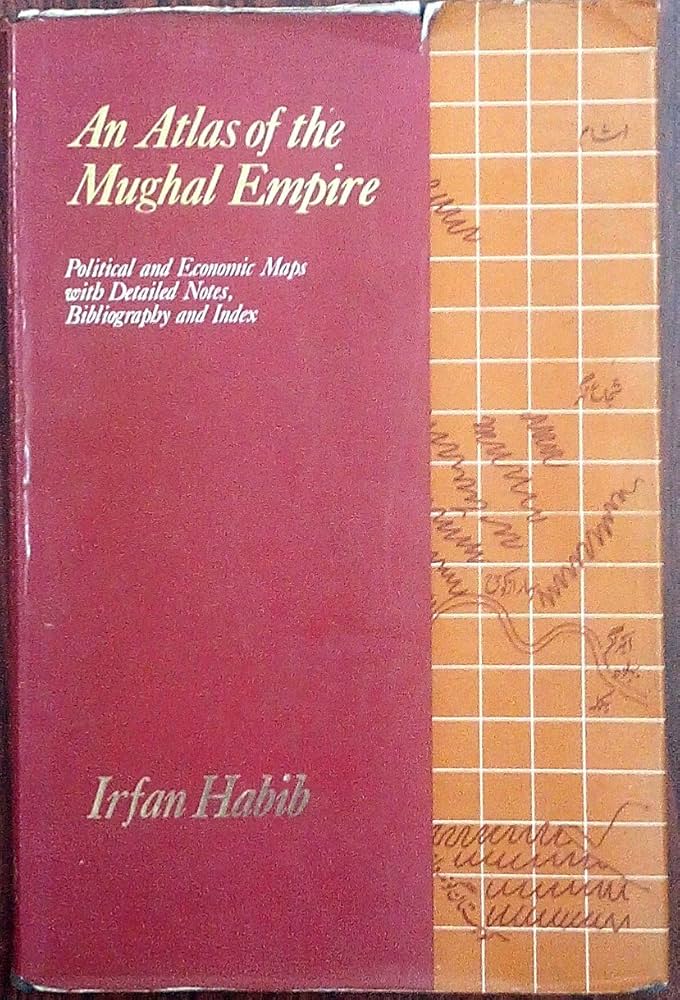
১৯৮২-তে প্রকাশিত ‘অ্যাটলাস অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার’ বইটির একেবারে সমকালীন হল ‘কেমব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া’-র প্রথম খণ্ড (১২০০ থেকে ১৭৫০ অবধি কালসীমায় বিধৃত), যেটি তপন রায়চৌধুরীর সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছিলেন অধ্যাপক হাবিব। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের দুনিয়াজোড়া সেরা বিশারদ-দের রচনায় সমৃদ্ধ অতি গুরুত্বপুর্ণ এই প্রবন্ধ সংকলন। হাবিব সাহেব নিজেও লিখেছিলেন কয়েকটি মূল্যবান অধ্যায়। গত তিন দশক ধরে সাংস্কৃতিক ইতিহাস-চর্চার ওপর আগ্রহ বাড়ার কারণে অর্থনৈতিক ইতিহাস-গবেষণাতে খানিক মন্দা এসেছে বটে; চার দশক আগের এই বইটির ওপর নজরও কমেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ইতিহাস বোঝার জন্য এই কাজকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উপরিউক্ত বইটির প্রায় উত্তরসূরি রূপে পাওয়া গেল ইরফান হাবিব প্রণীত আরও একটি গ্রন্থ (২০০১)— ‘ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ মিডিয়েভাল ইন্ডিয়া (১২০০-১৫০০)’। তাঁর লেখা এবং সম্পাদিত সব বইয়ের তালিকা দেওয়া এবং তার আলোচনা করা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব না; আমি এই কাজে যোগ্য ব্যক্তিও নই।
ইতিহাস-আশ্রয়ী ভূগোল এবং তার ভিত্তিতে মানচিত্র প্রণয়নে হাবিব সাহেবের আগ্রহ কিন্তু নিছক মুঘল আমলে আটকে নেই। গত দশকের অন্তিম বছরগুলি থেকে নতুন শতকের প্রথম দশ বছর তিনি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে নিয়মিতভাবে পেশ করে চলেছিলেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-নির্ভর মানচিত্র রচনা-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি; সঙ্গে প্রস্তাবিত মানচিত্রগুলিও দেখাতেন। এইগুলি তিনি পড়তেন হিস্ট্রি কংগ্রেসের প্রাচীন ভারত ইতিহাসের শাখাতে; অন্যান্য প্রবন্ধকারদের মতোই— কোনও বাড়তি সুযোগ বা বাড়তি সময় না চেয়ে। ওইসব প্রবন্ধ পাঠের পর আলোচনাতেও তিনি সমান উৎসাহী; আমি নিজেও নানা মন্তব্য করেছি অধিবেশনগুলিতে তাঁর পঠিত মানচিত্র-বিষয়ক নিবন্ধের ওপর। মতের মিল না ঘটলে তাঁর বিরক্তি বা উষ্মা দেখিনি কখনও। এই আলাদা আলাদা প্রবন্ধগুলি কালে একত্রিত হল ইরফান হাবিবের বইতে— ‘অ্যান অ্যাটলাস অফ এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া’ (২০১২)। সহযোগী লেখক ছিলেন তাঁর পুত্র ফইয়াজ হাবিব, মানচিত্রকার হিসেবে ফইয়াজ হাবিবের দক্ষতা ও মান্যতা বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। বইটি প্রকাশিত হওয়ার, পর পরই একটি কপি পাঠিয়েছিলেন সহৃদয় উপহার হিসেবে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। ১৯৮৬ সালে অশোকের আরামীয় প্রত্নলেখর বইটি পড়ে ব্রতীনবাবুর সঙ্গে হাবিব সাহেবের যে লাগাতার ইতিহাস-আলোচনার সূত্রপাত, সেই বৃত্ত পূর্ণতা পেল ইরফান হাবিবের প্রাচীন ভারতের মানচিত্রের বইটি দিয়ে।
সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং অতীত-বিশ্লেষণের যুগলবন্দি ইরফান সাহেবের ইতিহাস-চর্চার দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইগুলি সব-ই তাঁর পেশাদারি ইতিহাস-অনুসন্ধানের ফসল। কিন্তু অধ্যাপক হাবিবের ইতিহাস-রচনা কেবলমাত্র উচ্চতর গবেষণায় সীমিত থাকেনি। অতীতের তথ্যনিষ্ঠ এবং ব্যাখ্যাশ্রয়ী পাঠ যাতে বিশেষজ্ঞদের গণ্ডির বাইরে ইতিহাস-অনুরাগী সাধারণ পাঠক-সমাজের নাগালে সহজে আসে, তার জন্য তাঁর অবিরাম, অক্লান্ত প্রয়াসের কথা বলতেই হবে। এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব নিরন্তর বুঝতে পারি, বিগত তিন দশক ধরে উগ্র জাতীয়তাবাদী, আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদী, দ্বেষপ্রেমী, বিভেদপন্থী মতাদর্শের রমরমা প্রত্যক্ষ করতে করতে। ইতিহাস-বিকৃতির সচেতন এবং সুচতুর প্রয়াসের ফলে ইতিহাস নিয়ে ছিনিমিনি চলেছে প্রাতিষ্ঠানিক মদতে। এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ, যেনতেন প্রকারেণ মুঘল আমলকে ভারত-ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ব্যাপক তোড়জোড়। যে সহজ বুদ্ধি এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সোনার কেল্লার মন্দার বোসের ছিল— মুঘলকে বাদ দিলে রাজপুতরা কার বিরুদ্ধে লড়াই করে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি পাবেন (মন্দার বোস লালমোহনবাবুর মর্চে-ধরা নেপালি অস্ত্র দেখে বাঁকা মন্তব্য করেছিলেন: কোন পক্ষে লড়ছেন মশাই— মোগল না রাজপুত?)— সেই মামুলি বুদ্ধিটুকু তো স্বঘোষিত ইতিহাস-বিশারদদের ঘটে গজাল না। এক বিচিত্র ধারণা জনমানসে স্থান পেয়েছে যে, প্রকাশিত গুটি চার-পাঁচ বই আর দুই-তিনটি প্রবন্ধ হাতের কাছে মজুত থাকলেই ইতিহাস নিয়ে ছয় নম্বর পুস্তকটি লিখে ফেলা কোনও ব্যাপার-ই না। তার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে আরও এক আশ্বাস, সিনেমা দেখে (‘যোধাবাই’, ‘সম্রাট পৃথ্বীরাজ’, ‘ছাবা’ ইত্যাদি) ইতিহাস শিখে ও বুঝে নেওয়া নিতান্ত জলভাতের কারবার। কথাগুলি পাড়লাম এই জন্য যে, ইতিহাসের এই ভয়াবহ বিকৃতি ঠেকাতে এবং একাধারে সুস্থ চিন্তার ক্ষেত্র মজবুত করতে ইরফান সাহেব দীর্ঘকাল ধরে অনলস প্রয়াসে ব্যাপৃত। এই জন্য তিনি এক গ্রন্থমালার পরিকল্পনা করেছিলেন, যা আজও সজীব ও সক্রিয়। এই ইংরেজি গ্রন্থমালা ‘এ পিপল’স হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া’ বলে অভিহিত। এই গ্রন্থমালার প্রধান হোতা এবং সম্পাদক ইরফান হাবিব। এই গ্রন্থমালার অন্তর্গত বইগুলিতে ভারত-ইতিহাসের নানা জটিল প্রসঙ্গকে দুই মলাটের মধ্যে রাখা হয় খুব সহজভাবে; তবে তা কোনওভাবেই পাঠককে দুধের বদলে পিটুলিগোলা গেলানোর তরিকাতে নয়। রাজা-রাজড়াদের কথা গৌণ থাকে; আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা-ব্যবস্থার আলোচনা রাখা হয় অগ্রণী ইতিহাসবিদদের মতামত বিচার করে এবং বহু ক্ষেত্রে আকর তথ্য-উপাত্তের ইংরেজি অনুবাদ দিয়ে। অতি উপযোগী, টাটকা গ্রন্থ-প্রবন্ধের সন্ধানও পেয়ে যান আগ্রহী পাঠকরা। বক্তব্য পেশ করা হয় সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে, কিন্তু ইতিহাস চর্চার জটিলতাকে তরল না হতে দিয়ে। এই গ্রন্থমালার মান্যতা তর্কাতীত। ইরফান সাহেব সম্পাদনা ছাড়াও নিজেই একাধিক বই এই গ্রন্থমালায় লিখেছেন। কিছুকাল আগে ইতিহাস-আশ্রয়ী ঘটনার সফল কথাকার উইলিয়ম ডারলিম্পল রায় দিলেন যে, প্রধান প্রধান ভারতীয় ইতিহাসবিদ কেবল পেশাদারি ইতিহাস চর্চার মদত দেন, তাঁদের গবেষণার স্বাদ ইতিহাস-অনুরাগী সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ নেই। ডারলিম্পলের মতে, এই মানসিকতা একপ্রকার এলিটসুলভ অবস্থানের প্রকাশ। সাধারণ পাঠক নাকি এই অভাব বোধ করে বাধ্য হয়েই হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি-সেবিত জঞ্জাল এবং গাঁজাখুরির দিকে ঝোঁকেন। উগ্র দক্ষিণপন্থী ভ্রান্ত ইতিহাসবোধ যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে, তার জন্য পেশাদারি ইতিহাসবেত্তাদের নাক-উঁচু মনোভাবকে তিনি কাঠগড়ায় তুলে দিলেন। এই বক্তব্য তথ্যনিষ্ঠ নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। ডারলিম্পল সাহেব ইরফান হাবিবের অন্তত বিগত তিন দশকের এই উদ্যোগের সম্বন্ধে অবহিত কি না, তা নিয়ে সন্দেহ হয়। ৯৪ বছর বয়সেও ইরফান হাবিব এই গ্রন্থমালা রচনায় এবং প্রকাশনায় অক্লান্তকর্মা।
ইতিহাসের অসামান্য ব্যাখ্যাতার বাইরে অন্য এক ইরফান হাবিব আছেন। তিনি এক অবিশ্বাস্য রসিক কথক, তার পরিচয় পাওয়া যাবে উনি যখন আড্ডাধারী এবং স্মৃতির ভাণ্ডার খুলে বসেন। ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫-এ ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ কাগজে তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার ভিত্তিতে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন দেবযানী ওনিয়াল। ১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে এল দেশভাগের যন্ত্রণা আর হিংসাত্মক দাঙ্গার মারাত্মক অভিজ্ঞতা। ষোলো বছরের কিশোর ইরফান হাবিব সাক্ষী ছিলেন এক আশ্চর্য পরিস্থিতির। বহু জায়গায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ঘটলেও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কোনও দাঙ্গা দেখা দেয়নি। কারণ ওই বিশ্ববিদ্যালয়টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেখানে নিয়োগ করেছিলেন দক্ষতম সেনা ইউনিট, কুমায়ুন রেজিমেন্ট-কে। বহু শিক্ষক আলিগড় ত্যাগ করলেও একদিনের জন্যও ক্লাস বন্ধ হয়নি। এই বিবরণ পড়ে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়, আমাদের সীমাহীন অবক্ষয় দেখে।
ইরফান সাহেবের আরও একটি স্মৃতিচারণ, যা তিনি নিজে আমাকে বলেছিলেন, উল্লেখ করা দরকার। তিনি তখন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের তরুণ এক অধ্যাপক। ঘটনাটি ১৯৫০-এর মধ্যভাগের। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য বৃত্তি পেয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর পাসপোর্টের আবেদন নাকচ হয়ে গিয়েছে। সম্ভাব্য কারণ, তাঁর সাম্যবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ঘোষিত অবস্থান। তরুণ অধ্যাপকটি একটি রাগী চিঠি সরাসরি পাঠিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে; খোলাখুলি লিখেছিলেন যে, তাঁর ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের জন্যই তাঁকে এই অবিচারের শিকার হতে হল। এ-ও লিখে দিলেন, যে উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেন, তার সঙ্গে সরকারের ক্রিয়াকলাপের বিস্তর ফারাক। কয়েকদিন বাদে উপাচার্য ডক্টর জাকির হুসেন সাহেব তরুণ অধ্যাপককে জানান দেন যে, প্রধানমন্ত্রী ইরফান হাবিবকে সাক্ষাৎকারের জন্য সময় দিয়েছেন। সেইমতো ইরফান হাবিব নয়া দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে হাজির হন। পণ্ডিত নেহরুর কক্ষের দরজা খুলে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব এম ও মাথাই। ভেতরে যাওয়ার পর নেহরু তাঁর নাকচ হয়ে যাওয়া পাসপোর্ট আবেদনের ব্যাপারে কিছু করতে পারবেন না, এই কথা সোজা জানিয়ে দেন। অল্পকাল পরে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই পাসপোর্ট মঞ্জুর হল। কিন্তু তার চেয়ে ঢের চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা ছিল— প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কোথাও এবং প্রধানমন্ত্রীর কক্ষেও একটি দেহরক্ষী নেই, নেই কোনও সুরক্ষার ঘেরাটোপ । এই কথাগুলি বলার সময় ইরফান সাহেব ঘটনার দিন যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন, সেই একই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান।
ইরফান সাহেবের স্বাদু রসিকতাবোধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী থেকেছি একাধিকবার। অধিকাংশ রসিকতা করেন নিজেকে নিয়ে। কতবার বলেছি, এই কথাগুলি লিখুন না। জবাবে বলেছেন— এমনিতেই বহু লোক জানে আমি বুদ্ধু, তাতে আবার বাড়তি ইন্ধন দেওয়া কেন! একটি নমুনা পেশ না করলেই নয়। ২০১৭-তে আলিগড় গেলাম, ওঁর সঙ্গে দেখা হল ইতিহাস বিভাগে ওঁর নির্দিষ্ট ঘরে। উনি তখন ‘স্টাডিজ ইন পিপল’স হিস্ট্রি’ জার্নালের সম্পাদকীয় কাজ করছেন (আজও করে চলেছেন)। নানা কথার মাঝে অকস্মাৎ একটি পাণ্ডুলিপি দেখালেন। তাতে প্রাচীন ইতিহাসের এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিবন্ধ। রচনার বিষয়— প্রয়াত ব্রিটিশ পুরাবিদ কলিন রেনফ্রিউকে নিয়ে শ্রদ্ধালু স্মৃতিচারণ। ইরফান সাহেব সকৌতুকে বললেন, ‘নিবন্ধের প্রথম বাক্যটি কেটে দেব— লেখক চটবেন,কিন্তু কিছু করার নেই।’ প্রথম বাক্যটি ছিল, কলিন রেনফ্রিউ যথেষ্ট পরিণত কালে, আশি বছর বয়সে (‘অ্যাট দ্য রাইপ ওল্ড এজ অব এইট্টি’), প্রয়াত হয়েছেন। ‘এই কথা কেটে দেব, কারণ আমার নিজের বয়সই তো এখন ছিয়াশি!’ ৯৪-এ পা-রাখা ইরফান হাবিব সাহেব সংখ্যার নিরিখে নিশ্চয় আজ অতি-প্রবীণ। কিন্তু মানুষটি কখনও বুড়িয়ে যাননি, যাবেনও না।