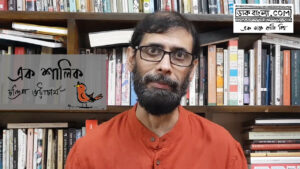প্রতিবেদনের ক্ষতি-বেদনা
আমাদের দেশে খবরের কাগজ বা মাসিক পত্রিকায় সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানের শিল্প বা রিভিউ বিষয়ক প্রতিবেদনের রীতির নাভিশ্বাস উঠতে-উঠতে এখন প্রায় অন্তিমকাল উপস্থিত। অতীতে কিন্তু এমন প্রতিবেদন বা রিভিউয়ের অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হয়ে থাকতেন মানুষ। বিশেষ করে নবীন, উঠতি শিল্পী, যাদের কাছে খবরের কাগজের শিল্পের পাতায় একটা ভাল রিভিউ, নিদেনপক্ষে নামটা ছোট করে ছাপানো বা একটা ফোটোগ্রাফও বিরাট ব্যাপার, তাঁদের মধ্যে এই উৎসাহ দেখা যেত। গত শতাব্দীর আশির দশকে, অর্থাৎ যে-সময়ে আমি পেশাদারি ভাবে গাইতে শুরু করছি, সে-সময়ে সারা দেশের প্রত্যেকটি নামী সংবাদপত্র একজন করে সঙ্গীত সমালোচকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, শিল্পের পাতায় নিয়মিত প্রকাশ করতেন রিভিউ এবং রিপোর্ট-জাতীয় প্রতিবেদন। কোনও কোনও সঙ্গীত সমালোচকের বেশ নামডাক হত, শিল্পীসমাজ তাঁদের রীতিমতো সমীহ করে চলত। অবশ্য সমালোচক এবং শিল্পীর মধ্যে প্রকাশ্যে কলহের খবরও কখনও-সখনও পাওয়া যেত, বিশেষ করে কোনও অভিজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পী যদি সমালোচকের কোনও অহেতুক টিপ্পনিতে বা তাঁদের সঙ্গীতের অসত্য, আধা-শিক্ষিত সমালোচনায় ক্ষেপে গিয়ে জনসমক্ষে ঝগড়া লাগাতেন। আমার অনুমান, শিল্পী এবং সমালোচক, বিভিন্ন সময়ে এই উভয় পক্ষেরই দোষ ছিল, অতএব তাঁদের সমান অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করাটা উচিত হবে না। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ থেকে সঙ্গীত সমালোচকদের নিয়ে কিছু মনে রাখার মতো স্মৃতি আজ তুলে ধরতে ইচ্ছে করছে। কারোর নাম যে প্রকাশ করছি না, তার কারণটাও স্পষ্ট— এ-দেশে রসিকতাবোধ জিনিসটাই লুপ্ত হতে বসেছে। তবে যে কাহিনিগুলো আজ শোনাব, তার একটাও মনগড়া গল্প নয়। আমার নিজের দেখা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে এ-ঘটনাগুলো আমি তুলে আনছি।
আমাদের দেশের রাজধানীতে একদা এক জ্ঞানী অথচ কলহপ্রবণ সঙ্গীত সমালোচক বাস করতেন। বড়-বড় তারকা শিল্পীদের সঙ্গীত নিয়েও তিনি এমন সব ঠোঁটকাটা, বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা প্রকাশ করতেন যে, সঙ্গীতসমাজে একেবারে তুলকালাম পড়ে যেত। লোকজন হতবাক হয়ে বলাবলি করত, এত বড় একজন শিল্পীর ব্যাপারে ভদ্রলোক এমন কথা বললেন? কেউ-কেউ তো বিশ্বাস করত, উনি ইচ্ছে করে শিল্পীদের খোঁচাতে এইসব লিখতেন, যাতে কলমের জোর দেখিয়ে তাঁদের একটু ঠান্ডা করা যায়! কিন্তু সেই সমালোচক অকাতরে, এক ফোঁটাও তোয়াক্কা না করে, চালিয়ে গেলেন তাঁর কাজ। একের পর এক সঙ্গীত অনুষ্ঠানে তিনি গটমটিয়ে ঢুকতেন, এবং যে-শিল্পীকে বেছে নিতেন, তাঁর বিষয়ে মাঝেমধ্যেই ছাপার হরফে বিষোদগার করতেন। কিন্তু এই মারকাটারি, বিষমাখানো প্রতিবেদন লেখা ছাড়াও তাঁর আর একটি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল— তিনি বোধহয় একই সময়ে সব জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারতেন! এই বিশেষ ক্ষমতাটি তিনি প্রকাশ করে ফেলেন অনিচ্ছাকৃত ভাবেই। তিনি একই দিনে, একই সময়ে, এক শহরের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত দুটি বা তার বেশি গানের আসরের রিভিউ করে বসলেন! যদি বুদ্ধি করে একটি আসরের প্রথম পরিবেশনা, তারপর অন্য একটি আসরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পরিবেশনা— এইভাবে একটু রিভিউ করতেন, তবে তাঁর একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত থাকা বা সঙ্গীতজগতের স্বার্থে নিজের সত্তাকে ভাগ-ভাগ করে ফেলার অলৌকিক শক্তির গোপন কথাটি গোপনেই থেকে যেত। ‘রণে-বনে-জলে-জঙ্গলে আমি সর্বত্রই সবসময়ে আছি’র এই অতিমানবিক ক্ষমতাটি লুকিয়ে রাখতে ভদ্রলোক এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি ভিন্ন-ভিন্ন প্রকাশনার জন্য দুটি করে রিভিউ লিখতেন, একটি নিজের ‘ভাল’ নামে, আর দ্বিতীয়টি হয় আদ্যাক্ষর ব্যবহার করে, নয় নিজের স্ত্রী-র নামে। তাঁর স্ত্রী অতি নিরীহ-নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, এবং তাঁকে কেউ কোনওদিন কোনও অনুষ্ঠানে চোখে দেখেনি। এর থেকে প্রমাণ হয়, তিনি হয় স্ত্রীকে নিজের পকেটে বা কাঁধের বড় ব্যাগটিতে করে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসতেন, নয় ভদ্রমহিলা অদৃশ্য ছিলেন! হাজার হোক, আমাদের দেশ যে অলৌকিক-অতিলৌকিকের দেশ, সমালোচক সাহেব সেটাই নতুন করে প্রমাণ করে দিলেন।
মারকাটারি, বিষমাখানো প্রতিবেদন লেখা ছাড়াও তাঁর আর একটি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল— তিনি বোধহয় একই সময়ে সব জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারতেন! এই বিশেষ ক্ষমতাটি তিনি প্রকাশ করে ফেলেন অনিচ্ছাকৃত ভাবেই। তিনি একই দিনে, একই সময়ে, এক শহরের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত দুটি বা তার বেশি গানের আসরের রিভিউ করে বসলেন!
এই রাজধানীতেই আর একজন সমতুল্য রকমের কোপনস্বভাব এবং আপাতজ্ঞানী সমালোচক থাকতেন, তাঁকে সবাই বেশ ভয়ও পেত। তাঁর স্বভাব ছিল খুব বিস্তৃত, লম্বা-লম্বা প্রতিবেদন লেখা, যার শব্দসংখ্যা এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে যেত। সমস্যা ছিল একটাই, প্রত্যেক বারই নিশ্চিত ভাবে দেখা যেত, আসলে সঙ্গীত নিয়ে মন্তব্য কেবল ওই শেষের কয়েকটি বাক্যে, তার আগে প্রায় আধপাতা জুড়ে কেবল আমড়াগাছি, যার পুরোটাই হয় চটকদার সব টীকাটিপ্পনি, নয় নানা অপ্রয়োজনীয়, মূলত অবান্তর প্রসঙ্গ। যেমন ধরুন, গায়িকার কানের ঝুমকা বা দুলের দুলুনি নিয়ে গোটা একটি অনুচ্ছেদ তাঁর লেখায় মাঝেমধ্যেই পাওয়া যেত, তবে এ-জিনিসকে তো আর অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা বলা চলে না! স্বাভাবিক ভাবেই, যে-প্রকাশনার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাদের সঙ্গে লেখালিখির কাজ তিনি চালিয়েই গেলেন, এবং প্রশংসাসূচক রিভিউ পাবার আশায় বেশ কিছু শিল্পী তাঁর সামনে হাত কচলে হেঁ-হেঁ করে যেতে ক্ষান্তও হলেন না। কিন্তু শেষে একদিন তিনি একটি চরম ভুল করে ফেললেন। একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থেকেই তার রিভিউ লিখে বসলেন, এবং লিখলেন এমন একজন অনুচরের পাঠানো তথ্যের উপর ভিত্তি করে, যে শয়তানি করে তাঁকে সঠিক তথ্য পাঠায়নি। ফলে পাঠক এবং সঙ্গীতপ্রেমীদের পড়ার জন্য প্রকাশিত হল একটি প্রতিবেদন, যেখানে যে মুখ্য তবলাবাদকের বাজনার অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করা হল, তাঁর আসলে প্রধান শিল্পীর সঙ্গে বাজানোর কথা হয়ে থাকলেও তাঁর দিল্লির ট্রেন অত্যন্ত দেরি করে আসায় বেচারা শেষপর্যন্ত সেদিন বাজাতেই আসতে পারেননি। সমালোচক যে সেদিন শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেনই না, অন্য কারোর পাঠানো সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে প্রতিবেদন লিখেছেন, এ-ঘটনার পর সে-কথা আর লুকিয়ে রাখা গেল না। এবার অবশ্য অলৌকিক কিছু ঘটল না, পাঠকরাও কিছুদিন উক্ত সমালোচকের লেখায় শাড়ি, ঝুমকা, কুর্তা ইত্যাদির বিস্তীর্ণ বর্ণনার হাত থেকে নিস্তার পেলেন।
ইদানীং সঙ্গীত সমালোচকদের সমাজেও টানাটানির বাজার, কারণ পয়সা দিয়ে লেখানো বা স্পনসর করা প্রচারের কাজ ছাড়া বেশির ভাগ প্রকাশনাই আজকাল শিল্পকলা বা সঙ্গীত নিয়ে প্রতিবেদন লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে ক’জন সঙ্গীত সমালোচক আজও মাটি কামড়ে পড়ে আছেন, তাঁরা মাঝেমধ্যে নিজেদের স্বঘোষিত মিউজিকোলজিস্ট বা সঙ্গীতবিশারদ হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। অবশ্য স্বঘোষিত পণ্ডিত বা ওস্তাদরা যে-বাজারে করে খাচ্ছেন, সে-বাজারে স্বঘোষিত মিউজিকোলজিস্টদেরই বা দোষ দিই কেমন করে? তবুও না বললেই নয়, তাঁদের লেখালিখির মধ্যে বিস্তর গণ্ডগোল রয়েছে। আজও অনুষ্ঠানে ‘মিউজিকোলজিস্ট’-এর উপস্থিতি ছাড়াই বহু রিভিউ লেখা হয়ে থাকে। কখনও-সখনও রেকর্ডিং দেখে এসব লেখা লেখা হয়, তবে সেক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং সততার খাতিরেই বলে দেওয়া উচিত, মূল অনুষ্ঠানের একটি রেকর্ডিং-এর রিভিউ করা হচ্ছে, অনুষ্ঠানের দিন সশরীরে লেখক উপস্থিত ছিলেন না। অনেক সময়ে উদ্যোক্তারাই পয়সা দিয়ে মিউজিকোলজিস্টদের অনুষ্ঠান বা ফেস্টিভ্যালে এরোপ্লেনে আসার ব্যবস্থা করে দেন। এসব ক্ষেত্রে যে-লেখক এই আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন, তিনি নিজের পৃষ্ঠপোষক সেই উদ্যোক্তারই অনুষ্ঠানের নিরপেক্ষ রিভিউ লিখবেন, এ-বিষয়ে কি ভরসা রাখা চলে? বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জুরি কমিটির সদস্য হিসেবেও আজকাল এইসব স্বঘোষিত মিউজিকোলজিস্টদের নিযুক্ত হতে দেখা যায়, কেউ-কেউ তো আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের কিউরেটর বা নির্বাচক পদে কাজ পেয়ে যান। একই ব্যক্তির পক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচিত করা, এবং তারপর কোনও প্রকাশনার জন্য সেই অনুষ্ঠানের চমৎকার প্রশংসা করে প্রতিবেদন লেখা— ব্যাপারটা কি আদৌ নৈতিক? আর যদি ধরেও নিই যে, এঁদের মধ্যে সবাই নিজেদের আয়োজিত অনুষ্ঠানের রিভিউ নিজেরা লেখেন না, নিজেদের থেকে একটু অন্যভাবে অন্য কারোর আয়োজন করা অনুষ্ঠানকে যে তাঁরা নিজেদের স্তরের বা নিজেদের থেকে একটু নিকৃষ্ট বলেই গণ্য করার প্রবণতা দেখিয়ে ফেলতে পারেন, সে-ব্যাপারেও নৈতিকতার প্রশ্ন উঠে আসে। যে-সমাজে নীতিবোধ বা সত্যনিষ্ঠা নিয়ে কেউই তেমন মাথা ঘামান না, সেখানে এ-জিনিসকে হয়তো স্বার্থের সংঘাত হিসেবে দেখা হবে না। তবে সোজা কথাটা সোজাসুজি বলে রাখাই বোধহয় কাম্য।
ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র