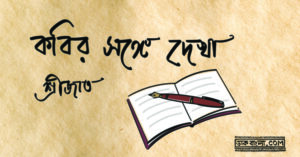যেসব এলাকা কয়েক দশকের মধ্যে গ্রাম থেকে মফস্সল আর মফস্সল থেকে শহর হয়ে যায়, সেখানে মানুষের বয়স খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। যেমন আমার বাড়ছে। হাফপ্যান্ট ছেড়ে ফুলপ্যান্ট ধরার কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের খেলার মাঠগুলো, সাঁতার কাটার পুকুরগুলো উঁচু পাঁচিল-ঘেরা হাউজিং কমপ্লেক্স হয়ে গেল। ফুরফুরে অবিবাহিত জীবনে নদীর যেসব ঘাটে সুন্দরী মেয়েদের ভাগ্যবান ছেলেদের সাথে বসে থাকতে দেখে দূর থেকে অভিশাপ দিতাম, বিয়ের এক দশক না পুরতেই সেইসব ঘাটে শপিং মল দাঁড়িয়ে পড়ল। বন্ধুদের অনেকের মুখ আর মনে পড়ে না। তারা কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, আমস্টারডাম, শিকাগোর গতিময় জীবনে সরে গেছে। যাদের বাবা-মা এখনও এখানে আছে, তারা অন্তত আরও একবার আসবে, ওঁরা মারা গেলে বাড়িটা প্রোমোটারের হাতে তুলে দিতে। যাদের বাবা-মা নেই তারা আর কখনও আসবে না। এইসব এলাকার মোড়ে-মোড়ে নতুন ফ্ল্যাট আর ভেঙে ফেলা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ পাশাপাশি। বৃদ্ধযুগের গলিত শবের পাশে নবযুগ আসার শব্দ যে হাতুড়ি-ছেনির কর্কশ সংঘর্ষ— তা কবি জানতেন বলে মনে হয় না। জানলে ‘প্রাণকল্লোল’ শব্দটা হয়তো লিখতেন না। অচেনা নতুন মানুষ আসছে, অথচ কোনও নতুন তরঙ্গ আমার মতো পুরনো বাসিন্দার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে না। পুরনো দোকানদারদের কাছে নতুন খদ্দেরদের কোনও হলুদ পাতার মাসকাবারি খাতা খোলা হচ্ছে না। সমস্ত নগদে তখুনি শোধ। এ-বাড়ির জানলা দিয়ে ও-বাড়ির কান্না দেখা যেত। মাঝে নতুন বাউন্ডারি ওয়াল হয়েছে, একতলায় কেবল গ্যারেজ আর কেয়ারটেকারের বসার ঘর। ফ্ল্যাটের চারপাশে মর্নিং ওয়াক, ইভনিং ওয়াকের জায়গা ছাড়া হয়েছে। তাই জানলাগুলো সরে গেছে দূরে। কান্নার আওয়াজ এখনও কানে আসে, কিন্তু কোন ফ্ল্যাটে কে কাঁদছে ঠাহর হয় না।
একের পর এক ভেঙে পড়া বাড়ি আর দর্পিত ফ্ল্যাটের পাড়া পেরিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ এক-একটা বাড়ি চোখে পড়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। কী আশ্চর্য! আশপাশের পরিবর্তন কী করে যেন ওগুলোর গ্রিলের গেট পেরোতে পারেনি। এইসব গাছ গজিয়ে যাওয়া ভূতুড়ে বাড়ির সামনে দাঁড়ালে বয়সটা খানিকক্ষণের জন্য থেমে যায়। মনে পড়ে, কোন বাড়িতে অমুকরা থাকত। কোথায় তমুক স্যার পড়াতেন। এই তো, এ-বাড়ির ছেলেটা আমার সাথে প্রাইভেট পড়ত দত্ত স্যারের কাছে। ও-বাড়ির মেয়েটা আমার চেয়ে দু’ক্লাস উঁচুতে ছিল, দোতলার বারান্দায় সারাক্ষণ ছাড়া থাকত একটা মুখরা ডোবারম্যান।
এইসব বাড়ির সামনে দিয়ে কখনও যেতে হলেই দাঁড়িয়ে পড়া আমার অভ্যাস। সেভাবেই একদিন আবিষ্কার করলাম বড়দিমাসির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মেনরোড থেকে অনেকটা ভিতরে কানাগলির শেষে বিরাট মাছ ধরার পুকুরের পাড়ে ওই বাড়িটা। গলিটা বড়দিমাসির আমলে কানা ছিল, এখন পুকুর বুজিয়ে ‘বৃন্দাবন অ্যাপার্টমেন্ট’ হয়ে যাওয়ায় মেনরোড থেকে সমান্তরাল রাস্তায় যাওয়ার শর্টকাট হয়ে গেছে। সেজন্যেই এত বছর বাদে এ-বাড়ির দিকে আসা হল। ঘোর বর্ষায় মেনরোড সারানোর কাজ চলছে, মাছি গলবার উপায় নেই। ভাগ্যিস এলাম! এক কোণে অলক্ষ্যে মরে যাওয়া বড়দিমাসির বাড়িটার সামনে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য চুলে পাক ধরা বন্ধ হয়ে গেল। স্কুলের শেষ ধাপের সেই দিনগুলোয় ফিরে যেতে-যেতে দেখি, আগাছায় ঢেকে যাওয়া বাড়ির খোলা থেকে যাওয়া পশ্চিমের জানলায় বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে একটা মোটা হুলো। বেড়াল কতদিন বাঁচে জানি না। এ কি বড়দিমাসির স্মৃতি ভুলতে পারে না বলেই ঘুরেফিরে এ-বাড়িতে আসে এখনও?
বড়দিমাসিকে ভোলা কিন্তু মোটেই শক্ত নয়। পুরনো বাসিন্দাদের মধ্যে আর কেউ মনে রেখেছে বলে তো মনে হয় না। বড়দিমাসির ছাত্রীরা এখন সকলেই মা, পিসিমা, মাসিমা, কাকিমা। মানুষকে মনে রাখার ক্ষমতা ওঁদের সবচেয়ে বেশি। স্কুলজীবনের দিদিমণি আর বন্ধুদের তো ছবির মতো মনে রাখেন। স্কুল ছাড়ার পর আর বেশি সুখস্মৃতি তৈরি হয় না বলেই হয়তো। তেমন দু’একজনকেও জিজ্ঞেস করে দেখেছি, বড়দিমাসির সম্পর্কে স্মৃতি আবছা। নামটা আর চেহারাটা মনে করতে পারেন। ‘খুব রাগী ছিলেন’, আর কিছু নয়। আসলে বড়দিমাসি কোনওদিন কোনও ছাত্রীর সাথে মিষ্টি করে কথা বলেনি।
আমাকে কিন্তু মিষ্টি খাইয়েছিল প্রথম দিনেই। আমাদের সবুজগ্রামের সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে পুরনো মেয়েদের স্কুল ললিতমোহন বালিকা বিদ্যাভবনের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তখন আমার বাবা। নতুন হেডমিস্ট্রেস আসছেন, ইন্টারভিউ হয়ে গেছে— এসব আলোচনা বাড়িতে শুনতাম, কান দিতাম না। তখন কান দেওয়ার বয়স নয়। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি কথাটা তখনও সবুজগ্রামে নতুন। আমি, বাবা, মা সেরকম একটা পরিবার। তাই মহিলা বলতে চিনি মা’কে, অরণ্যদেবের ডায়নাকে আর চাচা চৌধুরীর বউকে। বাড়িতে অনেক লোকজন আসত রোজ, কিছুদিন পরেই শুনলাম গার্লস স্কুলের নতুন হেডমিস্ট্রেস ভীষণ কড়া। তারপর শুনলাম ভীষণ অহংকারী। ক্রমশ নির্দয়, দজ্জাল, বাজে— এই শব্দগুলো এসে পড়ল। কেউ-কেউ দেখতাম বাবার কাছে এসে বিস্তর চেঁচামেচি করত। ‘এই মহিলাকে এবার তাড়াতেই হবে, দাদা। স্কুলটা কিন্তু উঠে যাবে নইলে।’ বাবা চিরকালই শিবঠাকুরের দলের লোক। সহজে উত্তেজিত হয় না, কিন্তু যেদিন রাগবে সেদিন মহাপ্রলয়। তবে বড়দিমাসির নামে হাজার অভিযোগ করেও কেউ প্রলয় সৃষ্টি করতে পেরেছিল বলে মনে পড়ে না। আমার জ্যাঠতুতো, পিসতুতো দিদিরা তখন ললিতমোহনের ছাত্রী। তারা বলত ‘বড়দি আসলে ব্যাটাছেলে। মেয়েছেলের অত মেজাজ হয়?’ সব শুনে আমার মনে তৈরি হয়েছিল একজন দশাসই মহিলার ছবি। চোখে মোটা চশমা, নইলে তাকালেই আগুন বেরিয়ে এসে ছাত্রীদের পুড়িয়ে ছাই করে দিত। আমাদের বাড়ির দরজার সমান লম্বা আর জানলার সমান চওড়া। স্কুলের উঠোনে দাঁড়ালে সূর্য ঢেকে যায়।
আমার লেখাপড়ায় মোটেই মন ছিল না, তাই যেদিন মা বলল, ‘সন্ধেবেলা আমরা গার্লস স্কুলের বড়দির বাড়ি যাব’, বেজায় ভয় পেয়েছিলাম। আমাদের একতলায় থাকত বড় জেঠিমা আর মেজদিদি, রাঙাদিদি। তারা থাকলে আমি ‘যাব না’ বলে বায়না ধরতামই, কিন্তু তখন জেঠিমা মেয়েদের নিয়ে ভাইফোঁটা দিতে বাপের বাড়ি গেছে। অতএব না গিয়ে উপায় ছিল না। দরজা খুলল যে, তার চেহারার সাথে কিন্তু আমার মায়ের বিশেষ তফাত নেই। দুজনেই ছোটখাটো, রোগাসোগা। মায়ের বরং চোখে গোল ফ্রেমের চশমা, সে-চশমা খুলে ফেললে মা অন্ধ। এর চোখে চশমাও নেই। পরনে এমন একটা শাড়ি, যার রং বলা শক্ত। মাথায় বেশ কয়েক গাছা পাকাচুল ছাড়া ভয় পাওয়ার মতো বিশেষ কিছুই নেই। দরজা খুলেই আমার হাত ধরে ঘরে এনে চেয়ারে বসিয়ে, বাবাকে নয়, মা’কেও নয়, আমাকেই জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কী খাবে বলো।’ তখন আমার বছর দশেক বয়স, অন্যের বাড়ির যে-কোনও খাবারই সুস্বাদু মনে করি, বাছবিচার নেই। সুতরাং প্রশ্নটা আমার কাছে দুরূহ। মুখ দেখে নিশ্চয়ই সে-কথা বোঝা গিয়েছিল। সময় নষ্ট না করে বেশ বড়-বড় দুটো রসগোল্লা আমাকে দেওয়া হল। বড়দের কথাবার্তা শুনতে-শুনতে জানলাম রসগোল্লাগুলো দোকানের নয়, বড়দিমাসির নিজের তৈরি। পরে লুচি-আলুর দম খাওয়া হল, সেগুলোও।
এক কোণে অলক্ষ্যে মরে যাওয়া বড়দিমাসির বাড়িটার সামনে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য চুলে পাক ধরা বন্ধ হয়ে গেল। স্কুলের শেষ ধাপের সেই দিনগুলোয় ফিরে যেতে-যেতে দেখি, আগাছায় ঢেকে যাওয়া বাড়ির খোলা থেকে যাওয়া পশ্চিমের জানলায় বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে একটা মোটা হুলো। বেড়াল কতদিন বাঁচে জানি না। এ কি বড়দিমাসির স্মৃতি ভুলতে পারে না বলেই ঘুরেফিরে এ-বাড়িতে আসে এখনও?
বাবা খেতে খেতে বলল, ‘স্কুল চালানোর এই পরিশ্রম, এর সাথে আবার রান্নাবান্নাও করেন? একটা রান্নার লোক রেখে দিলেই তো পারেন।’
বড়দিমাসি বলল, ‘আপনারা এলেন বলে শখ করে এত করলাম। একা মানুষের অত লাগে না কি? ওইটুকু রান্নার জন্যে আর রান্নার লোক কী হবে?’
আমার সাথে মাসি-সম্পর্ক সেদিনই স্থাপিত হয়েছিল। আমার নাম যতক্ষণে জানতে চাইল, ততক্ষণে দেড়খানা রসগোল্লা খেয়ে আমার ভয়-টয় উধাও। তাই উত্তর না দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করে বসলাম, ‘তোমার নাম কী?’
মা চোখ পাকিয়ে ধমকাল, ‘অ্যাই, এ কী অসভ্যতা!’
আর যে ভীষণ কড়া, অহংকারী, নির্দয়, দজ্জাল, বাজে— সেই মাসি একগাল হেসে বলল, ‘আহা, কী হয়েছে? নতুন পরিচয় হচ্ছে, নাম জিজ্ঞেস করবে না? কিন্তু আমার নামটা জানো, ইয়া লম্বা। প্রজ্ঞাপারমিতা দত্তচৌধুরী। অত বড় নাম ধরে কি ডাকা যায়, বলো? বাবা এদিকে একটা ডাকনামও দিয়ে যাননি, পারমিতা বলে ডাকতেন। কী করি এখন?’
মা বলল, ‘নাম জেনে ও কী করবে, দিদি? আপনাকে সবাই বড়দি বলে, ও-ও তাই বলবে।’
‘কেন? আমাকে এতটুকু ছেলেরও দিদিমণি হতে হবে কেন? এ তো ভারি অন্যায় কথা! না ভাই, তুমি বরং আমাকে মাসি… বড়দিমাসি বলে ডেকো। তোমার মা তো আমার ছোট বোনেরই মতো…’
রিকশা করে যখন বাড়ি ফিরছি, মা বাবাকে জিজ্ঞেস করল, ‘হ্যাঁ গো, অশোক-টশোক যে তোমার কাছে এসে এত নিন্দে করে মহিলার… তেমন কিছু তো দেখলাম না?’
‘আরে ওরা কিসু বোঝে না কি?’ বাবা তাচ্ছিল্য করে উত্তর দিল।
‘বোঝে না?’
‘ধুর। আসল কথা মহিলাকে দিদিমণিরা কবজা করতে পারছে না, তাই নেতাদের কাছে গিয়ে দিনরাত নালিশ করছে।’
‘কেন?’
‘আরে উনি লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ছাত্রী। বি.এস.সি. পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস, এম.এস.সি.-তেও তাই। ওঁকে এইসব উমাদি, শুভ্রাদি, মানসীদি— এরা কখনও সহ্য করতে পারে? ইনি যদি আগের হেডমিস্ট্রেসের মতো এদের সাথে আপোস করে চলতেন, তাহলে এরা কোনও গোলমাল করত না।’
‘ইনি করছেন না বুঝি?’
‘মোটেই না। ডাঁটের উপর রেখেছেন। স্কুলে আসতে দেরি করলে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন, ক্লাসে যেতে দেরি করার উপায় নেই, সারাক্ষণ রাউন্ড দিচ্ছেন। এদের এসব সয়? সবই ভাল, তবে একটাই দোষ ওঁর। লোকের মুখের ওপর যা বলার বলে দেন। ভদ্রমহিলার কৌশল বলে কিছু নেই। এত সোজাসাপ্টা লোক পৃথিবীর সর্বত্র বিপদে পড়ে। সারাক্ষণ শত্রু তৈরি করছেন তো…’
বাবার অনুমান নির্ভুল ছিল। বছরখানেকের মধ্যেই গার্লস স্কুলে ধুন্ধুমার লেগে গেল। বাবার কাছে দুজন বাদে সমস্ত শিক্ষিকার সই করা চিঠি জমা পড়ল, প্রজ্ঞাপারমিতা দত্তচৌধুরী প্রধান-শিক্ষিকা থাকলে কোনও দিদিমণি ক্লাস নেবেন না। এর মধ্যে বাবার সাইকেলে চড়ে বেশ কয়েকবার বড়দিমাসির বাড়ি গেছি। বাবা বড়দিমাসির সাথে বসে কথা বলেছে, আমি দু’কামরার বাড়িটা জুড়ে খেলে বেড়িয়েছি। টুলের উপর উঠে আলমারি থেকে মোটা-মোটা রঙিন ছবিওলা বই বার করে পাতা উল্টে গেছি। বড় হয়ে বুঝেছি, ওগুলো জীববিজ্ঞানের অত্যন্ত দামি বই, অনেকগুলোই বিদেশ থেকে আনানো। বড়দিমাসি ওগুলো নিয়েই বেঁচে থাকত। প্রথম আমাদের বাড়িতে এল দিদিমণিদের সেই বিদ্রোহের সময়। মনে আছে সন্ধেবেলা রিকশা করে এল, চেয়ারে বসল, আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালেও আমাকে জড়িয়ে ধরল না। ম্লান হাসল শুধু। ব্যাগ থেকে একটা লম্বা বাদামি খাম বার করে বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘অখিলবাবু, আমি আপনার বেশি সময় নষ্ট করব না, রিকশাটা ছাড়িনি। এটা নিয়ে আমাকে দায়মুক্ত করুন।’
‘এটা কী?’ বাবা অবাক।
‘রেজিগনেশন লেটার।’
‘কেন?’
‘আপনি হয়তো স্বীকার করবেন না, কিন্তু আমি খবর পেয়েছি। আমার নামে আপনার কাছে চিঠি এসেছে। আমি থাকতে দিদিমণিরা কেউ ক্লাস করবেন না।’
বাবা হেসে বলল, ‘না, অস্বীকার করব কেন? কিন্তু কথা হচ্ছে, স্কুলের অথরিটি তো দিদিমণিরা নন, অথরিটি হল ম্যানেজিং কমিটি। তার মিটিং ডাকা হবে, এত বড় ইস্যু যখন, তখন এটা নিয়ে মিটিঙে আলোচনা হবে, তারপর কিছু একটা সিদ্ধান্ত হবে। আপনার এখনই রিজাইন করার তো কারণ দেখছি না।’
বড়দিমাসির কথা শুনে মনে হল বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে রেখে এসেছে। চোয়াল শক্ত করে বলল, ‘ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তে বরখাস্ত হওয়ার জন্যে ওয়েট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় অখিলবাবু। আমার কাছে আত্মসম্মান সবচেয়ে বড় জিনিস। তার জন্যে আমি নিজের ভাইবোনের সাথেও সম্পর্ক তুলে দিয়েছি। এই চাকরির জন্যে সেটা স্যাক্রিফাইস করতে পারব না।’
বলেই উঠে পড়ল। বাবা হাত ধরে আটকে বলল, ‘আরে দিদি, তাড়া কীসের? ছোটভাইয়ের কথাটা পুরো শুনেই যান নাহয়।’
শুধু বাবা নয়, মা-ও অনেকক্ষণ ধরে সেদিন বড়দিমাসিকে বুঝিয়েছিল, চাকরি ছেড়ে চলে গেলে ফাঁকিবাজ বদমাইশরা জিতে যাবে, আর স্কুলটা হেরে যাবে। বাবা শেষে বলল, ‘আপনাকে আমাদের কারোর কথা শুনতে হবে না, আপনি মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যান। আপনি তো জানেন, এ-তল্লাটে মেয়েদের স্কুলগুলোর কী হাল। তা, আমাদের এখানকার মেয়েরা কি আপনার মতো লেখাপড়া শিখবে না কোনওদিন? বড়-বড় জায়গায় পড়াবে না, চাকরি-বাকরি করবে না? কেবল বিয়ে করবে আর বাচ্চা মানুষ করে যাবে জেনারেশনের পর জেনারেশন?’
সেই প্রথম এবং সেই শেষবার বড়দিমাসিকে একেবারে ভেঙে পড়তে দেখেছিলাম।
‘আমি কার কী ক্ষতি করেছি বলুন তো ভাই?’ বলতে বলতে বড়দিমাসি কেঁদে ফেলল। ‘স্কুলে ডিসিপ্লিনের দরকার নেই? দিদিমণিরা যদি যখন ইচ্ছে স্কুলে আসেন, মেয়েরা কী শিখবে? স্টাফরুমে গেলে মনে হত মাছের বাজার। সারাক্ষণ শাড়ির সেলসম্যান, এটা-সেটার সেলসম্যান এসে চলেছে। স্কুলের গেট হাট করে খোলা, যার যেমন ইচ্ছে আসছে-যাচ্ছে। একে মেয়েদের স্কুল, কোনও মেয়ের কিছু হলে গার্ডিয়ান এসে চেপে ধরবে না? লেখাপড়ার পরিবেশের কথা যদি বাদও দিই। দিদিমণিরা আমাকে কেন শত্রু ভাবছেন? যা করছি সবই তো মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে।’
এসব কথা স্কুলের মেয়েরা কোনওদিন জানতে পারেনি। তাই বোধহয় কেউ মনে রাখেনি, মনে করতেও চায় না। অবশ্য বড়দিমাসি যেখানে-যেখানে গেছে, কারোর মনেই বোধহয় কোনও সুখস্মৃতি রেখে আসেনি। সেদিনই কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিল, ‘আসলে আমি মানুষটাই খারাপ। নইলে কারোর সাথেই অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না? আপনি আমার রেজিগনেশনটা অ্যাকসেপ্ট করে নিন, অখিলবাবু। এর আগে চারটে স্কুল ছেড়েছি, এটা নয় পাঁচ নম্বরই হল। দেখি, কলকাতার দিকেই কোথাও কিছু পাই কি না। আর হেডমিস্ট্রেসের দায়িত্ব নেব না। সাধারণ টিচার হিসাবে স্কুলে যাব, ক্লাস করাব, খাতা দেখব, বাড়ি ফিরব। বয়স হচ্ছে, আর ঝামেলা করে দরকার নেই।’
বাবার অভ্যাস বা বদভ্যাস ছিল চরম বিষণ্ণ মুহূর্তেও রসিকতা করা। বলল, ‘বললেই হল? আপনি পারবেন না ওসব। দেখবেন হেডমিস্ট্রেসকেই ধমকে দিয়েছেন, তারপর চাকরি নিয়ে টানাটানি। আপনার দ্বারা হেডমিস্ট্রেস ছাড়া কিছুই হওয়া হবে না।’
‘কিন্তু আমার জন্যে যে স্কুলটা উঠে যাওয়ার জোগাড়? একজন টিচারও আমার পাশে নেই। এভাবে স্কুল চালাব কী করে?’
‘প্রথম কথা, একজনও পাশে নেই তথ্যটা ভুল। রমাদি আর ঝুমুরদি এই চিঠিতে সই করেননি, আমার সাথে কথাও হয়েছে। ওঁরা আপনার পক্ষে আছেন। আর এই বাকি খান্ডারনিদের আমি দেখে নেব। এসব গাঁয়ের পলিটিক্স আপনি বুঝবেন না। এদের পেছনে খুঁটি আছে তাই এত লাফাচ্ছে। সে-খুঁটি আমি উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা করছি। আপনি শুধু ক-টা দিন অপেক্ষা করুন, মাথা ঠান্ডা রাখুন।’
বড়দিমাসির কথা শুনে মনে হল বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে রেখে এসেছে। চোয়াল শক্ত করে বলল, ‘ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তে বরখাস্ত হওয়ার জন্যে ওয়েট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় অখিলবাবু। আমার কাছে আত্মসম্মান সবচেয়ে বড় জিনিস। তার জন্যে আমি নিজের ভাইবোনের সাথেও সম্পর্ক তুলে দিয়েছি। এই চাকরির জন্যে সেটা স্যাক্রিফাইস করতে পারব না।’
বড়দিমাসি সেদিন থেকে গিয়েছিল, আর স্কুলটাও বেঁচে গিয়েছিল। দিদিমণিদের বিদ্রোহ বেশিদিন চলেনি। ম্যানেজিং কমিটির পর পর অনেকগুলো মিটিং হয়েছিল। প্রথমটায় প্রবল চেঁচামেচি, তারপর কমতে-কমতে শেষে প্রজ্ঞাপারমিতা দত্তচৌধুরী নির্দোষ— এই সিদ্ধান্ত। বিদ্রোহে যে তিনজন ফাঁকিবাজ বয়স্ক শিক্ষিকা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাঁদের শো-কজের ভয় দেখাতেই বিদ্রোহ ঠান্ডা। বড়দিমাসি আরও দশ বছর সবুজগ্রামের গার্লস স্কুলের দাপুটে হেডমিস্ট্রেস হিসাবে কাজ করেছিল। স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ল, মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক হল, দুটো পরীক্ষাতেই স্কুলের মেয়েদের ফলাফল আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়ে গেল। দু-একজন মেয়ের বাবা-মা ছাড়া কেউ অবশ্য তার জন্যে বড়দিমাসির কোনও কৃতিত্ব স্বীকার করেনি। তবে আমাদের সবুজগ্রামে তখন সব রাস্তা পিচের হয়ে গেলেও গায়ে গেঁয়ো গন্ধ ছিল। তাই দিদিমণিদের, বিশেষ করে বড়দিদের, ডাক্তার থেকে মেথর অবধি সকলে সম্মান করত।
অবসর নেওয়ার এক বছর আগে বড়দিমাসি বাবাকে জিজ্ঞেস করল, ‘রিটায়ারমেন্টের পরে কোথায় থাকা যায় বলুন তো? বৃদ্ধাশ্রমগুলোর কি অনেক খরচা?’
বাবা তো অবাক। ‘মানে? আপনার তো আলিপুরে নিজের বাড়ি আছে!’
‘নিজের বাড়ি আর কোথায়? বাবার বাড়ি। সে তো ভাইয়েরা বলছে বাবা নাকি উইল করে গেছে ওদের নামে। করতেও পারে। আমার বাবার আগু-পিছু ভেবে কাজ করার অভ্যেস ছিল না। তাছাড়া আমার সাথে তো রাগারাগি হয়ে গেছিল চাকরি করা নিয়ে…’
বৃদ্ধাশ্রম সম্বন্ধে আমার গেঁয়ো বাবার বিশেষ ধারণা ছিল না। তাছাড়া বয়স্ক মানুষদের বৃদ্ধাশ্রমে থাকা তাদের প্রতি অন্যায় বলেই তখন সবুজগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা মনে করত। তাই বাবা বড়দিমাসিকে এখানেই জমি কেনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। বড়দিমাসির এক প্রাক্তন ছাত্রীর বাবা কন্ট্রাক্টর। তিনিই এই ছোটখাটো একতলা বাড়িটা করে দিয়েছিলেন। তখন কলেজে পড়ি, বাবা আমাকেই মাঝেমধ্যে পাঠাত খোঁজখবর নিতে। অল্প বয়স থেকেই হাই প্রেশারের রোগী, ততদিনে হার্টের অসুখ ধরে গেছে বড়দিমাসির। মেজাজটাও ক্রমশ আরও তিরিক্ষি। তাছাড়া ওই বয়সে একটা বুড়ির কাছে গিয়ে বসে থাকতে কারই বা ভাল লাগে? বুড়িছোঁয়া করে আসতাম। শুনতাম বড়দিমাসির সকলের প্রতি অভিযোগ। মুদি ওজনে ঠকায়, রিকশাওয়ালা বেশি ভাড়া নেয়, পেনশন তুলতে গেলে ব্যাঙ্কের লোক শুধু শুধু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করায়, কলকাতা থেকে অপোগণ্ড ভাইপো এসে টাকা চেয়ে বিরক্ত করে— অভিযোগ বেড়েই চলেছিল। সঙ্গে বাড়ছিল পোষা বেড়ালের সংখ্যা। বেড়াল পোষার শখ চিরকালই। সেই ছোটবেলা থেকেই একটা না একটা বেড়াল বড়দিমাসির বাড়িতে বরাবর দেখেছি। তার সাথে যেভাবে কথা বলত, মনে হত মানুষের সাথে কথা বলছে। তাদের হাবভাব দেখেও মনে হত তারা কথাগুলো বুঝতে পারছে। কিন্তু এই নতুন বাড়িতে আসার পর থেকে দেখলাম প্রথমে একটা মেনি, তারপর তার সঙ্গী হুলো, কিছুদিন পরে তাদের গুটিচারেক ছেলেমেয়ে, তাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনী— এভাবে বেড়ালের সংখ্যা বেড়েই চলল। কিছুদিন পরে এমন অবস্থা হল যে, ও-বাড়িতে সারাক্ষণই গোটাকুড়ি বেড়ালের দেখা মেলে। এক-একদিন সন্ধেবেলা আমার মা বড়দিমাসির সাথে গল্পগুজব করতে যেত। কিন্তু একা মহিলা, কথা বলার লোক নেই— এই সহানুভূতিকে অচিরেই ছাড়িয়ে গেল মায়ের বেড়ালে ঘেন্না।
তেমন বিজাতীয় ঘৃণা না থাকলেও যে-কোনও সুস্থ লোকেরই ও-বাড়িতে ঢুকলে অস্বস্তি হওয়ারই কথা। বাইরের ঘরে বসে কথা বলছি, হয়তো পায়ের কাছে এসে বসল একটা ছোট্ট বেড়ালছানা। বড়দিমাসির পাশ থেকে আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে একটা মোটা হুলো। আমার দু’পাশে দুজন বডিগার্ডের মতো বসে আছে। দেখতে পাচ্ছি খাটের তলায় একজন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি পাঁচিলের উপর লাইন দিয়ে বসে আছে পাঁচ-ছ’জন। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে দুজনের ঝগড়ার শব্দ, কথা বলতে-বলতে বড়দিমাসি মাঝে মাঝে ধমক দিচ্ছে, ‘আঃ! কী হচ্ছে তখন থেকে? একটু শান্তিতে কথা বলতে দিবি না তোরা?’ ধমক শুনে কয়েক সেকেন্ডের জন্য সে-ঝগড়া থেমে যায়, আবার চালু হয়। পরে একদিন বাবার সঙ্গে গিয়ে জানলাম, বড়দিমাসির পোষ্যের সংখ্যা ৬১-তে পৌঁছেছে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম আছে, থালা-বাটি-গ্লাস আছে। মালকিনের নিজের কাজের লোক আলাদা, পোষ্যদের কাজের লোক আলাদা। তার কাজ রোজ এদের খোরাকির ব্যবস্থা করা। নিজের চোখেই দেখলাম, রাত ন’টার একটু আগে সেই কাজের দিদি রান্নাঘরে শতরঞ্চি পেতে পংক্তিভোজনের ব্যবস্থা করলেন। তারপর থালার গায়ে গ্লাস দিয়ে সজোরে পেটালেন মিনিট দুয়েক। পোষ্যরা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, একে-একে হাজির হল। নিতান্ত ভদ্রজনের মতো বসে পড়ল নিজ-নিজ স্থানে, ভাত-মাছ-দুধ খেয়ে আবার চরতে বেরিয়ে গেল। বড়দিমাসি বলল শোওয়ার সময় হলে ওরা ফিরে আসে। পুঁটি আর নন্দু শোয় বড়দিমাসির বিছানায়, বাকিরা এদিক-ওদিক।
দেখে ভারি আশ্চর্য লাগল, মজাও যে লাগল না তা নয়। বন্ধুবান্ধবদের বেশ গল্প করে বলার মতো ব্যাপার। কিন্তু বাবার মুখ ভার। বাড়ি এসে মাকে বলল, ‘লীলা, বড়দি মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাচ্ছেন।’ আমাদের অবশ্য তা মনে হয়নি। মা শুনে বলল, ‘একা মানুষ তো, ওঁর কাছে তো তেমন কেউ যায়ও না, তাই বেড়াল নিয়েই থাকেন। তা থাকুন না। ক্ষতি কী? ওরকম তো অনেকেই হয়। কতজন আছে না, রাস্তায়-রাস্তায় কুকুরকে খাইয়ে বেড়ায়? তারা কি পাগল?’
‘কী জানি! আমার যেন কেমন লাগছে। উনি সারাক্ষণ বেড়ালগুলোকে নিয়েই বলে গেলেন। কোনটার বাচ্চা হবে, কে অন্য বাড়ি থেকে চুরি করে মাছ খেয়েছে বলে খুব বকেছেন, একটা নাকি সারাক্ষণ পড়ে-পড়ে ঘুমোয়— এইসব। অন্য কোনও কথাই নেই। অত মেধাবী, পরিশ্রমী একটা মানুষ সারাক্ষণ কেবল বেড়ালদের নিয়ে ভেবে চলেছে! এভাবে কতদিন সুস্থ থাকবেন?’
সুস্থ থাকা কাকে বলে আমার আজকাল গুলিয়ে যায়। চারপাশের অনেক মানুষকেই তো অসুস্থ, অসুখী মনে হয় আমার। কিন্তু সে-কথা তাদের বলি না, কাউকেই বলি না। কে জানে, তাদেরও আমাকে অসুস্থ মনে হয় কি না! সুস্থ থাকা মানে যদি হেঁটে-চলে বেঁচে থাকা হয়, তাহলে বড়দিমাসি তারপরেও বছর দুয়েক সুস্থ ছিল। তারপর একটা ভয়ানক স্ট্রোক হল, কয়েকদিন ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখতে হল। সংকট কেটে যাওয়ার পর পিজি হাসপাতালে দেখতে গেলাম বাবার সাথে। আগের কয়েক বছরের চেয়ে সেদিন বড়দিমাসিকে অনেক বেশি সুস্থ মনে হল। অথচ বলল, ‘অখিলবাবু, আমার আর বাড়ি ফেরা হবে না, বুঝলেন? ডাক্তাররা যা-ই বলুক। ফেরার যে আমার খুব দরকার আছে তা-ও নয়। টাকাপয়সা যা ছিল, হিসাব করে বেশিটাই ওই ভাইপোটাকে দিয়ে দিয়েছি। কী একটা ব্যবসা করবে বলছে অনেক বছর ধরে। আগে দিইনি, কিন্তু এখন তো আর আমার লাগবে না ওসব, তাই দিয়ে দিলাম। ব্যবসা করুক, উড়িয়ে দিক, যা পারে করুক। আর একভাগ রেখে দিয়েছি, আপনাকে ওটার দায়িত্ব নিতে হবে।’
‘আমাকে!’ বাবা তো আকাশ থেকে পড়ল। ‘আমাকে টাকা দেবেন কেন?’
‘না না, আপনাকে দিচ্ছি না। দিচ্ছি আমার বেড়ালগুলোকে।’
‘বেড়াল!’
‘হ্যাঁ, আপনি জানেন না? আমার তো এখন ১০৩ জন। আমি না থাকলে ওদের তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আমি একটা ট্রাস্টি বোর্ড তৈরি করে দিয়ে যাব। আপনার তো চেনা উকিল-টুকিল আছে, আপনি পরের দিন আসার সময় একটা ডিড তৈরি করিয়ে নিয়ে আসুন, আমি সই করে দেব। আমার ওই বাড়িটা আর বাকি টাকাপয়সা আমি ট্রাস্টি বোর্ডকে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি তার চেয়ারম্যান হবেন, অন্য কাউকে তো আমি বিশ্বাস করতে পারব না।’
আমি হেসে ফেলেছিলাম, বড়দিমাসি কটমট করে তাকাল। বাবা বলল, ‘কিন্তু বড়দি, অতগুলো বেড়াল সামলাবে কে? আমার তো সময় নেই।’
‘না না, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আরতি আছে তো। ও-ই তো রোজ ওদের খেতে-টেতে দেয়, ও সব জানে কী করে কী করতে হয়। আপনি শুধু টাকাপয়সার জোগানটা খেয়াল করবেন। আমি চাই বেড়ালগুলো ও-বাড়িতেই থাকুক, যেমন চলছে তেমনই চলুক। বেড়ালের নামে তো বাড়ি লিখে দেওয়া যায় না, আর দিলেই বা ওরা বাড়ি সামলাবে কী করে? তাই…’
বাবা ‘বলব না, বলব না’ করেও বলেই ফেলল যে, বেড়াল কুকুরের মতো অনুগত নয়। মালিক মারা গেলে অনেক সময় শোকে কুকুরও মারা যায়, কিন্তু বেড়ালের অত মায়া নেই। বড়দিমাসি না থাকলে ওরা আপনিই এদিক-ওদিক চলে যাবে, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেবে। কথাটা বড়দিমাসির একদম পছন্দ হল না। বেশ রেগেই বলল, ‘আপনি কিচ্ছু জানেন না। আমার বেড়ালরা সেরকম নয়। আমি চোখ বুজলেই আপনারা ভুলে যাবেন, ওরা কক্ষনো ভুলবে না। যাকগে, ভেবেছিলাম অন্তত আপনার উপর ভরসা করতে পারি। এখন দেখছি ভুল ভেবেছিলাম। আমাকে অন্য লোক দেখতে হবে।’
আমরা অপ্রস্তুত। বড়দিমাসি খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে হঠাৎ খুব বিশ্রীভাবে বলল, ‘আপনারা এখন আসুন।’ সেই শেষ দেখা। তার দু-একদিন পরেই খবর এল বড়দিমাসি মারা গেছে। আমরা যে ভুলে গেছি তাতে ভুল নেই। এমনকী এ-তল্লাটে ১০-১৫ বছরের পুরনো বাড়ি দেখলেই চোখ চকচক করে যে প্রোমোটারদের, তারা পর্যন্ত এই ৩০ বছরের পুরনো কাঠাদুয়েক জমির উপর পড়ে থাকা জংলা বাড়িটাকে ভুলে গেছে। তাই ভাবছি, জানলায় বসে থাকা বেড়ালটা কি বড়দিমাসির পোষ্যদের কেউ? অন্তত তাদের বংশধর তো হতে পারে? আমরা অতীত ভেঙে ভবিষ্যতের ইমারত তৈরি করি, ওদের তো আর ইমারতের প্রয়োজন নেই। ওরাও কি মনে রাখেনি বড়দিমাসির প্রাণঢালা ভালবাসা? আমরা ইতিহাস-বিস্মৃত বলেই যে ওরাও ইতিহাস-বিস্মৃত হবে, এমন তো কথা নেই!
ছবি এঁকেছেন সায়ন চক্রবর্তী