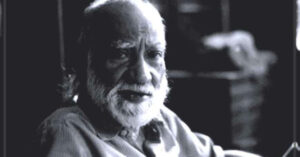আশির দশকে আমি যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় তৎকালীন ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের হাত ধরেই। অবশ্য ঠিক তা নয়, কারণ সরকারি ভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ১৯৫৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর, তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার স্বদেশি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যাদবপুরের পূর্বসূরি ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গল (এন সি ই বেঙ্গল)। একটি রীতিমতো দেশপ্রেমিক এবং প্রতি-ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, যার আবহে সবার আগে ভারতবর্ষের মানুষ এবং তাঁদের দাবি-দাওয়া-প্রয়োজন নিয়ে ভাবা হবে, এন সি ই বেঙ্গল ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। লক্ষ্য ছিল, কলা এবং বিজ্ঞানে শিক্ষাদান করা। এঁদের সহোদর প্রতিষ্ঠান, সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনের হাত ধরে ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিট্যুটের জন্ম, যা পরে এন সি ই বেঙ্গলের কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির সংলগ্ন হয়ে যায় (১৯৫৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানই রূপ বদলে হয়ে ওঠে কলা, বিজ্ঞান, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি— এই তিন বিভাগে বিভক্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)। এই এতগুলো বছর ধরে এন সি ই বেঙ্গল ছিল বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী চেতনার পরাকাষ্ঠা— ছাত্রদের মেসে বা ক্যান্টিনে তখন মাঝেমধ্যেই অনুশীলন সমিতির কর্মী বা বিপ্লবীদের উপস্থিতি এর প্রমাণ। শোনা যায়, কলেজের প্রশাসকেরা নাকি এন সি ই বেঙ্গলের ছাত্রদের সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিতেন তাদের এই ‘বেআইনি’ ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে মেলামেশা করতে।
এন সি ই বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠানের পিছনে কী কী কারণ ছিল, স্কুল ও কলেজের শিক্ষায় (বিশেষ করে বাংলার পূর্বাঞ্চলে) তার কেমন প্রভাব পড়েছে— এসব নিয়ে অনেক কিছুই বলা গেলেও, তা বলার স্থান বা কাল কোনওটাই এখন নয়। তবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কেন বহু আন্দোলন বা বিক্ষোভের শীর্ষে দেখা যায়, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তির ইতিহাস মাথায় রাখতেই হয়। বলে রাখা ভাল, এসব আন্দোলনের ফলে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মব্যবস্থায় নয়, যেসব উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয় নিজের পরিচালনার কাজে ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের বারবার শরিক করেছে (কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে), তাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। তবে সবার আগে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমটির কথা বলা যাক।
১৯৭০ সালের ৩০ ডিসেম্বর। তৎকালীন অস্থায়ী উপাচার্য প্রফেসর গোপাল চন্দ্র সেন সেদিন ক্যাম্পাসে তার কোয়ার্টারে ফিরছেন। উপাচার্যের পদে সেটিই ছিল তাঁর শেষ দিন। এর এক মাসের কিছু বেশি দিন আগে, ২০ নভেম্বর, বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন ছাত্রকে যখন নকশালবাদী হওয়ার অভিযোগে পুলিশ ‘এনকাউন্টার’ করে মেরে ফেলে, তখন প্রফেসর সেন জনসমক্ষে এর প্রতিবাদ করে পুলিশদের শাস্তির দাবি তোলেন— সেই প্রথম কোনও উপাচার্যের এমন প্রতিবাদ করা। তারও কিছু মাস আগে, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিভাগের ছাত্ররা যখন ‘বুর্জোয়া’ শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরীক্ষা বাতিল করার দাবি তোলে, প্রফেসর সেন জানিয়েছিলেন, ছাত্ররা যদি উচিত মনে করে, তাদের পরীক্ষা বয়কট করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, তবে যারা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাদের কোনওভাবেই বাধা দেওয়ারও তিনি বিরোধী। পরীক্ষায় তিনি নিজে সুপারভাইজর ছিলেন, এবং পুজোর ছুটির মধ্যেও নিজের বাড়ি থেকে প্রভিশনাল পাস সার্টিফিকেট দেওয়ার বন্দোবস্ত করে দেন। ডিসেম্বরের সেই নিয়তিনির্দিষ্ট দিনে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর সমস্ত অবদান, ছাত্রদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা, কোনও কিছুরই কোনও মূল্য থাকেনি— কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির কাছে তাঁকে নৃশংসভাবে ছুরির আঘাতে খুন করা হয়। সাধারণত ধরে নেওয়া হয়, নকশাল আদর্শে বিশ্বাসী এক বা একাধিক ছাত্রই এই খুন করেছিল। এ বিষয়ে নানা কানাঘুষো এখনও শোনা যায়, তবে প্রফেসর সেনের হত্যাকারীদের আজ পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়নি।
ভবিষ্যতে ক্যাম্পাসের কোনও ছাত্র-আন্দোলন এই নৃশংস ঘটনার ছায়া এড়াতে পারেনি— ২০১৪ সালে আন্দোলনরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে অন্য এক উপাচার্যের পুলিশ ডাকার সপক্ষে প্রফেসর সেনের হত্যাকেই যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছিল, যে ঘটনা জন্ম দেয় গত দশকের সম্ভবত বৃহত্তম ছাত্র আন্দোলন ‘হোক কলরব’-এর। যাদবপুরের ছাত্ররা যে ‘অতি-বামপন্থী’ ও হিংস্র চরিত্রের মানুষ, তার প্রমাণ হিসেবে, এবং প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার সমর্থনেও, এই ঘটনাকেই বারবার পেশ করা হয়।
১৯৮৪ সালে স্নাতক হিসেবে যখন আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, গোপাল চন্দ্র সেনের হত্যা তখনও জনস্মৃতিতে রয়েছে, তবে ছাত্রদের উদ্দেশ্য বা স্বভাবের ব্যতিক্রম হিসেবে, উদাহরণ হিসেবে নয়। ক্যাম্পাসে তখন স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (এস এফ আই) দাপট— বলাই বাহুল্য, তখন বামফ্রন্ট সরকারের আমল, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সবাদী) (সি পি আই এম) তখন প্রায় নিরঙ্কুশ। তবে অন্য কিছু পক্ষ সে-সময়ে সক্রিয় ছিল না, তাদের মধ্যে কেউ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অনুগামী, কেউ বা নিছক ‘সহযাত্রী’। এদের মধ্যে সবচেয়ে সাফল্য পেয়েছিল ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস ফ্রন্ট (ডি এস এফ)— ১৯৭৭ সাল থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিভাগের সমস্ত ছাত্র ইউনিয়নের ভোটে তারাই জয়ী হয়েছিল। যে বিষয়টা আরও উল্লেখযোগ্য, সেটা হল, তখন ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বা বিক্ষোভ কেবল ছাত্রসমাজেরই অধিকার বা দাবির প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকত না (যদিও সেগুলো মুখ্য বিষয় ছিল অবশ্যই)।
আমার যাদবপুরে ঢোকার কয়েক মাসের মধ্যেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর সকাল দশটা নাগাদ কলেজ পৌঁছে এই সংবাদ পেয়ে কতটা ভীত-সন্ত্রস্ত বোধ করেছিলাম, কীভাবে ছাত্ররা এবং শিক্ষকেরা শহরের শিখ-প্রধান অঞ্চলগুলোয় ছুটে গিয়েছিলেন যাতে রাজধানীর মত কলকাতাতেও ওই সম্প্রদায়ের উপর হিংসা না নেমে আসে, তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওইরকম কয়েকটি অভিযানে আমিও শামিল হই। যদিও রাজ্য প্রশাসনের দৃঢ়তা এবং তৎপরতার কারণে কোনও হত্যাকাণ্ড ঘটেনি— কিছু বাস অবশ্য পুড়েছিল, যতদূর মনে পড়ে— যাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সম্পর্ক নেই, তাঁদেরও রক্ষা করতে বিপদের মধ্যে ছাত্ররা যেভাবে স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিল, তা কিন্তু আজও বড় গর্বের বিষয়।
অন্য কিছু ঘটনাও মনে পড়ছে। ১৯৮৫ সালে শাহবানো মামলা, এবং রূপ কানোয়ারের ‘সতীদাহ’ (১৯৮৭), এই দুই ঘটনার অন্তর্নিহিত নারীবিদ্বেষকে চিহ্নিত করে গড়ে ওঠে বিক্ষোভ ও আন্দোলনে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। সত্যি বলতে, ভারতীয় সমাজের পিতৃতান্ত্রিকতার বিষয়ে আমাদের যে চেতনা, এবং নারী অধিকারের জন্য লড়াইয়ের যে প্রয়োজনীয়তা, সে ব্যাপারে আমার নিজের, এবং আমার অনুমান স্নাতকস্তরে আমার বেশিরভাগ সহপাঠীদের— বোধের মূলে সরাসরিভাবে রয়েছে যাদবপুরে শিক্ষার অভিজ্ঞতা। ভারতীয় অ্যাকাডেমিয়ার পরিসরে তথাকথিত ‘নারীবাদী চেতনা’র প্রসারের সাক্ষী থেকেছে আশির দশক, তাতে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যাদবপুরে ইংরেজি বিভাগে আমাদের এক অধ্যাপিকা, প্রফেসর মালিনী ভট্টাচার্যের কলমে পেয়েছি অপূর্ব সব নাটক— ‘মেয়ে দিলে সাজিয়ে,’ ‘এত রক্ত কেন,’ এবং ‘বাঁদর খেলা’ (শেষেরটি ছোট নাটিকা)। প্রত্যেকটি নাটকেরই বিষয় ছিল নারীর শোষণ এবং পণ্যীকরণ। শুধু ক্যাম্পাসে নয়, অন্য একাধিক কলেজে ও মঞ্চে (প্রায়ই ওপেন এয়ার মুক্তমঞ্চে) এইসব নাটক মঞ্চস্থ করেছে ছাত্ররা। আবার এই দশকেই ইংরেজি বিভাগের মালিনীদি, যশোধরাদি (প্রফেসর যশোধরা বাগচী), সজনীদি (প্রফেসর সজনী মুখার্জি), সুপ্রিয়াদি (প্রফেসর সুপ্রিয়া চৌধুরী), এবং অন্য অনেকেই, যেমন দর্শন বিভাগের প্রফেসর শেফালি মৈত্র, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর নবনীতা দেব সেন, ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর অনুরাধা চন্দ (এ তালিকা সম্পূর্ণ নয়)— এঁদের হাত ধরেই আমাদের জীবনে, আমাদের ক্লাসরুমে, ইউ জি আর্টস বিল্ডিং-এর ‘লবি’-তে (এটি আসলে একধাপ সিঁড়ি মাত্র) আমাদের আড্ডায় জমে ওঠা তুমুল তর্কে-বিতর্কে নারীবাদের প্রবেশ। এঁদের পরিশ্রমের ফসল ফলেছিল ১৯৮৮ সালে যাদবপুরে স্কুল অফ উইমেন্স স্টাডিজের পত্তনে। একটু আগে যেমন লিখলাম, এই স্কুলের প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পদক্ষেপেই ছিল ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ, গঠনমূলক ভূমিকা।
এই সময়েরই আর একটি সমগোত্রীয় ঘটনার প্রসঙ্গ এখানে সংক্ষেপে তোলা দরকার। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের পত্তনের মূলে সরাসরিভাবে রয়েছে ক্যাম্পাসে আশির দশকের জোরালো ফিল্ম মুভমেন্ট। এই মুভমেন্টের অগ্রভাগে ছিলেন ছাত্ররা, বিভিন্ন দূতাবাস, কনসুলেট ও সোসাইটির থেকে তাঁরা ফিল্ম জোগাড় করে আনতেন। এঁদের জন্যই ক্যাম্পাসের লক্ষ্মণরেখার বাইরে এক পা-ও না ফেলে আমরা ঘরে বসেই দেশ-বিদেশের অনবদ্য সব সিনেমা দেখতে পেয়েছি। এই চর্চায় পূর্ণমাত্রায় উৎসাহ জুগিয়েছেন আমাদের শিক্ষকেরাই, ট্যাক্সিভাড়া বা টিফিনের হাতখরচের রূপেই মাঝে মাঝে আমাদের কপালে জুটেছে সেই ‘উৎসাহ’।
আমাকে যেটা ভাবায়: রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নানা বিষয়ে ছাত্ররা কী ভাবছে— সে বিষয়ে শিক্ষকদের এবং কলেজ প্রশাসনের মনোযোগ দিয়ে শোনার এবং প্রায়ই ছাত্রদের দাবি-দাওয়া বা আন্দোলনে সমর্থন জানানোর এই রীতি। এর প্রভাব পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনে এবং পরিচালনায়, যার ফলে গোটা ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থার উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ এবং সমজাতীয়করণের যুগে দাঁড়িয়েও যাদবপুর একরকমের সক্রিয়তা বজায় রাখতে পেরেছে। ২০১৪ সালের হোক কলরব আন্দোলনের প্রতি শিক্ষকদের যে বিপুল সমর্থন, এবং বর্তমান অতিমারীর সময়ে ছাত্ররা আর শিক্ষকেরা যেভাবে হাতে হাত মিলিয়ে স্থানীয় (এবং অনেক সময়ে দূরবর্তী) গরিব মানুষের কাছে খাবার, জামাকাপড়, স্যানিটাইজার ইত্যাদি পৌঁছে দিয়েছেন, তাতে এই রীতিরই প্রমাণ পাওয়া যায়।
এ বছর বাংলাদেশের পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী, যে দেশটির জন্ম একেবারে সরাসরিভাবেই ছাত্র আন্দোলনের হাত ধরে (এ দাবির সপক্ষে যুক্তি রাখা যায়)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিক্ষোভে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা-শহিদদের জন্ম, তা থেকে শুরু করে পরবর্তী বহু ছাত্র আন্দোলন, যা শিক্ষার্থীদের মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে তুলেছে— একটি দেশের ভবিষ্যতের গঠনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে কী বিরাট অবদান রেখে গেছেন, সেসব কথা অগ্রাহ্য করে আমাদের পূর্বদিকের প্রতিবেশীর ইতিহাসকে বোঝা অসম্ভব। পূর্ব পাকিস্তানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক শক্তি ছিলেন এই ছাত্র আন্দোলনকারীরা, এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁদের ভাইবোনেদের থেকেও তাঁরা অনেক সমর্থন পেয়েছেন, বিশেষ করে ষাটের দশকে। দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা তাঁদের ভূমিকার যোগ্য সম্মান পেলেও, বাকিদের কথা খুব একটা বলা হয় না। ভবিষ্যতের কোনও ইতিহাসবিদ হয়তো এ বিষয়ে আরো বিশদে গবেষণা করবেন।
বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের ছাত্রদের প্রসঙ্গ তুলছি আমার নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে— ভারতবর্ষের অন্যতম সবচেয়ে সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত ক্যাম্পাসে ছাত্র হিসেবে, এবং পরে শিক্ষক হিসেবে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনেই ছাত্র আন্দোলনের তিনটি বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই। প্রথমত, ক্ষমতার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ছাত্ররা যেভাবে সত্যের কথা বলতে পারে, সেভাবে অনেকেই পারে না, বা পারলেও চায় না। যে কোনও আন্দোলনে যে আবেগ এবং উদ্দীপনা তাদের হাত ধরে আসে, তা দেখে, যত বয়স বাড়ে (এবং, তর্কসাপেক্ষভাবে, যত বেশি প্রাতিষ্ঠানিক হতে হয়) তত হিংসেই হয়। দ্বিতীয়ত, আপাতদৃষ্টিতে ছাত্রদের মধ্যে বিচক্ষণতার অভাব আছে মনে হলেও, অনেক সময়ে শিক্ষকদের বা গুরুজনদের আগেই তারা আসন্ন রাজনৈতিক বা সামাজিক সঙ্কটের আভাস পেয়ে যায়। ২০১৬ সালের ‘আজাদি’ আন্দোলন, বা ২০১৯-২০ সালে সিএএ-এনআরসি-এনপিআর (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-জাতীয় জনসংখ্যা তালিকা-জাতীয় নাগরিক তালিকা) বিরোধী আন্দোলন দেখলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, ছাত্র আন্দোলনের হাত ধরে প্রকৃত, মৌলিক রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব, বাংলাদেশের উদাহরণটি যার প্রমাণ।
এ ধরনের ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে? বা কী হওয়া উচিত? আমার অভিজ্ঞতা বলে, প্রথমেই রাষ্ট্র একটু নস্যাৎ করে দিতে চায় (একদল ছোটো বাচ্চা কীসব কথাবার্তা বলছে, বাস্তবে ওদের কথার কোনও গুরুত্ব নেই), তারপরে অস্বীকার করে (ছাত্ররা যা নিয়ে বিক্ষোভ করছে তার কোনও ন্যয্যতা নেই), তারপরে ছাত্রদের বলা হয় বাধ্য হতে, এসব না করে মন দিয়ে লেখাপড়া করতে (সরকারি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় হলে এক্ষেত্রে অকৃতজ্ঞ ঝামেলাবাজ ছাত্রদের উপর জনসাধারণের করের টাকা নষ্ট হওয়ার কাঁদুনি গাওয়া হয়)। এসব উপায় যদি কাজ না দেয়, তখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সাহায্য নেওয়া হয় (এই সন্ত্রাসকে সাধারণত প্রশ্রয় দেয় এবং সাহায্য করে শাসক রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুগত গোষ্ঠীরা)। তবে এর মধ্যে কোনও উপায়েই শেষরক্ষা হয় না। ১৯৬৮ সালের ইউরোপই হোক, অথবা পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের বাংলাদেশ, ছাত্রদের অসন্তোষকে রাষ্ট্রীয় গা-জোয়ারি দিয়ে চেপে দেবার চেষ্টায় প্রত্যেকবারই হিতে-বিপরীত হয়েছে। যাকে চেপে দেওয়া হয়, সে অনিবার্যভাবেই লুকোনো ক্ষতর মতো বিষিয়ে উঠতে উঠতে এক সময়ে আরও জোরালো রূপে ফিরে আসে। কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রকোপে এখন ক্যাম্পাসগুলো ফাঁকা হয়ে গেছে, ছাত্ররা যেসব বিষয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল, তার মধ্যে অনেক কিছুই এ কারণে একটু নজরের আড়ালে চলে গিয়েছে। তবে ক্যাম্পাস যখন আবার খুলবে, এবং ছাত্ররা যে জিনিসটি সবচেয়ে ভাল পারে— অর্থাৎ নিজেদের এবং অন্যদের জন্যে আরও সুন্দর, আরও উচিত একটা পৃথিবীর জন্য লড়তে— সে কাজে যখন আবার লিপ্ত হবে, তখন যে শাসক তাদের দাবিগুলো শুনেও শুনবে না, বা আরও অনুচিতভাবে গায়ের জোরে তাদের কণ্ঠরোধ করতে চেষ্টা করবে, সে নিজেরই বিরাট বিপদ ডেকে আনবে। আর তখন শুধু ছাত্ররা নয়, আমরা, যারা খাতায়-কলমে একটি স্বাধীন, গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক, আমাদের সবাইকেই তার মাশুল দিতে হবে।