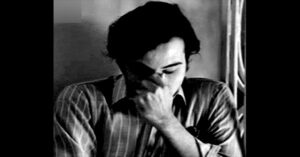যৌন পরিচয়ের বহুমাত্রিকতায় ‘অ্যাসেক্সুয়াল স্পেকট্রাম’ একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, যেখানে গ্রে-সেক্সুয়াল, ডেমিসেক্সুয়াল, ফ্রেসেক্সুয়াল, লিথসেক্সুয়াল, কোয়াইসেক্সুয়াল বা অটোকোরিসসেক্সুয়াল-এর মতো নানা শব্দ ব্যবহার করা হয়। খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতেই পারে, অ্যাসেক্সুয়াল স্পেকট্রাম কী? অ্যাসেক্সুয়াল স্পেকট্রাম আসলে একটি বর্ণালী বা ধারাবাহিকতা, যেখানে যৌন আকর্ষণ ‘আছে’ বা ‘নেই’— এই দুই ভাগে না দেখে, মাঝের সমস্ত ধূসর অভিজ্ঞতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই স্পেকট্রামের একপ্রান্তে থাকেন সম্পূর্ণ অ্যাসেক্সুয়াল মানুষ, যাঁরা কখনও যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন না। অন্য প্রান্তে থাকেন অ্যালোসেক্সুয়াল মানুষ, যাঁরা স্বাভাবিক বা ঘন ঘন যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন। মাঝের জায়গাটিই হল স্পেকট্রামের ধূসর অংশ, যেখানে আছে গ্রে-সেক্সুয়াল, ডেমিসেক্সুয়াল, ফ্রেসেক্সুয়াল, লিথসেক্সুয়াল প্রভৃতি পরিচয়।
যৌন আকর্ষণ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়, ভিন্নভাবে মানুষের জীবনে উপস্থিত হতে পারে। তাই অ্যাসেক্সুয়াল স্পেকট্রাম হল যৌন পরিচয়ের সেই ভাষা, যা প্রতিটি সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতাকে বৈধতা প্রদান করে। এই শব্দগুলো মূলত বোঝায়, যৌন আকর্ষণ সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করে না। কারও কাছে তা বিরল, কারও কাছে আবেগের সঙ্গে জড়িত, কারও কাছে প্রথমে উপস্থিত হলেও পরে মিলিয়ে যায়, আবার কারও কাছে কেবল কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে, প্রতিটি শব্দ আসলে একটি নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার নাম। গ্রে-সেক্সুয়ালিটি এমন এক যৌন-পরিচয়, যা সম্পূর্ণ যৌন আকর্ষণহীন (অযৌন বা asexual) এবং পূর্ণ যৌন আকর্ষণপ্রবণ (allosexual) পরিচয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে পড়ে। গ্রে-সেক্সুয়াল ব্যক্তিরা সাধারণত খুব কম ক্ষেত্রে, বিশেষ পরিস্থিতিতে বা দুর্লবভাবে যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন। অর্থাৎ, জীবনে কয়েকবার আকর্ষণ অনুভূত হওয়া, আবার কারও কাছে এর অর্থ হতে পারে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থায় আকর্ষণ জাগা। গ্রে-সেক্সুয়ালিটি কোনও স্থির বা দ্ব্যর্থহীন পরিচয় নয়, বরং যৌনতার বিস্তৃত বর্ণালীর একটি অন্তর্বর্তী ধাপ, যেখানে মানুষজন নিজেদের অভিজ্ঞতাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পান।
আরও পড়ুন: ট্রেনিং দিলে কি ডগ শো-র যোগ্য হয়ে উঠতে পারে পথকুকুররাও?
লিখছেন পিনাকী ভট্টাচার্য…
‘গ্রে-সেক্সুয়ালিটি’ শব্দটির ব্যবহার প্রথম শোনা যায় ২০০৬ সালের দিকে, অযৌনতা বিষয়ক বৃহত্তম অনলাইন কমিউনিটি AVEN (Asexual Visibility and Education Network)-এ। সেখানে অনেক সদস্যই বলতে শুরু করেছিলেন যে তাঁরা পুরোপুরি অযৌন নন, আবার স্পষ্টভাবে যৌন আকর্ষণ অনুভবকারীর মধ্যেও পড়েন না। তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল মাঝামাঝি, খুব সীমিত, বিরল বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতেই আকর্ষণ অনুভূত হয়। এই অনিশ্চিত বা ধূসর অঞ্চলের অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করার জন্যই কমিউনিটির ভেতরে ‘গ্রে’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ধীরে ধীরে এই শব্দবন্ধ ছড়িয়ে পড়ে ব্লগ, গবেষণা ও সামাজিক আলোচনায় এবং যৌনতার স্পেকট্রামে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় হিসেবে জায়গা করে নেয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, বেশিরভাগ মানুষ কৈশোর বা যৌবনের শুরুতেই নিজের যৌন পরিচয় স্পষ্টভাবে বুঝতে শুরু করে। কিন্তু গ্রে-সেক্সুয়ালদের ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি হতে দেরি হয়, কারণ তাঁদের যৌন আকর্ষণ খুবই সীমিত, অনিশ্চিত বা নির্দিষ্ট পরিবেশ ও আবেগঘন পরিস্থিতিতেই প্রকাশ পায়, যা সহজে ধরতে পারা যায় না। গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রে-সেক্সুয়াল মানুষ সাধারণ যৌনপ্রবণদের তুলনায় আকর্ষণের তাগিদ অনেক কম অনুভব করেন। অনেকের ক্ষেত্রেই আবার সেই আকর্ষণ দেখা দেয় কেবলমাত্র বিশেষ আবেগী সংযোগ বা বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে। সামাজিকভাবে প্রচলিত যৌন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা মেলে না। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা যায়, দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পরিচয় নির্মাণ। অর্থাৎ, নিজের অভিজ্ঞতা আর সমাজের প্রত্যাশার মধ্যে অমিল তৈরি হলে মানুষ বিকল্প কোনও পরিচয়ের সন্ধান করে। সেই খোঁজ থেকেই ‘গ্রে-সেক্সুয়ালিটি’ শব্দবন্ধ তাঁদের কাছে আত্মপরিচয় ও স্বস্তির একটি সুনির্দিষ্ট আশ্রয় হয়ে ওঠে।
গ্রে-সেক্সুয়ালিটি কোনও রোগ নয়। এটি মানব যৌনতার বহুমুখী রূপেরই একটি স্বাভাবিক অংশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ১৯৯০ সালে সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে বাদ দেয় এবং স্পষ্ট জানায় যে, যৌন আকর্ষণের ভিন্নতা কখনও রোগ নয়। একইভাবে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (APA) জানিয়েছে যে, অযৌনতা, গ্রে-সেক্সুয়ালিটি কিংবা অন্যান্য যৌন পরিচয় কোনও মানসিক ব্যাধি নয়, বরং মানুষের স্বাভাবিক যৌন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায়ও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, গ্রে-সেক্সুয়ালিটি কোনও চিকিৎসাজনিত সমস্যা নয়। এটি মূলত এমন একধরনের মানসিক অভিজ্ঞতা, যেখানে যৌন আকর্ষণ খুব সীমিত, বিশেষ পরিস্থিতিতে বা দুর্লভভাবে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, Bogaert (2015)–এর গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, যৌন আকর্ষণ ও তাগিদের মধ্যে বৈচিত্র্যই মানব-যৌনতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাই এই ধূসর অঞ্চলকে রোগ না ভেবে স্বাভাবিক বৈচিত্র্য হিসেবেই দেখা উচিত। গ্রে-সেক্সুয়ালিটি চিকিৎসার বিষয় নয়, বরং পরিচয়ের প্রশ্ন। যেখানে একজন মানুষ নিজের ভিন্ন যৌন অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে, নাম দেয় এবং সেটিকে নিজের অস্তিত্বের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে।়
সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, আধুনিক প্রজন্মের তরুণ–তরুণীরা আগের তুলনায় যৌনতা নিয়ে অনেক বেশি উদাসীন বা নিরাসক্ত। যুক্তরাষ্ট্রে ১৮–২৪ বছরের তরুণদের এক বড় অংশ জানিয়েছে, তাঁদের যৌন সম্পর্কের হার গত দুই দশকে নাটকীয়ভাবে কমেছে। একইভাবে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল (২০২১) জানিয়েছে, তরুণরা আজকাল আগের তুলনায় কম যৌন সম্পর্ক করছে এবং এর পিছনে সামাজিক মাধ্যমের অতি-নির্ভরতা, মানসিক চাপ, আর্থিক অনিশ্চয়তা ও সম্পর্কের পরিবর্তিত ধরণ উল্লেখযোগ্য কারণ। জাপানের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ৩০ বছরের কম বয়সি অবিবাহিতদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশের কোনও যৌন অভিজ্ঞতা নেই, অনেকেই নিজেদের প্রকাশ্যে যৌনতা নিয়ে উদাসীন বলে পরিচয় দিচ্ছেন। ভারতেও সাম্প্রতিক সমীক্ষায় একই প্রবণতা দেখা গেছে, যেখানে ১৮–৩২ বছর বয়সি শহুরে যুবকদের প্রায় ৩০ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা যৌন সম্পর্কে অল্প আগ্রহী বা সম্পূর্ণ অনাগ্রহী। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, এর সঙ্গে জড়িত একাধিক বিষয়। ডিজিটাল বিনোদনের প্রভাব, কেরিয়ার ও প্রতিযোগিতার মানসিক চাপ, যৌনরোগ ও অনিচ্ছুক গর্ভধারণের ভয় এবং পরিচয়ের বৈচিত্র্যের প্রতি বাড়তি স্বীকৃতি। এই প্রেক্ষাপটে গ্রে-সেক্সুয়ালিটি ধারণাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ আধুনিক তরুণদের মধ্যে অনেকেই টের পাচ্ছেন, তাঁদের যৌন আকর্ষণ আগের প্রজন্মের মতো ঘন-ঘন বা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বরং তা দুর্লভ, প্রেক্ষাপটনির্ভর বা বিশেষ আবেগঘন সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
ফলে গ্রে-সেক্সুয়ালিটি শুধু যৌনতার ধূসর অঞ্চল নয় বরং সমসাময়িক সমাজে যৌন পরিচয়ের নতুন বাস্তবতাকেও সামনে নিয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী গবেষণায় দেখা গেছে, যৌন পরিচয়ের বহুমাত্রিক মানচিত্রে গ্রে-সেক্সুয়ালিটি ধীরে ধীরে স্বীকৃতি পাচ্ছে, যদিও এখনও এটিকে আলাদা পরিসংখ্যান হিসেবে ধরা কঠিন। ২০২১ সালের ইপসস গ্লোবাল সার্ভে দেখা যায়, বিশ্বের প্রায় ১% মানুষ নিজেদের অযৌন বলে চিহ্নিত করেছেন। এই অযৌন পরিচয়ের ভেতরেই গ্রে-সেক্সুয়ালদের অবস্থান। Ace Community Survey (২০১৯) জানায়, অ্যাসপেকট্রামের মধ্যে প্রায় ১০.৯% মানুষ নিজেদের গ্রে-সেক্সুয়াল বা ডেমিসেক্সুয়াল হিসেবে শনাক্ত করেছেন। একইভাবে ২০২৩ সালের এক আন্তর্জাতিক গবেষণায় এই হার বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৫.৬%। অর্থাৎ, অযৌন সম্প্রদায়ের প্রতি দশ জনের অন্তত একজন ধূসর অঞ্চলের অভিজ্ঞতা বহন করেন। ভারতের প্রেক্ষাপটেও অনুরূপ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ২০২২ সালের ইপসস গ্লোবাল সার্ভে অনুযায়ী, দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর প্রায় ২% নিজেদের অযৌন হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। যদিও এর ভেতরে গ্রে-সেক্সুয়ালদের আলাদা সংখ্যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবুও আন্তর্জাতিক ধারা অনুযায়ী ধরে নেওয়া যায়, ভারতের অযৌন সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রে-সেক্সুয়াল পরিচয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।
ভারতেও সাম্প্রতিক সমীক্ষায় একই প্রবণতা দেখা গেছে, যেখানে ১৮–৩২ বছর বয়সি শহুরে যুবকদের প্রায় ৩০ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা যৌন সম্পর্কে অল্প আগ্রহী বা সম্পূর্ণ অনাগ্রহী। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, এর সঙ্গে জড়িত একাধিক বিষয়। ডিজিটাল বিনোদনের প্রভাব, কেরিয়ার ও প্রতিযোগিতার মানসিক চাপ, যৌনরোগ ও অনিচ্ছুক গর্ভধারণের ভয় এবং পরিচয়ের বৈচিত্র্যের প্রতি বাড়তি স্বীকৃতি।
ডেটিং প্রোফাইল বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই নিজেদের পরিচয়ের জায়গায় ‘গ্রে সেক্সুয়াল’ শব্দটি ব্যবহার করেন। এর উদ্দেশ্য শুধু তথ্য দেওয়া নয়, বরং নিজের অভিজ্ঞতার সীমানা আগেভাগেই স্পষ্ট করে দেওয়া। কারণ গ্রে-সেক্সুয়াল ব্যক্তিরা সচরাচর যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন না, আবার একেবারেই অযৌনও নন। এই অবস্থান যদি প্রোফাইলে উল্লেখ থাকে, তবে ভুল বোঝাবুঝি কমে, সম্পর্কের প্রত্যাশা স্পষ্ট হয়। একই সঙ্গে এটি আত্মপরিচয়েরও অংশ যেখানে মানুষ নিজের অবস্থানকে সমাজে দৃশ্যমান করে, আর একই ধরনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষদের সঙ্গে সংযোগ খুঁজে পেতে পারেন। অনেকে এটিকে আত্মমর্যাদার প্রকাশও মনে করেন। ফলে, প্রোফাইলে গ্রে-সেক্সুয়াল লেখা হয়ে ওঠে একাধারে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, পরিচয়ের ঘোষণা এবং সমাজে স্বীকৃতি দাবি করার একটি সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আধুনিক প্রজন্ম এই শব্দগুলো ব্যবহার করে মূলত দু’টি কারণে। প্রথমত, নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্য যাতে সমাজের চাপিয়ে দেওয়া স্বাভাবিক সংজ্ঞার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে দ্বন্দ্বে না পড়তে হয়। দ্বিতীয়ত, পরিচয় ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে একই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষদের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার জন্য। ফলে, এসব শব্দ ব্যবহার করা হয়ে দাঁড়ায় আত্মপরিচয়ের ঘোষণা, সামাজিক স্বীকৃতি দাবি এবং মানসিক নিরাপত্তা তৈরির একটি উপায়। এক অর্থে এগুলো আধুনিক প্রজন্মের কাছে কেবল যৌন পরিচয়ের শব্দ নয়, বরং আত্মপ্রকাশ ও স্বাধীনতার ভাষা। আগের প্রজন্মের মানুষের মধ্যেও অ্যাসেক্সুয়াল বা গ্রে-সেক্সুয়াল অভিজ্ঞতা ছিল, তবে তখন এ-বিষয়ে কোনও ভাষা বা স্বীকৃতি ছিল না। ফলে তাঁরা নিজেদের অনুভূতিকে প্রায়ই চাপা রাখতেন বা ভুল ব্যাখ্যা করতেন। অনেকেই ভাবতেন যৌন আকর্ষণ না অনুভব করা মানে শারীরিক সমস্যা বা মানসিক ব্যাধি। সমাজ ও পরিবারের চাপে অধিকাংশ মানুষ বিয়ে বা সম্পর্কের মধ্যে ঢুকতেন, যদিও ভেতরে আকর্ষণ কম ছিল যার ফলশ্রুতিতে সম্পর্কের ভেতরে দ্বন্দ্ব, অস্বস্তি বা অসন্তোষ তৈরি হত। আবার কেউ কেউ বিয়ে না করে একা থেকে গেছেন, কেউ জীবনের অন্য দিকগুলো যেমন কাজ, শিল্প বা আধ্যাত্মিকতায় নিজেকে নিমগ্ন রেখেছেন। মূল পার্থক্য হল, সেই সময়ে এই অভিজ্ঞতার কোনও নাম ছিল না, অথচ আধুনিক প্রজন্ম নতুন শব্দ ও ধারণার মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার পথ খুঁজে পেয়েছে। ফলে আজ বিষয়টি আর লুকনো নয়, বরং আত্মপরিচয় ও বৈচিত্র্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে।
(তথ্যসূত্র এবং কৃতজ্ঞতা : সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ডা: মানি দাস)