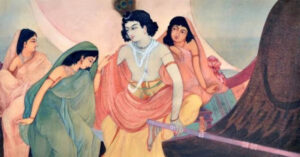উপদ্রবের উল্লাস
একটা সিনেমার প্রিমিয়ার হবে। তাই সিনেমা হল-এর লাগোয়া ফুটপাথটা সকাল থেকে একদম আটকে ছোট স্টেজ তৈরি করা হয়েছে, তার ওপর লাল কার্পেট, সেখানে রাত আটটা-সাড়ে আটটায় নায়ক, নায়িকা, পরিচালক, সংগীত-পরিচালক দাঁড়িয়ে কথা বলবেন, হাত নাড়বেন। উল্টোদিকের ফুটপাথেও গাদা জিনিস ডাঁই, ক্যামেরা-ট্যামেরা সেখানেই বসবে। স্টেজের পিছনে একটা বিরাট স্ক্রিন টাঙানো, ছবিটার ট্রেলার টানা চলছে। আর বিশাল বিশাল কয়েকটা স্পিকারে সিনেমার তিনটে গান বাজছে। এই চলাচলি শুরু হয়েছে দুপুর দুটো থেকে, আর একনাগাড়ে, একটুও না-থেমে, আছড়াচ্ছে রাত সাড়ে আটটা-নটা অবধি গাঁক-গাঁক ডেসিবেলে, যতক্ষণ না নক্ষত্ররা এসে ওই স্টেজে দাঁড়াচ্ছেন। তার পরেও সাড়ে দশটা অবধি চলবে, কিন্তু শেষ দেড় ঘণ্টা সামান্য কম ভলিউমে। তার মানে, টানা সাত-আট ঘণ্টা ধরে তিনটে গান লুপে বাজছে এবং একটা ট্রেলার লুপে চলছে।
আশপাশের বাড়ির লোকরা শুতে-বসতে পারছে না, পড়াশোনার তো প্রশ্নই নেই, গল্প করাও প্রায় অসম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা, মেজাজ ঠিক রাখা বিষম ব্যাপার, কারণ কানের ডগায় একই জিনিস তিন-চারবার পুনরাবৃত্ত হলেই বিরক্তি জন্মাতে থাকে, এখানে একশো-দুশো-আড়াইশোবার। আচ্ছা, এর উদ্দেশ্য কী? নিশ্চয়ই সিনেমার প্রচার। যে সিনেমার তিনটে গান দুপুর থেকে রাত বিরতিহীন শুনতে শুনতে আমি উন্মাদ হয়ে গেলাম, সে-সিনেমার প্রতি আমার কোনও প্রসন্নতা জন্মাতে পারে কি? ওই গান, যত ভাল গান হোক, আর কখনও শুনলে আমার মনে তীব্র বিবমিষা ও আতঙ্ক ছাড়া কিছু জন্মাবে কি? ওই সিনেমা হল-এর সামনে দিয়ে রোজ যাওয়ার সময় একটা তীব্র বিরাগ ও অনীহা আমাকে আক্রমণ করবে না কি?
প্রিমিয়ারের কত্তাদের যুক্তি সম্ভবত এই: আশপাশের বাড়ির লোকের কথা তো আমি ভাবব না, আমার টার্গেট রাস্তা দিয়ে চলা জনতা এবং বাস, অটো, গাড়ি, রিকশার স্রোতের ভেতর থাকা পাবলিক, যারা যেতে যেতে একঝলক দেখে ও শুনে প্রচুর মুগ্ধতা ও কৌতূহল নিয়ে বাড়ি ফিরবে। এবং সেই কারণেই ফুটপাথ আটকে ঘটা করব, যাতে কিছু লোকের প্রকাণ্ড অসুবিধে হলেও, বেশিরভাগ লোক হুল্লোড়টা দেখে খুশি হয়, তাদের মুখে সংক্রামক হাসি ফুটে ওঠে। এবং সত্যিই, তারকাদের প্রত্যাশায় রাস্তায় এমন ভিড় জমে যায় যে, বিকেল থেকেই রাস্তাটা পুরো অচল হয়ে পড়ে। তার মানে তত্ত্বটা হল, কয়েকটা লোককে আমি অনায়াসে ডিস্টার্ব করব, উত্ত্যক্ত করার ঝুঁকি নেব, কারণ তাতে অনেক বেশি সংখ্যক লোককে আকর্ষণ করার সম্ভাবনা বাড়ছে।
অতি অবশ্যই এর সঙ্গে আছে মস্তানির আনন্দ। আমাদের দেশে ধর্ম যে আনন্দে অহরহ স্নান করে। সে যখন-তখন বলতে পারে, আমি অষ্টপ্রহর টানা কোরাসে গান গাইব, এবং তা মাইক দিয়ে তোমার কানে গরগরিয়ে সেঁধিয়ে ছাড়ব, কিংবা খুব জোরে দিনে বহুবার মাইকে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার করব, অথবা রাতবিরেতে স্পিকারে গান চালিয়ে প্রবল নাচব। মিছিল করে রাস্তা আটকে হাঁটব, বা রাস্তা আটকে উপাসনা করব। অন্য কারও মৌলিক অধিকারের তোয়াক্কা না করেই আমি আমার ইচ্ছে ও খেয়াল অনুযায়ী চলব। এই স্বৈরাচারের রাজা তো রাজনীতি। রাস্তা আটকে সভা করব, বা অমুক বিষয়ে প্রতিবাদের খাতিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা আটকে রাখব, এবং যখন খুশি মাইকে জোরসে বক্তৃতা শোনাব। বিনোদনই বা এদের পথ ধরবে না কেন? এগুলোর মূলে আছে একটাই উদ্ধত বার্তা: যেহেতু আমার লোকবল বা অর্থবল বা বাহুবল বা সবকটাই আছে, সেহেতু আমি অন্যায় করব। কারণ তুমি তা নিয়ে ত্যান্ডাইম্যান্ডাই করতে এলে আমি তোমায় মুহূর্তে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দিতে পারি। এবং সেজন্যই অভিজাত ক্লাবে ধুমাধার গানের ফাংশন চলবে রাত বারোটা অবধি, বস্তিতেও চলবে, কারণ ক্লাবের নামে বা বস্তির লোকের নামে পুলিশে নালিশ করার ক্ষমতা গৃহস্থের নেই। সে সংঘবদ্ধ নয়, সে আধলা ইটের ঘায়ে অফিস যেতে পারবে না। তাই সিনেমা হল-এর মালিক ফুটপাথ আটকানোর ডাঁট প্রতি শুক্রবারেই (বা শনি, বা রবি, এখন প্রিমিয়ার যে-কোনওদিনই হয়) সংগ্রহ করতে পারবেন, কারণ রাজনীতির দাদাদের সঙ্গে তাঁর সাঁট আছে, পাড়ার রংবাজদের সঙ্গেও। রাস্তা না আটকালেও হত, তারকারা হল-এর ভেতরে স্ক্রিনের সামনে সমবেত হয়ে কথা বলতে পারতেন, গান না চালালেও হত, চালালেও তার শব্দের মাত্রা অনেক কম রাখা যেত, কিন্তু অন্যের পাঁজরার (এবং আইনের দাঁড়িপাল্লার) ওপর দিয়ে রোলার চালাবার মধ্যে যে ‘বেশ করব’ আত্মতৃপ্তিটা আছে, সেটা পাওয়া যেত না।
এর সঙ্গে আছে মস্তানির আনন্দ। আমাদের দেশে ধর্ম যে আনন্দে অহরহ স্নান করে। সে যখন-তখন বলতে পারে, আমি অষ্টপ্রহর টানা কোরাসে গান গাইব, এবং তা মাইক দিয়ে তোমার কানে গরগরিয়ে সেঁধিয়ে ছাড়ব, কিংবা খুব জোরে দিনে বহুবার মাইকে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার করব, অথবা রাতবিরেতে স্পিকারে গান চালিয়ে প্রবল নাচব। মিছিল করে রাস্তা আটকে হাঁটব, বা রাস্তা আটকে উপাসনা করব। অন্য কারও মৌলিক অধিকারের তোয়াক্কা না করেই আমি আমার ইচ্ছে ও খেয়াল অনুযায়ী চলব। এই স্বৈরাচারের রাজা তো রাজনীতি।
তবে পুরোটাকে এত কর্কশভাবে দেখারও কিছু নেই। আমাদের দেশ, রাজ্য, জাতি যে এতটা যাচ্ছেতাই, তার বড় কারণ এই নয় যে, লোকগুলো সব শয়তান। বড় কারণ হল, লোকগুলো ক্যালাস। মানে, মূর্খ ও নির্বিকার। তারা জানেই না, এই কাজগুলো আদৌ অন্যায়। একটা বাচ্চা যখন রোল খাওয়ার পর কাগজ-টুকরোগুলো হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় (ইশকুলে পড়েছে, বাতিল জিনিস ডাস্টবিনে ফেলতে হয়), বাবা-মা তাকে বলে, কী হল, ফেল! সে বলে, কোথায়? ‘কোথায় মানে? এখানে। যেখানে ইচ্ছে!’ কারণ মা-বাবা জানে, গোটা শহরটাকেই তো ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তার কারণ এ-শহরের রাস্তায় কোনও ডাস্টবিন কখনও ছিল না, আর এক-আধবার পুরসভা থেকে সে-ব্যবস্থা হলেও, ডাস্টবিনে বর্জ্য ফেলার অভ্যাস গড়ার সংস্কৃতি ছিল না। তাই সন্তানও পরেরবার থেকে ক্যাবলা চিহ্নিত না হওয়ার তাগিদে, তাড়াতাড়ি রোলের কাগজ রাস্তায় ফ্যালে, পরে বড়লোক হয়ে মার্সিডিজের কাচ নামিয়ে কাগজটা ছুড়ে দেয়। যে লোকটা রাস্তায় চলতে চলতে সারাক্ষণ পিচিক থুতু ফ্যালে, সে জানেই না এটা ভুল, বা অনুচিত, বা আদৌ অশোভন। তার কাছে এটা শ্বাস নেওয়ার মতোই স্বাভাবিক ব্যাপার। সেভাবেই, পাশের লোকটার অসুবিধে হলে যে আমায় নিজেকেই সরে বসতে হবে, লাইনে যে আমি গুঁতিয়ে ঢুকে যেতে পারি না, সিনেমা হল-এ প্রাণপণ চেঁচিয়ে ফোনে কথা বলতে পারি না, তিনতলার বারান্দা থেকে জঞ্জাল ছুড়ে দিতে পারি না— এই প্রাথমিক নিষেধগুলো সম্পর্কে আমাদের এককণাও ধারণা নেই। কেউ ধরিয়ে দিলে আমরা হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকি, যেন প্রলাপ বকছে। আমরা সারল্যের চোটেই মায়ের শ্রাদ্ধের প্যান্ডেল রাস্তা জুড়ে করি বা ‘বসে আঁকো’ প্রতিযোগিতা হচ্ছে বলে চেয়ারের ব্যারিকেড গড়ে গাড়ি ঘুরিয়ে দিই। আসলে, ‘আমার জন্য অন্য কারও অসুবিধে হচ্ছে না তো?’ সভ্যতার এই মূল বাক্যটি আমাদের ভূখণ্ডে প্রখর অচেনা। তাই নিয়ম মানাটাকে একটা শৌখিন ও অবান্তর কাণ্ড হিসেবে দেখা হয়। আগে যখন ট্র্যাফিক আইন ভাঙার জন্য পুলিশ (নির্দিষ্ট ট্র্যাফিক সপ্তাহে) জরিমানা করত, কিংবা বিনা টিকিটে রেলভ্রমণের জন্য লোককে ধরত, তখন পুলিশের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ আর বিরক্তিটা ছিল নিখাদ বিস্ময়-রঞ্জিত, যেন কেউ গ্রিক ভাষা না-জানার জন্য গ্রেপ্তার করছে। বা বলছে, হাঁচলে ট্যাক্স নেব।
আর যখন করাকরির মাত্রাটা বৃহৎ, যেমন ধর্মীয় উৎসব বা রাজনৈতিক সভা কিংবা বিনোদনের আসর, তখন তো আমার লকলকে লাইসেন্স জন্মাচ্ছে তোমার অসুবিধে ঘটাবার, কারণ মহৎ উদ্দেশ্যে খুচরো ঝঞ্ঝাট সয়ে নেওয়া তো তোমার দায়িত্ব! তার চেয়ে বড় কথা, মানুষ পুজো করছে বা বিপ্লব ঘটাচ্ছে, এতে ঝামেলার প্রসঙ্গটাই বা আসছে কীভাবে? বিনোদনের দাপটে নিরানন্দ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে কোত্থেকে? ছবির প্রিমিয়ারের বন্দোবস্তকারীরা হয়তো ভাবছেন, তাঁরা নিখরচায় দুর্দান্ত গান শুনিয়ে পাড়ার বেধড়ক মনোরঞ্জন করছেন এবং সেই আচমকা সামাজিক উপকারের জন্য প্রতিবেশীদের আকণ্ঠ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত (যেমন ধর্মবাজরা আত্মপ্রচারের জন্য নয়, অন্য লোককে পবিত্র করার জন্যেই গাঁতিয়ে ধর্ম-মন্ত্র হাঁকড়ান)। হয়তো হল-মালিকের চিত্রনাট্যে, পরের রবিবার প্রতিবেশী কত্তা বা গিন্নি বাড়িতে ওয়েব সিরিজ দেখতে দেখতে বলে উঠছেন, আজ এত ফাঁকা-ফাঁকা আর পানসে লাগছে কেন, গান কই, গান? প্রিমিয়ার নেই?