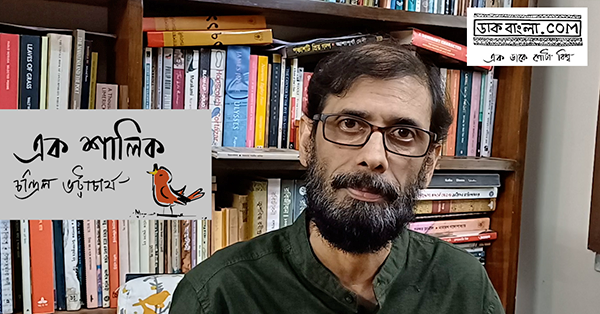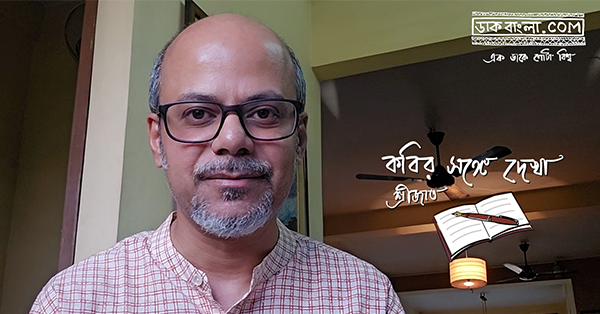‘দীপ জ্বেলে যাই’

 প্রহেলী ধর চৌধুরী (May 12, 2025)
প্রহেলী ধর চৌধুরী (May 12, 2025)যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছা, সময় কি ক্রমশ জটিল করে তুলছে মর্ত্যবাসীকে?’
বিদুর বললেন, ‘আমার মনে হয়, যত দিন যাচ্ছে ততই কোনও সার্বজনীন নীতি বা নির্দিষ্ট আদর্শে স্বস্তিবোধ করা কঠিন হয়ে উঠছে। অখণ্ড সত্যের ধারণা যেন চূর্ণ হয়ে পরিস্থিতি নির্ভর, আত্মবাদী বা আপেক্ষিক সত্যে পরিণত হচ্ছে মানবকল্যাণেরই স্বার্থে। হয়তো এই আধুনিকমনস্কতা। একেই হয়তো জটিল মনে হতে পারে।’
(মল্লার চট্টোপাধ্যায়, ‘মহাভারতের অন্তরালে’)
আকাশে বারুদের গন্ধ, বাতাসে সাইরেন আর বাতায়নে চেলপার্ক কালির আঁধার ঘনালে যুদ্ধ আসে। পর্দায় নয়, স্বপ্নে নয়, তর্কে নয়; মাটি কামড়ে, জান বাজি রেখে লড়ে যাওয়া সৈনিকের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বাজপাখি বলে যায়, মৃত্যু এসেছে। শত্রুপক্ষ উড়িয়ে দিয়েছে তিনশো মাইল দূরের ঘরবাড়ি, সন্তান, প্রিয়তমা-সহ গোটা মহল্লাটা। কিছু আর নেই… আসলেই নেই জেনে টলে পড়ার আগে জানু ভর করে বসা সৈনিকও বুলেটের বদলে দু-হাত ভরে নেয় মাটি। দেশের মাটি, প্রেয়সীর রক্তে ভেজা মাটি। তালগোল পাকিয়ে ছুড়ে দেয় বর্ডার তাক করে। মর। মরে যা তোরা সব।
ও-পারেও মরেছে তারই মতো কেউ। বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে তারও কেঁপেছিল বুক। সে জানত, তুমি ভুল ছিলে। তুমি জানতে, সে। যুদ্ধ মানেই জটিল তত্ত্ব। অখণ্ড সত্য বলে কিছু নেই। সাদা-কালোর বাইনারি পেরিয়ে গ্রে-জোন নেই কোত্থাও। কুরুক্ষেত্রে যে সত্যের বিচার হয়নি, আজও হবে না। তবু এখন, এই মুহূর্তে, শত অন্ধকারের মাঝে প্যারালাল পৃথিবীর রক্তাক্ত তোমরা দু’জনেই দাঁড়িয়ে আছ একই পঙক্তিতে। সুর নেই, প্রেম নেই, বিশ্বাস নেই। নিজের অস্তিত্বটা এখন ধরে রাখবে কোথায়, যদি না তোমার জীবনে এখনই দীপ জ্বেলে যেতে আসে কোনও নাইটিঙ্গেল। যদি না বলে, ‘আমি তো নার্স, এক-একজনের নিভে আসা জীবনে শুধু নতুন করে দীপ জ্বালানো আমার কাজ।’
আরও পড়ুন : সাদাত হাসান মান্টো যতটা ভারতের লেখক, ততটা পাকিস্তানেরও! লিখছেন রাজীব চৌধুরী…
আজ ১২ মে, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের জন্মদিন; ওয়ার্ল্ড নার্স ডে। আর আজ এই মুহূর্তে যখন বিশ্বের পঞ্চাশ থেকে একশো দশটি দেশে যুদ্ধ চলছে; যুদ্ধ চলছে ধর্মের নামে, বদলার নামে, জাতীয়তাবাদ কিংবা অঞ্চলের অধিকারের নামে, যতই আরও নব্যনতুন দেশ যুদ্ধে নামছে প্রতিদিন, ততই আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন নাইটিঙ্গেল। সেবিকা হিসেবে, মানুষ হিসেবে…

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল উনিশ শতকের কনস্ট্যান্টিনোপল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলছে। সেদিন যাঁর হাতে তৈরি স্বাস্থ্যবিধি সৈনিকদের মৃত্যুহার নামিয়ে এনেছিল বিয়াল্লিশ থেকে দুই শতাংশে, প্রতি আহতের সজ্জায় যাঁর বাতি হাতে নিভৃত রাতের প্রদক্ষিণ মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ পাঠাত অবিরাম, যিনি একাধারে পরিসংখ্যানবিদ ও আধুনিক নার্সিং-এর গুরু, স্বাস্থ্য-সংস্কারে পরিসংখ্যানের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের গুরুত্ব প্রথম তুলে ধরেছিলেন যিনি, সামরিক স্বাস্থ্যবিধি, জনস্বাস্থ্য সংস্কার কিংবা উন্নততর হাসপাতালের নকশা নির্মাণে যাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য; তিনি তো কোনও সাধারণ শিক্ষালয় গড়বেন না; গড়বেন বিশ্বের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ নার্সিং শিক্ষাকেন্দ্র— ‘ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ফ্যাকাল্টি অফ নার্সিং, মিড-ওয়াইফেরি অ্যান্ড প্যালিয়েটিভ কেয়ার’। বলবেন, ‘নিজের বোধশক্তিটাকে জাগাও, তবেই তো নতুন ভোরের আলো ফুটবে অন্তরে।’

‘দীপ জ্বেলে যাই’ চলচ্চিত্রে রাধা-র চরিত্রে সুচিত্রা সেন ঠিকই। সেবা যার ধর্ম, তাকে ধর্মনিরপেক্ষ হতেই হয়। হিন্দু-মুসলিম, অপরাধী-নিরপরাধী, সৎ-অসৎ, সংক্রমক রোগী থেকে মৃত্যুপথযাত্রী— সকলকেই সেবা দিতে হবে যার, সেবা ব্যতিরেকে অন্য কোনও ধর্ম নিয়ে চয়েস মেকিং-এর অবকাশ নেই তার। শ্রীমা-র মতো তাকেও বলতেই হয় যে, ‘আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।’ সেবাতেই তার জন্ম, সেবাধর্মেই তার মৃত্যু। ‘দীপ জ্বেলে যাই’ চলচ্চিত্রের রাধা সিস্টারের মতোই, মনে কিংবা শরীরে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে যেতে তাই তারা চোখ বুলিয়ে নেয় দেওয়ালে ঝোলানো সাদা-কালো বোর্ডে। যেখানে লেখা আছে সেই অমৃতবাণী— ‘তোমাদের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। বিনাশ নেই, ক্ষয় নেই, লয় নেই। তোমরা অমৃতের ছেলেমেয়ে। তোমাদের ভয় কি?’
চলচ্চিত্রের রাধা সিস্টাররা বাস্তবের শ্যারন অ্যান লেন, এলিসে ক্যাম্প, লিলি লিন্ড, ম্যারি রে, লরা রট্রে, একাতেরিনা তিয়েদোরো কিংবা ক্যাপ্টেন মারিয়া ইনে অরতিজ। যাঁরা সেবা দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন বিশ্বযুদ্ধে, ভিয়েতনাম ওয়ারে কিংবা টিবি রোগীর শুশ্রূষায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন লোকচক্ষুর আড়ালে। তাঁরা বাস্তবের সেই দেড় হাজার নার্স, যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। তাঁরা ৬ জুন, ১৯৪৪-এর সেই সেবিকার দল, যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ‘বিখ্যাত’ ‘অপারেশন নেপচুন’ বা কোড-নেম ‘ডি-ডে ল্যান্ডিং’-এর সময় ফিল্ড হাসপাতাল তৈরির জন্য সর্বাগ্রে পৌঁছে গিয়েছিলেন ফ্রান্সের নরম্যান্ডি উপকূলে। তাঁরা ২০২০ থেকে ’২১ সালের মধ্যে আমার-আপনার জন্য, কোভিডের বিরুদ্ধে ফ্রন্টলাইনে দাঁড়িয়ে লড়াই করে প্রাণ দেওয়া সেই দেড় লক্ষ সেবিকার দল, যাঁরা চলে যাওয়ার আগে আরও দেড় কোটি সিস্টারকে বলে গিয়েছিল, ‘দ্য শো মাস্ট গো অন।’

শ্যারন অ্যান লেন বিশ্বাস করুন, এঁরা আলাদা কেউ নন। ‘ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল’-এ নথিভুক্ত তেত্রিশ লক্ষ নার্স, মিডওয়াইভস আর আরও বহু আনরেজিস্টার্ড সেবিকার দল; হাসপাতাল কিংবা নার্সিং হোমে যাঁদের আমরা রোজ দেখি, যাঁরা প্রতিদিন আমার-আপনার সেবা-শেষে বাসে ট্রামে ঝুলে বাড়ি ফেরে, রোজ যাঁরা আমার-আপনার সরকারি হাসপাতালে ফেলে আসা পরিত্যক্ত পরিজনের চিকিৎসার দায়িত্ব তুলে নেয় স্বেচ্ছা তহবিল গড়ে, এঁরা তাঁরাই।
এঁরা তাঁরা, যাঁরা সামাজিক রক্ষণশীলতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নারীবাদী তরঙ্গের পথিকৃৎ হয়ে লড়ে গিয়েছেন মেয়েদের সমানাধিকারের লড়াই। সমাজের রক্তচক্ষু এড়িয়ে প্রতিদিন নাইট শিফটে ডিউটি করেছেন। ইভনিং শিফটে ডিউটি সেরে দূরপাল্লার ট্রেনে বাড়ি ফিরেছেন মধ্যরাতে। স্বামীকে অনুরোধ করেছেন, ‘ভাতটা যদি একটু বসিয়ে দাও আজ…।’ সন্তানকে বুঝিয়েছেন, ‘আমি শুধু তোমার মা নই। বিশ্বজোড়া আমার ঘর-সংসার…’
এঁরা তাঁরা, যাঁদের কোভিডে ঘরভাড়া দেয় না শহর, রাষ্ট্র দেয় না পরিচ্ছন্ন কাজের পরিবেশ, সমাজ যাঁদের হোয়াইট কলার জবের মর্যাদা দেয় না, ডাক্তাররা যাঁদের অভিজ্ঞতার দাম দেয় না, রোগী যাঁদের নিছক আজ্ঞাবাহকের বেশি কিছু ভাবে না; ‘জল দিন’, ‘বেড প্যান দিন’, ‘ডাক্তারবাবুকে একটু ডেকে দিন’-এর বাইরে শেয়ার করতে চায় না গুরুত্বপূর্ণ অসুস্থতার তথ্য, এঁরা তাঁরা।
এঁরা তাঁরা, যাঁরা সামাজিক রক্ষণশীলতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নারীবাদী তরঙ্গের পথিকৃৎ হয়ে লড়ে গিয়েছেন মেয়েদের সমানাধিকারের লড়াই। সমাজের রক্তচক্ষু এড়িয়ে প্রতিদিন নাইট শিফটে ডিউটি করেছেন। ইভনিং শিফটে ডিউটি সেরে দূরপাল্লার ট্রেনে বাড়ি ফিরেছেন মধ্যরাতে। স্বামীকে অনুরোধ করেছেন, ‘ভাতটা যদি একটু বসিয়ে দাও আজ…।’ সন্তানকে বুঝিয়েছেন, ‘আমি শুধু তোমার মা নই। বিশ্বজোড়া আমার ঘর-সংসার…’
এঁরা তাঁরা, যাঁরা চিকিৎসা-শাস্ত্রের এক বিরাট সিলেবাস পাশ করেই কিন্তু নার্স হওয়ার সুযোগ পান। বিশেষ করে বিএসসি বা জিএনএম নার্সিং-এর ক্ষেত্রে। যাঁদের তা পড়ার সুযোগ ঘটে না, তাঁরাও হাতে-কলমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখে নেন ধীরে ধীরে। তবু তাঁদের দর বাড়ে না। পুরুষ নার্সদের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। এদেশের নার্সদের কুড়ি শতাংশই যে পুরুষ, বলে না দিলে সে-কথা বিশ্বাস করে কয় জনা? তাই কলকাতার স্বনামধন্য হাসপাতালের এক মেল নার্স যখন নিজের প্রফেশনাল ক্রাইসিসকে আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের জায়গায় নিয়ে গিয়ে বলেন, ‘ঈশ্বরের সেবক পুরোহিত, মঠের সেবক মহারাজ। শুধু মানুষের সেবায় পুরুষ মানুষের দর নেই’— তখন নিজের অজ্ঞতা আর উপেক্ষাকে কী বলে লুকোব— ভেবে পাই না।
তো শেষমেশ বলার কথা এই যে, এতকাল ধরে যে নার্সিং প্রফেশনকে, নার্সদের কাজকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলাম না; অবমূল্যায়িত করলাম যাঁদের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা আর জ্ঞানকে, আজ যুদ্ধের আবহে যদি তাঁদের যুদ্ধদিনের আত্মত্যাগ, পরিশ্রম আর লড়াইয়ের কথা স্মরণ করে আত্মগ্লানি মোছার সামান্য চেষ্টা দিয়ে শুরু করি, সেই বা কম কী?
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook