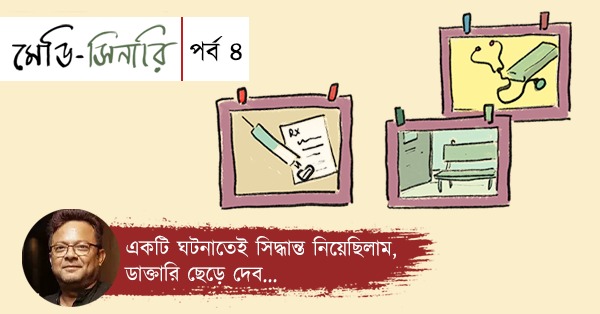একটি সন্ধে ও চিকিৎসক জীবন
চিকিৎসক-জীবনের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে প্রথমেই একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে।
তখন আমি বিআর সিং হাসপাতালে কর্মরত, মাস্টার্স ডিগ্রি করছি সেখানে, ডিএনবি, ইন্টারনাল মেডিসিনে। ২০০০ সালে আমি জয়েন করেছিলাম ওখানে। ১৯৯৯ সালে ক্যাকটাসের প্রথম অ্যালবাম প্রকাশিত। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন ২০০২ সাল। ‘নীল নির্জনে’-র অ্যালবামও ততদিনে মুক্তি পেয়েছে। ফলে, তখন আমাদের একটু জনপ্রিয়তা বেড়েছে। লোকে চিনতে পারে, এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি তখন। আমি তখন পিজিটি ইনটার্ন। আমাদের মাঝেমধ্যেই অন কল পড়ে। অ্যাডমিশন ইত্যাদি হলে আমাদেরই সামলাতে হয়।
এমনই এক রাতে, সাড়ে দশটা-এগারোটা নাগাদ এক বয়স্ক ভদ্রলোক এসেছেন ভর্তি হতে। বোঝা গেল, তাঁর সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে। যেমন হয়, একটা টেবিলে বসে রোগীর মেডিকেল হিস্ট্রিটা নথিবদ্ধ করতে হয়। সেই রোগীর ডায়াবেটিস আছে কি না, হাইপারটেনশনেক রোগী কি না, কী কী ওষুধ খান, হার্টের সমস্যা আছে কি না— এইসব খোঁজ নিচ্ছি, ট্রিটমেন্ট শুরুর আগে এই তথ্যগুলো লাগবে। ভদ্রলোকের বয়স ৭০-৭২ হবে। ওঁর ছেলে-বউমাদের থেকেই এই তথ্যগুলো নিচ্ছি। তাঁর নাতনি সেখানে তখন ছিল না। হঠাৎই সে এসে হাজির হল। সে কলেজপড়ুয়া, ১৭-১৮ বছর বয়স হবে। রোগীর বাড়ির লোক তখন উদ্বিগ্ন। সকলেই দুশ্চিন্তায়, অত রাতে অ্যাডমিশন হয়েছে। সেই অবস্থায় সেই নাতনি হঠাৎই এসে, আমাকে চিনতে পারে তৎক্ষণাৎ। এবং চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই, ওই থমথমে পরিবেশেই সে চিৎকার করে ওঠে— ‘আরে! সিধু না!’
সংগীতজীবনের প্রথমদিকে, কেউ চিনতে পারলে একটা আনন্দই হত। কিন্তু ওরম একটা গুরুগম্ভীর পরিবেশে, ওইভাবে আমাকে চিনতে পেরে একজন প্রায় লাফিয়ে ওঠায়, আমার মজাও যেমন হল, তেমনই কিছুটা অস্বস্তিতেও পড়লাম। সিস্টাররা রয়েছে, রোগীর আত্মীয়রা রয়েছে, সেই অবস্থায় এমন একটা উল্লাস সে প্রকাশ করে বসল, আমি কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ই হয়ে পড়লাম। হাসব না গম্ভীর হব, সেই নিয়ে প্রায় দিশাহারা হয়ে পড়লাম।
ছাত্রজীবনের একটা দুর্বিষহ, অথচ কিছুটা মজাদার একটা ঘটনাও মনে পড়ে। আমাদের প্রায় ১৪০ জনের ব্যাচ ছিল। সেখানে কয়েকটি মেয়ে ছিল পড়াশোনার ব্যাপারে অসম্ভব সিরিয়াস। তারা ছিল ফার্স্ট বেঞ্চার। মোটা কাচের চশমা পড়ত। আমরা যারা আড্ডাবাজ, ক্যান্টিনবাজ ছিলাম, তাদের সঙ্গে কিছুতেই পটত না এদের। তারাও আমাদের ঠিক মানুষ বলে মনে করত না, আমরাও তাদের খানিক ভিনগ্রহের প্রাণী ভাবতাম। কলেজে এসে তারা সারাক্ষণ পড়াশোনাই করে যেত। অফ পিরিয়ড হলেই চলে যেত লাইব্রেরিতে। ক্যান্টিনে তাদের প্রায় দেখাই যেত না। ওদিকে আমরা সারাক্ষণ ক্যান্টিনেই থাকতাম।
একদিন আমাদের ফরেনসিক মেডিসিনের প্র্যাকটিকাল ক্লাসের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে কাঁটাপুকুর মর্গে। প্রথমবার পোস্টমর্টেম দেখার উত্তেজনা নিয়ে গিয়েছি। আমাদের মাস্ক দেওয়া হয়েছিল কি না, এখন আর মনে নেই। প্রথমেই যখন অ্যাবডোমেন ওপেন করা হল, পেট যখন ফাঁক করা হল, তখন সে এক উৎকট গন্ধ চারপাশে!
ওদিকে রীতিমাফিক সেদিনও সেই ছাত্রীরা ফার্স্ট বেঞ্চার। মৃতদেহের ঠিক পাশেই ওরা রয়েছে। চার-পাঁচটা সারি পিছিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে। ফলে, গন্ধের আক্রমণটা মূলত ওদের ওপরেই হল। আর ওরাও, প্রায় পটাপট অজ্ঞান হতে শুরু করল। পুরোপুরি অজ্ঞান না হলেও, বেসামাল হয়ে পাশের জনের ওপর পড়ে যেতে থাকল। ফার্স্ট বেঞ্চার হওয়ার যে কতরকমের মুশকিল আছে, তা ওরাও সেদিন টের পেয়েছিল, আমরাও খানিক মজাই পেয়েছিলাম সেই ঘটনা দেখে।
রোগীর বাড়ির লোক তখন উদ্বিগ্ন। সকলেই দুশ্চিন্তায়, অত রাতে অ্যাডমিশন হয়েছে। সেই অবস্থায় সেই নাতনি হঠাৎই এসে, আমাকে চিনতে পারে তৎক্ষণাৎ। এবং চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই, ওই থমথমে পরিবেশেই সে চিৎকার করে ওঠে— ‘আরে! সিধু না!’
ডাক্তারি ছেড়ে দেব, এই সিদ্ধান্ত একদিনেই নিইনি। তবে হ্যাঁ, একটা সন্ধের ঘটনাতেই ঠিক করেছিলাম, অন্তত ছ’মাসের জন্য ডাক্তারিটা মুলতবি রাখব।
সেটাও ছিল একটা বইমেলার সময়। তখন ময়দানে বইমেলা হত। বিভিন্ন পত্রিকার তরফ থেকে সন্ধেবেলা গান-আড্ডার একটা আসর বসানো হত সেই সময়। সেই আসরগুলোর প্রতিবেদনও বেরত সেই কাগজে। এটা ২০০৩ সালের কথা। একটি নামী পত্রিকার তরফ থেকে একদিন আমরা, ক্যাকটাস, ডাক পেয়েছি। সেখানে যাওয়াটা তখন, আমাদের ব্যান্ডের জন্য খুব দরকারি।
এমনিতে, হাসপাতালের তরফ থেকে আমার গান ও কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষায় কখনও বাধা দেওয়া হয়নি। সহকর্মীরাও সহযোগিতা করত সবসময়। কিন্তু, ঘটনাচক্রে সেদিনও অন কল পড়েছে, এবং আগে থেকেই আমার সহকর্মীরা ছুটি নিয়ে রয়েছেন। আমি পড়লাম ফ্যাসাদে! ব্যান্ডকে জানালাম, আমি পারব না যেতে। ব্যান্ডের বাকিরা বলল, ‘তুই না এলে, ব্যাপারটা বাতিল করাই শ্রেয়। তুই আমাদের স্পোকসপার্সন। তুই না গেলে কী করে হবে?’
আমি তখন মহা ধন্দে। কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না। সেদিন যিনি মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন, তাঁকে গিয়ে জানালাম, ‘পাঁচটার সময় তো ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়, তখন কোনও কাজ থাকে না। তখন বেরিয়ে আমি যদি আটটা নাগাদ ফিরে আসতে পারি অনুষ্ঠান শেষে?’
সেই সিনিয়র ডাক্তার রাজি হয়ে গেলেন এককথায়।
আমিও মহানন্দে গেলাম। একঘণ্টায় পৌঁছলাম, অনুষ্ঠানও সময়মাফিক শেষ হল, কিন্তু ফিরতে ফিরতে তিনটি ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। কারণ, ময়দানের বাইরে তখন বীভৎস জ্যাম হত। ফলে, আমার হাসপাতালে পৌঁছতে পৌঁছতেই দশটা বাজল।
ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে পৌঁছেছি। একজন সিস্টার আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, ‘ডক্টর রায়, আপনি কোথায় ছিলেন?’
আমার পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে আমি সেই সিস্টারকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন, কোনও সমস্যা হয়েছে?’
সিস্টার আমাকে বললেন, ‘আজ সন্ধে থেকে ওয়ার্ড যেমন ডিস্টার্বড হয়ে আছে, কী বলব! তিনজন পেশেন্টকে আইসিইউ-তে ট্রান্সফার করতে হয়েছে, চারজনের অ্যাডমিশন হয়েছে!’
আমি খুবই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। এই কাজগুলো তো আমারই করার কথা! শুনলাম, স্যর সব সামলে নিয়েছেন।
আমি টুকিটাকি যা কাজ বাকি ছিল, সেসব সামাল দিয়ে আমি গেলাম স্যরের সঙ্গে দেখা করতে। লজ্জা, ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে আমি ক্ষমা চাইলাম স্যরের কাছে বারবার করে, আমার অবস্থাটা ব্যাখ্যা করলাম।
উনি রেগে গেলেন না, কোনও কটুকথা বললেন না, শুধু গম্ভীরভাবে একবার বললেন, ‘হুম!’
এর ফলে আমার অপরাধবোধ আরও বেড়ে গেল। নিজের ঘরে ফিরে এসে সারারাত ধরে ভাবলাম, ডাক্তার হিসেবে নিজের কর্তব্য পালনই যদি না করতে পারি, তাহলে তো কোনও মানেই হয় না এই পেশায় থাকার।
পরেরদিন সকাল ন’টায় দায়িত্ব অন্য একজনকে অর্পণ করে আমি সেই যে ফিরে এলাম, আর কখনও ফিরে যাইনি হাসপাতালে। দু’দিন বাদে কেবল একটা আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠিয়েছিলাম।
সেই আমার ডাক্তারিতে ইতি দেওয়ার শুরু।