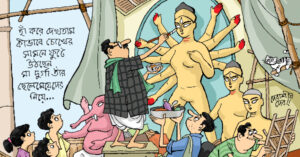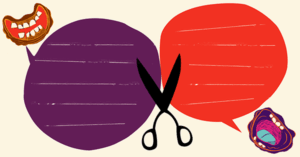পিছুটান ও ফেরিওয়ালার ডাক
সেই দু’জন মানুষের কথা খুব মনে পড়ে আজও। সেই দু’জন বুড়ো মানুষ। যাঁদের নাম জানি না, আর জানাও হবে না কোনওদিন। ঠিকানা জানতাম না কক্ষনও, আর কখনও জানবও না। কোত্থেকে তাঁরা আসতেন, আর কোথায়ই বা মিলিয়ে যেতেন, সেসব হদিশও রাখিনি। তবু, মনে পড়ে আজও তাঁদের কথা। আরও বেশি করে মনে পড়ে এইসব দমচাপা, কাঠফাটা গ্রীষ্মের দুপুরগুলোয়। যখন বাইরে পাড়া শুনশান, পাখি আর কুকুর-বেড়ালরা গাছের ছায়ায় গুটিসুটি, এমনকী রিক্সাও সওয়ারি নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, কেবল কিছু ক্লান্ত কাক ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে কেন কে জানে, সেইরকম তপ্ত, প্রখর, নির্দয় রোদের গ্রীষ্মদিনগুলোয় আরও বেশি করে মনে পড়ে তাঁদের কথা। কেননা, ওই গরমের জনহীন দুপুরগুলোতেও ওই দু’জন মানুষ ছুটি নিতেন না। নিতেন না, নাকি জীবনের হাত থেকে ছুটি পেতেন না, তখন অত বুঝতাম না। কেবল এটুকু বুঝতাম, ওঁদের দু’জনেরই কেবল জাদু জানা ছিল, ওই গরমের মধ্যেও আমাদের বাড়িছাড়া করবার। আমরা মানে যারা তখন ক্লাস ফোর কি ফাইভ, গরমের লম্বা, টানা ছুটি চলছে। তারা অপেক্ষা করতাম, কখন দুপুর আসবে। আর কখন, দুপুরের শান্ত, ভারী পিঠে চেপে আমাদের পাড়ায় আসবেন তাঁরা। ওই দু’জন বুড়ো মানুষ।
প্রথমজন ছিলেন বেশ শীর্ণকায় আর দীর্ঘদেহী। রোগা মানুষ লম্বা হলে বোধহয় আরও রোগা দেখায়, তাঁকেও সেইরকমই দেখাত। তিনি যে আসছেন, তা আমরা একটু আগে থেকেই বুঝতে পারতাম। কেননা তাঁর আগে আমাদের কাছে এসে পৌঁছত তাঁর ডাক। সে-ডাকও তাঁরই মতো লম্বা, দীর্ঘ। মানুষটি শনপাপড়ি বিক্রি করতেন। মাথার ওপর গামছা ঘুরিয়ে বেঁধে নিয়ে তার ওপর বসানো থাকত একখানা গোলাকার ঝুড়ি, খুব পাতলা সাদা কাপড়ের এক আস্তরণ বিছিয়ে দেওয়া থাকত তার ওপর। আর সে-কাপড় সরালেই দুপুর-রোদে ঝলমল করে উঠত মিঠে-হলুদ রঙের শনপাপড়ির ঝাঁক। সে যেমন এক নিত্যদিনের আকর্ষণ ছিল, তার চেয়েও বড় টান ছিল তাঁর ওই আশ্চর্য ডাক। তাঁর বিপণনের কৌশল। শনপাপড়ি শব্দটা পরপর দু’বার খুব টেনে টেনে লম্বা করে হাঁকতেন তিনি, খুব ঝিমধরা, প্রায় বিষণ্ণ এক সুরে। ‘শঅন পাপড়ি, শন পাআআপড়িই’… বানান করলে এইরকম হবার কথা। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, বছরের পর বছর, দুপুরের পর দুপুর, ঠিক একই সুরে, একই ছন্দে ডাকটা আসত তাঁর গলা থেকে। বুঝতে পারতাম, এমনকী স্কেলেরও নড়চড় হচ্ছে না। অথচ দড় কোনও গাইয়ে তো নন তিনি। আজ বুঝি, শিল্পের চেয়েও চর্চা কখনও বড় হয়ে ওঠে। ওই ফিরিওয়ালা মানুষটির গলায় শিল্প ছিল না। ছিল চর্চা, অভ্যেস, অধ্যবসায়। তাই শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা একই ভাবে ডেকে উঠতে পারতেন, সওদার টানে, রোজগারের আশায়।
কখনও-সখনও আমরা এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে মিলে তাঁকে ঘিরে ধরলে তিনি একটু ছায়া খুঁজে নিয়ে মাথার মিঠাইয়ের বোঝাটা নামাতেন, তারপর একখানা শনপাপড়ি হাতে তুলে ভেঙে-ভেঙে আমাদের সক্কলকে দিতেন। পুজোর প্রসাদের মতো ওইটুকু পেয়েই আমরা যে কী খুশি হতাম, তার ইয়ত্তা নেই। আজকের বিপণনের ভাষায় একেই হয়তো বলে ‘স্যাম্পল’ বিলি করা, উনি সেটা করতেন খুশির ছদ্মবেশে। কেননা হাত পেতে চাখার পর রোজ যে আমরা কেউ না কেউ ওঁর কাছ থেকে কিনতে পারতাম, এমন নয়। মাথায় গামছার বিড়ে পাকিয়ে ঝুড়ি চাপিয়ে আবার তিনি ডাকতে-ডাকতে আবছা হয়ে যেতেন দূরের রোদে। কেবল আমাদের মুখে লেগে থাকত অনায়াস খুশির ঝিকমিক।
কে জানে, হয়তো আমারই ভুল, হয়তো স্বাদ আসলে ছোটবেলার, সুগন্ধ আসলে স্মৃতির, তাই সমসময় আর কিছুতেই অতীতকে টেক্কা দিতে পারে না আজ।
আরেকজন যিনি আসতেন, তাঁর দৈহিক উচ্চতা আগেরজনের চেয়ে বেশ খানিকটা কমই ছিল মনে পড়ে, আর শরীরের গড়ন ছিল চৌকোনো। মাথাভর্তি সাদা চুল, পরতেন একখানা সাদা পাজামা আর নীলসাদা মলিন চেক শার্ট। যত দিন তাঁকে দেখেছি, ওই এক পোশাকেই দেখেছি। তবে হ্যাঁ, আজ আর তাঁর হাঁকটা ঠিকঠাক মনে পড়ে না। সে-হাঁক নিশ্চিত ভাবেই আমাদের টানত না তেমন, তাই মনে রাখার প্রয়োজন হয়নি। হাঁকের অবশ্য দরকারও হত না। তিনি পাড়ার যে-যে রাস্তা দিয়ে ফিরি করতে-করতে যেতেন, তার প্রতিটি ভরে উঠত এক মিঠে সুগন্ধে। তাঁর পেটের কাছে ঝোলানো থাকত অ্যালুমিনিয়ামের একখানা তোবড়ানো মাঝারি বাক্স, আর সেই বাক্সে সার বেঁধে পাশাপাশি শুয়ে থাকত প্যাটি আর পেস্ট্রি।
তখন এরকম প্যাটি-পেস্ট্রির বাড়বাড়ন্ত হয়নি কলকাতা শহরে, সেসব ছিল খুবই দুর্লভ খাবার। কদাচিৎ কোনও দোকানে কাচের আড়ালে সাজানো থাকলেও সেসব আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরেই ছিল। হাতের কাছে শুধু ছিলেন এই মানুষটি। ওইরকম গরমাগরম দুপুরবেলায় তিনি পাড়ায় ঢুকলেই প্যাটির তপ্ত নোনতা সুবাস আর পেস্ট্রির মিঠে সুগন্ধে রাস্তাঘাট ম-ম করে উঠত। সেই গন্ধের পিছনে ধাওয়া করে আমরা বেরিয়ে আসতাম যে-যার ছুটির দুপুরের বাড়ি ছেড়ে ওই কড়া রোদে, যেমন পাইপার-এর সুরের পিছনে বেরিয়ে এসেছিল সেই বিখ্যাত ইঁদুরেরা। প্যাটি আর পেস্ট্রি’র সুগন্ধ বেড়ে তিনগুণ হয়ে যেত, তিনি যখন আমাদের সামনে সেই অতিপরিচিত জাদুবাক্সের ডালাটি খুলে ধরতেন। কী আশ্চর্য ব্যাপার, অতক্ষণ ধরে ফিরি করছেন, অথচ তাঁর ওই বাক্সের প্রতিটি প্যাটি থাকত গরম, আর প্রতিটি পেস্ট্রি নরম। এ-জিনিসের স্বাদ যে চেখে না-দেখেছে, তাকে বোঝানো অসম্ভব। বড় হয়ে দেশে-বিদেশে অনেক ক্যাফে বা পাতিসেরি-তে এ-দুই বস্তুই বহু খেয়েছি, কিন্তু ওই চৌকোনো চেহারার বুড়ো মানুষটির মতো আশ্চর্য স্বাদ আর কেউ উপহার দিতে পারেনি।
কে জানে, হয়তো আমারই ভুল, হয়তো স্বাদ আসলে ছোটবেলার, সুগন্ধ আসলে স্মৃতির, তাই সমসময় আর কিছুতেই অতীতকে টেক্কা দিতে পারে না আজ। কত কী যে বদলে যেতে দেখলাম এই কয়েক বছরে, তার হিসেব রাখা ভার। আর এই শেষ দু’তিন বছরে তো ভালমন্দ খেতে গেলে বাড়ি থেকে বেরোতেও হয় না। মিঠে চাও বা নোনতা, খাদ্য চাও বা পানীয়, অর্ডার করলেই বাড়ির দরজায় কেউ না কেউ হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু রোজ সেইসব মুখেরা বদলে যাচ্ছে। তা ছাড়া তারা কেউ নিজের জিনিস ফিরি করছে না, তারা সরবরাহ করছে কেবল। এই কয়েক দশকে আমরা ফিরি থেকে সরবরাহে উন্নীত হলাম, এই যা। কেবল মনে হয়, নাম-না-জানা ওই দু’জন অলীক বুড়ো মানুষের সঙ্গে বিক্রিবাটা’র বাইরেও আমাদের একরকমের সম্পর্ক ছিল, তাঁরা একদিন না এলে আমাদের মনকেমন করত, আমাদের কেউ দলে কম পড়লে তাঁরা খোঁজ নিতেন। আজ সব আছে, কেবল সেই সম্পর্কটুকু বাদ দিয়ে। গরমের দুপুরগুলোয় তাই রোদ এত চড়া, চিনি আর নুন, দুটোই আগের চেয়ে কম যে…
ছবি এঁকেছেন চিরঞ্জিৎ সামন্ত