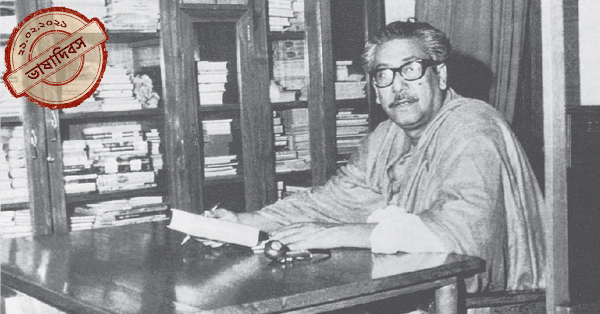২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনের নানা আয়োজনে, বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বহুমাত্রিক জীবনের নানা দিক উন্মোচিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলা একাডেমি-সহ নানা প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে— যা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর গবেষণায় যোগ করেছে নতুন মাত্রা।
বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্বদানের বিভিন্ন পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর সৃষ্টিশীল সত্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা কম-বেশি অবহিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রকাশিত লেখক বঙ্গবন্ধুর অনবদ্য সৃষ্টি বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা গ্রন্থ থেকেই আমরা তাঁর পঠনের বিষয়গত বৈচিত্র্য— রাষ্ট্র পরিচালনা পর্বে এসে পঠিত বিষয়ের বাস্তবসম্মত প্রয়োগের বহু নজির দৃশ্যমান হতে দেখি। একই সঙ্গে পরিবারের অন্য সদস্যদের ভেতরেও পাঠাভ্যাস ও সাহিত্যপ্রীতি কত গভীর ভাবে প্রোথিত করতে পেরেছিলেন তাও আমরা এ লেখায় প্রত্যক্ষ করব।
তাঁর তিনটি মৌলিক গ্রন্থ ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, ‘কারাগারের রোজনামচা’, ‘আমার দেখা নয়াচীন’ এবং ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৯ সময়কালে ‘দৈনিক ইত্তেফাক’ ও ‘দৈনিক পাকিস্তান’-এ প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর লেখা পাঁচটি প্রবন্ধ ‘নেতাকে যেমন দেখিয়াছি’, ‘শহীদ চরিত্রের অজানা দিক’, ‘স্মৃতির মিছিল: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী’, ‘আমাদের মানিক ভাই’, ‘আমার মানিক ভাই’ ইত্যাদি। শিরোনাম থেকেই প্রণিধান করা যায়, শেষোক্ত লেখাগুলো বঙ্গবন্ধু মূলত তাঁর জীবনে গভীর ভাবে প্রভাব রেখে যাওয়া দু’জন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে লিখেছেন।
বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও মায়ের অনুরোধে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, আইন পেশার আড়ালে সেই দিকটি ঢাকা পড়ে গেছে— তাঁর সহোদর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একজন বিশিষ্ট কবি, শিল্প সমালোচক ও শিক্ষাবিদ। বঙ্গবন্ধু এবং তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর সম্পর্ক আরও গভীর হয় কলকাতা জীবনের শুরু থেকে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে লেখনীর মাধ্যমে জনমানুষের মনে প্রোথিত করার ক্ষেত্রে মানিক মিয়া ও দৈনিক ইত্তেফাকের ভূমিকার কথা আমরা সকলেই জানি। বঙ্গবন্ধু তাঁর বইতেও সে কথা বলে গেছেন।
বঙ্গবন্ধুর পাঠক ও লেখক সত্তার ভিত রচিত হয়েছিল কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই। বেকার হস্টেলে তাঁর কক্ষটি পরিণত হয়েছিল পূর্ব বাংলা থেকে পড়তে আসা ছাত্রদের প্রধান কেন্দ্রে। তৎকালীন বেকার হস্টেলের আবাসিক শিক্ষক ও পরবর্তী সময়ে জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান তাঁর স্মৃতিকথায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের সহজাত গুণের প্রশংসা করেছেন। কলকাতা জীবনে তিনি অনেক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের অনেকে পরবর্তী সময়ে লেখক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলকাতা ও ঢাকাকেন্দ্রিক অনেক লেখক-সাংবাদিকের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে সে সময়েই।
পাঠক বঙ্গবন্ধুকে আমরা তাঁর মৌলিক লেখা, বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও নানাবিধ বিবৃতির মধ্যে খুঁজে পাই। বঙ্গবন্ধু ২১ ডিসেম্বর ১৯৫০-এ একটি চিঠিতে হোসেন শহীদ সোহওরাওয়ার্দীকে লিখছেন—
‘আপনি কথা দিয়েছিলেন, আমাকে কিছু বই পাঠিয়ে দেবেন। এখনও পাইনি। ভুলে যাবেন না এখানে আমি একা আর বই-ই আমার একমাত্র সঙ্গী।’
এরকম আরও একটি চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি— বঙ্গবন্ধুর জীবনে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছার প্রভাব অপরিসীম। স্বামীর দুঃসাহসিক রাজনৈতিক জীবনের সহযাত্রী ও অনুপ্রেরণা তিনি। ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে ১৬.৪.৫৯ তারিখে স্ত্রীকে যে চিঠিটি বঙ্গবন্ধু লেখেন, তা প্রণিধানযোগ্য:
‘রেনু, আমার ভালোবাসা নিও। ঈদের পরে আমার সাথে দেখা করতে এসেছো ছেলেমেয়েদের নিয়ে আস নাই। কারণ তুমি ঈদ করো নাই। ছেলেমেয়েরাও করে নাই। খুবই অন্যায় করেছো। ছেলেমেয়েরা ঈদে একটু আনন্দ করতে চায়। কারণ সকলেই করে। তুমি বুঝতে পারো ওরা কত দুঃখ পেয়েছে। আব্বা ও মা শুনলে খুবই রাগ করবেন। আগামী দেখার সময় ওদের সকলকে নিয়া আসিও। কেন যে চিন্তা করো বুঝি না। আমার কবে মুক্তি হবে তার কোন ঠিক নাই। তোমার একমাত্র কাজ হবে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা শিখানো। টাকার দরকার হলে আব্বাকে লেখিও কিছু কিছু মাসে মাসে দিতে পারবেন। হাছিনাকে মন দিয়ে পড়তে বলিও। কামালের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল হচ্ছে না। ওকে নিয়মমতো খেতে বলিও। জামাল যেন মন দিয়ে পড়ে আর ছবি আঁকে। এবার একটা ছবি এঁকে যেন নিয়ে আসে আমি দেখব। রেহানা খুব দুষ্টু ওকে কিছুদিন পরে স্কুলে দিও জামালের সাথে। যদি সময় পাও নিজেও একটু লেখাপড়া করিও। একাকী থাকতে একটু কষ্ট প্রথমে হতো। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে চিন্তা নাই। বসে বসে বই পড়ি। তোমার শরীরের প্রতি যত্ন নিও। ইতি— তোমার মুজিব।’
এই চিঠি দু’টি এবং জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার ‘স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড় বেদনার’ লেখাটি থেকে জানতে পারি— ‘মা প্রচুর বই কিনতেন আর জেলে পাঠাতেন। নিউ মার্কেটে মা’র সঙ্গে আমরাও যেতাম। বই পছন্দ করতাম, নিজেরাও কিনতাম। সব সময়ই বই কেনা ও পড়ার একটা রেওয়াজ আমাদের বাসায় ছিলো।’ এ থেকে আমরা বুঝতে পারি কেবল নিজে নয়, তিনি গোটা পরিবারের মধ্যে প্রোথিত করতে পেরেছিলেন সাহিত্যবোধ।
বঙ্গবন্ধুর লেখক-জীবনেও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছার প্রভাব বিষয়ে শেখ হাসিনা লিখছেন, ‘আমার মায়ের প্রেরণা ও অনুরোধে আব্বা লিখতে শুরু করেন। যতো বার জেলে গেছেন আমার মা খাতা কিনে জেলে পৌঁছে দিতেন। আবার যখন মুক্তি পেতেন তখন খাতাগুলি সংগ্রহ করে নিজে সযত্নে রেখে দিতেন। তাঁর দূরদর্শী চিন্তা যদি না থাকতো তাহলে এই মূল্যবান লেখা আমরা জাতির কাছে তুলে দিতে পারতাম না।’ এই ধারা প্রজন্মান্তরে বহমান। আমরা জানি বঙ্গবন্ধুর এযাবৎ প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থ এবং ১৪ খণ্ডে প্রকাশিতব্য (যার পাঁচটি ইতোমধ্যে প্রকাশিত) ‘SECRET DOCUMENT OF INTELLIGENCE BRANCH ON FATHER OF THE NATION BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN’ এবং এখনও অপ্রকাশিত আরও কিছু গ্রন্থের সম্পাদনার ক্ষেত্রে সুলেখক মাননীয় শেখ হাসিনার কতটা শ্রম ও নিষ্ঠা নিয়োজিত। উল্লেখ্য যে, তিনি নিজেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্রী।

উল্লেখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ‘কারাগারের রোজনামচা’ ও ‘আমার দেখা নয়াচীন’ গ্রন্থ দু’টি প্রকাশের আগেই এর নকশা-বিন্যাস ও মুদ্রণ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল— সে জন্য পাণ্ডুলিপিগুলো বার বার পড়তে হয়েছে। ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’— যা বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোর ও রাজনৈতিক উপলব্ধির উন্মেষ পর্ব, নির্ভীক পথচলা ও বিবেকী আত্মার বয়ান। ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয় ‘কারাগারের রোজনামচা’— যেখানে বিধৃত হয়েছে জেল-জীবনের নিবিড় অভিজ্ঞতা, ষাটের দশকের সংগ্রামমুখর দিনের অভিজ্ঞতা এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনে আত্মত্যাগের বয়ান। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিকিং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ১৯৫৪ সালে জেলে বসে লেখা স্মৃতিনির্ভর ভ্রমণকাহিনি। এই তিনটি বইয়ের ক্ষেত্রে একটি ঐক্য লক্ষণীয়— সবগুলো বই-ই বঙ্গবন্ধু লিখেছিলেন কারারুদ্ধ অবস্থায়। বঙ্গবন্ধুর রচনাশৈলীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে কোনও ঘটনার বর্ণনায় স্থান বা ব্যক্তিবিশেষের পরিচয় তিনি নিজেই অল্প কথায় তুলে ধরেন। সে জন্য তাঁর বইয়ের শেষে খুব বেশি টীকা-টিপ্পনী ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। ভাষা নির্মিতির জায়গায়ও তিনি অনন্য। সহজতার সৌন্দর্য যেখানে আমাদের বিমোহিত করে। তথ্যের পরিবেশনা, যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ, ঘটনার পর্যবেক্ষণ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যা বিষয়ে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে, ঐতিহাসিক পরস্পরা বিবেচনায় রেখে তিনি যে বক্তব্যগুলো রেখেছেন, তা বহু পরে সত্যে পরিণত হয়েছে। এই দূরদর্শিতা তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যেমন আমরা পাই, একই ভাবে তাঁর রচনাবলিতেও একই সত্য নিহিত। নয়াচীন প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বছরে তাঁদের অগ্রযাত্রার উন্মেষকালে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা পরবর্তী সময়ে বাস্তবে রূপ পেতে দেখি। অপ্রিয় সত্য উচ্চারণেও তিনি দ্বিধান্বিত নন— এমনকী তা যদি হয় খুব কাছের মানুষের বিষয়েও। এই সততা তাঁর লেখাকে আরও বেশি বস্তুনিষ্ঠ করেছে।
‘পূর্ব পাকিস্তান সংগীতশিল্পী সমাজ’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে ১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে এক সংবর্ধনার আয়োজন করে। সঙ্গীতশিল্পীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক মানপত্রে বঙ্গবন্ধুকে ‘বঙ্গ সংস্কৃতির অগ্রদূত’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।
বাংলা সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ ভাষণে তিনি বলেছিলেন:
‘দেশের গণমুখী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য-সঙ্গীতে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখকে প্রতিফলিত করতে হবে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন।’
… … … …
‘আমি স্বীকার করি আমাদের কবি, শিল্পী সাহিত্যিকরা এখনও তাঁদের ন্যায্য মর্যাদা পাচ্ছেন না। আমি আশ্বাস দিচ্ছি যদি আমরা ৬ ও ১১ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন লাভে সক্ষম হই, তাহলে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সবকিছুই পাবেন। সবকিছুই হবে তাঁদের। ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের অর্থই হচ্ছে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক স্বাধিকার। জয় বাংলা শ্লোগানের লক্ষ্য এই সামগ্রিক স্বাধিকার অর্জন। জনগণের সরকার কায়েম হলে বাংলার মাটিতে জাতীয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠা ও একটি জাতীয় ‘ললিতকলা একাডেমী’ গঠন করতে হবে।’
বঙ্গবন্ধু ১৯৭১-এ তাঁর প্রতিশ্রুত ‘ললিতকলা একাডেমী’র বাস্তবায়ন করেছিলেন ১৯৭৪ সালে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ তারিখে জাতীয় সংসদে একটি বিল পাসের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি’ প্রতিষ্ঠিত হয়।
‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগারের রোজনামচা’ গ্রন্থদ্বয়ে স্বাধিকার-প্রত্যাশী বাংলার মানুষের এবং নিজের সংগ্রামী জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষার যে-ছবি বঙ্গবন্ধু এঁকেছেন, তা আমাদের জানিয়ে দেয়, মাত্র ৫৬ বছর বয়সের ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ পরলোকবাসী হলেও তাঁর প্রধান কাজটি অসমাপ্ত থাকেনি। জীবনব্যাপী যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন তিনি— আমরা পেয়েছি একটি মানচিত্র ও একটি পতাকা।
২০২০ সালে ২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় কবিতা উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে কিছু কথা বলেছিলাম, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তার অংশবিশেষ উল্লেখ করছি:
‘তরুণ বয়স থেকেই সাহিত্যানুরাগী বঙ্গবন্ধু কবিতার নিবিড় পাঠক। জেল জীবনে একাকিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্বকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করতেন। রবীন্দ্র-নজরুলসহ সমকালীন বাংলা ও বিদেশি সাহিত্যের শুধু খোঁজ-খবরই রাখেননি— সেগুলো আত্মস্থ করেছেন গভীর ভাবে। ইতোমধ্যে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থসমূহে এমিল জোলা থেকে শুরু করে কবি নাজিম হিকমত, মাজহার আলী, মনোজ বসু, জসীমউদ্দীন, শহীদুল্লা কায়সারের লেখা সম্পর্কে আলোকসঞ্চারী মন্তব্য পাঠকদের মুগ্ধ করে। শিল্পকলা ও সঙ্গীতের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, সঙ্গীতশিল্পী আব্বাসউদ্দীন, আবদুল আলীমের সঙ্গেও ছিল বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক সম্পর্ক। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৭-র কাগমারী সম্মেলন, ১৯৭৪ বাংলা একাডেমি আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলন সর্বোপরি একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ছিল তাঁর নখদর্পণে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রবীন্দ্র শতবর্ষে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রচর্চাকে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল— প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধভাবে সেই অপচেষ্টাকে নস্যাৎ করে। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’— আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হল বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক আগ্রহে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনিই। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর বিদ্রোহী কবিকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কবির সম্মানে অভিষিক্ত করেন। নিজে কত বড় কবি-মনের মানুষ হলে এই কালজয়ী সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া সম্ভব হয়। এসব থেকে কী শিক্ষা আমরা গ্রহণ করব?’
বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর সাংস্কৃতিক বোধ। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রশ্নে রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎমুখী। কত আগেই— ১৯৫২-এ পিকিং শান্তি সম্মেলনে তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে প্রদত্ত বাংলা ভাষণ দেওয়ারও ২২ বছর আগে।
বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর সাংস্কৃতিক বোধ। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রশ্নে রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎমুখী। কত আগেই— ১৯৫২-এ পিকিং শান্তি সম্মেলনে তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে প্রদত্ত বাংলা ভাষণ দেওয়ারও ২২ বছর আগে। সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ভারতের সাহিত্যিক মনোজ বসু, তাঁর বয়ানে প্রথম দর্শনের অনুভূতি জানতে পারি— ‘শেখ মুজিবুর রহমান জেল খেটে এসেছেন, যারা বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সহযাত্রী। এই সেই তরুণ যার ভাষণে মানুষ পাগল হয়ে ওঠে।’ সেই সুদূর ’৫২-তেও তাঁর বক্তৃতার সম্মোহনী শক্তি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর ১৯৭১-এর ৭ মার্চের অবিনাশী ভাষণ, যা আজ মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ, ‘ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের দলিল’। যে মহাকাব্যিক ভাষণের জন্য ১৯৭১-এর এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘নিউজউইক’ সাময়িকী তাঁকে ‘পোয়েট অব পলিটিক্স’ অভিধায় অভিষিক্ত করে। তাঁর অমিত উচ্চারণে ৭ মার্চ ১৯৭১ সাত কোটি জোড়া চোখ স্থির হয়েছিল একটি আঙুলে। হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির দিশা খুঁজে পেয়েছিল একটি জাতি। ন’মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর পঠন, উচ্চারণ ও লেখনী একই সূত্রে গাঁথা। সমস্ত জীবন দিয়ে তিনি যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন তার নাম— বাংলাদেশ। তেরো শত নদী বিধৌত এই রক্তভেজা বাংলার মাটির প্রতিটি ধূলিকণা তিনি মর্মে ধারণ করেছেন, পাঠ নিয়েছেন হাজার বছরের শৃঙ্খলিত জীবনের শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাসের দীর্ঘশ্বাস থেকে আর শাশ্বত মুক্তির অবিনাশী স্লোগান ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি কণ্ঠে তুলে দিয়েছেন মুক্তিকামী একটি জাতির কণ্ঠে। তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন— আজ ও আগামী দিনের বাঙালির জন্য একটি মহাগ্রন্থ।