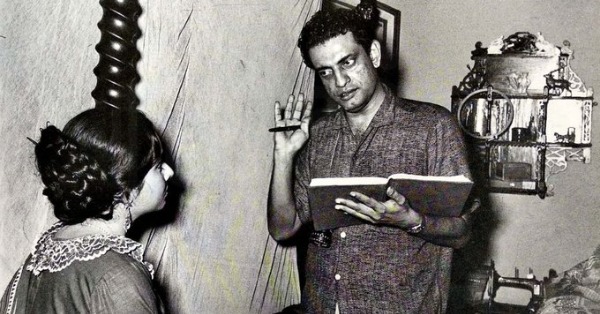ডেটলাইন : পর্ব ২৩

 তপশ্রী গুপ্ত (May 24, 2025)
তপশ্রী গুপ্ত (May 24, 2025)ওশো আশ্রমে মধুচক্র?
আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাত আটটায়। কেন পোখরার মতো একটা ট্যুরিস্ট স্পটে, যেখানে সূর্য ডোবার পর সাধারণ পর্যটকদের তেমন কিছু আর করার নেই, সেখানে শ্যুটিং করতে গেলে যেতে হবে রাত আটটার পর? তাছাড়া এটা তো রেস্তোরাঁ বা নাইটক্লাব নয়, যোগা আশ্রম কাম মেডিটেশন সেন্টার। প্রশ্ন করেছিলাম। স্মিত হেসে জবাব দিয়েছিলেন সুদর্শন গুরুজি, ‘সারাদিনের কাজকর্ম সেরে সবাই এখানে আসে রাতে, রিল্যাক্স করতে, মানে নার্ভ সুদিং যোগা আর ধ্যান করতে। আপনি কি দিনের বেলা ফাঁকা আশ্রমে শুট করবেন?’
সত্যিই তো, কত কষ্ট করে খোঁজ পেয়েছি এই ওশো আশ্রমের! ঠিক ধরেছেন, সাত-আটের দশকের সেই দুনিয়া-কাঁপানো আচার্য রজনীশের (নিজেকে ‘ভগবান রজনীশ’ নাম নিজেই দিয়েছিলেন) ওশো আদর্শ মেনে তৈরি পোখরার এই ‘অধ্যাত্ম-চর্চা’ কেন্দ্র। একঝলকে মনে করিয়ে দিই বর্ণময় চরিত্র রজনীশকে। আধ্যাত্মিকতার অন্য মানে প্রচার করে গুরু হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন যিনি, আশ্রম খুলেছিলেন আমেরিকার ওরেগনে। আর্থিক কেলেঙ্কারির দায়ে মার্কিন মুলুকে রজনীশপুরম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ১৯৮৫ সালে, সেদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে পুনের আশ্রমে এলেন, ফিল্মস্টার থেকে শিল্পপতি, দেশি-বিদেশি সেলিব্রিটি শিষ্যদের লাইন পড়ে গেল, গ্যারাজে ৩৯টা রোলস রয়েস, চারপাশে সুন্দরী ‘সাধনসঙ্গিনী’-দের ভিড়। যথেচ্ছ যৌনতা, প্রচুর কেচ্ছা, আয়কর হানা, কী না চলত বিশাল গেটের ওপাশে! অবাক লাগল ভেবে, যেখানে ১৯৯০ সালে মৃত্যু হয়েছে খোদ গুরুর, তার এত বছর পরেও এই ২০০৮ সালে তাঁর নামে এমন ঝকঝকে আশ্রম চলে কীভাবে নেপালে? কৌতূহল স্বাভাবিক। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এরকম অধিক কৌতূহলের মাশুল আমাকে দিতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। এই যাত্রা কান ঘেঁষে বেরিয়েছিলাম, নয়তো আমাকে আর ক্যামেরাম্যানকে থাকতে হত নেপালের জেলে।
জীবন এক উৎসব। এই কথাটা যে কতবার বলছেন পোখরার এই যোগা গুরু। তিনি কিন্তু নেপালি নন, সম্ভবত ভারতীয়, চোস্ত ইংরেজি ও হিন্দি বলেন, অত্যন্ত পরিশীলিত ব্যবহার। দুধ-সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে তাঁকে দেখাচ্ছেও চমৎকার। বিদেশিরা আসছেন দেখছি, হিপিও এল একদল, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁকে আলিঙ্গন করছেন ও ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন। গুরু আমাদের ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে রজনীশের বাণী দিচ্ছেন। রেকর্ড হচ্ছে তাঁর কথা। ‘নন জাজমেন্টাল অ্যান্ড প্লেফুল আপ্রোচ টু এক্সিসটেন্স’, ‘দু’জন মানুষের মধ্যে যত শারীরিক ও মানসিক ঘনিষ্ঠতা বাড়বে ততই কমা উচিত প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতি’— এই জাতীয় ধোঁয়াশা মার্কা কথাবার্তা। সেই সঙ্গে আবার তান্ত্রিক মতে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করার পদ্ধতিও বলছেন।
ভক্তপুরের মন্দিরে ঢুকলে মনে হয়, প্রাচীন সভ্যতায় প্রবেশ করলাম!
তপশ্রী গুপ্তর কলমে ‘ডেটলাইন’ পর্ব ২২…রাত বাড়ছে। হোটেল থেকে বেশ অনেকটাই দূরে চলে এসেছি, পোখরার এদিকটা বেশ নির্জন। আর এই সেন্ট্রালি এসি আশ্রমে তো বাইরের কোনও শব্দই ঢুকছে না। জানি না কেন, ঠিক মেডিটেশন বা যোগার মতো ‘নিরামিষ’ গন্ধ পাচ্ছি না এখানে। বলেই ফেললাম, ‘এবার ভেতরটা দেখি।’ অমায়িক ভঙ্গিতে কার্পেট থেকে উঠে দাঁড়ালেন, ‘আসুন।’ দরজা খুলতেই অন্ধকারের ঝাপটা। ঘরের ভেতরে জোরালো নিয়ন আলো ছেড়ে বেরোতেই লালচে ডিম লাইট। চোখ সইয়ে ওর পিছু পিছু দোতলায় উঠেও একইরকম ঢিমে আলো। শুনশান চারপাশ। ক্যামেরাম্যান নিজের চিন্তায় ব্যস্ত, ফিসফিস করে বলল, ‘এই আলোতে কিছু ছবি হবে না।’ আমি হাত তুলে আশ্বস্ত করলাম, নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা হবে। ভাবলাম, ধ্যান আর যোগা দুটোই তো মনঃসংযোগের ব্যাপার, তাই এরকম নিভু নিভু আলো।
প্রথম দরজাটা খুললেন গুরুজি। বিরাট হলঘর। ওই যেসব সাহেব-মেমদের ঢুকতে দেখেছিলাম, তারা এখানেই। আবছা আলো, গন্ধে মালুম হল, গাঁজা-চরসের ধোঁয়ায় সৃষ্টি হয়েছে কুয়াশা। তারপর একঝলক যা দেখলাম, তাকে অবাধ যৌনতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। হতবাক আমি এবং ক্যামেরাম্যান। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে নামতে শুরু করেছি। কৌতূহলের চক্করে রাতবিরেতে এরকম একটা গা ঘিনঘিনে পরিবেশে এসে পড়ে নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল। বুঝলাম, বিদেশিরা নেপালে এসে এরকম মধুচক্রের সন্ধান পায় হোটেল বা দালালদের থেকে। বেরনোর আগে শুধু কঠিন গলায় বললাম, ‘আপনি কি ভেবেছিলেন আমরা নীল ছবি তুলি?’ গুরুজি একটুও রাগলেন না। হাত জোড় করে সেই সিগনেচার হাসিটা ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে বললেন, ‘ইটস অল অ্যাবাউট ওশো ফিলসফি। জীবন তো একটাই। লিভ লাইফ টু দ্য ফুলেস্ট।’
সাধে একে ‘জুয়েল অফ দা হিমালয়াস’ বলে! আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে বরফমোড়া অন্নপূর্ণা রেঞ্জ এমন স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইচ্ছে হবে একছুটে পৌঁছে যাই। তা যদিও সম্ভব নয়, তবে মাত্র আঠাশ-ত্রিশ কিলোমিটার দূরেই সেই স্বর্গীয় বিভা। আসলে অন্নপূর্ণা সার্কিটের গেটওয়ে পোখরা ট্রেকারদের স্বপ্নের জায়গা, যাকে বলে শাংগ্রি-লা, পৃথিবীর বুকে একটুকরো স্বর্গ।
বাইরে বেরিয়ে ক্যামেরাম্যানকে বললাম, ‘খানিকটা হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সি ধরব। এসব জায়গা থেকে বেরিয়েছি, লোককে জানালে বিপদ হতে পারে।’ ঠিকই ভেবেছিলাম। পরদিন সকালে হোটেল ম্যানেজারকে ক্যাসুয়াল ভঙ্গিতে আশ্রমটার নাম বলতেই আঁতকে উঠলেন, ‘ম্যাডাম মত যাইয়ে। ভেরি ডার্টি প্লেস। ওসব বিদেশিদের থেকে ডলার মারার জায়গা। রেগুলার পুলিস রেড হয়। আবার ঘুষ খেয়ে ছেড়ে দেয়।’ আশ্বস্ত করলাম তাঁকে, ‘আরে না না, ওসব জায়গায় আমাদের কী কাজ? একজন বলছিল, তাই জিজ্ঞেস করলাম।’ মনে মনে ভাবছি, ওই ঘণ্টাতিনেক সময়ের মধ্যে যদি পুলিশ আসত, কী কেলেঙ্কারিই না হত!

ফেওয়া লেক প্রথমেই এরকম একটা অস্বস্তিকর গল্প শোনালাম বলে ভাববেন না পোখরা জায়গাটা খারাপ। বরং ঠিক উল্টো। সাধে একে ‘জুয়েল অফ দা হিমালয়াস’ বলে! আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে বরফমোড়া অন্নপূর্ণা রেঞ্জ এমন স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইচ্ছে হবে একছুটে পৌঁছে যাই। তা যদিও সম্ভব নয়, তবে মাত্র আঠাশ-ত্রিশ কিলোমিটার দূরেই সেই স্বর্গীয় বিভা। আসলে অন্নপূর্ণা সার্কিটের গেটওয়ে পোখরা ট্রেকারদের স্বপ্নের জায়গা, যাকে বলে শাংগ্রি-লা, পৃথিবীর বুকে একটুকরো স্বর্গ। পোখরা সেই আশ্চর্য ট্যুরিস্ট স্পটগুলোর একটা যার নিজের উচ্চতা হাজার মিটারের কম হওয়া সত্ত্বেও ৬,০০০ মিটারের বেশি উচ্চতার পর্বতমালা ধরা দেয় খালি চোখে, সামনে কোনওরকম বাধা ছাড়াই। আর পোখরার ফেওয়া লেকে মচ্ছপুছরের মাছের লেজের মতো শৃঙ্গের ছায়া যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা যাঁরা অরোরা বোরিয়ালিস চাক্ষুষ করেছেন, তাঁদের থেকে কিছু কম নয় বলেই আমার ধারণা। চির-রহস্যময় মচ্ছপুছরে, যার শৃঙ্গজয় নিষিদ্ধ, কারণ নেপালিদের বিশ্বাস, মহাদেবের আবাস পবিত্র মচ্ছপুছরে-তে পা রাখা পাপ। তাই নেপাল সরকার সামিটের অনুমতি দেয় না। একবার একটি ব্রিটিশ পর্বতারোহী দল এই শর্তে অভিযান করেছিল যে, তারা শৃঙ্গ পর্যন্ত যাবে না। কথা রেখেছিল তারা। মাত্র দেড়শো ফিট আগে পতাকা পুঁতে নেমে এসেছিল।
ফেওয়া লেকে অনেকরকম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের ব্যবস্থা আছে। ক্যানোয়িং, কায়াকিং, প্যারাগ্লাইডিং ট্যুরিস্টরা, বিশেষ করে বিদেশিরা প্রাণ ভরে উপভোগ করে। আমরা অবশ্য একটা শিকারা টাইপের নৌকো ভাড়া করলাম। এমন সুন্দর স্বর্ণালী বিকেলে গান রেকর্ড করতে চাই, বলামাত্র মাঝি ধরল ‘রেশম ফিরি রি, রেশম ফিরি রি’। আশেপাশের নৌকোতে যত নেপালি ছিল, সবাই গলা মেলাল। নেপালের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকগীতি। মানে উতল হাওয়ায় উড়ছে রেশমি কাপড়। সব দেশেই বোধহয় মাঝিদের প্রিয় গান থাকে দু-চারটে। এপার-ওপার দুই বাংলাতেই নদীর বুকে গান রেকর্ড করতে গিয়ে দেখেছি, কী অনায়াসে বৈঠা বাইতে বাইতে খোলা গলায় ভাটিয়ালি কিংবা দেহতত্ত্বের গান ধরে মাঝিভাই। বৈঠার ছন্দে মিলে যায় গানের ছন্দ, জলের ছলাৎ ছলাৎ আর হাওয়ার শনশন শব্দের সঙ্গে সুর মিশে তৈরি হয় মনকেমনের তিস্তা। আরও অনেক জলভ্রমণের মতো এই যাত্রাতেও আমাদের আছে একটা গন্তব্য— ফেওয়া হ্রদের মাঝখানে একটা ছোট্ট দ্বীপে বরাহী মন্দির। তার আগে দেখছি, ক্যামেরার লেন্সে ঢাকনা পরাতেই পারছে না ক্যামেরাম্যান, এত অপূর্ব চারপাশ। দূরে পাহাড়ের সারি ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে, তাদের মাথায় আলতো কমলা আলো লেপ্টে আছে, ‘যেতে নাহি দিব’ শুনে যেমন থমকে যেতে হয়, যাব জেনেও।

বরাহী দেবতা এই বিশাল মিষ্টি জলের লেকটা আসলে প্রাকৃতিক হলেও পরে বাঁধ তৈরি করে এর জল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। কাচের মতো স্বচ্ছ জলের একটু নিচেই প্রচুর বড় বড় মাছ খেলা করছে। দ্বীপে যখন ভিড়ল নৌকো, তখনও দিনের আলো পুরোপুরি মরে যায়নি। ছোট মন্দির ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে। সামনে গম ছড়িয়ে পাখিদের খাওয়াচ্ছে কিছু লোক। মন্দিরের ভেতরে আলো-আঁধারিতে দেখলাম, বিগ্রহটি ভারি অদ্ভুত। মাতৃকা মূর্তির মুখটি বরাহের, দেহ নারীর। দুর্গার এক রূপ। শুনলাম, প্রতি শনিবার নাকি এখানে প্রচুর পাখি বলি হয়। নেপালে মন্দিরে-মন্দিরে এই পশুপাখি বলি ব্যাপারটা বন্ধ তো দূরের কথা, কমানোও যাচ্ছে না শত আন্দোলন, এমনকী, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেও।

গুপ্তেশ্বর মহাদেব মন্দিরের গুহা পোখরায় অনেক মন্দির, গুম্ফা আছে। বলতে গেলে মহাভারত হবে। শুধু দুটো অন্যরকম স্পটের কথা বলব। ডাভিস ফলস আর গুপ্তেশ্বর মহাদেব গুহা। পৃথিবীর বহু ঝরনায় আপনারা যেমন গল্প শোনেন, এখানেও প্রায় তাই। ১৯৬১ সালে এক সুইস দম্পতি আসেন পোখরার এই ঝরনা দেখতে। ঘটে যায় দুর্ঘটনা। ডাভি নামের শ্বেতাঙ্গিনী তীব্র স্রোতে ভেসে যান। তাঁর স্বামীর ইচ্ছেতেই নাকি এর নাম রাখা হয় ‘ডার্ভিস ফলস’। তবে মজার বিষয় হল, লোকের মুখে মুখে ‘ডার্ভিস’ হয়ে গেছে দেবীস। তাই অনেকে এই জলপ্রপাতের দৈব মাহাত্মেও বিশ্বাসী।
সে যাই হোক, তীব্র সেই জলধারা দেখার মতো। রেলিং ঘেরা ডেক থেকে দেখতে পাবেন, এর জল অনেকটা নিচে নদীর ধারার মতো বয়ে গিয়ে ঢুকে গেছে এক অন্ধকার গুহায়। তার নাম গুপ্তেশ্বর মহাদেব গুহা। ষোড়শ শতাব্দীতে নাকি এই গুহার সন্ধান পেয়েছিল স্থানীয় মানুষ। শিব, পার্বতী ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও নাকি ছিল গুহার ভেতর। নতুন সংযোজন দেখলাম মহাদেবের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে কামধেনু আর সুইচ টিপলে তার বাঁট থেকে দুধ ঝরে পড়ছে। কোনও মহাভক্তের দান হবে হয়তো! গুহার ভেতরটা খুব অন্ধকার, পায়ের নিচে জলস্রোত, ছাদ থেকে জল পড়ছে মাথায়, সিঁড়িগুলো মারাত্মক পিছল। চারপাশে গুম গুম জলের শব্দ, ভয় হবে, কখন না জানি পাথর ভেদ করে গোটা জলপ্রপাতটাই নেমে আসে গুহায়! আর এ তো ছোটখাটো গুহা নয়, প্রায় দু’হাজার মিটার লম্বা। দুটো ভাগ আছে। ভেতরের অংশে বর্ষাকালে ঢোকা বারণ। জলের উচ্চতা বেড়ে যায় তখন, ডুবে যেতে পারে মানুষ। এখান থেকে একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে সোজা জলপ্রপাতে। সেখান দিয়ে নামার সময় জলের যে ভয়ংকর শব্দ বুকের ভেতর ধাক্কা দেবে, সেটা সামলে গুহার সরু মুখ থেকে বেরিয়ে এবড়োখেবড়ো পাথরের ওপর সাবধানে পা ফেলে পৌঁছে যেতে পারেন ঝরনার কাছে, ধোঁয়ার মতো জলে ভিজিয়ে নিতে পারেন শরীর।
কিন্তু মনে রাখবেন, আবার ওই পাথরের ফাঁক গলে ঢুকে অন্ধকার গুহার ভেতর দিয়েই ফিরতে হবে পুরোটা পথ। দ্বিতীয় কোনও সহজ বেরনোর রাস্তা নেই। অতএব ‘জলাতঙ্ক’ থাকলে এতদূর না আসাই ভাল!
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook