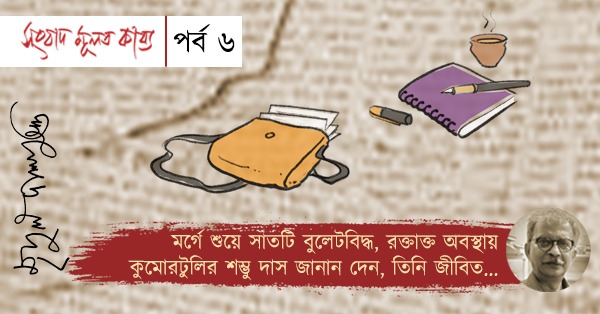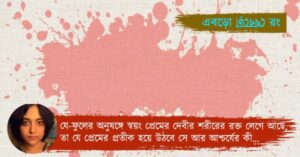‘আগামী’
আমাদের কালের রাজনীতিক অসীম চট্টোপাধ্যায় কারামুক্তির পর একটি লেখায় বলেছিলেন, ‘চারু মজুমদার আমাদের হাতে রং-তুলি ধরিয়ে দিয়ে একটি মস্ত বড় ক্যানভাসে রামধনুর ছবি আঁকতে দিয়েছিলেন। আমরা তা পারিনি, আমরা ভেঙে ফেলেছি চিত্রপটটি।’ আমি বলবই, রাজনীতিতে তা সম্ভব না হলেও, বাংলা কবিতায় আমার বন্ধুরা রামধনু এঁকে দিয়েছেন। সত্তর দশকের ওই সূচনা সময়েই, ১৯৭২/’৭৩ সালে কবিতা সিংহ সত্তর দশকের কবিদের একটি সংকলন সম্পাদনার কাজে হাত দেন। সংকলনটি বের হয় ১৯৭৪-এ। ‘সপ্তদশ অশ্বারোহী’ নামে সেকালে হইচই ফেলা ১৭ জন কবির কবিতার ওই সংকলনটির মুখবন্ধে কবিতা সিংহ আশা প্রকাশ করেছিলেন, এই সংকলনটির কবিদের তিন-চারজন কবি আগামীর বাংলা কবিতায় আলোকিত হয়ে উঠবেন। এখন, এই বয়সে, মনে হয়, তা ঘটেছে। আমি বলবই, আমার বন্ধুরা, অপরূপ। এই সংকলনে জ্বলজ্বল করছে অনন্য (রায়), তুষারদা (চৌধুরী)-র কবিতা। আছে ধূর্জটি চন্দর কবিতা, তিনজনই প্রয়াত হয়েছেন, অকালে। ধূর্জটিদার ‘এবং’ পত্রিকাতে আমার সাত কবিতা প্রকাশ হওয়ার পর, সেগুলি দেখেই কবিতা সিংহ আমার কাছে কবিতা চেয়েছিলেন। ‘সপ্তদশ অশ্বারোহী’ সংকলনটিতে তারকাপুঞ্জে আমার নিষ্প্রভ উপস্থিতি আছে।
উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজে ভর্তি হলাম। নতুন কবিতা লিখলেই সহপাঠী শুভ্র, উদয়, বিদ্যুৎ, শ্যামলী, আকবরদের পড়াতাম। উদয়, শুভ্রর কাছে এখনও আমার লেখা কবিতার একটি-দু’টি চিরকুট আছে, শুনেছি। পরে উদয় হাজরা আমাদের কলেজেই জীববিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হয়েছিল, শুভ্র মুখোপাধ্যায় ছিল হুগলি মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ। বিদ্যুৎও কলকাতায় কলেজে পড়াত।
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর থেকেই শ্রীরামপুরে সোমনাথদা, গৌতমদা, রমাদি এবং সমবয়সি পল্লব, দেবুদের সঙ্গে কবিতা নিয়ে মাতামাতি শুরু করায় শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরির তৎকালীন গ্রন্থগারিক সচ্চিদানন্দদা, সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য লাইব্রেরির ভেতরের একটি নিভৃত বড় ঘর খুলে দিয়েছিলেন। সেখানে মস্ত ওভাল টেবিল ঘিরে অনেক চেয়ার। আর চারিদিক কাঠের র্যাকে ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘মাসিক বসুমতী’, ‘কবিতা’, ‘দেশ’, ‘অমৃত’— এসব পত্রিকা সাজানো। চামড়া, রেক্সিনে বাঁধানো এসব পত্রিকা পাঠের স্মৃতি এই বয়সেও মনে ঝলমল করছে। রোজ বিকেল গড়ালে যেতাম লাইব্রেরির ওই আড্ডায়।
১৯৭০-’৭১-এ শ্রীরামপুরে বটতলায় এই শহরের প্রথম বহুতল আবাসনটি তৈরি হয়। তৎকালে আইনশৃঙ্খলা বলবৎ রাখতে ওই উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের আবাসন গড়া হয়েছিল। লাইব্রেরিতে আমাদের আড্ডা যখন জমজমাট, এক সন্ধ্যায় এলেন দুই তরুণী । একজন বুলাদি, তিনি এসেছেন বটতলার ওই আবাসন থেকে, এক পুলিশ অফিসারের মেয়ে। সঙ্গে তাঁর বন্ধু লিলিদি। দিন গড়াতে লাগল। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় বুলাদি সঙ্গে নিয়ে এলেন তুষার রায়কে। আমরা উল্লসিত হলাম। শুনলাম তুষারদা বুলাদিদের আত্মীয়। এরপর মাঝে মাঝেই আমাদের আড্ডায় এসেছেন তুষারদা, আমাদের বাড়িতেও এসেছেন। লাইব্রেরির আড্ডা থেকে আমাকে ও দেব গঙ্গোপাধ্যায়কে বিযুক্ত করে তুষারদা নিয়ে যেতেন ধাঙড় বস্তিতে, টিনবাজারের পানশালায়। আমাদের কবিতা শুনতেন। নিজের লেখা শোনাতেন: ‘দামী সাবান গায়ে ঘষে ঘষেও ফর্সা হতে পারছ না বলে দুঃখ? তাহলে কোমরে ব্লেড ঘুরিয়ে দু-হাতে গেঞ্জি তোলো চামড়ার/ অমনি বেরিয়ে পড়বে কী আশ্চর্য রং রক্তাভ…’
১৯৭১ সালে আমি যখন সবে কলেজে ঢুকেছি, সেই সময়ই সাত-গুলি শম্ভুর ঘটনাটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তা যেন এক রূপকথা। কুমোরটুলির নকশালপন্থী তরুণ শম্ভু দাস পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর পুলিশ তাঁকে লায়ালকার মাঠে নিয়ে গিয়ে পিছন থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি করে। এরপর রক্তাপ্লুত দেহটি নিয়ে গিয়ে মর্গে রাখে।
হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই, ১৯৭১ সালের ১২-১৩ আগস্ট কাশীপুর-বরানগর অঞ্চলে নারকীয় গণহত্যায় রাজ্যে ভয়াল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। দু’দিন ধরে ওই অঞ্চলে শাসক ও তাদের সহযোগীদের সশস্ত্র ঘাতক বাহিনী সঙ্গে পুলিশ নিয়ে শতাধিক নকশালপন্থী তরুণকে হত্যা করে। ওই অঞ্চলে বহু জন নিখোঁজ হন। বরানগর গণহত্যার কিছুদিনের মধ্যে কোন্নগরের নবগ্রামেও সাতটি মৃতদেহ পাওয়া যায় কিশোর-তরুণদের। রাজ্যের বেশ কয়েকটি কারাগারে রাজনৈতিক বন্দিহত্যারও ঘটনা ঘটে ওই সময়। ভুয়ো সংঘর্ষ বা ফেক এনকাউন্টারে বন্দিহত্যার ঘটনা ঘটত মাঝে মাঝেই। গ্রেপ্তার হওয়া বন্দিদের ছেড়ে দিয়ে পিছন থেকে গুলি করে মারার ঘটনা হয়ে উঠেছিল রীতি বা প্রথা। যাদবপুরের বাঘাযতীন পল্লির অদূরে লায়ালকা মাঠটি হয়ে উঠেছিল এক বধ্যভূমি।
ওই বাঘাযতীন পল্লিই ছিল বাংলা বিভাগ-পরবর্তী কালে আমাদের পরিবারের সদর। আমার বাবার কাকা সপরিবার থাকতেন বাঘাযতীন পল্লিতে। সেখানে বাল্যে বাঘাযতীনের কাজিপুকুরে আমি সাঁতার শিখেছি।

যা বলছিলাম, বাঘাযতীনের অদূরে লায়ালকা মাঠটি ছিল বধ্যভূমি। বলি তাহলে সাত-গুলি শম্ভুর কথা। ১৯৭১ সালে আমি যখন সবে কলেজে ঢুকেছি, সেই সময়ই সাত-গুলি শম্ভুর ঘটনাটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তা যেন এক রূপকথা। কুমোরটুলির নকশালপন্থী তরুণ শম্ভু দাস পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর পুলিশ তাঁকে লায়ালকার মাঠে নিয়ে গিয়ে পিছন থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি করে। এরপর রক্তাপ্লুত দেহটি নিয়ে গিয়ে মর্গে রাখে। ওই সময় সিপিআই সাংসদ অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আইনজীবীদের একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল। তাঁরা ভুয়ো সংঘর্ষের বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখতেন। ওই মর্গে গিয়ে যখন তাঁরা বুলেটবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহগুলি দেখছেন, তখন নড়েচড়ে শম্ভু বুঝিয়ে দেন, তিনি বেঁচে আছেন! হইহই পড়ে যায় হাসপাতালে! চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এই সংবাদ। আলোড়ন সৃষ্টি হয় চিকিৎসা-মহলে। শম্ভু দাসের চিকিৎসায় বসে মেডিকেল বোর্ড। সাতটি বুলেট বিঁধেছিল তাঁর দেহে। দেখা যায়, কোনও বুলেটই তাঁর শরীরের অভ্যন্তরের কোনও অঙ্গ (হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি) স্পর্শ করেনি। শরীরের ভেতরের ফাঁকা স্থানগুলি (ক্যাভেটি) ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। শম্ভু বেঁচে যান। কারাবাসের পর ১৯৭৭-’৭৮-এ মুক্ত হন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় ডোরিনা ক্রসিংয়ের পথসভায় মুরারীদা, যিনি কুমোরটুলির, এখন শ্রীরামপুরে থাকেন, আমার সঙ্গে শম্ভুদার আলাপ করিয়ে দেন। দীর্ঘকায় মানুষটিকে প্রণাম করি আমি। শুনেছি, বছরখানেক আগে প্রয়াত হয়েছেন শম্ভুদা।
বরানগরের গণহত্যার খবর পেয়ে আমরা একেবারে নড়েচড়ে বসেছিলাম। খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম তুষারদা, ভাস্করদা, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্য। অলোকনাথ আমার সমসাময়িক কবি, সে ছিল ভাস্করদার খুবই ঘনিষ্ট। সদ্য ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছিল সে। লাইব্রেরির আড্ডায় বেশ কিছুদিন তুষারদা না আসায় আমাদের উদ্বেগ যথেষ্ট বেড়ে গেল। সে-যুগে ছিল না মোবাইল ফোন, বাড়িতে বাড়িতে ল্যান্ডফোনও ছিল না। বিপদের ঝুঁকিতে আমাদের কেউ বরানগরে খোঁজখবর নিতে রাজি হল না।
আমি এবং আমাদের সমকালীন বন্ধুরা ওই সব আগুনের ভেতর থেকে ভস্ম মেখে বেরিয়ে এসেছি।
বরানগরের গণহত্যার খবর পেয়ে আমরা একেবারে নড়েচড়ে বসেছিলাম। খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম তুষারদা, ভাস্করদা, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্য। অলোকনাথ আমার সমসাময়িক কবি, সে ছিল ভাস্করদার খুবই ঘনিষ্ট। সদ্য ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছিল সে। লাইব্রেরির আড্ডায় বেশ কিছুদিন তুষারদা না আসায় আমাদের উদ্বেগ যথেষ্ট বেড়ে গেল। সে-যুগে ছিল না মোবাইল ফোন, বাড়িতে বাড়িতে ল্যান্ডফোনও ছিল না। বিপদের ঝুঁকিতে আমাদের কেউ বরানগরে খোঁজখবর নিতে রাজি হল না । সেসময় হুট করে ‘দেশ’ পত্রিকায় একসঙ্গে অলোকনাথের দু’টি কবিতা প্রকাশ হওয়ায় আমাদের দুর্ভাবনা বেড়ে গেল।
অবশেষে এক সন্ধ্যায় তুষারদা এসে সবার খবর দিলেন, সন্দীপন, ভাস্করদার খবরে স্বস্তি পেলাম, কিন্তু যেই বললেন, অলোকনাথের কোনও খোঁজ নেই, মন হায় হায় করে উঠল।
মাসকয়েক বাদে পাশের পাড়ার সুনীল, যার ডাকনাম প্রিন্স, আমাকে জানাল, ব্যাঙ্কে অলোকনাথ তাঁর সহকর্মী। অলোকনাথ আমাকে জানাতে বলেছেন, বরানগর ছেড়ে ইছাপুরে চলে এসেছেন তাঁরা। পরে বরানগরের বাড়িটি তাঁর বাবা বিক্রি করে দিয়েছেন। প্রিন্সের মাধ্যমে অলোকনাথদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল।
জরুরি অবস্থার পর, ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের সময় সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট তার নির্বাচনী ইস্তাহারে কাশীপুর-বরানগর গণহত্যা, বারাসত গণহত্যা, নবগ্রাম গণহত্যা এবং কারাগারগুলিতে বন্দিহত্যার তদন্ত ও শাস্তিবিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। হা হতোস্মি! কমিশন বসিয়েও তার রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হয়নি। ওই একই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও পরবর্তী সরকারের কাছে তা আশা করা যায় না।
‘সংবাদ মূলত কাব্য’— বিষ্ণু দে-র কাব্যপংক্তিটি তখনও রচিত না হলেও, হয়তো হাওয়া-বাতাসের ভেতরে ছিল। বরানগরের ওই গণহত্যায় ব্যথিত মনে আমি ‘আগামী’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটি আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘জলপাইকাঠের এসরাজ’-এ আছে।
নব্বই দশকের গোড়ার দিকে, সৌম্য, যার কলেজি নাম তথাগত দাশগুপ্ত, এখন আমেরিকায় আছে, সে আমাকে তাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে নিয়ে যায়। সেখানে একটি ক্লাসঘরের দেওয়ালে সে দেখিয়েছিল, আমার ‘আগামী’ কবিতার লাইন লেখা রয়েছে, তুলির বড় বড় হরফে :
‘ভাবো, সেদিনের উৎসব/ বরানগরের গঙ্গার জল থেকে আবার এসেছে উঠে/ তিনশো তরুণ…’