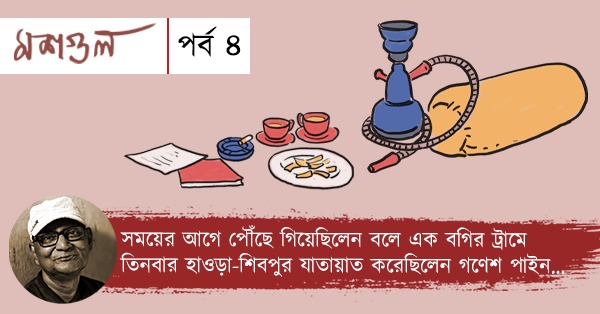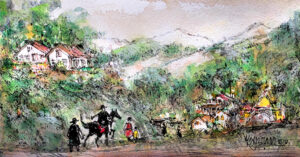গণেশ পাইনের সঙ্গে…
গণেশ পাইনের কথা বলতে গেলে বলাইদাকে না ছুঁয়ে এগনোর উপায় নেই। বলাইদা, পোশাকি নাম সৌরেন মিত্র, গল্পকার, ছবি আঁকিয়ে, পরবর্তীকালে ‘পরিবর্তন’ পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ছয়ের দশকের শেষের দিকে, আমি হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়ে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছি। করছি আর কবিতার মধ্যে ক্রমশ সেঁধিয়ে যাচ্ছি, আঞ্চলিক একটি কবিতা পাঠের আসরে আমার কবিতা কীভাবে যেন বলাইদাকে স্পর্শ করে। তিনি বাজার যাওয়ার পথে আমাকে ডাকেন, তাঁর ভাললাগা জানান আর তাঁর কাজের জায়গায় মাঝেসাঝে আসতে বলেন। সেদিন বুঝিনি, পরে ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছি— কী একটা এলেবেলে কবিতা আমাকে সারাজীবনের জন্য, এক স্নেহশীল, নানা বিষয়ে পড়াশোনা করা এক নির্মলহৃদয় দাদাকে পাইয়ে দিয়েছিল। বলাইদার কাজ তখন ডাঃ মানিক পালের কম্পাউন্ডারি। বেলা বারোটা নাগাদ ডাক্তারবাবু কলে বেরিয়ে গেলে ডাক্তারবাবুর ছড়ানো চেম্বারের একপ্রান্তে আমাদের আড্ডা চলে। মাঝে মাঝে কেউ এসে ইঞ্জেকশন নিয়ে যায়।
একদিন দেখি, বলাইদা চাইনিজ ইঙ্কে ছবি আঁকছেন। সেই ছবির কোনও কোনও জায়গায় ব্যান্ডেজের ইঙ্ক লাগিয়ে ছবির ওপর চেপে ধরে অদ্ভুত এচিংয়ের এফেক্ট নিয়ে আসছেন। সেদিন ছবি নিয়ে কথা হল। বলাইদার আবাল্য স্বপ্ন ছিল, আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার। বাবার অকালে হারিয়ে যাওয়ার ফলে দিদি-ভাই-বোন এবং মায়ের দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ায় দিশাহারা বলাইদা বন্ধুবান্ধব এবং স্বয়ং ডাক্তারবাবুর পরামর্শে শর্ট কোর্স করে ডাঃ মানিক পালের কম্পাউন্ডারের পদে যোগ দেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমিত আর্ট কলেজে ভর্তি হয়। বলাইদা তাই চেম্বার বন্ধ হওয়ার পর নাকেমুখে গুঁজে ছোটেন আর্ট কলেজে। অমিতের সূত্রে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়। তাদের একজন গণেশ পাইন। বলাইদা আর্ট কলেজের বিশাল চত্বরে ঘুরে বেড়ান আর মাস্টারমশাইদের উড়ে আসা শিক্ষা আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করেন। এইরকমই একদিন, ক্লাসের বাইরে বলাইদাকে দেখে শিক্ষক স্পষ্টতই বিরক্ত হন, এবং ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলাইদাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন ও ক্লাসের দরজা বন্ধ করিয়ে দেন। বলাইদার এই লাঞ্ছনা বন্ধু অমিতকে তো বটেই, গণেশ পাইনকেও খুব আহত করে। সেদিন থেকেই বলাইদা ঢুকে পড়েন গণেশ পাইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবৃত্তে।
আরও পড়ুন : কফিহাউসের আড্ডায় পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল শুরু করেছিলেন দেশলাই খেলা! পড়ুন গৌতম সেনগুপ্তর কলমে মশগুল পর্ব ৩…
এরপর কেটে গেছে বেশ কিছু দিন। ওঁদের সখ্য বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকটাই। আমাদের তৎকালীন জ্ঞানবুদ্ধির মানচিত্রে গণেশ পাইন ছিলেন না। গল্পে গল্পে গণেশ পাইনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। গণেশ পাইনের আঁকা ছবিও দেখলাম। গণেশ পাইনের ছবি আমাকে টানছিল ভেতরপানে। বলাইদা একদিন আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ৩/১ কবিরাজ রো-তে। গণেশ পাইনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হল। গণেশ পাইন হলেন, গণেশদা। ওঁর নরম স্বভাব, স্নিগ্ধ কথাবার্তা আর স্নেহপরায়ণতা আমাকে অনেকটাই কাছে টেনে নিল। আবার আসতে বললেন। কয়েকবার দেখা হওয়ার পর ওঁকে একটা প্রচ্ছদ এঁকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম, আমাদের আরেক দাদা ত্রিদিব মিত্রর প্রথম বই ‘প্রলাপ দুঃখ’-র। চমৎকার প্রচ্ছদ হল। ত্রিদিবদা খুব খুশি। ত্রিদিবদা ও তাঁর স্ত্রী আলো মিত্রর সঙ্গে পরিচয় হল গণেশদার। ত্রিদিবদার পরবর্তী বই ‘ঘুলঘুলি’-রও প্রচ্ছদ এঁকে দিলেন গণেশদা।

এইসব প্রচ্ছদের সূত্রে গণেশদার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আরও গাঢ় হল। স্বল্পকালীন আড্ডাও হত মাঝে-মধ্যে। এর কয়েকবছর পর যখন আমাদের কাগজ ‘উলুখড়’ শুরু হল, তার দ্বিতীয় সংখ্যায় সৌরেন মিত্র লিখলেন গণেশ পাইনের ওপর পূর্ণাঙ্গ একটি প্রবন্ধ। আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে, এককভাবে শুধু গণেশদার ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ সম্ভবত সেই প্রথম। আমরা তখন জানি, বসন্ত কেবিনে গণেশদাকে ঘিরে একটা আড্ডা বসে। সেই আড্ডায় শিল্পী, গল্পকার, পত্রিকার সম্পাদকরা শামিল হন। আমরা আড্ডা মারতাম পাশের নীলিমা কেবিনে।
প্রথম প্রথম যখন গণেশদার সঙ্গে পরিচয় হয়, আমরা তাঁর ধার ও ভার বুঝতাম না। ধীরে ধীরে তাঁর সম্পর্কে পড়ে, ছবি দেখে তাঁর সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা হয়। তবে গণেশদার সঙ্গে কথা বলার সময় ওঁর দিক থেকে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ ছিল না। গণেশদার কাজের জায়গা ছিল মন্দার মল্লিকের স্টুডিও। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে, দরজার কাছে দাঁড়ালে তিনি তর্জনী দিয়ে নিচের দিকে দেখাতেন। নিচে ছিল এক চায়ের দোকান। রামকৃষ্ণ টি শপ গোছের নাম। আমরা, আমি ও প্রিতম সেখানে বসতে না বসতেই গণেশদা নেমে আসতেন। চা-টোস্ট খেতে খেতে গণেশদা আমাদের সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। কোনও কোনও লেখক বা কবিকে নিয়ে আমাদের মতামত। আর আমরা কোথাও বেড়াতে গেলে তো কথাই নেই। তাঁর আদ্যোপান্ত কৌতূহল! গণেশদা প্রশ্ন করতেন, উত্তর শুনতেন মন দিয়ে, কিন্তু নিজের কথা বেশি বলতেন না। সম্ভবত, আমাদের ততটা যোগ্য মনে করতেন না। গণেশদার হাঁটা, কথা বলার ধরন আমরা খুঁটিয়ে লক্ষ করতাম। আশ্চর্য পরিশীলতায় মোড়া ছিল তাঁর জীবনটা। সেইসময় গণেশদা সিগারেট খেতেন এবং ধোঁয়া ছাড়তেন মাথা নিচু করে নিজের বুকের দিকে।
শুধু কথা বলা নয়, অনেকসময় আমরা অল্প দূর থেকে গণেশদাকে লক্ষ করতাম। ভাল লাগত। সন্ধেবেলা কবিরাজ রো থেকে বেরিয়ে ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত নাতিদীর্ঘ শিল্পী নাতি-মন্থর, নাতি-দ্রুত চলনে হেঁটে যেতেন। যেন আড়াল থেকে খুঁজে নিচ্ছেন তাঁর শিল্পের দানা।
একবার আমাদের প্রেসের অমলদা কিছু টাকা সেদিনই দিতে বললেন। কখনও তিনি টাকা চাইতেন না, চাইলেন যখন, তখন নিশ্চয়ই খুব দরকার। আমরা একটু বিপদে পড়লাম। বেশি টাকা নয়, কিন্তু সে-টাকাও তখন বেকার আমাদের কাছে ছিল না। কী করি ভাবতে ভাবতে সেই মন্দার মল্লিকের স্টুডিও, সেই রামকৃষ্ণ টি শপ। গণেশদাকে বলতে তিনি টাকাটা এমনভাবে বের করে দিলেন, যেন তিনি অনেকদিন আগে ধার নিয়েছিলেন, দিতে দেরি হল বলে আমরা যেন কিছু মনে না করি!
ওই দোকানেই একবার কথা বলতে বলতে আমাদের শিবপুরের এক বগির ট্রামের কথা ওঠে। এক বগির ট্রাম মানে, সেই ট্রাম ঘোরানোর জায়গা না থাকায় দু’দিকে দুটো ড্রাইভারের কেবিন। গন্তব্যে পৌঁছে ড্রাইভার সামনের কেবিন থেকে বেরিয়ে পিছনদিকের কেবিনে চলে আসত। তখন সেটাই সামনের কেবিন। নিয়মিত শিবপুর ট্রাম ডিপো থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাতায়াত করত সেই ট্রাম। শুধু সকাল আর বিকেলে দু’বার ডালহৌসি এবং ফেরত। ওই এক বগির ট্রামের কথা গণেশদা নাকি জানতেন না! এই ট্রামের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী হয়ে পড়লেন তিনি। ঠিক হল, পরের রবিবার তিনি ওই ট্রামে চেপে হাওড়া থেকে শিবপুরে আমাদের বাড়ি যাবেন। আমরাও খুব আহ্লাদিত! গণেশ পাইন আসবেন ‘উলুখড়’-এর সদর দপ্তরে। চারটে নাগাদ উনি আসবেন। আমরা চারটের একটু আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছি শিবপুর ট্রাম ডিপো-তে। যখন পৌঁছই, তখন ডিপো-তে ট্রাম ছিল না। ট্রাম এল, গণেশদা নামলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোনও অসুবিধে হয়নি তো?’
গণেশদা উত্তর দিলেন, ‘না না! একটু আগে এসে পড়েছিলাম, তখন তোমাদের আসতে অনেক দেরি, তাই রাস্তায় অপেক্ষা না করে, ওই ট্রামে চেপেই তিনবার হাওড়া-শিবপুর করলাম। বুঝলে, বেশ মজা লাগল!’
এই হল গণেশদা! বলা হয়নি আগে, গণেশদা ছিলেন ‘উলুখড়’-এর প্রথম স্বতঃপ্রণোদিত গ্রাহক।
শুধু কথা বলা নয়, অনেকসময় আমরা অল্প দূর থেকে গণেশদাকে লক্ষ করতাম। ভাল লাগত। সন্ধেবেলা কবিরাজ রো থেকে বেরিয়ে ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত নাতিদীর্ঘ শিল্পী নাতি-মন্থর, নাতি-দ্রুত চলনে হেঁটে যেতেন। যেন আড়াল থেকে খুঁজে নিচ্ছেন তাঁর শিল্পের দানা। আমরা জানতাম, এইসময় তাঁর মুখোমুখি হওয়া, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায় না। একদিন কে যেন, হয়তো প্রিতম, বলেছিল, ‘মনে হয়, জীবনানন্দ বেরিয়েছেন পথ পরিক্রমায়।’
২
শৈবালকে যে বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম, তাতে গণেশদার ভূমিকা ছিল প্রবল। আবার শৈবালের সূত্রেই গণেশদার সঙ্গে ফিকে হয়ে যাওয়া সম্পর্কটা আবার পোক্ত হল। শৈবাল সময়সুযোগ পেলেই গণেশদার সঙ্গে আড্ডায় বসত, আর আমাকে এসে সেই আড্ডার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিত। আমার লেখা নিয়ে শৈবালের বেশ বাড়াবাড়ি রকমের ভালবাসা ছিল। সেইসব কবিতার কিছু কিছু গণেশদাকে শুনতে হত। এইভাবে, পরোক্ষভাবে গণেশদার সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হল। গণেশদার সিনেমা নিয়ে আগ্রহের কথা সবাই জানে। মাঝে মাঝে শৈবাল ভাল সিনেমা দেখাতে গোর্কি সদনে বা নন্দনে নিয়ে আসত গণেশদাকে। তখন, সিনেমার শেষে চা খেতে খেতে কথাবার্তা হত গণেশদার সঙ্গে। সেবার, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে বেশ কিছু টিকিট হস্তগত হয়েছিল বুদ্ধদা (বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত)-র সৌজন্যে। বার্গম্যানের রেট্রোস্পেকটিভের বেশ কিছু ছবি আমি আর গণেশদা দেখেছিলাম। ছবি দেখার পর গণেশদা ছবি সম্পর্কে তাঁর কিছু কিছু অনুভূতির কথা বলতেন। শুনতে খুবই ভাল লাগত, এক মহান শিল্পীর মুখে অন্য মাধ্যমের আরেক শিল্পীর শিল্পকর্মের আলোচনা।
এই সময়ে আমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। সবাই জানে, চলচ্চিত্র উৎসব তখন থেকেই সারা কলকাতার বিভিন্ন সিনেমা হলে ছড়িয়ে দেওয়া হত। আমরা ওরিয়েন্ট সিনেমা হলে একটি পোলিশ ছবির পাস পেয়েছিলাম। শৈবাল সেদিন যেতে পারেনি। গণেশদার সঙ্গে কথা হল, যে আগে আসবে, সে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়বে। আমি গিয়ে দেখি, গণেশদা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলে রেখেছেন যে, ওঁর পিছনে আরেকজন আছেন। আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এ-পর্যন্ত ঠিকই ছিল। একটু পরে এলেন বিকাশ ভট্টাচার্য, এবং তিনিও এসে গণেশদাকে দেখে আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। সিনেমাটা ভীষণ ভাল ছিল, নাম মনে পড়ছে না। সিনেমা দেখব কী! আমার একপাশে গণেশ পাইন, অন্যপাশে বিকাশ ভট্টাচার্য!
একদিন শৈবাল এসে বলল, ‘অরণি, দোলের আগের সন্ধেবেলা কবিতার আসর বসবে আমাদের বাড়িতে। গণেশদা আপনার কবিতা শুনবেন।’
গণেশদার জন্য কষ্ট হল। নিশ্চয়ই শৈবাল গণেশদাকে জপিয়েজাপিয়ে রাজি করিয়েছে। কী আর করেন গণেশদা, অগত্যা!
শৈবাল তখন একটা গাড়ি কিনেছিল। সেই গাড়িতে কবিরাজ রো থেকে গণেশদাকে তুলে মিন্টো পার্কের কাছে আমার অফিস থেকে আমাকে নিয়ে চলল সরশুনা। ওর বাড়ি। নানা বিষয়ে গল্পগাছা হল, জলখাবার হল। মালবিকার হাতে জাদু আছে!
অতঃপর কবিতা! বেশ কিছু কবিতা পড়েছিলাম। কবি একজন, শ্রোতা দু’জন। অবশ্য একজন ফ্লাইং শ্রোতাও ছিল, মালবিকা ঘোষ। আবার খাওয়াদাওয়া। যখন আসর সাঙ্গ হল, তখন রাত দশটা। একজন ফিরবে কবিরাজ রো, আরেকজন হাওড়া-শিবপুর। বিদ্যাসাগর সেতু তখনও নির্মীয়মান!
শৈবাল প্রথমে বলল, ‘থেকে যান আপনারা!’ কাজ হল না, তখন বলল, ‘চলুন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।’ শেষপর্যন্ত রফা হল, ও আমাদের চৌরাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেবে, ওখান থেকে আমরা ট্যাক্সি ধরে চলে যাব।
রাতের শহরের একটা আলাদা আবেদন আছে। কথা বলতে বলতে আসছিলাম। একটা কথাই স্পষ্ট মনে আছে। গণেশদা প্রশ্ন করেছিলেন, ‘অরণি, তোমার উপন্যাস লিখতে ইচ্ছে করে না?’ উত্তরটাও মনে আছে। বলেছিলাম, ‘না, এখনও না।’ নির্জন, জনবিরল ধর্মতলায় এসে গণেশদা বললেন, ‘চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।’ আমি তীব্র আপত্তি করে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লাম। কী জানি, কোন পুণ্যের ফলে বাড়ি ফিরতে অসুবিধে হয়নি। শুধু রাত্তির হয়েছিল অনেকটা, আর সে তো আমার হয়েই থাকে।
৩
শৈবাল আকস্মিকভাবে চলে গেল ২০০০ সালে। গণেশদা মধ্য কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন দক্ষিণে। যোগাযোগ প্রায় শূন্য। ক্বচিৎ-কদাচিৎ কোনও সভায় বা প্রদর্শনীতে দেখা হত।
২০১০ সালে ‘উলুখড়’ পত্রিকার একাদশ সংকলনের ক্রোড়পত্র হল গণেশ পাইন। গণেশদার চিঠি। সৌরেনদাকে লেখা চিঠির সঙ্গে আশ্চর্য সব ছবি। যে ছবি আগে দেখার সম্ভাবনা ছিল না কারও। গণেশদার ছবি নিয়ে দীর্ঘ, অসাধারণ প্রবন্ধ লিখলেন সৌরেন মিত্র, বলাইদা।