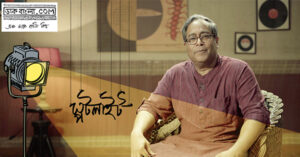রবিঠাকুরের খোঁজে
এপ্রিলে এত ঠান্ডা ভাল লাগে বাঙালির? ভাবা যায়, নববর্ষের সাজে জামদানি, কাঁথা স্টিচের ওপর চাপানো ভুটকো কোট আর মাথায় উলের টুপি? ২০২৪-এর এপ্রিল মাসে রেকর্ড ঠান্ডা পড়েছিল লন্ডনে। তার সঙ্গে ফ্রি সম্বৎসরের লন্ডন-স্পেশাল মেঘলা আকাশ আর টিপটিপ বৃষ্টি। ওখানকার বাসিন্দারাই বিরক্ত তো আমরা যারা কলকাতাইয়া ঘেমো গরমে এসির বিলাসেও অস্থির থাকি, তাদের অবস্থা ভাবুন! সে যাই হোক, শহরটি যে চমৎকার, তা আর আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে এপ্রিলে বাকিংহামের রাজপ্রাসাদ থেকে পাড়ার পার্ক সর্বত্র টিউলিপের রংবাজি, ফুটবল স্টেডিয়ামের সামনের রাস্তায় দলের ফ্ল্যাগ নিয়ে মাতামাতি, দেড়শো পেরনো পাতালপথে টিউব স্টেশনে অকস্মাৎ ভিক্টোরীয় আমেজ— সব মিলিয়ে দিব্যি একটা রোম্যান্টিসিজম জড়িয়ে থাকে সারাক্ষণ। কিন্তু বাঙালি যেখানে যায়, রবিঠাকুরের ছোঁয়া চায়। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তিতে তাঁর বিলেত-বাড়ির যা ভূমিকা, তাতে একে তীর্থক্ষেত্র বললে কম বলা হয়। লন্ডনের শহরতলি হ্যাম্পস্টেড যথেষ্ট বিখ্যাত, তবে ‘তত বিখ্যাত নয় এ হৃদয়পুর’ মানে রবিঠাকুরের বাসাটি, সেটা টের পেলাম কিছুটা খোঁজখবরের পরই। এই বিদেশবিভুঁইয়ে অত যে সহজ নয় সেখানে পৌঁছনো, বুঝলাম পথে নেমে, বা বলা ভাল ভূগর্ভে নেমে।
আমার যেমন স্বভাব, কনফিডেন্টলি ভুল কথা বলা! বিশেষ করে ঠিকানা বা দিকনির্দেশের ব্যাপারে। এরকম অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে, তারা অনেকেই পরবর্তীকালে আমার সফরসঙ্গী হতে অস্বীকার করে। টিউবের ম্যাপে হ্যাম্পস্টেড ওয়েস্ট নামের একটি স্টেশন দেখে সঙ্গে থাকা মেয়ে আর এক ভাইকে বললাম, এই তো পেয়ে গেছি, চল আমরা চট করে হ্যাম্পস্টেড ঘুরে আসি। আমার মেয়ে সেই চটজলদি টিপসে এতটুক কান না দিয়ে গুগল ম্যাপ খুলল। এবং আবিষ্কৃত হল, হ্যাম্পস্টেড ওয়েস্ট-এর সঙ্গে আদৌ হ্যাম্পস্টেডের কোনও সম্পর্ক নেই। পুরো জল আর জলপাই কেস! বিকেল চারটে বাজে। সেটা অবশ্য কোনও ব্যাপার না, কারণ সন্ধে নামতে অন্তত আটটা। সদ্য বেরিয়েছি ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম দেখে। লন্ডনের হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি এলাকা। জানলাম, সাউথ কেনসিংটন টিউব স্টেশন থেকে পিকাডিলি লাইনে লেসেস্টার স্কোয়ার স্টেশনে যেতে হবে, আবার সেখান থেকে ধরতে হবে নর্দার্ন লাইনের ট্রেন, সেটা নিয়ে যাবে হ্যাম্পস্টেড। শুনতে যতটা জটিল মনে হল, তা কিন্তু মোটেই নয়। লন্ডনের লাইফলাইন এই টিউব এমনভাবে জাল বিছিয়েছে পাতালে যে কম খরচে, কম সময়ে, কম ঝকমারিতে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যায়। আসলে গণ পরিবহণ ব্যবস্থাটা এতই স্বস্তির যে, বিকল্প ভাবে না কেউ; বিশেষ করে লন্ডনের বিখ্যাত জ্যামের কথা মাথায় রেখে। আর উবেরের অবিশ্বাস্য ভাড়ার কথা নাই-বা বললাম!
মেঘছেঁড়া আলো গায়ে মেখে যখন দাঁড়ালাম হ্যাম্পস্টেড স্টেশনের সিঁড়িতে, ততক্ষণে মন ভাল হয়ে গেছে। গেটের মুখে লেখা কিটসের কবিতার লাইন। আসলে এই নিরিবিলি অভিজাত এলাকায় যে শুধু রবীন্দ্রনাথকে বাড়ি খুঁজে দিয়েছিলেন বন্ধু রদেনস্টাইন তা নয়, বিভিন্ন সময়ে এখানে থেকেছেন কিটস থেকে ডি এইচ লরেন্স— সাহিত্যের বহু নক্ষত্রই। শিহরন জাগল। এই টিউব স্টেশন, এই পাথর-বাঁধানো রাস্তায় পা রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ; সঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রবাস বাড়ির ঠিকানা থ্রি ভিলাস অন দ্য হিথ, ভেল অফ হেলথ, লন্ডন এন ডব্লিউ খ্রি। আবার গুগল ম্যাপের শরণাপন্ন। হাতে মোবাইল নিয়ে আমার মেয়ে হাঁটতে লাগল, পিছনে আমরা। হাঁটছি আর ভাবছি, এই টিউব স্টেশন তো তখনও ছিল। বিশ্ব ঘুরে আসা রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদেশের মাটি, চারপাশে সাহেব-মেমের দল বা পাতালরেল ভ্রমণ, কোনওটাই অচেনার আনন্দ নয়। বরং সেই সফরে তিনি সম্ভবত কিছুটা টেনশনে, কারণ সঙ্গে এনেছেন ইংরেজি অনুবাদে ‘গীতাঞ্জলি’র পাণ্ডুলিপি। বন্ধু স্যর উইলিয়াম রদেনস্টাইন কথা দিয়েছেন, আইরিশ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটসকে দিয়ে লিখিয়ে দেবেন জম্পেশ ভূমিকা। নোবেলের সম্ভাবনা অবশ্য তখন ‘দূর গগনের তারা’। টেনশন তুঙ্গে উঠল যখন আবিষ্কার করা গেল, পুত্র রথী সেই অমূল্য ধনসমেত অ্যাটাচিটি ফেলে এসেছেন টিউবের কামরায়। রবীন্দ্রনাথ তো নিজেই লিখেছেন, ‘যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কতকাল’, তাই মনে হয় আমজনতার মতো উত্তেজিত হয়ে হায়-হায় তিনি করেননি সেই মুহূর্তে। স্বস্তির কথা, সেই অ্যাটাচিটি পাওয়া গেল দিন দুয়েক পরে লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডের লস্ট প্রপার্টি অফিসে। আমার তো মনে হয়, সেই ফিরে পাওয়ার দিনটি উদযাপন করা দরকার বিশেষভাবে, কারণ ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি আসলে এশিয়া মহাদেশের প্রথম নোবেল। যদিও আমরা সেই ঐতিহাসিক সম্পদ রক্ষা করতে পারিনি, সেটা অন্য প্রসঙ্গ।
একটা প্রাইভেট প্যাসেজের শেষে গথিক স্থাপত্যের সাদা ভিলা, ভিক্টোরীয় আমলের মতো বড়-বড় সাদা জানালা, বিশাল নীল সদরদরজা। ওই দরজা আমাদের জন্য খুলবে না জানি, কারণ এই বাড়িটির বর্তমান মালিক পছন্দ করেন না রবীন্দ্রনাথের নাম করে এসে ভেতরে ঢুকতে চাওয়া, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গান গাওয়া, ওঁর ‘প্রাইভেসি’তে ব্যাঘাত ঘটানো।
টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাঁটছি পাথুরে ফুটপাথ ধরে। চওড়া রাস্তার দু’ধারে সারি-সারি আঠারো শতকের লাল ইটের বাড়ি। কোনওটার নীচে ঝলমলে ফুলের দোকান, কোনওটার-বা আধুনিক ক্যাফে। কী ভেবে একটা বাড়ির বাগান থেকে রাস্তায় উপচে আসা নাম-না-জানা গাছের লাল টুকটুকে একটা ফুল পাড়লাম। যদি অঞ্জলি দেওয়ার সুযোগ পাই! আধ মাইল মতো হেঁটে খুব পুরনো গির্জা পেরিয়ে ডানদিকে একটা গলি। চিনতে অসুবিধা হবে না, মুখেই পাঁচিলের গায়ে লেখা— হ্যাম্পস্টেড স্কোয়্যার এন ডব্লিউ থ্রি। বুকের ধুকপুক বেড়ে গেছে। শেষপর্যন্ত তাহলে আমরা পৌঁছতে পারলাম সেই তীর্থে! এখনও অবশ্য বেশ কিছুটা হাঁটা বাকি। একটা বড় রাস্তার ক্রসিং পড়ল, সেটা পেরিয়ে এবার ম্যাপে দেখাচ্ছে বাঁ-দিক। আহা! কী অসাধারণ সেই বনপথ! চড়াই-উতরাই পেরিয়ে একটু হাঁফ ধরেছে ঠিকই, কিন্তু প্রাণসখার অভিসারে ‘অগম পারে’ চলে যাওয়া যায়, এ তো সামান্য ছায়াঢাকা সবুজ পথ। একটু আগেও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই ভেজা পাতা থেকে টুপটাপ জলের ফোঁটা করছে মাথায়। ওই তো একটা প্রাইভেট প্যাসেজের শেষে গথিক স্থাপত্যের সাদা ভিলা, ভিক্টোরীয় আমলের মতো বড়-বড় সাদা জানালা, বিশাল নীল সদরদরজা। ওই দরজা আমাদের জন্য খুলবে না জানি, কারণ এই বাড়িটির বর্তমান মালিক পছন্দ করেন না রবীন্দ্রনাথের নাম করে এসে ভেতরে ঢুকতে চাওয়া, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গান গাওয়া, ওঁর ‘প্রাইভেসি’তে ব্যাঘাত ঘটানো। ঘাড় উঁচু করে দেখলাম, দোতলায় লাগানো ব্লু প্লাক— Rabindranath Tagore (1861-1941) Indian poet stayed here in 1912. লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের স্বীকৃতি এই ব্লু প্লাক লাগানো হয় দেশি-বিদেশি বিশিষ্টজনেদের বাসভবনে। যেমন আছে ভগিনী নিবেদিতা, নীরদ সি চৌধুরী বা আরও বহু হেরিটেজ তকমার বাড়িতে।
আমরা যথাসম্ভব নীচু গলায় কথা বলছিলাম। ভেতর থেকে পোষ্যের গুরুগম্ভীর ডাক শোনা যাচ্ছে। এই ভর বিকেলেও চারপাশ একেবারে নিঝুম। ধনী ও সংস্কৃতিবান লোকেদের বাস এই এলাকায়। কোলাহল তো দূরের কথা, পথেঘাটে মানুষের দেখা পাওয়াই ভার। আলো কমে আসছে। দু’দণ্ড বসলাম সিঁড়িতে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কবি কি এখানে বসেই রাতের আকাশের দিকে চেয়ে লিখেছিলেন, ‘আজি যত তারা তব আকাশে। সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে’? কী জানি! শুধু এটুকু তথ্য লেখা আছে বইতে, ওই গানটি এই হ্যাম্পস্টেডে থাকার সময়ে রচিত। আবার ঝিরিঝিরি বারিধারা, তার মধ্যেই হাতে ধরে রাখা ফুল রাখলাম চওড়া রেলিঙে। চোখ ভরে এল জলে, ফিসফিস করে বললাম, ‘যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে/মিলাব তায় জীবনগানে’। আমার বিশ্বাস, যেদিন লন্ডনে বিদ্বজ্জন সভায় পড়া হয়েছিল ‘গীতাঞ্জলি’, সেদিনও এমনই আবেগে ভেসে গেছিলেন নামকরা কবি-সাহিত্যিকেরা। নয়তো এক অশ্বেতাঙ্গের নাম কি তাঁরা সুপারিশ করতেন নোবেল পুরস্কারের জন্য? পরাধীন, গরিব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে যে-ভারতবর্ষকে তাঁরা চেনেন, সেখানকার এক অখ্যাত, অজ্ঞাত কবির এই জীবনবোধ, এই ভাষা, এই ব্যঞ্জনা?
লন্ডনের গোধূলি দীর্ঘস্থায়ী। তা বলে রোদ আশা করবেন না। বেশির ভাগ সময়ে আকাশ মেঘলা বলে সন্ধে নামার আভাস থেকে যায় অনেকক্ষণ। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে আলো তেমন না ঢুকলেও ঠান্ডা পড়ছে জমিয়ে। ফেরার ঘুরপথ ধরলাম। আর একটু দেখে যাই জায়গাটা। বুনো গন্ধ আসছে; এমনকী সবুজের মাঝখানে একটা টিলাও দেখা যাচ্ছে। দু-একজন পোষা কুকুরের চেন ধরে ইভনিং ওয়াক করতে-করতে ঢুকে যাচ্ছে জঙ্গলে। ঘরে ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির বাড়ছে। কাঠবেড়ালি, ভামবেড়াল তুরন্ত চলে যাচ্ছে রাস্তা পার হয়ে। তাদের সঙ্গে কি কবির দেখা হত প্রবাসের অলস দুপুরে? ১৯১৩ সালের ১৫ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে পূর্ণিমা রাতে বনভোজনে যাওয়ার পথে গরুর গাড়ি আটকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল সেই অমোঘ টেলিগ্রাম, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট হয়েছিল তার শব্দমালা— SWEDISH ACADEMY AWARDED YOU NOBEL PRIZE IN LITERATURE.
সেদিন হয়তো কবির মনে পড়েছিল অন্যমনে পথ চলার এই তুচ্ছ সঙ্গীদের কথা। প্রণতি জানিয়েছিলেন তিনি হ্যাম্পস্টেডের দিনরাত্রিকে, তাঁর নোবেলের ভিত্তিভূমিকে।
ছবি : অর্য্যাণী ব্যানার্জি