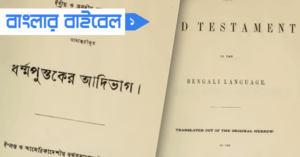‘ফুলসরিয়া’
পরিণত বয়সেই চলে গেলেন গুরুজি। মারক রোগের আক্রমণে মাসখানেকের মধ্যেই অবসান নেমে এল তাঁর জীবনে। ওই দেহকান্তি তাই মলিন হল না একটুও। সকালবেলা তাঁর নাচের ইনস্টিটিউটে গিয়ে ঝিনির মনে হল, ঠিক যেন কোনও ভোরের উৎসব। সুগঠিত চেহারার ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য নৃত্যশিল্পীদের উপস্থিতিতে সে-যে কী জৌলুস! চারদিক খোলা নৃত্যমণ্ডপের চাতালে তিনি শুয়ে আছেন এক অপূর্ব প্রসন্নতায়। আজ তাঁর জীবনের শেষ অঙ্ক। নিষ্প্রাণ দেহেও তাই সাজ, কপালে চন্দন। মাথার কাছে অর্ধেক নারকেলমালায় ঘি ঢেলে যে-সলতেটা ডোবানো, সেটাই জ্বলছে এক মোটা শিখায়; জ্বলন্ত ধূপের গন্ধে এসে মিশছে, কাঁচা নারকেল, ঘি আর কর্পূরের সুবাস। নিম্নাঙ্গে সোনালিপাড় গরদের সাদা ধুতি, সোনালি কোমরবন্ধ দিয়ে আঁটা; গলার ঠিক নীচে, সেই চওড়া সোনালি নেকলেস। নিরাবরণ ঊর্ধ্বাঙ্গে মোটা দুটি মালা; একটি কমলা রঙের ‘কনকাভরম’ ফুলের; আর অন্যটি সবুজ তুলসীপাতার। হাতের কবজি এবং বাহুতেও সোনালি গয়না। ঘুঙুরজোড়াটিই শুধু আজ আর পরা নেই তাঁর পায়ের দু’গোছে; সিল্কের কাপড়ে ঢাকা একটা ছোট টুলের ওপর কাঁসার থালা রেখে, তারই ওপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঠিক তাঁর পাশটিতে। পায়ের কাছে রাখা আরও কয়েকটি বগি থালা; পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সেখানেই মালা দিচ্ছে সকলে। বাগানের মধ্যে ফুটে থাকা ফুলেই সুরভিত হয়ে উঠছে তাঁর শেষ শয্যা; অসংখ্য পাখির ডাকেই, মৃত্যু এসে যেন অভিবাদন জানাচ্ছে তাঁকে। এই মঞ্চেই কতবার কত অনুষ্ঠানে ঝিনি তাঁকে নাচতে দেখেছে। আজ সেখানেই তিনি শুয়ে আছেন, জীবিত অনুরাগীদের শেষ নমস্কারের স্পর্শ নিয়ে। এমন এক অভিনব দৃশ্য ঝিনি আর কখনও দেখেনি।
বহু বছর পার করে, ঝিনির আজ মনে পড়ছে নিজের স্টুডিওঘরে শুয়ে তার বাবার সেই মৃত্যু দৃশ্য। এতদিন যা ভাবলেই তার মনে হত, ভয়াবহ শোক এবং কালো অন্ধকারে জ্বলে ওঠা চিতার আগুন, আজ যেন স্তিমিত হয়ে এল সেই কষ্টবোধ; এমন এক মৃত্যুদৃশ্য উপহার দিয়ে গুরুজিই যেন স্নেহের প্রলেপ বুলিয়ে দিলেন তার দু’চোখে। ঝিনির মনে হল যে, তার বাবাও তো চলে গেছেন তাঁর নিজের স্টুডিওঘরে শুয়েই; নিজের শবশয্যার ছবি একেবারে যেন নিজের হাতেই এঁকে দিয়ে। দেওয়ালভরা ছবি আর জানলার ফাঁকে-ফাঁকে বয়ে যাওয়া গোধূলির আলোমাখা এক নদী। ঝিনির মনে পড়ল, গুরুজি বলতেন, তালের সঙ্গে ফাঁক এবং সম— এ সবই কত জরুরি। বলতেন, শ্বাসের মধ্যে দিয়ে তাল অভ্যাস করে আমরা যেমন বাঁচি, ঠিক তেমনই ‘সম’ অভ্যাস হল আমাদের মৃত্যু-প্রস্তুতি; এগিয়ে গেলেই হবে না। থামতেও জানতে হবে। প্রতি মুহূর্তে বাঁচা এবং একইভাবে প্রতি মুহূর্তে মরাও। ঝিনি বুঝতে পারল যে, অনেক কথা শোনার পরমুহূর্তেই যে তা বোঝা যায় এমন নয়; অনেক পরে তা ধরা দেয়, উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে। আজ যেমন তার মনে হল, শোক কত সুন্দর! তা যেন জীবনেরই এক প্রসারিত রূপ। কতজনের কতরকম মৃত্যুদৃশ্যই না ভিড় করে এল ঝিনির মনে! মনে পড়ল, সুখবীর সিং নেহালের মৃত্যুতে শাফিকার দেওয়া ইন্টারভিউ। তিনিও চলে গেছেন কয়েক বছর আগে। ঝিনি ঠিক জানে না যে, শহরতলির এক বৃদ্ধাশ্রমে শেষজীবনে বসবাস করা সুখবীরজির শেষশয্যা যে কেমন হয়েছিল! অদ্ভুত এক বোধে আক্রান্ত হয়ে ঝিনির মনে হল যে, সে এবং শাফিকা দুজনেই এখন গুরুহীন। তবে কি এবার তারা মুখোমুখি দাঁড়াবে! শাফিকা তো ঝিনিকে চেনেই না! ঝিনি একা চিনলে কী করে আর মুখোমুখি হওয়ার প্রশ্ন উঠছে!
২
সুখবীর সিংয়ের মৃত্যুর সময়ে শাফিকা দিল্লি গিয়েছিল, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার আনতে। মৃত্যুর খব পেয়েই সে বলেছিল যে, সে যখন তার ছবির জন্য পুরস্কার পেল, তখন তার জীবনের আসল পুরষ্কারটিই হারিয়ে গেল জীবন থেকে! ঝিনি ভাবতে বসল যে, এরকম ভাবে সে কি ভাবতে পেরেছে! তার জীবনে ঠিক কোনটি পুরস্কারস্বরূপ! আর ঠিক এখানেই সে আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে শাফিকার। ঝিনির মনে পড়ল, সন্তানদের মধ্যে ছবি আঁকার বীজ পুঁতে দেবার জন্য তার বাবার সে কী উন্মাদনা! সবচেয়ে অভিনব ছিল, নিজেদের হাতে গড়া সেই ইশকুলের প্রথম সরস্বতী পুজোয়, তাঁর দুই মেয়ের হাতেখড়ি অনুষ্ঠান। কলকাতা থেকে নিজের মাস্টারমশাই চিত্রী বসন্ত গাঙ্গুলিকে আনা করিয়ে তাঁর কাছেই হাতে খড়ি হল ঝিনি আর তার বোনের। দুজনকে তাঁর নিজের কোলের দুই পাশে বসিয়ে দুটো নতুন স্লেটে খড়ি দিয়ে ছবি আঁকালেন, ইঁদুর আর বেড়াল। দুই মেয়ের আঙুল ছুঁয়ে মাস্টারমশাইয়ের আঁক কাটায় অক্ষরের বদলে যখন রেখা ফুটে উঠল, তখন একটু শান্ত হল রণেন। তরুলতা এবং মিতা অনেকবার বলা সত্ত্বেও তরুলতার গুরুদেবের দেওয়া, স্লেটের ওপর অ-আ-ক-খ লিখে সেই হাতেখড়িকে তো নস্যাৎ করে দিয়েছিল রণেন।
শীতের সময়ে বারান্দার হুকে টাঙানো গাছগুলোতে এসে পড়ত ভোরের রোদ্দুর। সেই আলোয় ফুলের ছায়ায় যখন আলপনা আঁকা হয়ে যেত বারান্দাটায়, পড়া থেকে তুলে এনে বাবা বলতেন, ‘চক দিয়ে এখুনি এঁকে ফেল; রোদ পড়ে গেলেই ফুলগুলোও হারিয়ে যাবে!’ একটা আঁক কেটে বলতেন, ‘এই লাইনটাকে দু’ভাবে ছোট করা যায়; দু’পাশ মুছে দিয়ে, আবার এটার পাশেই বড় একটা লাইন টেনে দিয়ে’; বলতেন, ‘সেটাই তো তোকে ঠিক করতে হবে যে, কোনটা তুই কীভাবে করবি’! ঝিনির কাছে বাবা মানেই ছবি আঁকা। আর তা যে শুধু দেওয়ালে টাঙানো বা বিক্রির জন্য তা নয়! বিজয়ার কার্ড বা পেজমার্ক ছাড়াও অক্ষরের সঙ্গে ছবি মিশিয়ে চিঠিতেও, কেমন সব টুকরো-টুকরো ছবি! তাদের বাড়ির ঠিকানাটাও ছবিতে শিখিয়েছিলেন বলে, পরীক্ষার পড়াতেও সেটাই ঝিনি তৈরি করছিল— ‘তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখ প্রশ্নে।’ মা না থাকলে, ঠিকানা লেখার জায়গায় ঝিনি বোধহয় শূন্যই পেয়ে আসত। এখন অবশ্য ঝিনির আর সে-অসুবিধে নেই; কারণ ছবিতে লেখা ঠিকানাসমেত বাড়িটাই তো লোপাট হয়ে গেছে! বাবার দেওয়া আরও এক উপহারের কথা মনে পড়ছে ঝিনির। মায়ের অনুমতি না নিয়ে তাঁর সিল্কের শাড়ি পরে খেলতে চলে যাওয়ায়, ভয়ানক বকুনি খেয়েছিল ঝিনি। পরদিনই নিজের ধুতিতে ফেব্রিক পেইন্ট করে, সেটাকে শাড়ি বানিয়ে বাবা বলেছিলেন, ‘এটা তোমার শাড়ি।’ বাবার এই প্রশ্রয়ে ঝিনির মা মিতা আরও রেগে গিয়ে সেই শাড়িটাও তুলে রেখে দিয়েছিলেন ঝিনির নাগালের বাইরে।
মা কি তাকে শহুরে বনসাই বানাতে চেয়েছিলেন! চেয়েছিলেন, তার পিঠে একটা কাঠামো লাগিয়ে, সিধে করে রাখতে! চারিদিকে ডালপালা মেলে বাবার ওই বেঁচে থাকাটাকে বড় বেশি উদ্বৃত্ত মনে হত তাঁর! ঝিনিও কি তাই চাইনি? পোষ-মানানো সংসার, চেনা চাকরি, মাস মাইনে এবং…। কী এই এবং? ফলে এমনই মনে হয়েছে ঝিনির যে, এই ক্রমহীন জীবনে সে শুধুই একজন সংগ্রাহক। সে সংগ্রহ করে চলেছে কিছু মুহূর্তের স্মৃতি; আর সমানেই মিলিয়ে চলেছে চারপাশের সঙ্গে। অন্যদের থেকে আলাদা হলেও, কীসে যে সে আলাদা, সেটাই তার কাছে স্পষ্ট নয়। কারণ সে তো খোঁজেনি কীসে তার স্ফূর্তি! নিজেই সে ডেকে এনেছে দুর্বিপাক; আবার সেটাই সামাল দিতে-দিতে কেটে গেছে অনেকটা সময়। ছোটবেলার একটা নিটোল সময়কে আঁকড়ে ধরে, সমানেই তাচ্ছিল্য করে গেছে নিজের বড় হয়ে ওঠার শর্তগুলো; নিজেকে সে কোথাও খোঁজেইনি।
ঝিনির মনে হল, আজ সে পারবে। এক জীবনে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন পর্বের ঝিনিদের, তাই সে সরিয়ে রাখল দূরে। তার মনে পড়ল ছোটবেলায় পড়া একটা বইয়ের কথা। সে-বইটার গল্পের সঙ্গে ছাপা ছবিগুলো তার বাবারই আঁকা। একটা ছোট ছেলে; তার কাকা তাকে শেখাতে লাগল চাষবাস; আর মামা চাইল যে সে হয়ে উঠুক এক জবরদস্ত মাঝি! ছেলেটা কিন্তু চাষিও হল না, মাঝিও হল না। সে হয়ে গেল সাপুড়ে। বাঁশি নিয়ে বেরিয়ে গেল, সাপুড়েদের খোঁজে। ঝিনি তাই ভাবতে বসল, জীবনের বাকিটুকু ঠিক কী নিয়ে কাটাবে সে! যে-পরিচয়ে সে হয়ে উঠবে আসল ঝিনি এবং এক আসল সুগন্ধা!

‘ফুলসরিয়া’। এ–ধন্দ তো আজও গেল না যে কে এই ‘ফুলসরিয়া’! বাবার বড় ভয় ছিল যে, তাঁর আসল ঝিনি না হারিয়ে যায়! ছেলেধরার প্রসঙ্গ উঠলেই বাবা বলতেন ‘ফুলসরিয়া’। আমিও অমনি গুটিসুটি মেরে, মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে চোখ বুজে ফেলতাম। কিন্তু দুপুর শেষ হয়ে, তিনটে বাজলেই খুটখাট শব্দে আমি ঠিক বুঝে যেতাম যে, ঠাকুমা এবার দরজার ‘ছেকল’ খুলে নীচে নেমে রাঙাদিদাদের উঠোনে যাবেন চা খেতে। আমিও বেড়ালের পায়ে নিঃশব্দে উঠে, গুটি গুটি বেরোতে গেলেই চোখ বন্ধ করেই বাবা বলতেন, ‘ফুলসরিয়া’। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও বাবা যে কী করে টের পেয়ে যেতেন, কে জানে! সাবধান করে দিতে একদিনই বলেছিলেন যে, দুপুরবেলা ছেলেধরা ঘুরে বেড়ায়; তোমাকে ধরে অন্য দেশে নিয়ে যাবে। নাম বদলে দিয়ে ওরা ডাকবে, ‘ফুলসরিয়া’ বলে; সবাই তখন ওই নামেই চিনবে তোমাকে; আমরা তোমাকে হঠাৎ দেখে, চিনতে পেরে ‘ঝিনি, ঝিনি’ বলে ডাকলেও তুমি তখন সাড়াই দেবে না। বুঝতেই পারবে না যে, ‘ঝিনি’ বলে কাকে ডাকছি আমরা! আসলে তখন তো ওরা তোমাকে ‘ফুলসরিয়া’ বানিয়ে নিয়েছে।’
এসব শুনে ভয়ংকর কান্না জুড়তাম আমি! ঠাকুমা এসে অনেক বোঝালেও, আমার মনে কিন্তু ‘ফুলসরিয়া’ হয়ে যাবার ভয়টা পাকাপাকি ভাবে রয়েই গেল। মাঝে মাঝে তিনতলায় বাবার স্টুডিওঘরে গিয়ে, তাকিয়ে থাকতাম দেওয়ালে টাঙানো বাবার আঁকা ছবিগুলোর দিকে। কত মানুষের মুখ! একজনও চেনা নয়। বাবা কি তবে ছেলেধরাদের মুখ এঁকে রাখেন? এরা সব কারা! কোথায় থাকে!
আজ কোথায় মিলিয়ে গেছেন মা, বাবা, ঠাকুমা! মিলিয়ে গেছে, সেই বাড়িটার কালো ঘর, সাদা ঘর, লাল ঘর! কিন্তু আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি যে, কত অসংখ্যবার ছেলেধরায় ধরে নিয়ে গিয়ে, নানা ছলছুতোয় ‘ফুলসরিয়া’ই বানিয়ে দিতে চেয়েছে আমাকে; আর আমিও বারবার মাঠ পেরিয়ে, ঘাট পেরিয়ে, এক ছুট্টে পালিয়ে আসতে চেয়েছি। কিন্তু ফিরব কোথায়? আমার কি কোনও ঘর আছে? মনে-মনে তাই আঁকড়ে থেকেছি বাবার সেই স্টুডিওঘরটাই; বিশ্বাস করেছি যে, বাবার আঁকা ওই ভূতুড়ে মুখ ‘দামড়ি সিং’, ‘গারো মেয়ে’ বা ‘মুন্সি রাম’— এরা কেউ ছেলেধরা নয়। আসল ছেলেধরারা লুকিয়ে আছে, মিথ্যে ভালোবাসার মোড়কে এবং নানা সম্পর্কের বেড়াজালে। ক্রমাগত এরাই আমাকে চুপিসাড়ে বদলায় আর ফিসফিস করে ডাকতে থাকে নানা নামে; ওদের ডাকা সব নামেই তাই, আমি শুধু শুনি, ‘ফুলসরিয়া’… ‘ফুলসরিয়া’… ‘ফুলসরিয়া’। বাবার চিনিয়ে দেওয়া ওই নামটাই তো বারবার আমাকে ‘ঝিনি’তেই ফেরায়। একা হয়ে গেলেও সাবধানে পা ফেলে, সতর্কে বুঝে নিতে চেষ্টা করি, কাদের কাছাকাছি গেলে আবার আমার সব কিছু বদলে যায় বা বদলে যেতে পারে। কারণ এভাবেই তো ক্রমেই আমি ভুলে গেছি আমার নিভৃত অক্ষরমালা, চুড়ো করে বাঁধা খোঁপার বাঁধন, আর মনের গহনে অফুরন্ত আনন্দের টলমলে স্রোত। আজ এতকাল পরে আমি বুঝেছি যে, বাবার আঁকা ওই মুখগুলো আসলে তাদের, যারা কিছুতেই ‘ফুলসরিয়া’ হয়ে যায়নি। যে যার মতো এঁটে আছে, নানা রঙে আর রেখায়— ‘দামড়ি সিং’, ‘গারো মেয়ে’ বা ‘মুন্সি রাম’। আর আছে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে শাফিকা— এক লম্বা সফর।
ড্রেসিং টেবিলে রাখা, ছোট্ট আমাকে কোলে নিয়ে বাবার সেই হাত উঁচু করে আকাশে ছুড়ে দেওয়ার ছবিটাই বারবার দেখি। দেখি যে বাবা আর আমি দুজনেই কেমন খিলখিল করে হাসছি। বাবার ওই অনায়াস হাসিতেই এমন এক আশ্বাস ধরা আছে যে, ‘ফুলসরিয়া’ই আজ আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে, দূর থেকে দূরে। এখন আমিই তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি নির্মূল করব বলে। বুঝতে পেরেছি যে, এই ‘ফুলসরিয়া’-ভয়টাই হল আমাকে দিয়ে যাওয়া তাঁর সর্বোত্তম আশীর্বাদ।
ঝিনির মনে হল, আজ সে পারবে। এক জীবনে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন পর্বের ঝিনিদের, তাই সে সরিয়ে রাখল দূরে। তার মনে পড়ল ছোটবেলায় পড়া একটা বইয়ের কথা। সে-বইটার গল্পের সঙ্গে ছাপা ছবিগুলো তার বাবারই আঁকা। একটা ছোট ছেলে; তার কাকা তাকে শেখাতে লাগল চাষবাস; আর মামা চাইল যে সে হয়ে উঠুক এক জবরদস্ত মাঝি!
গুরুজি চলে যাবার পরেও অনুশীলন করি। বাড়ির কাছেই, নতুন একটা স্পেস কিনে সাজিয়েছি। ফাঁকা হলঘরের একটা দেওয়ালে যে–আয়না, সেটার ফ্রেমে গিজিগিজি করে হুক লাগিয়ে, গলিয়ে দিয়েছি কাঁসার ঘুঙুর। জানলা-দরজায় লাগিয়েছি শাড়ি কেটে বানানো পর্দা; এক কোণে রেখেছি মায়ের দেওয়া সেই পুরনো পিলসুজ, যার ওপরে বসানো একটা সাবেক জলপ্রদীপ। গাছের গুঁড়িটাকে টেবিলের মতো কেটে তার ওপরে বসিয়েছি একটা তামার তাট। আঁকার সময়ে যে কালো পাথরবাটিটায় জল রেখে তুলি ডোবাতেন বাবা, সেটাতেই জল রেখে ফুল ভাসিয়ে দিই; তামার থালার ওপর সেটা রাখায়, কালো পাথরবাটিটাকে আরও উজ্জ্বল লাগে। আমি নাচ শুরু করলেই আরও দুজন ঝিনিও একসঙ্গেই নেচে ওঠে; একজন আমার প্রতিবিম্ব; আয়নাটায় ফুটে উঠে, আমাকে যে সংশোধন করায় ক্রমাগত; আমার পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের শব্দ পেয়ে, মৃদু কম্পনে দুলতে থাকে আয়নার ঘুঙুরগুলোও; আর অন্যজন আমারই ছায়া; প্রদীপের মোলায়েম আলোতে যা জেগে ওঠে কখনও মেঝেতে, কখনও-বা দেওয়ালে; আমার সর্বাঙ্গের প্রতিটি রেখা দিয়ে ওই ছায়াটাই আলপনা আঁকে রোজ সন্ধেবেলা। আমি ছাড়া, এই ঘরে বসবাস করে হাতে গোনা কয়েকজন— আমার প্রতিবিম্ব, আমার ছায়া, প্রদীপের আলো, তামার তাট, কালো পাথরের বাটি আর ওই ঘুঙুর সাজানো আয়নাটা। গুরুজির দেওয়া ঘুঙুরজোড়াটা লুকিয়ে রাখি, পাশের ঘরের ছোট্ট আলামারিটায়; গাঢ় সবুজ রঙের একটা সিল্কের বটুয়ায়। ওটাই তো আমার সিন্দুক।
আজ, আয়নার বদলে চোখ চলে গেল, দেওয়ালের ছায়াটার দিকে। আমি তখন বাঁ-হাতের মুদ্রায় হাতটা উঁচুতে তুলে চাঁদ আর ডান হাতের তর্জনীতে হাত নীচু করে সেই দিকে তাকাবার ভঙ্গিতে; দু’হাতের মাঝখানে অনেকটা ফাঁক; মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছি যে! আমি হেলে আছি ডানদিকে; কিন্তু তাকিয়ে আছি বামদিকের চন্দ্রমুদ্রায়— দূরের আকাশে। মুদ্রা বা ভঙ্গি বদল না করে, অনড় হয়ে যা দেখলাম, সে এক অব্যর্থ ইঙ্গিত। বাবা সবসময়ে বলতেন, ‘কাউকে দোষী করে তুমি যখন তর্জনী উঁচিয়ে একটা আঙুল তার দিকে দেখাচ্ছ, বাকি তিনটে আঙুল কিন্তু তোমার দিকেই; আর ওই তিনটে আঙুলকে শাসনে বেঁধে রেখেছে বুড়ো আঙুল; এভাবেই আমরা নিজের দোষ না দেখে অন্যকে তেড়ে যাই!’ আজ অবাক হয়ে দেখলাম, ডান হাতের সেই তর্জনী নির্দেশ করছে চাঁদ! আর তর্জনীর সঙ্গে সমান ভাবে খুলে গিয়ে ওই বুড়ো আঙুলের সহযোগেই তো তৈরি হয়েছে অর্ধচন্দ্র; সেইসঙ্গে বাকি তিনটে আঙুলও আর আমাকে নির্দেশ না করে, কোরকের মতো উন্মুখ হয়ে ঊর্ধগামী আকাশের দিকে। বাঁ-হাতের চন্দ্র-মুদ্রায় যেন সেই উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস যা আমি দেখিয়ে চলেছি ডান হাতের পাঁচটা আঙুলে। বাবা যে ‘পার্সস্পেক্টিভ’ শেখাতেন, এতদিনে সেটাই যেন সম্পূর্ণ হল, গুরুজির আশীর্বাদে। এই-ই তো এক নতুন পথ!
বড় পূর্ণ মনে হল নিজেকে। শাফিকার ক্যানভাসে ছড়িয়ে থাকা সবুজ রঙের সেই আলোর স্পর্শ আজ যেন আমার চেতনায় এবং সর্বাঙ্গ জুড়ে। জলের নীচে বেঁচে থাকা গুচ্ছ-গুচ্ছ প্রবাল; না চিনলে যেগুলোকে শ্যাওলা বলে মনে হয়। আজ আমি তা সঠিক চিনেছি।
অন্ধকারে আলোর রং— সত্যি তো এক মায়াময় সবুজ!
(সমাপ্ত)
ছবি একেছেন শুভময় মিত্র