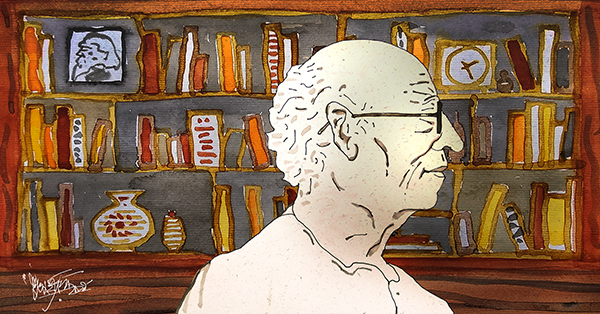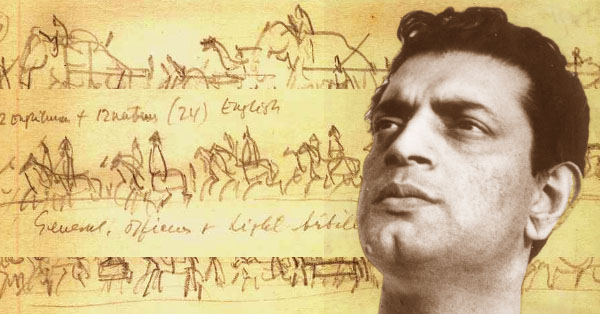গঙ্গা বয়ে যায়

 রাস্কিন বন্ড (Ruskin Bond) (August 13, 2022)
রাস্কিন বন্ড (Ruskin Bond) (August 13, 2022)দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়, বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে অন্য একটি ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। ব্রিটেন তখন দুই খুব ভিন্ন স্বভাবের ভারতীয় নেতার চাপে ছিল। যুদ্ধের খরচের কারণে ব্রিটেনের অর্থনীতির তখন টলোমলো অবস্থা, সুতরাং ব্রিটেন দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সম্মত হয়।
কিন্তু সেই স্বাধীনতার যথেচ্ছ মূল্য চোকাতে হল। দেশভাগ।
যখন সিমলায় আমার বোর্ডিং স্কুলের খেলার মাঠে ভারতীয় পতাকা উঠেছিল, আমি তখন ১২ বছর বয়সী একজন স্কুল-পড়ুয়া। আমাদের বহু বছরের পরিচিত ‘ইউনিয়ন জ্যাক’ ধীরে ধীরে নেমে এল।
বাতাসে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা ছিল। একটি নতুন দেশ জন্ম নিল, এবং আমরা– ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সামাজিক স্তরের প্রায় ২০০ ছাত্র সেই জন্মের সাক্ষী থাকলাম। অঝোর ধারায় বৃষ্টিতে, মল পর্যন্ত কুচকাওয়াজ করে গিয়ে আমরা যোগ দিলাম একটা জনসভায়। সেই সভায় বিখ্যাত মানুষদের বক্তৃতা শুনলাম, সেই প্রথম স্বাধীনতা দিবসে। তখন সিমলা ছিল দেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী এবং ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন তখনও সিমলায় তাঁর বাসভবনেই ছিলেন।
সেই সময়ে তো টেলিভিশনের কোনও ব্যাপারই ছিল না, ইন্টারনেটের তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু রেডিওতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। যে ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর সারা বিশ্ব সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান আর লক্ষণীয় ছিল ইংরেজি ভাষার ওপর তাঁর দখল।
তখনকার দিনে আমরা যে কী অসম্ভব ভাবে রেডিওয়র ওপর নির্ভরশীল ছিলাম, তা এখন বোঝানো দায়। খবরের জন্য, আমাদের নেতাদের বার্তা বা বক্তৃতার জন্য, দেশ-বিদেশের খেলা আর ক্রিকেট ম্যাচের ধারাভাষ্য শোনার জন্য, রেডিওই ছিল আমাদের একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী।
মেলভিল ডি মেলো ছিলেন তখনকার সবচেয়ে বিখ্যাত সংবাদ-পাঠক এবং ধারাভাষ্যকার। তিনি আমাদের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁর পরিচিত, গম্ভীর কণ্ঠস্বর বেয়ে আমাদের কাছে ভেসে আসত প্যারেডের বর্ণনা, উদযাপনের উল্লাস কিংবা বিপর্যয়ের বেদনা ।
ভারত ভাগ হয়ে গেল। স্বাধীনতার ঘণ্টা বাজানোর তাড়াহুড়োয়, ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ও পঞ্জাবকে বিভক্ত করতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন আমাদের নেতারা।
আমাদের স্কুলও বিভক্ত হল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিবাদের কারণে নয়। আমাদের ছেলেদের এক-তৃতীয়াংশ লাহোর এবং বর্তমান পাকিস্তানের অন্যান্য শহর থেকে বোর্ডিং-এ এসেছিল। বাজারের সহিংস দলগুলির হুমকির মুখে পড়েছিল আমাদের স্কুল। মধ্যরাতে, আমাদের সমস্ত মুসলিম ছেলেদের আর্মি ট্রাকে একসঙ্গে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেওয়া হল তাদের নতুন দেশের সীমান্তে। তারা নিরাপদে পৌঁছেছিল ঠিকই, কিন্তু আমি আর কোনও দিন তাদের দেখতে পাইনি।
একটি বিশাল জনসংখ্যার স্থানচ্যুতি ঘটেছিল। ভয়ঙ্কর দাঙ্গা, গণহত্যা এবং মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে সেই জায়গা-বদলাবদলির মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল । পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ তাঁদের বাড়িঘর ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন; একই ভাবে লাখ লাখ মুসলমান, পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু কোনও পক্ষই অপূরণীয় ক্ষতি বা যন্ত্রণা এড়াতে পারল না। হত্যা আর প্রতিশোধের তাণ্ডব চলেছিল অসংখ্য দিন, অসংখ্য সপ্তাহ, অসংখ্য মাস ধরে।
ব্রিটেন অবশ্য বরাবরই ভারতকে তাদের সাম্রাজ্য-মুকুটের সেরা রত্ন হিসেবে বর্ণনা করেছে। কিন্তু সেই রত্নটিই তখন খানখান হয়ে গিয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য মাউন্টব্যাটেনের ওপর তখন ব্রিটিশ সরকারের প্রবল চাপ। আর সেই চাপের ফল হল ভয়াবহ। অন্তত সেই সময়ে তো এই ফল ভয়ঙ্করই ছিল।
আমাদের স্কুলও বিভক্ত হল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিবাদের কারণে নয়। আমাদের ছেলেদের এক-তৃতীয়াংশ লাহোর এবং বর্তমান পাকিস্তানের অন্যান্য শহর থেকে বোর্ডিং-এ এসেছিল। বাজারের সহিংস দলগুলির হুমকির মুখে পড়েছিল আমাদের স্কুল। মধ্যরাতে, আমাদের সমস্ত মুসলিম ছেলেদের আর্মি ট্রাকে একসঙ্গে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেওয়া হল তাদের নতুন দেশের সীমান্তে। তারা নিরাপদে পৌঁছেছিল ঠিকই, কিন্তু আমি আর কোনও দিন তাদের দেখতে পাইনি।
সেই শীতে যখন আমি দেরাদুনে বাড়ি এলাম, তখন চরম সংকটের সময়টা কেটে গিয়েছে। আমার বয়স ১৩, ব্রিটিশ এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বাবা-মায়ের সন্তান, যার জন্ম ভারতে। কেউ কখনও আমাকে হেনস্থা করেনি, না দিল্লিতে, না দেরাদুনে। সেই সময় একদিন আমি আমাদের বিস্তৃত ময়দান পেরিয়ে একটি সিনেমা হল-এ ঢুকেছিলাম ছবি দেখতে। ছবিটির নাম ছিল ‘ব্লসমস ইন দ্য ডাস্ট’।
ফিল্ম শুরু হওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যেই ফিল্ম দেখানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, লাইট জ্বলে উঠল এবং ম্যানেজার একটি ঘোষণা করলেন।
‘আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু এখনই আমাদের এই অনুষ্ঠানটি বন্ধ করতেই হবে। আমরা এইমাত্র খবর পেয়েছি যে গান্ধীজিকে গুলি করা হয়েছে।’
গান্ধীজি তখন আর আমাদের মধ্যে নেই।
সেই দিন অদ্ভুতভাবে নীরব একটা শহরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আমি বাড়ি ফিরেছিলাম। কোনও দাঙ্গা নেই, রাস্তায় কোনও স্লোগান নেই। দেশ হতবাক! সারা দেশ বজ্রাহত। হত্যাকারী এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর মতাদর্শের সঙ্গে মহাত্মার তীব্র মতাদর্শগত পার্থক্যই তাঁকে এই পথে চালিত করেছিল। তিনি এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করলেন, যিনি অন্য যে কোনও ব্যক্তির চেয়ে হয়তো বেশি করে, হয়তো বা বেশি দিন ধরে স্বাধীনতার দীর্ঘ আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন।
সময়ের সাথে সাথে দেশ এই মর্মান্তিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠল।
ভারত সর্বদা বিদেশি আগ্রাসন, ঔপনিবেশিক শোষণ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প হোক বা ঘূর্ণিঝড়, এমনকী মহামারীর সঙ্গে লড়াই করে আরও শক্তিশালী হয়ে ‘কামব্যাক’ করে।
মাঝে মাঝে সময় লাগে, কিন্তু ভারত সেরে ওঠে।
ঋতু চলে যায়, ফসল ওঠে, আম পাকে, বর্ষা আসে আর যায়, বরফ গলে যায়, গঙ্গা বয়ে যায়…
‘আ লিট্ল বুক অফ ইন্ডিয়া: সেলিব্রেটিং ৭৫ ইয়ারস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স’ থেকে নির্বাচিত অংশ
ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook