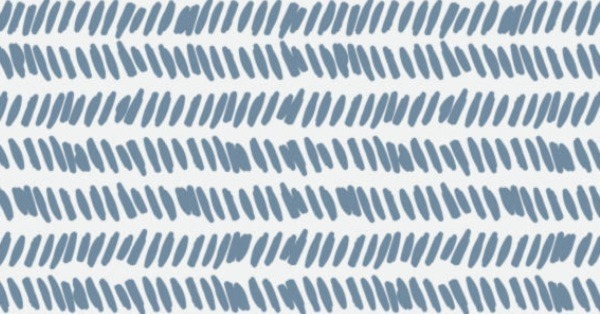সত্যজিতের শহরতলি

 সুব্রত মজুমদার (March 5, 2022)
সুব্রত মজুমদার (March 5, 2022)গমগমে মহানগর কলকাতা থেকে পশ্চিমে দুশো কিলোমিটার দূরে ম্রিয়মাণ আসানসোল শহর। সেখান থেকে সাত কিলোমিটার দক্ষিণে টিমটিমে বার্নপুর উপনগরী। শহরতলি বললে নেহাতই বাড়িয়ে বলা হবে। বিরাট একটা ইস্পাতের কারখানা, আর সেই কারখানা ঘিরে তৈরি হয়ে ওঠা একটা উপনগরী। স্মল টাউন। বার্নপুর স্টেশন রোড আর সার্কুলার রোডের সংযোগস্থল থেকে একটু এগিয়ে গেলে একটা রেল ওভারব্রিজ। রাস্তা থেকে রেললাইন পেরিয়ে ব্রিজের অন্য দিকে কারখানায় ঢোকার একটা গেট। দশ নম্বর গেট— তাই ব্রিজের নাম দশ নম্বর ব্রিজ। ভাঙাচোরা সিঁড়ি ভেঙে কারখানার কর্মীরা যায়, অনেকে কাঁধে সাইকেল নিয়েও উঠে যায়, খুব একটা উঁচুতে নয় ব্রিজটা। ব্রিজের ওপর দাঁড়ালে অল্প দূরে স্টেশনটাও দেখা যায়। সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল, তারপর একদিন সন্ধে ছ’টার সময়, ওই ব্রিজের ওপর থেকে রতনলাল মজুমদার মণিলাল মজুমদারকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের নীচে ফেলে খুন করেন।
এটা একদম বানানো গপ্পো। সরি, ভুল বলা হল— গপ্পটা বানানো নয়। গল্পটা সত্যজিৎ রায়ের ১৯৭০ সালে লেখা ‘রতনবাবু ও সেই লোকটা’। ‘সেই লোকটা’ মানে মণিলাল মজুমদার। শুধু রতনবাবুর সঙ্গে নামের মিল নয়— তিনি হচ্ছেন নিজেকে সবার চেয়ে আলাদা ভাবা রতনবাবু, রতনলাল মজুমদারের কার্বন কপি। শহরতলিতে বেড়াতে গিয়ে দুজনের আলাপ ও পরিচয়। রতনবাবু ক্রমে জানতে পারলেন মণিলাল আর তাঁর পছন্দ-অপছন্দ, চেহারা, গলার স্বর, জীবনের ছোটোখাটো ঘটনা, মায় জন্মের তারিখ— সব মিলে যাচ্ছে। রতনবাবু দেখলেন যে তাঁর নিজস্বতা, তার চারিত্রিক অনন্যতা— ইউনিকনেস— ধরে রাখতে গেলে দুজনই তো বেঁচে থাকতে পারেন না, একজনকে পৃথিবী থেকে সরে যেতে হয়। বা সরিয়ে দিতে হয়। তাই একদিন সন্ধেবেলায় রেলের ওভারব্রিজের ওপর থেকে ধাক্কা মেরে ট্রেনের নীচে ফেলে রতনলাল খুন করলেন মণিলালকে। কিন্তু রতন যা করেছেন সেইটা মণিলালকেও তো করতে হবে— নাহলে আর তাঁরা মানিকজোড় হলেন কীসের! তাই পরের দিন ওই ব্রিজের ওপর থেকেই অশরীরী মণিলাল রতনবাবুকে ধাক্কা মারলেন ওই ট্রেনটারই নীচে।
এই গপ্পোটাই আমার কাছে সজীব হয়ে উঠত দশ নম্বর ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে বার্নপুর স্টেশনের দিকে তাকিয়ে। ছেলেবেলায় আমার কাছে এই গপ্পের স্থান পরিবর্তনটা দিব্যি ‘কেন, হতেই তো পারে’ মনে হত। গপ্পের সিনি স্টেশনও তো ইস্পাতনগরী টাটানগরের কাছে। তবে টাটানগর নয়, এই বার্নপুর শহরেই আমার জন্ম আর বড় হওয়া। বার্নপুর সিনেমায় প্রথমবার গুগাবাবা দেখা, ওই স্টেশন রোডের বুক এম্পোরিয়ামে নিখিলদার থেকে ফেলু, শঙ্কু আর সত্যজিতের অন্যান্য বই কিনে পড়া। সত্যজিতের গল্পে, সিনেমায় যতবার শহরতলির পটভূমিকা বা শহরতলির মানুষজন ঘুরে ঘুরে এসেছে, ততবারই মনে হয়েছে সেই গল্পটা (বা ছবিটা) আরো একটু ভাল ভাবে বুঝলাম। গল্পের চরিত্রগুলিকে একটু গভীরে গিয়ে চিনলাম। শহরের চরিত্রের সাথে শহরতলির চরিত্রটাকে মিলিয়ে নিলাম, সেখানকার লোকজনের মানবিকতার তফাতটা উপভোগ করলাম। এর মধ্যে দিয়েই একটু বেশি কাছের মনে হয়েছে সত্যজিৎ রায়কে।
সত্যজিৎ তো আগাগোড়া ভীষণ রকম শহুরে মানুষ। গড়পার, বালিগঞ্জ, লেক টেম্পল রোড থেকে বিশপ লেফ্রয়। অক্টারলনি মনুমেন্ট থেকে মেরেকেটে দশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যেই থেকেছেন সারা জীবন। তাহলে ওঁর গল্পে আর সিনেমায় স্মল টাউন— শহরতলি, মফঃস্বল— ফিরে ফিরে আসে কেন? উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক খোদ ক্যালকাটা ট্রিলজির প্রথম ছবি, ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’— তাতেই দম আটকে আসা কলকাতা থেকে শেষ দৃশ্যে সত্যজিৎ আমাদের নিয়ে গেলেন কোনো এক ছোট্ট শহরতলিতে। এই ছবিটার কথা একটু পরে হবে, কিন্তু শহুরে জীবনের দৈনন্দিতার ক্লান্তি, নাগরিক জীবনের কিষ্টতা থেকে সাময়িক মুক্তি পেতেই কি এই মফঃস্বলের হাওয়া বদল? হতেই পারে— নিজের ছবির শুটিংয়ের জন্য কলকাতা ছেড়ে তো অনেক জায়গায় যেতেন উনি, আর ওঁর ওই অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি খাটিয়ে নির্ঘাত গল্পের রসদ তুলে আনতেন সঙ্গে করে। পত্রিকা চালাবার কারণে সেই রসদ থেকে তৈরি করতেন অসাধারণ সব গল্প। সত্যজিৎ রায়ের বাণিজ্যিক সেন্স বেশ ভালই ছিল— তিনি কি জানতেন যে শহরের চেয়ে শহরতলির ছেলেমেয়েদের হাতে সময় থাকে অনেক বেশি? (কথাটা এখন একদমই বেঠিক, কিন্তু সত্তরের দশকের বার্নপুর উপনগরীতে বিলকুল খাপে-খাপ। টিভি নেই, অন্য কোনো রকম মনোরঞ্জনের সুবিধে নেই, কিন্তু লাইব্রেরি আছে একটা একদম প্রথম শ্রেণির আর জমজমাট। তাই অগাধ বই পড়ার সুযোগ)। একদিকে যেমন শহুরে পাঠক-পাঠিকাদের একঘেয়েমি দূর করতে শহরতলির অবতারণা, তাঁর নিজের চোখ আর অভিজ্ঞতা দিয়ে শহুরে পাঠকদের শহর থেকে দূরের জীবনকে চেনানো, সেখানকার মানুষদের সাথে আলাপ করানো, অন্যদিকে মফঃস্বলের পাঠক-পাঠিকাদের তাদের চেনা জিনিস, চেনা পরিবেশ, চেনা জীবনধারার মধ্যে নিয়ে ফেলে দেওয়া।
সত্যজিৎ হয়তো শহরতলিকে গল্পে ও সিনেমায় কিছুটা নিয়ে আসতেন দ্বৈততা বা ডুয়ালিজমকে তুলে ধরার জন্য। ওঁর বেশ কিছু ছবিতে, এমনকী গল্পেও, বিপরীতধর্মী চরিত্রের ছড়াছড়ি। ‘দেবী’ ছবিতে ধর্মান্ধ কালীকিঙ্কর ও তাঁর পুত্র নাস্তিক উমাপ্রসাদ। ‘সীমাবদ্ধ’ ছবির কর্পোরেটের প্যাঁচালো শ্যামলেন্দু আর তার সরলমতি শ্যালিকা সুদর্শনা (যিনি সব জটিল প্রশ্নের মুখে সরল ভাবে ‘সেটা-ভাল-না-খারাপ’ জিজ্ঞেস করতেন— যাঁর কাছে সবকিছু হয় কালো, নয় সাদা, ধূসর রঙের শহুরে বিস্তারের ব্যাপারটা থেকেই তিনি বিচ্ছিন্ন)। ‘গণশত্রু’র নীতিবান ডক্টর অশোক গুপ্ত ও তাঁর নীতিহীন ছোটভাই নিশীথ গুপ্ত। সত্যজিতের কাজে এই বিপরীতধর্মের সংঘাত চরমে উঠছে ‘আগন্তুক’ ছবিতে— সভ্যতার হয়ে একতরফা যুক্তি খাড়া করে চলেছেন চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলা ঘোর শহুরে মানুষ ব্যারিস্টার পৃথ্বীশ সেনগুপ্ত, আর সেই প্রশ্নবাণ ঠেকাচ্ছেন (কিছুটা জর্জরিতও হচ্ছেন) সভ্যতাকে এড়িয়ে চলা, ‘সভ্যতা সম্বন্ধে খুব bitter’ wanderlust-প্রিয় মনোমোহন মিত্র। ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবিতে রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ চৌধুরী পাখির রোস্ট খেতে ভালোবাসেন, আর তাঁরই শ্যালক জগদীশ হলেন পক্ষী-বিশারদ (তাই ধরা যায় পাখি ভালবাসেন)— তিনি পাখির বই আর দূরবিন নিয়ে ঘোরেন! এই ধরনের চারিত্রিক দ্বৈততার সঙ্গে একটা জিওগ্রাফিক ডুয়ালিজম যোগ করলে যে সংঘাতটা আরো জোরালো হয়, এইটা সত্যজিতের মনে হয়ে থাকতে পারে।
১৯৮০ সালে লেখা ‘চিলেকোঠা’ গল্পটাই ধরা যাক। শহরতলির ছোট ছেলেটি, বন্ধুর প্রাইজ পাওয়া মেডেল চুরি করে বলে ‘হারিয়ে গেছে’। এই দুটি ছেলের মধ্যে সফল হওয়ার (নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে আর্থিক ভাবে সফল হওয়ার) ব্যাপারে সত্যজিৎ বেছে নিলেন বাঁকা পথে চলা ছেলেটিকে। গল্পে তিনিই বড় হয়ে হলেন এক ধনী শিল্পপতি। একটু খুলে বলি। আদিত্যনারায়ণ চৌধুরী কলকাতা শহরের ডাকসাইটে শিল্পপতি, কিন্তু ছেলেবেলায় স্রেফ হিংসার বশবর্তী হয়ে প্রিয় বন্ধু শশাঙ্ক স্যানালের ‘পণরক্ষা’ আবৃত্তি করে পাওয়া মেডেলটা বাবাকে দেখাবে বলে চেয়ে নিয়ে গায়েব করে দেয়। প্রায় কোয়ার্টার সেঞ্চুরি পরে, স্রেফ নিয়তির টানে শহর ছেড়ে জন্মস্থান শহরতলি ব্রহ্মপুরে এসে আদিত্য হঠাৎ দেখা পেয়ে গেলেন ওই ব্রহ্মপুরেই থেকে যাওয়া, অসফল শশাঙ্ক সান্যালের। শশাঙ্ক অসফল হতে পারেন, বোকা নন— আদিত্যকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করলেন সেই ‘পণরক্ষা’ কবিতাটা। বিবেকের দংশনে কাঠখড় পুড়িয়ে চুরি করা মেডেল পৈতৃক বাড়ির চিলেকোঠা থেকে উদ্ধার করে শশাঙ্ক সান্যালের কাছে নিয়ে গিয়ে ফের মিথ্যে বলতে গিয়ে ধরা পড়ে, মেডেলের মূল্য নয়, মেডেলটাই ফেরত দিতে বাধ্য হলেন আদিত্যনারায়ণ। খেয়াল করুন, একটা ছোট্ট গল্পে কতগুলো সংঘাত, কতগুলো বৈপরীত্য এনে ফেলেছেন সত্যজিৎ রায়— ভাল বনাম খারাপ, সফল বনাম অসফল, আর শহর বনাম শহরতলি। শেষের বৈষম্যটা চারিত্রিক বৈষম্যের সঙ্গে মিলে গল্পটাকে বেশি নাটকীয় করে তুলেছে। কলকাতার সাহেব মানুষ প্রায়-গ্রাম ব্রহ্মপুরে নগেনখুড়োর দোকানে টিনের চেয়ারে বসে নানখাটাই খেতে খেতে ঊনত্রিশ বছর পরে শশাঙ্কর দেখা পেলেন: এই ভৌগোলিক সংঘাতটা চারিত্রিক বিভাজনগুলিকে স্পষ্টভাবে তুলে এনেছে আর বৈষম্যটাকে আরো মজবুত করেছে।
একটা ছোট্ট গল্পে কতগুলো সংঘাত, কতগুলো বৈপরীত্য এনে ফেলেছেন সত্যজিৎ রায়— ভাল বনাম খারাপ, সফল বনাম অসফল, আর শহর বনাম শহরতলি। শেষের বৈষম্যটা চারিত্রিক বৈষম্যের সঙ্গে মিলে গল্পটাকে বেশি নাটকীয় করে তুলেছে। কলকাতার সাহেব মানুষ প্রায়-গ্রাম ব্রহ্মপুরে নগেনখুড়োর দোকানে টিনের চেয়ারে বসে নানখাটাই খেতে খেতে ঊনত্রিশ বছর পরে শশাঙ্কর দেখা পেলেন: এই ভৌগোলিক সংঘাতটা চারিত্রিক বিভাজনগুলিকে স্পষ্টভাবে তুলে এনেছে আর বৈষম্যটাকে আরো মজবুত করেছে।
সত্যজিতের গল্পের কিছু চরিত্র আবার শহরের জাঁতাকল থেকে উদ্ধার পেতে শহরতলিতে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। ক্যালকাটা ট্রিলজিতে শহরটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্র। সেখানে ভাঙা রাস্তা, মোমবাতি জ্বেলে পরীক্ষার খাতা দেখা, ঘুষ, জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নের বোমাবাজি, বেকার সমস্যা। একরকম নেতিবাচক চরিত্রই বলা চলে কলকাতা শহরটাকে। তার তুলনায় মফঃস্বল মুক্তির অনাবিল খোলা হাওয়ার জায়গা। সেখানে ‘নায়ক’ ছবির ফ্যানদের চোখের মণি অরিন্দম চ্যাটার্জি পুরস্কার নিতে দিল্লি যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে নিশ্চিন্তে স্টেশনে নেমে মাটির ভাঁড়ে চা খেতে পারেন। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ ছবিতে ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়ে বিফলতায় হন্যে হওয়া সিদ্ধার্থ রাগে চণ্ডাল হয়ে কলকাতায় ইন্টারভিউ বোর্ড চুরমার করে, খাতায় কালি ঢেলে, ভাঙচুর করে বেরিয়ে আসে। শেষমেশ শহরতলিতে চাকরি নিয়ে সেখানকার হোটেলের ছাদে দাঁড়িয়ে তার পরিচিত না-দেখা পাখির ডাক শুনতে পায়। সিদ্ধার্থ কলকাতাতে থাকার সময় নিউ মার্কেটের পাখির বাজার চষে ফেলেছিল এই পাখিটার ডাক শুনবে বলে। পায়নি। শহরতলি তাকে দুটোই দিল: চাকরি আর পাখির ডাক। এইখানেই সিদ্ধার্থর মুক্তি— হোটেলের ছাদে দাঁড়িয়ে সে শুনতে পেল খোলা হাওয়ায় ভেসে আসা ‘রাম নাম সৎ হ্যায়’। শহরতলিতে গিয়ে কি সিদ্ধার্থর শহুরে সত্তার মৃত্যু ঘটল? ‘আগন্তুক’ ছবির কথা একটু আগে বলেছি। সেই ছবির একটা চরম সংঘাতের দৃশ্যে শহুরে মানুষের প্রশ্নবাণে জর্জরিত অভিমানী মনোময় মিত্র নিজের না-শহুরে পরিচয় কাউকে বোঝাতে না পেরে, আর থাকতে পারেননি রোল্যান্ড রোডে তার একমাত্র আত্মীয় ভাগ্নি অনিলার বাড়িতে। তিনি শান্তি পেয়েছিলেন শহর থেকে অনেক দূরে সাঁওতালদের মধ্যে। একটা মজার কথা না বলে থাকতে পারছি না, এই শহর থেকে পালানোর ব্যাপারে সত্যজিৎ বেশ কনসিস্টেন্ট ছিলেন— তাঁর গপ্পে শহরে কুকাজ করে পালিয়ে সবাই মফঃস্বলেই যেতেন— কেউ খুব একটা অন্য শহরে যাওয়ার কথা ভাবতেন না। যেমন মিস্টার শাসমল। ‘মিস্টার শাসমলের শেষ রাত্রি’ গল্পে পার্টনারকে ‘খুন’ করলেন (আদতে বন্দুকের টিপ মিস করেছিলেন— থাঙ্কস টু ইয়েট এনাদার শহুরে ফেনোমেনন: লোডশেডিং), পালিয়ে উঠলেন উত্তর বিহারের ফরেস্ট বাংলোতে। কেন, শহরের মধ্যে লুকিয়ে থাকাটাই তো বেশি সহজ? বা আরেক শহরে চম্পট দিলেও তো লুকোনো যায়! না কি শাসমলের ওই পথ ধরে নেপাল পালানোর প্ল্যান ছিল? গল্পে যদিও ওঁর সেই সুযোগ আর হয়নি। সেই রাত্রে ওঁর হাতে মারা যাওয়া সব জীবজন্তু একে একে এসে দেখা দিল, সেই পার্টনারও হাজির হলেন। প্রথমে শাসমলের মনের ভূত হয়ে, আর তার খানিক পরেই একদম সশরীরে ও স-পুলিশে।
সত্যজিতের বেশ কিছু গল্পে শহুরে লোকেরা একটু কুটিল— খলনায়ক টাইপের। ‘চিলেকোঠা’ গল্পটার ব্যাপারে আগেই একটু আভাস দিয়েছি। সত্যজিৎ হয়তো লক্ষ করেছিলেন যে শহুরে লোকেরা শহরে অলিগলি চলি রাম করতে করতে মগজেও জিলিপির প্যাঁচ গজিয়ে ফেলেন। এই চরিত্ররা অনেকেই শুরু থেকে খারাপ নন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধনদৌলত আর সাফল্য অর্জন করে তাঁরা একদম একশো আশি ডিগ্রি বদলে গিয়েছেন। তাঁদের পুরোনো দিনগুলি ও তার সাথে সেই দিনের পরিচিতদের ভুলে যেতে শুরু করেছেন। যেমন বিপিন চৌধুরী। ‘বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম’ গল্পের নামকরা শিল্পপতি (শিল্পপতিদের প্রতি রায়বাবুর ‘প্রীতি’ বেশ বোঝা যাচ্ছে)! কিন্তু বিপিনবাবু সাফল্যের অহংকারে পুরোনো বন্ধুদের অবজ্ঞা করেন। ‘ধাপ্পা’ গল্পে পুরোনো বন্ধুর সন্তানদের সামান্য একটা অটোগ্রাফ দিতে অস্বীকার করেন দ্য গ্রেট ম্যাজিশিয়ান সমরেশ ব্রহ্ম। (যাঁরা অর্থের অহংকারে মানবিকতা হারিয়ে ফেলেন তাঁদের প্রতি সত্যজিৎ বিশেষ সদয় ছিলেন না। বিপিনবাবুকে হুড্রু ফলস-এ আছাড় খাওয়ান। সমরেশকে যদিও স্রেফ কিছুদিনের মনঃকষ্টে রেখেই রেহাই দেন)। ‘খগম’ গল্পে কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়া, ফ্লাই ফ্ল্যাপ দিয়ে মশা মারা, ঘোর শহুরে মানুষ ধুর্জটিবাবু খামোখা মাথা গরম করে ভরতপুরের বাবাজির পোষা কেউটে মেরে দিলেন। ‘ফটিকচাঁদ’ গল্পে ফটিকের বাবা শরদিন্দু সান্যাল হারুনের প্রাপ্য পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার বেমালুম চেপে দিলেন। অথচ এই হারুনই ফটিককে উদ্ধার করে, আশ্রয় দিয়ে, গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ফটিকের সাময়িক স্মৃতিলোপের অবস্থা ঠিক হতেই তাকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। আর সেই লোকের প্রাপ্য টাকাই ঝেড়ে দিলেন ব্যারিস্টার সান্যাল? ফটিকের বাবার মতো এরকম ছোট, মাঝারি, সস্তা পদস্খলনের উদাহরণ সত্যজিতের অনেক কাজেই আছে, কখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে, আবার কখনো সেইটাই গল্পের প্রধান উপপাদ্য। সত্যজিৎ তাঁর গল্পে বারবার দাঁড়ান একলা মানুষ, ব্যর্থ মানুষ, সামাজিক ভাবে বেশ একটু হ্যাটা হওয়া মানুষের পাশে, তাঁদের যে পদস্খলন হয়নি— এটাই তাঁদের মস্ত বড় অর্জন, সত্যিকারের সাফল্য, অনেক সময়ই সত্যজিৎ এই চরিত্রগুলিকে মিলিয়ে দেন শহরতলির সঙ্গে, বঙ্কুবাবু শহরে থাকলে কি আর পেতেন তাঁর আকাশপারের বন্ধুটিকে?

‘আগন্তুক’ ছবিতে সভ্যতাকে এড়িয়ে চলা, ‘সভ্যতা সম্বন্ধে খুব bitter’ মনোমোহন মিত্র (উৎপল দত্ত) এবং বাবলু (বিক্রম ভট্টাচার্য্য) মফঃস্বলের ছেলেমেয়েরা হামেশাই শহরে পৌঁছায় ভাগ্য অন্বেষণে, কেউ চাকরির সূত্রে, কেউ ব্যবসার সূত্রে। অর্থাৎ সেইরকম পরিস্থিতে— যেখানে আগের চেয়ে বেশি টাকাপয়সা উপার্জনের একটা প্রবল সম্ভাবনা আছে। সেই টাকা যেন মাথা ঘুরিয়ে না দেয়, মানবিকতার কম্পাসের কাঁটা যেন ট্রু-নর্থ থেকে বিচ্যুত না হয়, এইরকম একটা সতর্কবাণী এই ধরনের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে সত্যজিৎ চারিয়ে চেয়েছিলেন তাঁর পাঠক-পাঠিকা কিংবা সিনেমা-দর্শকদের মনে। ‘সীমাবদ্ধ’ ছবিটাতে ফিরে আসি। টানটান সংকট। রপ্তানি করা হবে যে ফ্যানগুলো, তাতে রং করার ত্রুটি ধরা পড়েছে। ক্রেতা মাল ফেরত দিলে (দেবেই) কোম্পানির লোকসান। আরো বড় লোকসান শ্যামলেন্দুর— তার আর ডিরেক্টর হওয়া হবে না। এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার মাইনেটাও হবে না। সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতে ব্যাঁকা আঙুলে ঘি তুলতে শ্যামলেন্দুর মধ্যে দিয়ে সত্যজিৎকে লেবার অফিসার তালুকদার খুঁজে বের করতে একদমই বেগ পেতে হয়নি। তালুকদারের সাহায্যে হিন্দুস্তান পিটার্স-এর ফ্যান বিভাগের ইউনিয়নের বোমাবাজির চোটে ফ্যাক্টরি লক-আউট হয়ে গেল। আইনগত কারণেই ফ্যানগুলি আর ইরানে গেল না। শ্যামলেন্দু ডিরেক্টর হল। তালুকদারের পদোন্নতি হল। আর হাসপাতালে পড়ে রইল একটা বোম খাওয়া দারোয়ান— তিওয়ারি। হয়তো পশ্চিমের কোনো একটা ছোট শহর থেকে মহানগরে এসেছিল অর্থান্বেষণে। রাজায় রাজায় যুদ্ধে বেচারা উলুখাগড়া ভিক্টিম হয়ে পড়ে রইল!
এই সুবিধাবাদী শহুরে মানুষের তুলনায় সত্যজিতের শহরতলির লোকেরা অনেক সাধাসিধে। গুপী হয়তো একটা এক্সট্রিম— বটতলার বুড়োদের টিটকিরিকে ‘সুখ্যাত’ হিসেবে ধরে অকারণ আনন্দ পায়! কিন্তু সত্যজিতের অন্য লেখায় শহরতলির লোকেরা, বিশেষ করে যাদের মধ্যে উগ্র অর্থনৈতিক সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা তুলনামূলক ভাবে কম, তারা অনেক নম্র আর নীতিপরায়ণ মানুষ— ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ ছবিতে বিকাশ সিংহের ভাষায়— ‘ভালমানুষ’। এই সাধাসিধে শহরতলির মানুষরা শহরে এসে যে বেগতিকে পড়ে, সেইরকম উদাহরণ আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক দেখেছি। ইস্পাত কারখানার কর্মীরা, অফিসাররা, অনেকে রিটায়ার করে কলকাতায় এসে শহরের জীবনযাত্রার সাথে মানিয়ে নিতে হাবুডুবু খেতেন। শহরের স্বাচ্ছন্দ্যের মোহ কাটলে তাঁদের অনেককেই কয়েক বছর পরে দেখেছি, ‘নাঃ, আমার দুর্গাপুর বা আমার রানিগঞ্জ বা আমার আলিপুরদুয়ারই বেশ ছিল’ অবস্থায় পৌঁছে যেতে। নিম্নবিত্ত মানুষ হলে তো কথাই নেই, আরো ভোগান্তি কপালে! সত্যজিতের কিছু গল্পেও সেইরকম নমুনা আছে। ‘কাগতাড়ুয়া’ গল্পটাই ধরুন। অভিরাম বর্ধমানের কাছের একটা গ্রাম থেকে চাকরি করতে যায় শহরে— মৃগাঙ্কবাবুর বাড়িতে। সেখানে সে মৃগাঙ্কবাবুর ঘড়ি চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়, আর চাকরি খুইয়ে গ্রামে এসে অসুখে পড়ে মারা যায়। বেচারা অভিরাম যে মৃগাঙ্কবাবুর ঘড়ি চুরি করেনি সেটা বেঁচে থাকতে সে প্রমাণ করে যেতে পারল না। মারা গিয়ে, কাকতাড়ুয়া হয়ে, তার গ্রামের কাছে গাড়ি খারাপ হওয়া মৃগাঙ্কবাবুর স্বপ্নে এসে জানিয়ে যেতে হল যে সে নিরাপরাধ! তবে হ্যাঁ, সত্যজিতের কিছু গল্পে বা ছবিতে উল্টোটাও আছে। মানে শহরতলির লোকেরা শহরের লোকদের ঠকাচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে অবিশ্যি সেটাকে ফচকেমি বলে চালিয়ে দেয়া যায়, যেমন ‘বিষফুল’ গল্পে কাঠঝুমরির ভগবান আর পবিত্রবাবু মিলে চেঞ্জে আসা হাঁপানির রুগী বেচারা জগন্ময়বাবুকে মানুষ-মারা ফুলের গাছের ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিল! স্রেফ এই কারণে যে, জগন্ময়বাবু তাঁদের এক পরিচিত লেখকের ছুটি কাটানোর সময়ে থাকার বাংলোটি দখল করে ছিলেন। অবশ্য এই রকম ফচকেমির চেয়ে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে রয়েছে গ্রাম থেকে আসা ‘চারুলতা’র উমাপদ চরিত্রটি— তার মধ্যে পুরোমাত্রায় খলনায়কের চাল!
গল্পে, সিনেমায়— প্রায় যে কোনো সৃষ্টিশীল কাজে, এমনকী সমাজব্যবস্থায়ও, খলনায়কের চারিত্রিক ত্রুটিগুলোকে প্রকট করতে নায়কের ভাল দিকগুলো জোরালো করে তুলে ধরাটাই নিয়ম। সাদা-কালোর তফাতটা এতে বেশি মজবুত হয়। অধিকাংশ সময় সত্যজিৎ সাদা রং বেশি চড়িয়েছেন শহরতলির চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে। এটা একটা প্রচলিত স্টিরিওটাইপের ধারা বজায় রাখা (শহর কুটিল, আর শহরতলি সরল— এটা একটা স্টিরিওটাইপ ছাড়া কিচ্ছু নয়, আমরা সবাই জানি, কিন্তু জেনেও অনেকে এই সরলীকরণে বিশ্বাসও করি), না কি পাঠক-দর্শকের প্রতি একটা পথ-নির্দেশিকা— সেটা বলা আমার পক্ষে দুষ্কর। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, ছোটবেলায় সত্যজিতের লেখা পড়তে গিয়ে আমার কাছে শহরতলির চরিত্রগুলি ভীষণ চেনা চেনা লাগত, আর মনে হত, আরেব্বাস, এই লোকটা তো শহরে থেকেও দিব্যি আমাদের ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে পারে! আর একটু বড় হয়ে, শহরের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের মধ্যের বিপিন চৌধুরীকে, আদিত্যনারায়ণ চৌধুরীকে, সমরেশ ব্রহ্মকে চিনে নিতে সুবিধে হয়েছে সত্যজিতের পথ-নির্দেশিকা দেখে। চিনতে পেরেছি ‘জন অরণ্য’ ছবির স্যুট-টাই পরা, ফ্লুরিজ-এ খেতে যাওয়া কর্পোরেট-দালাল নটবর মিত্তিরকে। চিনতে পেরেছি ফরেস্ট বাংলোর দারোয়ানের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ‘থ্যাঙ্ক গড ফর করাপশন’ বলা ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র অসীমকে।
আমাদের ছেলেবেলার তুলনায় পৃথিবীর মানচিত্র এখন অনেক বেশি সমতল। সত্যজিতের সময়কার শহর আর শহরতলির সামাজিক ফারাক এখন অনেকটাই কমে এসেছে। এই ফারাকটা কমে আসাতে অর্থনৈতিক উন্নতিও ঘটেছে। হয়তো সামাজিক উন্নতিও ঘটেছে। কিন্তু মানবিকতার উন্নতি ঘটেছে, এর প্রমাণ খুব বেশি মিলছে না। সত্যজিতের চরিত্রাঙ্কনে এই চটজলদি অর্থনৈতিক অগ্রগতিই তো যত গন্ডগোলের গোড়ার কারণ! কীভাবে সেই গন্ডগোলের আঁচ থেকে বেঁচে থাকতে হবে? কীভাবে ধরে রাখা যাবে ‘শহরতলির’ মানবিকতা? যে মানবিকতা সামাজিক অগ্রগতির ধারাকে পা মিলিয়ে চলতে শেখায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে? এই প্রজন্মের শহরতলির ছেলেমেয়েরা আমাদের মতো সত্যজিতের লেখা বা সিনেমা গোগ্রাসে গেলে কি না জানি না, তবে বইয়ের তাক থেকে বাঁধাই ছিঁড়ে যাওয়া, হলদেটে হয়ে যাওয়া বইগুলো বের করে পড়লে এখনো চরিত্রগুলোকে দিব্যি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। তাদের ব্যবহারের তারতম্যে সাদা আর কালোর ফারাকগুলো মনে হয় এখনো আশেপাশে দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। তাই তখন সত্যজিতের লেখাগুলিকে, ছবিগুলিকে সত্যিই কালজয়ী মনে হয়। মনে হয় চিরদিনের মত অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার আগে ‘আগন্তুক’-এর মনোমোহন মিত্র তাঁর ভাগ্নির ছোট ছেলেটিকে প্রশ্ন করছেন, ‘কোন জিনিসটা কখনো হবে না কথা দিয়েছ?’ আর বাবলুর মত আমরা বলে উঠছি, ‘কূপমণ্ডূক’!
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook