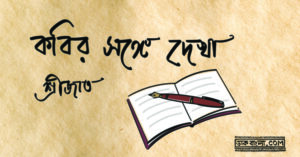শিলং। অদূরে পাহাড়ের ঢালে বিলি কাটছে মেঘ। অলস মধ্যাহ্নে, একটি দেওদার গাছের ছায়ায় খ্যাতনামা বাঙালি ভাষাবিদের বই পড়ছিল অমিত রায়। বিষয়: বাংলা শব্দতত্ত্ব। যাঁর দৌত্যে ‘শেষের কবিতা’র প্রোটাগনিস্টের সঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আলাপ ঘনীভূত হয়েছিল উপন্যাসের পৃষ্ঠায়, সেই রবীন্দ্রনাথই অবশ্য তার এক দশক আগে সুনীতিবাবুর সঙ্গে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বাংলা ভাষার ইতিহাসের অন্যতম স্মরণযোগ্য শব্দতাত্ত্বিক সংলাপে। সুনীতিকুমার-সহ অনেককেই, বিশ-তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ নাগাড়ে উপরোধ করেছিলেন একটি আগন্তুক ইংরিজি শব্দের বিকল্প বাংলা পরিভাষা খুঁজতে। শব্দটি: ‘কালচার’। আক্ষরিক অনুবাদের নিগড় থেকে বেরিয়ে, বাংলা ভাষায় কালচার-এর স্বীকরণ ঘটানো যায় কি, এ-হেন সন্ধানেই ওই সময়কালে তৎপর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশের দশকের গোড়ায় সেই আকাঙ্ক্ষিত শব্দের উদ্বোধন ঘটালেন সুনীতিকুমার-ই৷ শব্দটি: ‘সংস্কৃতি’!
বাঙালির ‘ইডিওলজি’ আদতে কোনটা? লিবারালিজম? বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ? মার্কসবাদ? এই শতকের গোড়ায় এমন বেয়াড়া প্রশ্ন তুলেছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, ইতিহাসবিদ অ্যান্ড্রু সার্টোরি। তাঁর বিপুলবপু সন্দর্ভে সার্টোরি অবশ্য নিশ্চিত: বাঙালির মতাদর্শ একটাই! তা, কালচার। ওরফে, সুনীতিকুমার-প্রবর্তিত সংস্কৃতি। কিন্তু, সংস্কৃতি-কে কালচারের পাটোয়ারি অনুবৃত্তি হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া যাবে না। বরং, শব্দ হিসেবে সংস্কৃতি-র অভিযাত্রাই শুরু হয়েছিল বাংলাভাষী মননের স্বরাজচর্চার দ্যোতনায়।
‘কখনও কখনও হয় এমন, যখন নিতান্তই হালনাগাদ কোনও শব্দকে বহু তামাদি, প্রাচীন ও দূরবর্তী মনে হয়। বাংলায় কালচারের প্রতিশব্দ-অর্থে সংস্কৃতি শব্দটাও এই গোত্রের,’ রবীন্দ্রনাথ-সুনীতিকুমারের এই আলাপচারিতায় আলো ফেলে এক বক্তৃতায় একদা এমনই বলেছিলেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ শতকের বিশের দশক। তদ্দিনে কালচার-অর্থে বঙ্কিমের চালু করা ‘অনুশীলন’ অস্তগতপ্রায়। হাতফেরতা পরিভাষা হিসেবে আসীন নবজাত ‘কৃষ্টি’। ওর আশেপাশেই, ১৯২২ সালে সুনীতিকুমার ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। প্যারিস-নিবাসী মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে ওই সময়ই উনি প্রথম অবগত হন মরাঠিতে দিব্য-বহাল ‘সংস্কৃতি’র অস্তিত্বের। ‘Culture-এর বেশ ভাল প্রতিশব্দ ব’লে শব্দটি আমার মনে লাগে,’ অনেক পরে, চল্লিশের দশকের প্রথম পাদে, ‘সোনার বাংলা’ পত্রিকার ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যায় স্মরণ করবেন সুনীতিকুমার। ‘আমার বন্ধু শব্দটি পেয়ে আমার আনন্দ দেখে একটু বিস্মিত হন— তিনি ব’ললেন্ যে তাঁরা তো বহুকাল ধ’রে মারাঠী ভাষায় এই শব্দ ব্যবহার করে আসছেন্’— লিখেছিলেন তিনি।
কালচার হিসেবে কৃষ্টির ব্যবহার নিয়ে সুনীতিবাবুর আপত্তিটা ছিল মোদ্দা। ওঁর প্রথম যুক্তিটা আদ্যন্ত শব্দতাত্ত্বিক। মূল লাতিনে ‘কালচার’ শব্দটার তিনটে অর্থ হয়, তাঁর প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন তিনি। কী কী? পয়লা নম্বর, col ধাতুর রণন, যার আভিধানিক অর্থ চাষ করা— অতএব, প্রস্তাবিত কৃষ্টির সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠ ভাবে লাগসই। কিন্তু এর বাইরেও, যত্নআত্তি কিংবা পুজো করার অর্থেও কালচারকে ভাবার রেওয়াজ রয়েছে লাতিনে, এ-ও উপরি জানিয়েছিলেন তিনি। মাথায় রাখতে হবে, ছাপার অক্ষরে, লাতিন তত্ত্বমূলের সূত্রে তাঁর এই অভিমত যখন লিপিবদ্ধ রাখছেন সুনীতিকুমার— তখনও প্রকাশিতই হয়নি কালচার-এর ত্রিস্তরীয় অর্থ-উদ্ঘাটন করে রেমন্ড উইলিয়ামসের বিস্ফোরক ‘কিওয়ার্ডস’! উইলিয়ামসের ওই বই বেরোনোর সম্ভাবনা তখনও তিন দশক দূরত্বের। আদি লাতিন শব্দ খুঁড়ে এর পর সুনীতিকুমারের বিশদ ব্যাখ্যান: কালচারের জুড়ি হিসেবে বাংলায় বড়জোর উৎকর্ষ-সাধনও চলে যেতে পারে, কিন্তু কৃষ্টি কদাপি নয়। ‘কৃষ্টির অর্থগত পরিবর্তন বৈদিক আর সংস্কৃত-সাহিত্যে যা দেখা যায়, তা থেকে কিন্তু বাংলায় গৃহীত কালচার-অর্থ সমর্থিত হয় না,’ পর্যবেক্ষণ তাঁর।
সুনীতিকুমার-সহ অনেককেই, বিশ-তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ নাগাড়ে উপরোধ করেছিলেন একটি আগন্তুক ইংরিজি শব্দের বিকল্প বাংলা পরিভাষা খুঁজতে। শব্দটি: ‘কালচার’। আক্ষরিক অনুবাদের নিগড় থেকে বেরিয়ে, বাংলা ভাষায় কালচার-এর স্বীকরণ ঘটানো যায় কি, এ-হেন সন্ধানেই ওই সময়কালে তৎপর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশের দশকের গোড়ায় সেই আকাঙ্ক্ষিত শব্দের উদ্বোধন ঘটালেন সুনীতিকুমার-ই৷ শব্দটি: ‘সংস্কৃতি’!
বৈদিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ‘সংস্কৃতি’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন তিনি– ‘কৃষ্টি’ শব্দটার তিন ধরনের কার্যকারিতা রয়েছে। প্রথমত, কর্ষণ এবং চাষ-করা খেত— এই দুই কৃষিজ দ্যোতনা বহন করে কৃষ্টি। এর পাশাপাশিই, কর্ষণক্ষেত্রের ব্যঞ্জনা প্রসারিত হয় দেশ ও জাতির বৃহত্তর দ্যোতনায়। এ যদি তরুণ বৈদিক সাহিত্যর দৃষ্টান্ত হয়, সুনীতিকুমারের প্রস্তাবনা: পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই নিছক চাষবাসের নিগড়ে আটকে যেতে থাকে কৃষ্টির একদা-গভীরতর অর্থ। আর, সংস্কৃতি? ক্ষিতিমোহন সেনের অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে সুনীতিকুমার দেখালেন, ‘সংস্কৃতি’র ঐতিহাসিক উল্লেখ যদিও-বা নেই বৈদিক সাহিত্যে, তবু, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইশারা রয়েছে তার। সুনীতিকুমারের মন্তব্য: কালচার-এর ব্যাপকতর ব্যঞ্জনার সঙ্গে সংস্কৃতি-শ্লিষ্ট এই ভাবরাজি মোটেই খাপছাড়া নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও, সংস্কৃতির পরম কর্তব্য নির্দিষ্ট রয়েছে কালচারের মতোই— তার উদ্দেশ্য হল, নিজের নৈতিক উৎকর্ষের দিকে যাত্রা। সেই শ্লোকে বলা হচ্ছে— ‘শিল্পই হল আত্মসংস্কৃতি’ (যা ‘ছন্দের প্রকৃতি’ নামের বক্তৃতায়, ১৯৩৩-এ, উদ্ধৃত করবেন রবীন্দ্রনাথ)।
অবশ্য, ‘কৃষ্টি’ বিষয়ে সুনীতিকুমারের আপত্তি কেবলই শব্দতত্ত্বের চৌখুপিতে আটক ছিল না সে-দিন। ওঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুযোগ ছিল সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ অর্থের অপব্যাখ্যা নিয়ে। ‘সংস্কৃতি’ নামের ওই প্রবন্ধে সুনীতিকুমার সভ্যতা এবং সংস্কৃতি, উভয় ধারণাকে কিঞ্চিৎ দূরত্বেই রাখতে চেয়েছেন। সুনীতিকুমার দেখালেন, সভ্যতার ধারণা প্রাচীন সময় থেকেই রমরমিয়ে রয়েছে। তুলনায়, ‘সংস্কৃতি’র বোধ ঈষৎ নবীন। আদি গ্রিসে, কিংবা বৈদিক ভারতে, কে সভ্য আর অসভ্যই বা কে, এর একটা নিক্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কোথাও তার মানদণ্ড ছিল পল্লবিত নগরসভ্যতার সংশ্লেষ, আবার ভারতের মতো ব্যতিক্রমী জায়গায় বর্ণব্যবস্থাই ছিল সেই প্রত্যাশিত মাপনি। অধিকাংশতই, পুরবাসী যিনি, তিনিই সিভিল তথা সভ্য— যা, আদতে, ‘সিভিটাস’ তত্ত্বমূলের প্রতি অনুগত, অর্থাৎ শহর। আরবি উপাত্ত যাচাই করলেও দেখা যাবে, মদিনাবাসী যিনি, তিনিই সংস্কৃতিবান। সভ্যতার ধারণা আবার ব্যাপকার্থে ফিরে আসে আধুনিক সময়ে, ইংরেজ শ্রেষ্ঠত্বের বাহন হয়ে, সঙ্গে জুড়ে যায় নবোদ্ভূত ডিসিপ্লিন: নৃতত্ত্ব। কিন্তু, এই ধরনের ‘পার্থিব’, ‘ভৌত’ বহিরঙ্গ ছাড়াও, উদ্বৃত্ত থেকে যায় জাতির অনির্বচনীয়, অবিচ্ছিন্ন, বিমূর্ত অন্তঃসার। ইটকাঠ, ঘরবাড়ি আর নগরসভ্যতার কেজো ফিরিস্তি দিয়ে ধরা সম্ভব নয় তা। মোদ্দায়, সেটিই সংস্কৃতি! এ ভাবেই ‘সংস্কৃতি’ শব্দে সুনীতিকুমার ধরতে চান প্রতিটি সভ্যতার অন্তর্লীন সত্তাসার: তার অমোঘ প্রেরণাভঙ্গি, তার ধ্রুব প্রকাশমাধ্যম। এ-হেন বিমূর্ত অভিব্যক্তিকে অতঃপর ‘কৃষ্টি’ অভিধায় সাঁটানো বড়ই গা-জোয়ারি, এমনই পর্যবেক্ষণ ছিল তাঁর। যদিও, সভ্যতা আর সংস্কৃতির আপাত-দ্বৈত স্বীকার করেও সুনীতিকুমারের সংযোজন: উভয়ের দেনাপাওনা কেবল অবিমিশ্র বিরোধের নয়, বরং অন্তরঙ্গ সমবায়েরও বটে। সভ্যতা আর সংস্কৃতি সেখানে একে অন্যের ঘনিষ্ঠ সম্পূরক। ইউরোপীয় ভাষায় ‘কালচার’ আর ‘সভ্যতা’র সম্পর্ক, ফলত, সমানুপাতিক। এই সূত্রেই, ‘সংস্কৃতি’ প্রবন্ধে সুনীতিকুমারের এক লাইনের উপমান-আশ্রিত সংজ্ঞায়ন— ‘সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা…– culture।’
সুনীতিকুমার-প্রণোদিত এসব যুক্তিকে ব্যবহার করে তিরিশের দশকের গোড়ায় কৃষ্টির বিরুদ্ধে কার্যত ধর্মযুদ্ধে নামলেন রবীন্দ্রনাথ। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ততদিনে যুক্তি দেখিয়েছেন, ‘কৃষ্টি নবরচিত নয়, কিন্তু অর্থে অবিকল কালচার।’ এমন চিন্তাশূন্য, অপরিমেয় কৃষ্টি-ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন দাঁড়ালেন সুনীতিকুমারের পক্ষে। কালানুক্রমিক রবীন্দ্ররচনার খতিয়ান নিলে দিব্য বোঝা যাবে, কোনও-না-কোনও তরিকায়, তিরিশের দশকের গোড়ায় লিখিত বিচিত্র রচনারাজির ফাঁকফোকরে রবীন্দ্রনাথ গুঁজে দিচ্ছিলেন কৃষ্টি-বিষয়ক তাঁর অসন্তোষ। এর উদাহরণ অজস্র, যা মিলবে ওই সময়ে লিখে ফেলা ‘গদ্যছন্দ’, ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’, কিংবা ‘মানুষের ধর্ম’-র খাঁজে-কন্দরে। তাসের দেশের সংশোধিত বয়ানে এগোতে থাকে রাজা আর ইস্কাবনের সংলাপ: হতভম্ব রাজা ইস্কাবনবৃন্দের গলায় কৃষ্টির জয়নাদ শুনে জিগ্যেস করেন, ‘কৃষ্টি? এটা কী জিনিস?’ জবাব আসে ফিরতি— ‘কৃষ্টি মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন!’ এই কৌতুকী টিপ্পনীতেই কৃষ্টি-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নারাজ মনোভঙ্গি প্রকাশিত। ওই সময়েই রবীন্দ্রনাথ সবিস্তার চিঠি লিখলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে, পরবর্তীতে যা ‘কালচার ও সংস্কৃতি’ নামে আদল পায় আস্ত প্রবন্ধের। রবীন্দ্রনাথের বিরক্তিময় অনুযোগ: ‘কালচার্ শব্দের একটা নতুন বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েছে; চোখে পড়েছে কি? কৃষ্টি। ইংরেজি শব্দটার আভিধানিক অর্থের বাধ্য অনুগত হয়ে ঐ কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে। এঁটেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কাম্ড়ে ধরে ভাষার গায়ে ওটাও তেমনি কামড়ে ধরেছে। মাতৃভাষার প্রতি দয়া করবে না তোমরা?’ চিঠির তারিখ: ৮ ডিসেম্বর, ১৯৩২। ওই চিঠিতেই স্পষ্ট জানালেন তাঁর আক্ষেপ– ‘অন্য প্রদেশে ভদ্রতা বোধ আছে। এই অর্থে সেখানে ব্যবহার হয় ‘সংস্কৃতি’।… তোমাদের সম্পাদকবর্গের কাছে (অর্থাৎ, পরিচয়ের কাছে) আমার এই প্রশ্ন, চিৎপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষ বা চিত্তোৎকর্ষ শব্দটাকে কালচার অর্থে চালালে দোষ কি?’ অস্যার্থ: ইংরিজির খিদমত-খাটা ‘কৃষ্টি’তে জমি-চষার দ্যোতনাটুকু বহাল। বাংলা মননের স্বরাজে উন্মুখ রবীন্দ্রনাথের কাছে, এই আকাট অনুকরণ সম্ভবত ঈষৎ অনভিপ্রেত ছিল।
মাথায় রাখতে হবে, গোটা উনিশ শতক ধরেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কালচারের তত্ত্বকল্প জাঁকিয়ে বসছিল ক্রমশ। জার্মানি ছেয়ে ফেলে কুলতুর আর বিল্ডং-এর ধারণা, ওদিকে ১৮৬০-এর দশকে ম্যাথু আর্নল্ডের ‘কালচার অ্যান্ড অ্যানার্কি’ নামধেয় ইস্তেহারে সমাজের ওপর বুর্জোয়া কর্তৃত্বের দাবি কালচারে মণ্ডিত হয়ে, আদল পায় এক শীলিত নন্দনবিভার। অবশ্য, কালচারের বঙ্গীকরণের রেওয়াজ স্রেফ সুনীতিকুমারে আরম্ভ হয়নি। তার মুখপাত উনিশ শতকেই! ততদিনে বাংলা প্রবন্ধের আর এক বাতিঘর, বঙ্কিমচন্দ্র সুপারিশ করে ফেলেছেন কালচারের আকাঙ্ক্ষিত পরিভাষার। বঙ্কিমের মত: কালচার-এর উপযুক্ত বাংলা জুড়ি, ‘অনুশীলন’। ওঁর সংলাপী বই, ‘ধর্ম্মতত্ত্ব’-এর পাতায় অবশ্য এমন বিশদ ব্যাখ্যান নেই। বরং গুরু আর শিষ্যের দ্বিপাক্ষিক কথোপকথনের ফাঁকে, আচার্য ঈষৎ ফুকরে ওঠেন: ‘কালচার বিলাতী জিনিষ নহে। উহা হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ।’ এমন সরোষ ঘোষণার জের ছিল কিছু কাল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামী তরুণদের চর্চায় পল্লবিত হয়ে, বঙ্কিম-প্রস্তাবিত অনুশীলন-ধর্ম সাড়া ফেলেছিল ব্যাপক। আস্তে-আস্তে থিতিয়ে আসে তার জের। ১৯২০-র দশক। তদ্দিনে দেশের রাজনৈতিক ভরকেন্দ্র সরে গেছে বাংলা থেকে। সুভাষচন্দ্র বসু-র উত্থান ভবিষ্যতের জঠরে। শিক্ষিত বাঙালির বৈঠকখানা থেকে অন্তর্হিত হতে হতে, জাতীয়তাবাদ ক্রমেই প্যান-ইন্ডিয়ান চেহারায় আবির্ভূত। প্রদেশে-প্রদেশে মানসিক লেনদেন ঘনিয়ে উঠছে ক্রমশ, বাঙালির একক রাজ কার্যত খর্ব। ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রে ধীরে ধীরে চারিয়ে যাচ্ছে যুক্তপ্রদেশীয় কাঠামোটুকু। এমন আবহেই, সুনীতিকুমার মরাঠি থেকে ধার নেন শব্দ। গড়ে তোলেন বাঙালি সংস্কৃতির নিজস্ব নিশান। কিন্তু, সুনীতিকুমার সংস্কৃতির এই বয়ানকে বদ্ধ রাখতে চাননি বাঙালি জাতিসত্তার এঁদো সনদে। শব্দের এই আন্তর্জাতিক বিনিময়ই তার অমোঘ প্রমাণ। অতীতে, বঙ্কিম যেখানে কালচারে মিশিয়ে দিয়েছিলেন চর্যা-র দ্যোতনা— সুনীতিকুমারের সংস্কৃতি-ভাবনা জারিত হয় সত্তার নান্দনিক ক্রমোত্তরণে।
সভ্যতার ধারণা আবার ব্যাপকার্থে ফিরে আসে আধুনিক সময়ে, ইংরেজ শ্রেষ্ঠত্বের বাহন হয়ে, সঙ্গে জুড়ে যায় নবোদ্ভূত ডিসিপ্লিন: নৃতত্ত্ব। কিন্তু, এই ধরনের ‘পার্থিব’, ‘ভৌত’ বহিরঙ্গ ছাড়াও, উদ্বৃত্ত থেকে যায় জাতির অনির্বচনীয়, অবিচ্ছিন্ন, বিমূর্ত অন্তঃসার। ইটকাঠ, ঘরবাড়ি আর নগরসভ্যতার কেজো ফিরিস্তি দিয়ে ধরা সম্ভব নয় তা। মোদ্দায়, সেটিই সংস্কৃতি! এ ভাবেই ‘সংস্কৃতি’ শব্দে সুনীতিকুমার ধরতে চান প্রতিটি সভ্যতার অন্তর্লীন সত্তাসার
শুধু সুনীতিকুমার নন। এর কয়েক দশক পর বিতর্কে অংশ-নেওয়া নীহাররঞ্জন রায়ের কলমেও উঠে এল একই অবস্থান। ‘কৃষ্টি, কালচার, সংস্কৃতি’-তে নীহাররঞ্জন লিখলেন: শিল্পকলা বা সাহিত্য, যা কিনা সংস্কৃতির পরিধিভুক্ত— তা তাৎক্ষণিক চাহিদার বস্তু নয়। নিতান্ত ভাতকাপড় আর জৈবিকতার অনেক দূরবর্তী সংস্কৃতির সেই ধারণা। সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে শুদ্ধতা, শীলন আর সম্মার্জনার গভীর তাৎপর্য— যা নিজেকে বস্তুদুনিয়ার উৎকট হাঁ-মুখো গ্রাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ব্যক্তিমানুষের অন্তর্দেশে জারিয়ে দেয় অধ্যাত্মিক ক্রম-উত্তরণের নকশা। ফলে, আত্মকর্ষণের এই মহতী প্রকল্পে এঁদো পার্থিবতাকে টেনে আনলে মুশকিল। একই কথা কি সুনীতিকুমারেও শোনা যায় না, যিনি সংস্কৃতিকে দেখবেন অন্তঃকরণের ক্রম-উড়াল হিসেবে? অতঃপর, সুনীতিকুমার-প্রণীত সংস্কৃতিবোধের ঈপ্সিত লক্ষ্যবিন্দু: সত্তার পরম মুক্তি।
সুনীতিকুমারের প্রস্তাবনা অবশ্য জীবৎকালেই খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে বহু বার। তার ইতিহাস দীর্ঘ। ১৯২০-র দশকেই অনুযোগ ব্যক্ত করেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি: কালচারে সঙ্গত করতে শ্রেষ্ঠ প্রতিশব্দ নিঃসন্দেহে কৃষ্টি। এটিমোলজি দিয়ে ব্যাখ্যা করে সবিস্তারে বিদ্যানিধি বোঝান, কালচারের মূলে যেহেতু লাতিন উৎস কুলতুরা, মানে চাষবাস, বাংলা অর্থেও সেই ব্যঞ্জনাকে নিরাপত্তা দেওয়া প্রতিশব্দকারের জরুরি কর্তব্য। কেউ বলতেই পারেন, রবীন্দ্র-প্রস্তাবিত শব্দে অ-ভদ্রলোক কায়িক শ্রমের সঙ্গে ভদ্রলোকের সংস্কৃতিচর্চার পোশাকি দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল। এমনও বলতে পারেন কোনও সমালোচক: গতর-খাটানো শ্রম-বিষয়ে রবীন্দ্রভুবনের অভ্যস্ত অবজ্ঞাই প্রকাশিত হয় এসব পর্যবেক্ষণ থেকে। সম্ভবত, কালচারের ব্যাপক দ্যোতনাকে কর্ষণের নিত্যবৃত্ত, পৌনঃপুনিক, শ্রমসাধ্য, কর্জ-করা তকমায় সাঁটতে চাইছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। যা-হোক, ‘পরিচয়’ পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ১৯৩১ সালে লেখা প্রবন্ধে মেলে বিকল্প শব্দ: ‘পরিশীলন’। নিজেকে ক্রমাগত উৎকর্ষণের মাধ্যমে আত্মসত্তাকে শীলিত, শোধিত আর উন্নততর করে তোলার ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথে ছিলই। সুধীন্দ্রনাথে যেন তার-ই অন্তিম ঘোষণা। কালচারের এ-হেন সনদকে সে-দিন মোটেই বরদাস্ত করতে পারেনি ‘শনিবারের চিঠি’-র মতো পত্রিকা। সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব গবেষক সমর্পিতা মিত্র তাঁর থিসিসের অপ্রকাশিত অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ‘শনিবারের চিঠি’-র তরফে সুনীতিকুমারদের তীব্র ব্যঙ্গ করা হচ্ছে ‘কালচার-অভিমানী ঠাকুর-পূজারীগণ’-মর্মে!
এহ বাহ্য। সুনীতিকুমারের প্রস্তাবনায় জোরালোতম ধাক্কাটা এল সম্ভবত দেশভাগের সময়। ততদিনে বাঙালি মুসলিম ইন্টেলেকচুয়ালরা জ্ঞানচর্চায় বাঙালি হিন্দুর খবরদারিকে সজোরে প্রশ্ন করছেন। তাঁদের সাফ বক্তব্য: রাজনৈতিক স্বাধীনতা, যা সাকার হয়ে উঠবে পূর্ব পাকিস্তান গঠনের প্রক্রিয়ায়, তা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রাকশর্ত ছাড়া নিতান্তই বেপথু। ফলে রব উঠল: তৈরি করতে হবে সংস্কৃতির নতুন ব্যঞ্জনার্থ। উর্দু-আরবি শব্দ থেকে ধার-করা ‘তমদ্দুন’ হয়ে উঠল সুনীতিকুমার-মথিত সংস্কৃতির আশু প্রতিদ্বন্দ্বী: এই প্রথম, কালচারের দ্যোতনা সরাসরি মিশে গেল আইডেন্টিটি রাজনীতির দেহে। তমদ্দুন-কেন্দ্রিক আজাদির স্লোগান উস্কে দিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ছায়া। আবুল মনসুর আহমেদের মতো বিদ্দ্বজ্জনরা ‘সংস্কৃতি’কে অভিযুক্ত করলেন বাঙালি হিন্দুর মতাদর্শগত প্রচারযন্ত্র হিসেবে। একদিকে ‘মাসিক মোহাম্মদী’-র মতো সাময়িকপত্রের পাতায় তাঁদের অভিযোগ: বঙ্গসংস্কৃতি-প্রকল্পের সমস্ত আইকনই জন্মগত ভাবে বাঙালি হিন্দু। অন্যদিকে, সংস্কৃতি-নামক ধারণাটিই দাঁড়িয়ে রয়েছে সংস্কার-এর বীজভাবনার ভিত্তিতে। এই সংস্কার-রাজনীতির গভীরতম প্রভাব পড়েছিল ভাষা-সংস্কারে। সার্টোরির মতো ধীমান গবেষক দেখান, এ-হেন সংস্কার-প্রক্রিয়ার জেরে, এ-দেশে আধুনিকতার প্রভাতমুহূর্তে, রাতারাতি বাস্তুচ্যুত হল অগুনতি ফারসি শব্দ, অতীতে যারা অনায়াসে নিমজ্জিত ছিল বাংলা ভাষার দেহে। আবুল মনসুর আহমেদদের অভিযোগ— উৎকট সংস্কৃতায়ন-প্রক্রিয়ার শব্দপ্রচ্ছদের অন্তরালে গজিয়ে উঠল বাংলা ভাষার নতুন শরীর— খর্ব হল ভাষার ওপর মুসলমানি কর্তৃত্ব। সে-দিন আহমদদের বক্তব্য ছিল, এই অপার ভাষাসন্ত্রাসের থেকে সংস্কৃতির ধারণাটিকে বিযুক্ত রাখা কঠিন।
এ-ই যদি মুখপাত হয়, আরও কিছু কথা বলার বাকি থাকে। এই বিভাজনকামী, স্বশাসনপ্রিয় রাজনীতি-ভঙ্গিমাকে কেমন চোখে দেখতে পারতেন সুনীতিকুমার? সম্ভবত, তাঁর বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে এ-হেন রাজনৈতিক উচ্চারণ সাযুজ্যপূর্ণ ছিল না৷ বিশ্বপ্রতীতী বিশ শতকের যে যে বাঙালি ইন্টেলেকচুয়ালকে আলোড়িত করেছে সব চেয়ে বেশি, সুনীতিকুমার তাঁদের অগ্রগণ্য। সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর মতামত তাই অনায়াসে মিলে যায় সভ্যতা আর মানবপ্রজাতির রংধনু-স্বপ্নের সঙ্গে। সুনীতিকুমারের সংস্কৃতি-বিষয়ক সমস্ত ভাবনার অভ্যন্তরে যা খেলা করেছে, তা, এক নিখিল একবোধ। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় মনে করিয়েছিলেন, কালচার-এর সূক্ষ্ম সংবেদকে অনেক ক্ষেত্রেই মেলানো যাবে না আইডেনটিটি-র তত্ত্বকল্পের সঙ্গে। গোলকায়িত ভুবননামায়, ‘কালচার’ মানে আদতে অগুনতি ‘বদ্ধখোপ ও নিশ্ছিদ্র সারূপ্য বা আইডেনটিটি-র জোট’, মন্তব্য করেছিলেন শিবাজীবাবু। তারই জের টেনে, সুনীতিকুমারের বিশ্বভাবনায় আমরা আবিষ্কার করি ‘আইডেনটিটি’কে স্থাণুবৎ, চিরনিষ্পন্ন গুণাবলির সমাহার হিসেবে দেখার বিরুদ্ধে সজোর প্রতিবাদ। যেমন, ‘সংস্কৃতি’ নামের প্রবন্ধে সুনীতিকুমার থেকে-থেকে মনে করান: ‘সংস্কৃতির চরম রূপ কোনো এক সময়ে চিরকালের জন্য ব’লে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতি-ও গতিশীল ব্যাপার।’ কীরকম? ভারত-ইতিহাস ছানবিন করে সুনীতিকুমার তাঁর দৃষ্টান্ত তুলে আনেন। ‘প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার বিশিষ্ট রূপ পাবার পরে, এদেশে ইসলামী সংস্কৃতির আবির্ভাব হ’ল।’ এর পরেই তাঁর অনিবার্য মন্তব্য— ‘ইসলামী আর ভারতীয়, এই দুইয়ের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল বিরোধের সংঘাত নয়।’ অতঃপর, সুনীতিকুমারের তর্জমায়, ‘কালচার’-নামক ভাবকল্পটি নিয়ত-চলিষ্ণু ও গতিশীল, তা কোনও একমেটে, শিলীভূত সত্তাসার নয়। এক বিপুল বিশ্বজনীন মানবতার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিপাতই ছিল সুনীতিকুমারের কুললক্ষণ— বৈচিত্র আর বিবিধতাই যার আত্মা। তিনি লেখেন: ‘আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্বসংস্কৃতি… (যা) পৃথিবীর তাবৎ মানবজাতি বা মানব-সমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত ক’রে একে এক করে তুলবে।’ ঠিক এই কারণেই, কোনও পলিটিক্যাল কারেক্টনেসবাদী ঘোর নিষ্ঠার সঙ্গেও সুনীতিকুমারকে ‘এসেনশিয়ালিস্ট’ বা সারবাদী বলে দাগিয়ে দিতে পারবেন না। এ-কথা সুনীতিকুমার ওই প্রবন্ধেই লেখেন যে, ‘বিবাদের মধ্যে সংবাদ আবিষ্কার করে, এক মহান্ মিলন-সংগীত গাইবার চেষ্টা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম কথা,’ কেননা, ভারত এমন এক ব্যাপ্ত ভূগোল— যেখানে সমন্বয় আর একীভবনের দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ‘এক নব-দৃষ্ট জাতিতে নিলীন হয়ে গেল।’ অর্থাৎ, মিশ্রণেই ইতিহাসের সার্থকতম অভিব্যক্তি, এবং সহিষ্ণু উদারতাই রচনা করেছে ভারতের ধ্রুব চিত্তপট— এই আপ্তবাক্যে আস্থাবান ছিলেন সুনীতিকুমার। এই করতে গিয়ে, যে ভারত-সংস্কৃতির প্রতিমান তুলে ধরছেন তিনি— কোনও একমাত্রিক সংজ্ঞায় তাকে দাগানো যাবে না। সেই ভারত অনেকান্ত। পাষণ্ডেরও সেখানে বলার হক রয়েছে, অধিকার রয়েছে নিজের সত্যের পক্ষে কথা বলার। উপরিতলের নানাবিধ প্রপঞ্চের অন্তরালে, সুনীতিকুমার দেখান, আর্য আর অনার্য, অস্ট্রিক আর দ্রাবিড়ের এই মিলিত জোটেই ভারত-সংস্কৃতির চিরন্তন জিয়নকাঠি লুকোনো। তার ভেতরে চলাচল করে নানাবিধ আলোছায়া, থাকে করুণা, অহিংসা, মৈত্রী, ন্যায়ের প্রতি জিজ্ঞাসু, এক ঋতবাদী ভারতভাবনা।
সুনীতিকুমারের কল্পিত এ-হেন শান্তিময় ঐক্যভাবনা আজকের হিংসাদীর্ণ সময়ে কার্যত হেরে গেছে। উনি মানুষী একতাবোধের স্বপ্ন দেখেছিলেন একদা, আর আজকের ক্রান্তিকালে তা পর্যবসিত প্রযুক্তি আর শ্বাসরোধী শাসনতন্ত্রের আ-ভুবন, একচ্ছত্র দুনিয়াদারিতে। আর, গ্লোবালাইজেশনের মধ্যস্থতায়, সুনীতিকুমারের কল্পিত নিখিল বিশ্বচরাচর পর্যবসিত হয়েছে স্রেফ করতলধৃত ‘গ্লোব’-এর ধারণায়। আজকের দুনিয়া যখন গ্লোবায়নের একচ্ছত্র দাপটে ত্রস্ত, বিশ্বের ধারণা সংকুচিত হতে-হতে জড় ও মর বর্তুলাকার আমলকিতে পর্যবসিত— সুনীতিকুমার তখন কী-ই বা করেন? আজও কি, ক্কচিৎ, এ-দৃশ্য দেখা যাবে ইতস্তত: শিলং। অদূরে পাহাড়ের ঢালে বিলি কাটছে মেঘ। অলস মধ্যাহ্নে, একটি দেওদার গাছের ছায়ায় খ্যাতনামা বাঙালি ভাষাবিদের বই পড়ছে অমিত। অমিত রায়!