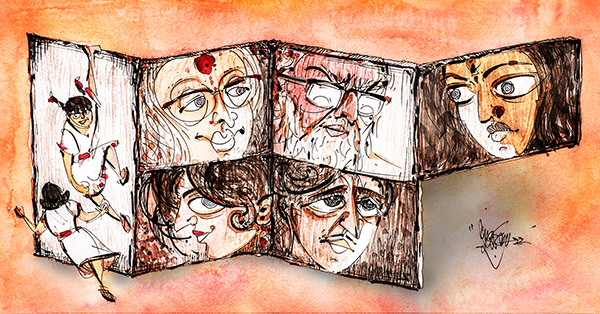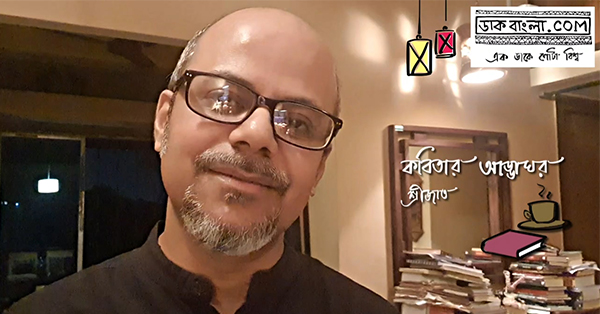উত্তরবঙ্গ ডায়েরি: পর্ব ৫

 সুমনা রায় (Sumana Roy) (July 2, 2021)
সুমনা রায় (Sumana Roy) (July 2, 2021)ঠেকে দেখা বই
সোশ্যাল মিডিয়াতে হইহই করে বইয়ের দোকান জিনিসটার এতটা উদযাপন না দেখলে বোধহয় জানতেই পারতাম না, বা অন্তত এইভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখতে পেতাম না, ‘সভ্য’ মানবজীবনে বইয়ের দোকান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সোশ্যাল মিডিয়ার ধর্ম মেনেই এই উদযাপন, আদিখ্যেতা এবং ফেটিশে পরিবর্তিত হতে বেশি সময় লাগে না। এ পরিবর্তনের ধাক্কা এতটাই প্রবল যে, এর প্রভাবে কারওর বইয়ের দোকানে যাতায়াত আছে কি না এবং কেউ শিক্ষিত কি না, এই দুটি ধারণা এক হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। শেক্সপিয়র অ্যান্ড কোম্পানি, দ্য স্ট্র্যান্ড, বাহরিসনস, দ্য বুকশপ অ্যাট জোড়বাগ, কিতাবখানা ইত্যাদি নামগুলো মুখে মুখে ঘুরতে শুরু করে। এই নামগুলোর সঙ্গে, এই জায়গাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এক ধরনের জৌলুস, বার বার জোর করে যেটাকে দেখানো হয়। এই জৌলুসটাই হয়ে ওঠে উচ্চমানের পাঠক হবার অভিজ্ঞান, এবং তার ফলে একটি উচ্চমানের সাংস্কৃতিক জীবনবোধের রূপক। মাঝে মাঝে এ ব্যাপারটাই বিরক্তিকর লাগত। উত্তরবঙ্গে এ ধরনের বইয়ের দোকান নেই, যেমন নেই ভারতবর্ষের বহু জায়গাতেই। তবে কি সেখানকার বাসিন্দাদের বই-জীবন বলে কিছু নেই?
বই কেনার মতো বই বিক্রি করার কথাও দোকানের কারওর মাথায় আসত না। আমাদের শহরে বই পড়ার রেওয়াজের যে কী অবস্থা, তার একটি বড়সড় প্রমাণ ছিল এই উদাসীনতা।
আশির এবং নব্বইয়ের দশকে ইংরেজি বই (উপন্যাস বা পদ্য সংকলন) কিনতে পাওয়া যায়, শিলিগুড়িতে এমন বইয়ের দোকান বলতে ছিল একমাত্র ‘মডার্ন এজেন্সিজ।’ সেখানে ফ্রিজ এবং অন্যান্য ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি বিক্রি হত, টাইপরাইটার বিক্রি হত, দোকান জুড়ে বিক্রি হত আরও অনেক কিছুই যা এ মুহূর্তে আমার স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে এসেছে। ঝাপসা হয়নি কেবল দোকানের এক কোণায় সাজানো কয়েকটি শেল্ফ। কারণ স্কুল-কলেজের সিলেবাসের বাইরের সব লেখকদের সঙ্গে সেখানেই মোলাকাত হত। তাঁদের বইয়ের ঝকঝকে যত সংস্করণ, ওখানে না জানি কত বছর ধরে, হয়তো কত দশক ধরেই রাখা ছিল, কারণ ওগুলো কিনত এমন কাউকে আমি দেখিনি। মনে আছে বিক্রম শেঠ-এর ‘দ্য গোল্ডেন গেট’ পড়েছিলাম ওই শেল্ফগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে, যাতে পয়সা না দিয়েই পড়ছি দেখতে পেয়ে কেউ না ধমক দেয় বা হাতে-নাতে ধরে ফেলে। বই কেনার মতো বই বিক্রি করার কথাও দোকানের কারওর মাথায় আসত না। আমাদের শহরে বই পড়ার রেওয়াজের যে কী অবস্থা, তার একটি বড়সড় প্রমাণ ছিল এই উদাসীনতা।
কলেজপাড়ায় পাওয়া যেত বাংলা বই। যদিও পাশাপাশি অনেকগুলো দোকানই সার বেঁধে ব্যবসা করত, কিন্তু শহরের লোকজন পুরো এলাকাটাকেই একটি দোকানের নামে ডাকত— বাণী লাইব্রেরি। এবার বাণী লাইব্রেরি ওই দোকানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো দোকান ছিল বলেই এ ব্যবস্থা কি না, তা বলতে পারব না। সেখানে স্কুল-কলেজের সিলেবাসের বই-ই বিক্রি হত, তবে কালেভদ্রে (এবং গত শতাব্দীতে এ ঘটনা একটু কম বিরল ছিল) দেখা হয়ে যেত বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ করা ব্যোদলেয়ারের বাংলা সংস্করণের সঙ্গে, অথবা চোখে পড়ত উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের ইতিহাস, এমনকী স্থানীয় কোনও বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের সাম্প্রতিকতম সংখ্যাটিও। দোকানগুলোকে দেখতে একেবারে ওষুধের দোকানের মতো ছিল— বই রাখা থাকত খদ্দেরদের নাগালের বাইরে। আর শুধু তাই নয়, দোকানে কর্মচারী হিসেবে যে ভদ্রলোকেরা (হ্যাঁ, সে দোকানে কোনও মহিলা কর্মচারী ছিলেন না) থাকতেন, তাঁদের ব্যবহারও ছিল প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ বেচা ফার্মাসি কর্মচারীর মতো। যেভাবে দোকানে গিয়ে ‘মাথা ধরেছে’ বললেই উপশম হিসেবে হাজির হয় এক পাতা স্যারিডন ট্যাবলেট, ঠিক সেভাবে বাণী লাইব্রেরি গিয়ে ‘ইংলিশ অনার্স পেপার ওয়ান’ বললেই রোগের ওষুধ হিসেবে হাতে তুলে দেওয়া হত একখানা লং বা কম্পটন-রিকেটস, কিংবা ডেভিড ডাইকস।
বইয়ের দোকানে বসে বই পড়া, কফি খাওয়া, লেখা— এসব ছিল আমাদের মফস্সলের কল্পনার অনেক বাইরে। মডার্ন এজেন্সিজ বা বাণী লাইব্রেরিতে বসার কোনও ব্যবস্থা ছিল না।
বইয়ের দোকান যে রীতিমতো আড্ডা মারার জায়গা হতে পারে, সেটা প্রথমবার টের পেলাম শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ মিনি-মার্কেটের ‘বুকস’ দোকানে গিয়ে। জামা-কাপড়, খাবার, ওষুধ, খেলনা, জেরক্স ইত্যাদি হরেক রকম দোকানের পিছনে একটি লুকোনো দোকান— আর লুকোনো মানে সত্যিই লুকোনো। এই দোকানের মালিক ছিলেন তপন মজুমদার। দোকানেই বাংলা সাহিত্যের একজন ছাত্র আমাকে বলেছিল, সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের ভাই এই তপনদা। তপনদা একজন অসাধারণ মানুষ— ভদ্র, সবাইকে খাতির করতেন, খদ্দেরদের উৎসাহ জোগাতেন একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে, কথায় কথায় নতুন বইয়ের সন্ধান পেতে। আর কলকাতা থেকে আমরা যে বই-ই চাইতাম, ঠিক জোগাড় করে দেবার ব্যবস্থা করতেন। জীবনে যত শিক্ষক পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে অদৃশ্য ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের কথা যখন ভাবি, বাকিদের মধ্যে তপনদাকেও মনে পড়ে।
অর্ণব, যার নম্বরটা আমার ফোনে ‘অর্ণব বুকস’ বলে সেভ করা আছে, এই ব্যাপারটাকে আরও কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, ওর কীর্তি ছিল এই শহরটায় এমন একটা জিনিস শুরু করা যা প্রকৃত অর্থে কোনওদিনই ছিল না— একখানা লাইব্রেরি। ও নিজে এটাকে বইয়ের দোকান বলত, আদতে ব্যপারটা তা-ই ছিল বটে। তবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন নম্বর গেট থেকে যখন ছাত্ররা বেরিয়ে এসে এ.এন.ই. বুকস-এ ঢুকত, অর্ণব সবাইকে এগিয়ে দিত জলের বোতল। ছাত্রদের যে বই দরকার, বা যে বই পড়ার ইচ্ছে, তা কেনার টাকা সবার বেশির ভাগ সময় থাকে না। অর্ণব তাই ওদের বই পড়তে এবং আড্ডা মারতে বসিয়ে দিয়ে নিজে একটু দূরে সরে যেত। মাঝে মাঝে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য বইয়ের যে অংশটা দরকার, সেটা ওদের জেরক্স করার অনুমতি দিত, কিছুদিনের জন্য বইগুলো ধার নিতে দিত, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আবার কোনও বই পড়তে ফিরে এলে তাদের খাতির করত, ওদের আলোচনাগুলোও শুনত কান পেতে। ওর দোকানে বেশির ভাগ বই-ই ছিল পড়ার সিলেবাসের বাইরে— নতুন একখানা বই ছাত্রদের হাতে গুঁজে দিয়ে ওর বলার অভ্যেস ছিল ‘এটা দেখো।’ যে কোনও শিক্ষক বা সিলেবাসের চেয়ে অনেক বেশি বইয়ের সঙ্গে ছাত্রদের আলাপ করিয়েছে অর্ণব।
অর্ণব আজ আর নেই। ওর পুরো নামটা বললাম না, ওকে আমরা যারা ভালবাসতাম তারা অনেকেই ওর পদবি জানতাম না। মানুষ মারা গেলে তার কাছের লোকগুলোর অনাথ লাগে, ঘরছাড়া লাগে নিজেদের। এত মানুষের স্নেহের পাত্র অর্ণবের মৃত্যু এ শহর-মফস্সলকে বইহীন, বইয়ের অনাথ করে দিয়ে গিয়েছে।
ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook