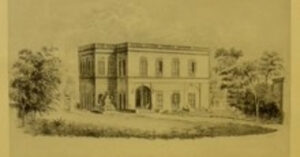ধূমকেতু-র নজরুল: পর্ব ২
নবযুগ পত্রিকা প্রকাশের জন্য মুজফ্ফর আহমেদ ও নজরুল ইসলামকে ফজলুল হকের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। কিন্তু ধূমকেতু প্রকাশনার সুযোগ, বলতে গেলে, পায়ে হেঁটে তাঁদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছিল। হাফিজ মাসউদ আহমেদ নামের ‘একজন লোক’ নিজে এসে প্রথমে মুজফ্ফর আহমেদকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনার প্রস্তাব দেন, যার খরচ-বাবদ মাসউদ আহমেদ আড়াইশো টাকা বিনিয়োগে প্রস্তুত। প্রখর বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মুজফ্ফর আহমেদ শোনার পরেই সে-প্রস্তাব নাকচ করে দেন। মাসউদ আহমেদ তখন নজরুল ইসলামের কাছে গিয়ে একই প্রস্তাব রাখেন। নজরুল সে-সময় সদ্য কুমিল্লা থেকে কলকাতা এসে সেবক দৈনিক পত্রিকায় যোগ দিয়েছেন (সময়টা ১৯২২-এর মে-জুন), কিন্তু কাজে খুব একটা তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। মাসউদ আহমেদের প্রস্তাব শোনামাত্র তিনি তা প্রায় লুফে নেন, বন্ধুবৃত্তে জানান না-দিয়েই। আসলে নজরুল তখন হাত খুলে এবং নিজের মতো করে প্রতিবাদী লেখালিখির একটা জায়গা খুঁজছিলেন। মনে রাখতে হবে, এর মাত্র কয়েকমাস আগেই তাঁর সাড়া-জাগানো রচনা ‘ভাঙার গান’ প্রকাশিত হয়ে গেছে বাঙলার কথা পত্রিকায়। সেই শান্তিপূর্ণ অসহযোগের সময়কালে নজরুল তাঁর প্রলয়বিষাণে কারার লৌহকপাট ভেঙে ধ্বংসনিশান ওড়ানোর সুর বাজিয়ে স্ব-চেতনার গতিমুখকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন পরাধীন মানুষজনের সামনে।
নতুন কাগজের নাম হল ধূমকেতু, এ-নাম নজরুলেরই দেওয়া। সম্পাদক হলেন তিনি, মুদ্রক ও প্রকাশক হিসাবে নাম থাকল আফজলুল হকের। ‘বাণী চেয়ে’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ অনেকের কাছেই চিঠি পাঠালেন নজরুল (নবযুগ পরবর্তী সময়ে নজরুল বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন, ধূমকেতু-র লেখালিখিতে তার স্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়)। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীর শেষ চার পঙ্ক্তি ছিল—
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।
এই বাণীকে শিরোধার্য করে নতুন কাগজ আত্মপ্রকাশ করল, প্রতিটি সংখ্যাতেই আট পঙ্ক্তির এই পদ্যটি ছাপা হয়েছিল।
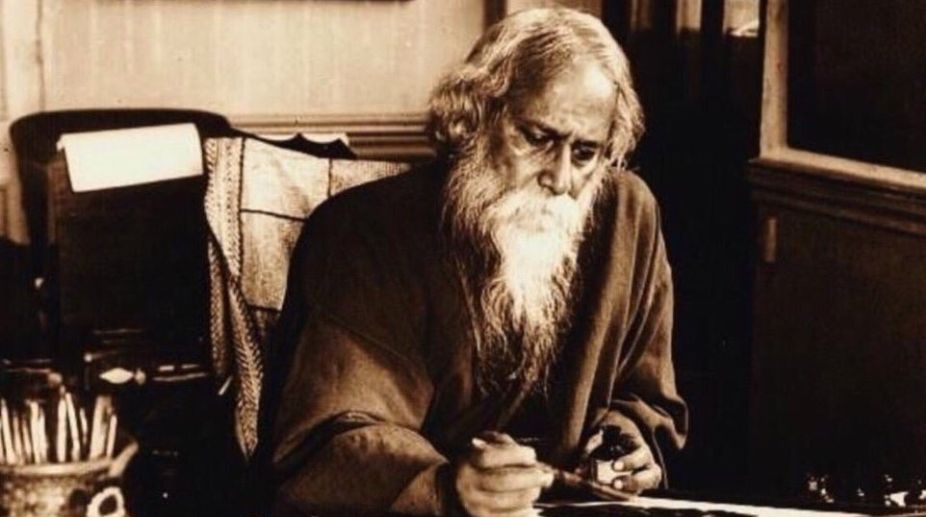
মুজফ্ফর আহমেদ যদিও ধূমকেতু-র প্রথম প্রকাশের তারিখ ১২ আগস্ট, ১৯২২ বলেছেন, ধূমকেতু-র প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১১ আগস্ট তারিখে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ সংরক্ষিত প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদপটে তা স্পষ্টভাবে মুদ্রিত রয়েছে। পত্রিকাটি— নজরুল-সুহৃদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—প্রথমে সাপ্তাহিক হিসেবে বের হলেও কখনও কখনও সেটি সপ্তাহে দু-বারও বের হয়েছে। এই তথ্যটিও সঠিক নয়। পত্রিকাটি হবে অর্ধসাপ্তাহিক, এটা ধূমকেতু সম্পাদকের প্রাক্-প্রকাশনা সিদ্ধান্ত, ওই প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদপটেই পত্রিকার নামলিপি ও ধূমকেতুর একটি ছবির নীচে ছাপা রয়েছে ‘সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইবে’। প্রকাশের অনতিবিলম্বে পত্রিকাটি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছিল। তা না হলে কিছুটা মুশকিলই হত, কারণ আর্থিক সংকট শুরুর দিন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল; মাসউদ আহমেদ দুশো টাকা দিয়েই হাত গুটিয়েছিলেন (মুজফ্ফর আহমেদ পরে একটা সাংঘাতিক তথ্য জানতে পেরেছিলেন— মাসউদ আহমেদ আসলে পুলিশের নিয়োজিত, পুলিশই তার মারফত ওই দুশো টাকা পাঠিয়েছিল)। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি কপি বিক্রি হয়ে যেত বলে কিছুটা টাকা উঠে আসত। ক্রেতা-পাঠকদের সিংহভাগ ছিল শিক্ষিত তরুণের দল।
এই জনপ্রিয়তার বিষয়টিকে মুজফ্ফর আহমেদ সমালোচকের চোখে দেখেছেন। “‘ধূমকেতু’ জনগণের নিকটে পৌঁছাতে পারেনি। শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর ভিতরে তার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেই ‘ধূমকেতু’ খুব বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও এই শ্রেণীর লোক। কাজেই, নজরুলের আবেদনে তাঁরাই নতুন ক’রে চেতনা লাভ করেছিলেন। এটা আমার অনুমানের কথা নয়। শুধু যে তরুণেরা নজরুলের নিকটে আসছিলেন তা নয়, সন্ত্রাসবাদী ‘দাদা’রা (নেতার) এসে তাকে আলিঙ্গন ক’রে যাচ্ছিলেন। ১৯২৩-’২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার যে মাথা তুলল, তাতে নজরুলের অবদান ছিল, একথা বললে বোধ হয় অন্যায় করা হবে না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দু’টি বড় বিভাগের মধ্যে ‘যুগান্তর’ বিভাগের সভ্যরা তো বলছিলেন, ‘ধূমকেতু’ তাঁদেরই কাগজ।”
নতুন সাহচর্যে নজরুলের উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা নিয়ে তাঁর দু-বছর আগের সতীর্থ বোধ করি কিঞ্চিৎ বিরক্তই ছিলেন (যদিও ছদ্মনামে ধূমকেতু-র একাধিক সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন বলে জানা যায়)। সম্ভবত, নজরুলকে একবার তিনি বলেওছিলেন (বা লিখেছিলেন) যে, এইসব শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে মেতে থাকলে শ্রমিক-কৃষকের কথা সে ভাববে কখন! এতদসত্ত্বেও, দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে নজরুল যে নির্দ্বিধ ও নিঃসংশয় ছিলেন— সে-কথা অকুণ্ঠ স্বরে বারবার বলেছেন মুজফ্ফর আহমেদ। এমনকী, নলিনীকান্ত সরকার যখন বলতে চেয়েছেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি নজরুল নন, অরবিন্দ ঘোষ প্রথম তুলেছিলেন—মুজফ্ফর আহমেদ তখন তথ্য দিয়ে সে-যুক্তি খণ্ডন করে দেখিয়েছেন, এ-প্রসঙ্গে অরবিন্দর ব্যবহৃত শব্দগুলি হচ্ছে ‘অটোনমি’ বা ‘সেলফ গভর্নমেন্ট’ (গভর্নেন্স?); ‘ইন্ডিপেন্ডেন্স’ বলে যে ছোট্ট শব্দটি, তা অরবিন্দ কখনওই ব্যবহার করতে চাননি। নজরুল-ই প্রথম বাংলায় ‘পূর্ণ স্বাধীনতা’ কথাটা ব্যবহার করে প্রকাশ্য বার্তা দিলেন ধূমকেতু-র পাতায় (১৩ অক্টোবর, ১৯২২)।
“সর্বপ্রথম ‘ধূমকেতু’ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।
“স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেন না, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।”
মনে রাখতে হবে, এটা ১৯২২-এর কথা, যখন করমচাঁদ গান্ধী বলছেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস পেলে তিনি ইউনিয়ন জ্যাক ওড়াতে প্রস্তুত! ধূমকেতু-র নজরুল প্রমাণ করেছিলেন, বামপন্থার কক্ষপথ থেকে যদি তিনি সরেও থাকেন, তবে তা নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য কদাচ নয়।
নতুন সাহচর্যে নজরুলের উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা নিয়ে তাঁর দু-বছর আগের সতীর্থ বোধ করি কিঞ্চিৎ বিরক্তই ছিলেন (যদিও ছদ্মনামে ধূমকেতু-র একাধিক সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন বলে জানা যায়)। সম্ভবত, নজরুলকে একবার তিনি বলেওছিলেন (বা লিখেছিলেন) যে, এইসব শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে মেতে থাকলে শ্রমিক-কৃষকের কথা সে ভাববে কখন! এতদসত্ত্বেও, দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে নজরুল যে নির্দ্বিধ ও নিঃসংশয় ছিলেন— সে-কথা অকুণ্ঠ স্বরে বারবার বলেছেন মুজফ্ফর আহমেদ।
ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত একাধিক খরশান নিবন্ধ লেখার জন্য নজরুলের বিরুদ্ধে সিডিশনের মামলা দায়ের হতে পারত। হল কিন্তু ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতাটি লেখার অপরাধে।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,– আসবি কখন সর্বনাশী?
দেব-সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে
রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে?
—এইরকম প্রবল দ্রোহী উনসত্তরটি পঙ্ক্তি আছড়ে পড়েছিল ২৬ সেপ্টেম্বরের ধূমকেতু-র পৃষ্ঠায় এবং অচিরেই ইংরিজিতে অনূদিত হয়ে পৌঁছে গেল কসাইখানার কর্তাব্যক্তিদের টেবিলে। ৮ নভেম্বর পুলিশ এল পত্রিকারএবং একই সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি-র দফতরে, গ্রেফতার হলেন মুদ্রক ও প্রকাশক আফজলুল হক। নজরুল ইসলাম তখন কলকাতার বাইরে ছিলেন, যদিও এর পনেরো দিনের মধ্যেই কুমিল্লা থেকে তিনিও গ্রেফতার হয়ে যান। ১৯২৩-এর ১৬ জানুয়ারি চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শোনালেন। নজরুল ইসলাম জেলে গেলেন, তাঁর নিজের ভাষায় ‘কারাশুদ্ধির জন্য’। ধূমকেতু চিরতরে নিভে গেল।
যে-বছরে নজরুল ইসলাম ধূমকেতু পত্রিকাটির সূচনা করছেন, ঠিক সেই বছরেই (১৯২২) মুজফ্ফর আহমেদ কলকাতায় গড়ে তুলছেন ভারত সাম্যতন্ত্র সমিতি। সাম্যতন্ত্রের কক্ষপথ থেকে এইসময়েই নজরুলের দূরত্ব তৈরি হল কেন, তা অভিনিবেশের সঙ্গে পৃথক আলোচনা দাবি করে। মতান্তর কিন্তু মৈত্রীর অবসান ঘটাতে পারেনি এবং অভিযাত্রাও এখানেই শেষ হয়নি। নজরুল পুরনো কক্ষপথে ফিরেছিলেন আরও একবার। সে হল সাপ্তাহিক লাঙল পত্রিকার পর্ব।
কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা বলছে—
“ধূমকেতু’র নজরুল ইসলাম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের নিকট হতে বীরের কবি মর্যাদা পেয়েছিল। ‘ধূমকেতু’তেও জনগণের স্বার্থের কথা যে একেবারেই থাকত না তা নয়, তবুও কৃষকের স্বার্থের কাগজ ছিল না ‘ধূমকেতু’। কিন্তু নজরল ইসলাম যে সাপ্তাহিক ‘লাঙ্গল’-এর প্রধান পরিচালক হলো এটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের ভালো লাগল না। ‘লাঙ্গল’ নামটিই এমন যে ‘ভূমির’ ছোট-বড় মালিকেরা তা পছন্দ করতে পারলেন না। দেশের মধ্যবিত্ত যুবকেরা ভূমির সঙ্গে সংসৃষ্ট ছিলেন। ভূমি হতে-পাওয়া আয় তাঁরা ভোগ করতেন, কিন্তু ভূমি হতে কোনো উৎপাদন তাঁরা করতেন না, সেই কাজটি করতেন কৃষকেরা। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে মধ্যবিত্ত যুবকেরা অকাতরে জেল খাটতে পারতেন, প্রাণ বিসর্জনও দিতে পারতেন, কিন্তু ভূমিতে ছিল তাঁদের স্বার্থ। আজকের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে এই জিনিসটা বুঝতে চাইলে চলবে না। এটা বুঝতে হবে উনিশশ’ বিশের দশকের অবস্থাকে সামনে রেখে। …এই অবস্থায় বের হয়েছিল সাপ্তাহিক লাঙল। তাতে ছাপা হয়েছিল নজরুল ইসলামের বিরাট কবিতা ‘সাম্যবাদী’ ও ‘কৃষকের গান’, ইত্যাদি।”
সে-পর্বের কথা বারান্তরে।