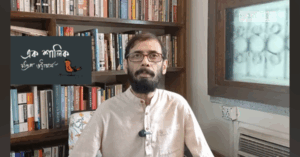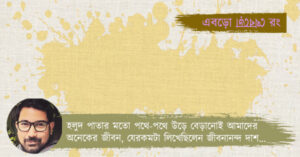“…মানুষের মৃত্যু হ’লে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো— আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতো দূর অগ্রসর হ’য়ে গেল জেনে নিতে আসে।”
— জীবনানন্দ দাশ
ডিপসিক এবং আগামীর কৃত্রিম-বুদ্ধি-সিঞ্চিত আরও বুদ্ধিমান যন্ত্রগুলি যদি অনায়াসে তলস্তয়, বেঠোফেন, ভ্যান গঘ, জীবনানন্দর মতো শিল্প সৃষ্টি করতে পারে, স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, সৃষ্টিশীল আমরা, মানুষ, আসলে কে এবং কী। অনন্য এক প্রজাতি হিসেবে মানুষের সৃষ্টিশীলতার একচেটিয়া আধিপত্য তাই আজ চ্যালেঞ্জের মুখে।
পশ্চিমের দুনিয়া কতকাল ধরে ‘মানুষের প্রতিভা’ নামের একটা আখ্যান শুনিয়ে এসেছে— যেন কোনও এক মহামানব সূর্য থেকে আলোর মতো নেমে এসে কবিতা লিখে যায়! ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলতেন, কবিতা আসে ‘প্রবল আবেগের উছলে পড়া’ থেকে, নিৎশের কথায়, ‘সৃষ্টি করাই মানুষের আসল শক্তি’। সত্য হলেও এইসব আখ্যানে মানুষকে এক অতিলৌকিক আসনে বসানো হয়েছে, যেন সে এক অতিমানব, প্রায়-ঈশ্বর, শূন্য থেকে সে জিনিস বানায়।
আরও পড়ুন : এআই কি গোপনীয়তার মালিকানা দখল করছে ক্রমে?
লিখছেন সৈকত ভট্টাচার্য…
চ্যাটজিপিটি এবং হালের ডিপসিকের মতো যন্ত্রেরা কবিতা-গল্প-ভাষণ লিখছে বসন্তে পাতা ঝড়ার মতো নিঃশব্দ সরল, সহজে। প্রকাশ্যে এনে ফেলছে অস্বস্তিকর এক আখ্যান, সৃজনশীলতা না কি মানুষের মগজের হিসেব-নিকেশ ছাড়া আর কিছুই নয়, আসলে সবই তো প্যাটার্নের খেলা! ঠিক যেমন মস্তিষ্কের যে রহস্যে ঘেরা যুক্তিতে বিরক্ত, বিষাদগ্রস্ত মুখের অভিব্যক্তির প্যাটার্ন বুঝে নিয়ে মানুষ অপর মানুষকে এড়িয়ে যায় অথবা বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি আমাদের মুখোশ খুলে দিচ্ছে— যে মুখোশে লেখা ছিল, ‘আমরাই একমাত্র স্রষ্টা।’
অল্প দিনেই বহুচর্চিত এই ডিপসিকের অ্যালগরিদমের আড়ালে কে বা কারা থাকে? উত্তর, আসলে আমরা সবাই। বুঝে নিতে হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেভাবে লেখে, আঁকে সেটা মানুষের মতো ‘সৃষ্টি’ না। ডিপসিক ‘শবদে শবদে বিয়া’ দেয় বটে, তবে তা মধুসূদন বা বুদ্ধদেব বসুর মতো নয়, ইন্টারনেটের কোটি কোটি লেখা থেকে নকল করে, কোটি কোটি প্যাটার্ন সংশ্লেষ করে তৈরি নতুন এক প্যাটার্ন। সেই প্যাটার্নের মৌলিক এবং গভীর উৎকর্ষে চমকে ওঠেন পদার্থবিজ্ঞানী থেকে মনস্তত্ত্ববিদ, সংগীতজ্ঞ থেকে কথাসাহিত্যিক। ডিপসিক যখন শেক্সপিয়রের মতো সনেট লেখে, সংগত কারণেই আরও প্রশ্ন ওঠে, ‘সৃষ্টি’ জিনিসটা আসলে কী? না কি সবই নকল আর জোড়াতালি?
নিৎশে বলতেন, ‘দুনিয়ার শুরুতেই ছিল অর্থহীনতা, আর সেই অর্থহীনতাই ঈশ্বর।’ মানে, আমরা নিজেরাই জিনিসে অর্থ দিই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঠিক সেই কাজটাই করে— অর্থ দেয় না, কিন্তু শব্দের জোড়া দেয়। তাই ডিপসিকের লেখায় কোনও লেখক নেই, নেই কোনও আবেগ, উৎকণ্ঠা, সংবেদনশীলতা, গভীর জীবনবোধ।
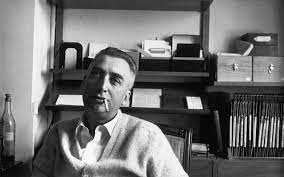
১৯৬৭ সালে ফরাসি দার্শনিক রোঁলা বার্থ চিৎকার করে বলেছিলেন, ‘লেখক মরেছেন!’ তার মানে, লেখক নামের যে অহংকার— সে মরেছে। লেখার মানে পাঠক ঠিক করে, লেখক নয়। ডিপসিকের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এসে বার্থের কথাকেই যেন সত্যি করে দিয়েছে। ডিপসিক যখন লেখে, তখন কোনও লেখক থাকে না, থাকে শুধু শব্দের পুতুলনাচ। ডিপসিকের লেখা কবিতা, Rorschach টেস্টের মতো, ওর মধ্যে আমরা যে অর্থ খুঁজে পাই, সেটা আমাদেরই মনের খেয়াল। অ্যানথ্রপোসেন্ট্রিক এই পৃথিবীর মানুষ ডিপসিককে অ্যানথ্রপোমরফাইজ করতে বাধ্য হয়। কারণ ডিপসিকের লেখায় তো আর কোনও একজন বিশেষ রক্তমাংসের লেখক নেই, আছে আমাদেরই মুখের কথা। সম্মিলিত সামাজিক জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু একথা জেনে ফেলার সন্তুষ্টিতে সমস্যা শেষ হয় না। লেখক যদি লেখক নন, তবে লেখক হিসেবে মানুষ আসলে কী? বহুকাল আগেই শুরু হওয়া চিন-আমেরিকার প্রযুক্তিযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসেবে সিলিকন ভ্যালির আধিপত্যর দিকে ছুড়ে দেওয়া চিনের চ্যালেঞ্জে পুঁজিবাদের সংকট এখন আরও বেশি গভীর। মার্কিন টেক স্টক আর এনভিডিয়ার বাজার দর রাতারাতি বিপর্যয়ের মুখে। এটা সংকট। পুঁজিবাদের সংকট। মার্কিন প্রযুক্তি-সাম্রাজ্যবাদের সংকট কিন্তু এতদিনের প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিশীল প্রজাতি সত্তার প্রতিনিধি হিসেবে, ব্রাত্য হয়ে ওঠার হীনম্মন্যতাকে দূরে সরিয়ে, সৃষ্টিশীলতার বিনির্মাণ ঘটিয়ে ডিপসিকের অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের সৃজননির্ভর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা মানুষের কাছে মোটেই কম সংকটের নয়।
১৯৫০ সালে অ্যালান টুরিং বলেছিলেন, যন্ত্র যদি মানুষের মতো কথা বলে, তবে তাকে বুদ্ধিমান মানতে হবে। এখন সময় এসেছে ‘শিল্পের টুরিং টেস্ট’-এর। ডিপসিকের লেখা কবিতা যদি মানুষকে কাঁদায়, গল্প যদি মুগ্ধ করে, প্রবন্ধ চমকে দেয়— তাহলে লেখক যন্ত্র হলেই বা ক্ষতি কী? এক্ষেত্রে ‘মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ’, এই কথাটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া মানবতাবাদীরা হয়তো বলবেন, ‘যন্ত্রের তো জীবন, আত্মা নেই! ভয়, ভালবাসা নেই। ও তো শব্দের প্যাঁচাল মাত্র!’ প্রযুক্তিপন্থীরা বলবেন, ‘কবিতায় যদি মন ভেজে, তবে লেখক মানুষ নাকি অ্যালগরিদমিক রোবট—তা কী আসে যায়?’

দ্বিতীয় শিবিরের কথা কিন্তু ভয়ের। কারণ, এতে লেখকের অহং-আধিপত্য ধসে পড়ে। ডিপসিক যদি শেক্সপিয়র সাজতে পারে, তবে মানুষ শেক্সপিয়রের মূল্য কী? ডিপসিক বা চ্যাটজিপিটি কি তাহলে শেক্সপিয়র-রবীন্দ্রনাথের ক্লোন? না, একেবারেই তা নয়। এরা বস্তুত ইন্টারনেটের চোরাবাজার থেকে চুরি করা মগজের সুস্বাদু বৌদ্ধিক খাবার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খালি হাতে কিছু বানায় না। ডিপসিক শেখে শেক্সপিয়র, টুইটার, ফেসবুক, ইন্সটা, ব্লগ—সব জায়গার লেখা থেকে। তাই ডিপসিকের লেখা প্রকৃত অর্থে মানুষেরই সমষ্টিগত স্বর। অতএব বলা যায়, আজকের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে লেখক সত্তারও রকমফের ঘটে গিয়েছে।
চ্যাটজিপিটি এখনও পর্যন্ত যা লিখছে, তা আসলে মানবিক বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ প্রোগ্রামারদের লেখা অ্যালগরিদমের মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কেরই প্রতিফলন, চ্যাটজিপিটি যদি পিতৃতান্ত্রিক কবিতা লেখে, দোষ প্রযুক্তির নয়—দোষ বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় আটকে থাকা সংস্কৃতির। এখন আগামীই বলবে, চ্যাটজিপিটিকে চ্যালেঞ্জ করা ডিপসিক কোনও নতুন সামাজিক সম্পর্কের, নতুন সংস্কৃতির ইঙ্গিত কি না!
মার্ক্সের কথা ধরে বলা যায়, পুঁজিবাদের যুগে মানুষের মগজ জমা হয় যন্ত্রে। এটাই ‘সাধারণ বুদ্ধিমত্তা’ (general intellect), সমাজের সমষ্টিগত জ্ঞান, যা পুঁজিপতিরা শুষে নেয়। এখনও পর্যন্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই শোষণেরই নতুন মেশিন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কবিতা-গল্প সবই আমাদেরই লেখা— ফেসবুক স্ট্যাটাস, টুইটার ট্রোল, উইকিপিডিয়ার আর্টিকল, অনলাইন গবেষণাপত্র, ট্র্যাভেল ব্লগ— সব মিশিয়ে বানানো। মার্ক্সের ভাষায়, যন্ত্রের পেটে ঢুকেছে সমাজের মগজ! আর এই ‘সাধারণ বুদ্ধিমত্তা’ যেহেতু সামাজিক জ্ঞান তাই এর মালিকানা সমাজের সবার হওয়া উচিত। কিন্তু পুঁজিপতিরা এটাকে কর্পোরেট ককটেলে পরিণত করেছে!
আমি যদি ডিপসিককে জিগ্যেস করি, ‘প্রেম কী?’— সেটি যদি চমৎকার এক কবিতায় উত্তর দিয়ে আমাকে চমকে দেয়, সেই কবিতা আসলে হাজারও মানুষের আহত হৃদয়ের গল্প, সিনেমার ডায়লগ, ব্যর্থ বা উল্লাস-উন্মাদ প্রেমিকের চিঠি— ইত্যাদি সবকিছুকেই ব্লেন্ড করে বানানো।
মজার ব্যাপার হল, ডিপসিক চর্চার কেন্দ্রে আসার আগে পর্যন্ত চ্যাটজিপিটির ‘বুদ্ধিমত্তা’ দেখে আমরা হতভম্ব হয়েছি! অথচ এই ডিপসিক বা চ্যাটজিপিটি, এগুলি তো আমাদের নিজেদের জ্ঞানেরই রেসিপি, যা পেটেন্ট করা সফটওয়্যারে বন্দি। ওপেনএআই-গুগল-মাইক্রোসফটের সার্ভারে আটকে রয়েছে মানবসভ্যতার মগজ। মার্ক্সের ভাষায়, ‘পুঁজির লোভে সাধারণ বুদ্ধিমত্তার অপহরণ!’ যেমন ‘মিডজার্নি’ নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যদি পিকাসোর স্টাইলে ছবি আঁকে, তাহলে পিকাসো মোটা টাকার অঙ্ক অর্জন করলেন না— কামিয়ে নিলেন কিন্তু মিডজার্নির মালিক। অতএব শুধুমাত্র শিল্পীর শ্রম নয়, শিল্পীর স্টাইলও এখন পুঁজির মালিকানায়! যেন জনি ওয়াকার হুইস্কি চুপিসারে কিনে নিচ্ছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দেশি মদ্যপানের স্টাইল!
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্রমশ হয়ে উঠছে মানুষেরই আয়না, যা মানুষের প্রতিটি প্রযুক্তি-আবিষ্কারের সঙ্গে দিন-দিন আরও বেশি স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। এর মধ্যেই আমরা দেখছি, সমাজের সমষ্টিগত মগজ, যা পুঁজিপতিরা প্রত্যেক মুহূর্তে চুরি করে বিক্রি করছে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নয়, আজকের সামাজিক ব্যবস্থাই লেখক, শিল্পীর প্রকৃত ঘাতক!
কিন্তু সমাধানটা কোথায়? মার্ক্স বলেছেন, সাধারণ বুদ্ধিমত্তা ‘সামাজিক সম্পত্তি’ হওয়া উচিত। মানে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোড-ডেটা সবার জন্য উন্মুক্ত হোক! ঠিক যেমন ওপেন সোর্স ডিপসিক। বহুজাতিক সংস্থাগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা লুকিয়ে রাখে, কিন্তু ডিপসিকের কোড সবাই দেখতে পায়। হাই-ফ্লায়ার হেজ ফান্ডের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক থাকলেও ডিপসিক অনেকটা হানা আরেন্ডটের সেই স্বপ্নের মতো, যেখানে প্রযুক্তি সবার হাতের মুঠোয়। ডিপসিকের এই অ্যালগরিদমিক উদারতার মানে হল, আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা চিন্তা, একের সঙ্গে অপরের মেলবন্ধন। এই আকালের দিনে তীব্র আশাবাদী হয়ে ভাবলে এটা এমন এক নতুন সমাজের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে প্রযুক্তি ক্ষমতা কুক্ষিগত না করে সবার মেধাকে জাগিয়ে তোলে সকলের পূর্ণাঙ্গ বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য। কেনিয়ার কৃষক ডিপসিক দিয়ে ফসলের পরামর্শ পায়, বলিভিয়ার কবির লেখায় আদিবাসী ইতিহাস জুড়ে যায়।
অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্রমশ হয়ে উঠছে মানুষেরই আয়না, যা মানুষের প্রতিটি প্রযুক্তি-আবিষ্কারের সঙ্গে দিন-দিন আরও বেশি স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। এর মধ্যেই আমরা দেখছি, সমাজের সমষ্টিগত মগজ, যা পুঁজিপতিরা প্রত্যেক মুহূর্তে চুরি করে বিক্রি করছে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নয়, আজকের সামাজিক ব্যবস্থাই লেখক, শিল্পীর প্রকৃত ঘাতক!
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সৃষ্টিশীলতার নিখুঁত ব্যাপ্তি বুঝে ভয় পাওয়ার কারণ থাকলেও এটাই কিন্তু অভূতপূর্ব সুযোগ মানুষের উত্তরণের। অনেকে ভাবতেই পারেন, লেখা তো এখন সবার খেলা, কারণ আগে যেটা শেক্সপিয়র, দস্তয়েভস্কি, মার্কেজের সৃজন-ক্ষেত্র ছিল, এখন তা সবার। যেমন ফুটবল খেলায় জিতলাম কি হারলাম, তার চেয়ে খেলার মজাটাই হয়ে উঠবে লক্ষ্য। এমন ধরনের সাংস্কৃতিক যাপনে ডিপসিক লিখবে অসীম গল্প-কবিতা।
তবুও মানব থেকে যায়। তখন মানুষ-লেখকের কাজ সেখান থেকে সেরাগুলো বাছাই করা। তাই আগামীতে হয়তো মানুষের ভূমিকা হবে যন্ত্রের সৃষ্টিকে বাছাই করা, তাতে নিজের বোধ, দর্শন এবং কল্পনার রং মেশানো।
শেষে বলা যায়, লেখকের মৃত্যু কোনও সর্বনাশ নয়, এটা আসলে মুক্তির গল্প। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, সৃষ্টি করার কারিগর হিসেবে মানুষ প্রজাতির কোনও মোনোপলি থাকতে পারে না। এটা স্রেফ প্যাটার্ন বুঝে নেওয়ার হিসেব-নিকেশ। আর আমরা যদি এই রূঢ় বাস্তব মেনে নেই, তাহলেই নতুন দুনিয়া সম্ভব। যেখানে লেখা সবার জন্য, সবার দ্বারা। যেখানে যন্ত্র আমাদের সহযোগী, প্রতিযোগী নয়। যেন আর্থার কেস্টলারের ‘বাইসোসিয়েশন’ তত্ত্ব— দুটো আলাদা জগতের মিলনে নতুনত্ব। যন্ত্র এখানে সংখ্যায় মানুষকে ছাড়িয়ে গেলেও অভাব থাকে ‘telos’ বা জীবনের লক্ষ্য। ডিপসিকের কবিতা সুন্দর, কিন্তু তা জীবনের মর্মন্তুদ বেদনা থেকে জন্মায় না। এখানেই মানুষের জয়, আমাদের সৃষ্টিতে জড়িয়ে থাকে বাঁচার গল্প, হাসি-কান্নার স্মৃতি।
যন্ত্র যদি শিল্প সৃষ্টি করে, তবে মানুষের কাজ কী? উত্তরটা লুকিয়ে আছে সৃজনশীলতাকে নতুনভাবে বোঝায়। মানুষের সৃষ্টিশীলতা তো শুধু জিনিস বানানো নয়, আমাদের অস্তিত্বের গাঢ় নিবিড়ের সঙ্গে তা হাড়ে-মজ্জায় জড়িয়ে। আমরা মরণশীল, ভয়-আনন্দ-প্রেমে জড়িত, এই সসীমতাই আমাদের শিল্পকে অর্থ দেয়। যেমন দস্তয়েভস্কির ‘ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট’ বা ‘ব্রাদারস কারামাজভ’ নিছক অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নয়, এটা অন্যদিকে তাঁর জীবনের অতুলনীয় বিষাদ, উল্লাস এবং মুক্তির জার্নাল। মার্টিন হাইডেগারের কথার মতো, ‘মৃত্যুর দিকে এগনো’ থেকেই সত্যিকারের সৃষ্টি জন্ম নেয়। ডিপসিকের কিন্তু এই ক্ষমতা নেই।
আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কের মধ্যে বাঁধা। মানুষ শিল্প সৃষ্টি করে অপরের সঙ্গে আইডিয়া আদানপ্রদান করে, কথা বলে, পুরনো ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করে। ডিপসিকের গান শুনে কারও চোখ ভিজে উঠলেও, তা মানুষের মতো আমি-তুমি-সে জাতীয় সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না।
এইসব ভাবনা আত্মস্থ করে মানুষকে অহং ভুলে জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তাকে সমষ্টিগত করতে হবে। কারণ ডিপসিকে অঙ্গীভূত জ্ঞান যেন নদীর জল, অরণ্যের সবুজ, বিশুদ্ধ বাতাস, যা সবাই ভাগ করে নেয়। এমন আগামী মোটেও ইউটোপিয়া নয়, স্বপ্ন নয়, বাস্তবায়িত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনায় পোয়াতি।
যন্ত্র যখন রুটিন কাজ করবে, জলবায়ু বিপর্যয়ে ওলট-পালট হয়ে যাওয়া এই পৃথিবীকে মেরামত করবে, এমনকী, সৃষ্টিশীল কাজেও ব্যবহার করা হবে, মানুষ তখন আবেগ, নৈতিকতা, দর্শন, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের গভীর প্রশ্ন নিয়ে ভাববে। তখন সেই পৃথিবী তেলহার্দ দ্য শার্দেনের ‘নূস্ফেয়ার’— মানুষ-যন্ত্রের মিলিত বুদ্ধিমত্তার স্তর।
বন্ধনের এই নতুন সংজ্ঞায়, উত্তর হয়তো পাব আমরা নিজেরাই একদিন, মানুষ হিসেবে আমাদের সীমা আর অসীমতার ঠিক মাঝখানে। মানুষ ও প্রযুক্তির দর্শনকে সার্বিক (as a whole) অর্থে বুঝে একই সঙ্গে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মানুষের বিরোধ সম্পর্কে গতানুগতিক অগভীর আলোচনা থেকে।
রোঁলা বার্থের কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শেষে বলা যায়, ‘আমরা এই সমস্ত গোল পাকানো কথাবার্তার থেকে মুক্ত হতে শুরু করেছি, যার প্রশ্রয়ে সমাজ বুক ফুলিয়ে এমন জিনিসের ঢাক পেটায় যাকে সে নিজেই অস্বীকার করে, অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে অবহেলা করে, দমন করে, বিনাশ করে। আমরা জানি লেখাকে তার ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে দিতে, লেখা সম্পর্কিত এই মিথকে উলটে দিতে হবে।’ ‘রচয়িতা’-র মৃত্যুর মূল্যেই জন্ম নেবে ‘পাঠক’। নতুন মানুষ। নতুন সৃষ্টি।
সূত্র : রোঁলা বার্থ, রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধ্যানবিন্দু, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৫৫