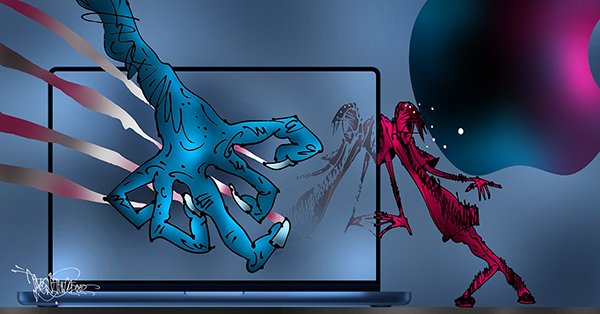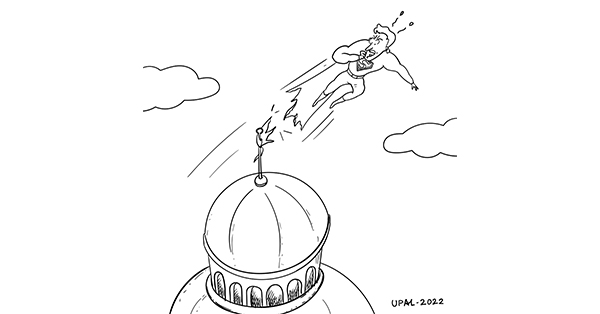কথা-বার্তা
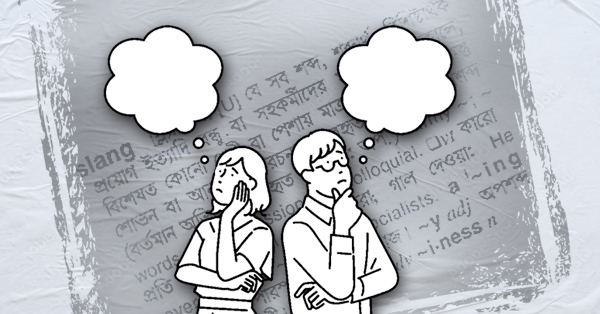
 ঋতু সেন চৌধুরী (May 14, 2025)
ঋতু সেন চৌধুরী (May 14, 2025)চিত্তে সুখ নেই ভায়া, ঝি-বেটি পালিয়েছে’… বাঙালির এমন অমোঘ উক্তির ভিতর গৃহ-পরিচারিকা বা গৃহ-কর্মী ঢুকে পড়লে রসবোধে কিঞ্চিৎ টান পড়বে না? অনেকেই বলবেন, ভাষার তো একটা স্বাভাবিক চলন আছে। বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতাকে সীমিত করে— খর্ব হয় ভাষার মাত্রা, গতি, ছন্দ, তার মজা। তাছাড়া মুখের কথা, কথার কথা, কথায়-কথায় বাড়তে থাকা কথার মধ্যে ঠিক-ভুলের চুলচেরা বিচার করে কী লাভ? ছোটখাট মানুষ বলে ডাকলে বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো যাবে তো? কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখলে কি সে দেখতে পাবে? বেশ্যা বা প্রস্টিটিউট না বলে যৌনকর্মী বললে, হোমো না বলে গে বা লেসবিয়ান বললে, গৃহবধূ না বলে হোম মেকার বললে, স্বামীকে জীবনসঙ্গী, গরিবকে নিম্নবিত্ত বললে কি বদলে যাবে সব? না, সব তো বদলাবে না! তবে, এই ‘সব’ বদলে যাওয়ার দাবিটাই কি অমূলক নয়? মুখের কথায় বদলে যাবে সব, এও কি সম্ভব? মনোভাব না বদলালে তো সবই নামকাওয়াস্তে!
আরও পড়ুন: একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে নিজেকে নারীবাদী ভেবে শ্লাঘা বোধ করা আমি টের পাই, কাউকে ‘মিনসে’ বললে আখেরে তেমন কিছুই মিন করা হচ্ছে না! লিখছেন হিয়া মুখোপাধ্যায়…
অনেক সময়ে মনে হয় যেন কথাবার্তায় রাজনৈতিক শুদ্ধতার উপর অতিরিক্ত মনোযোগ বৈষম্য এবং বৈষম্যের মূল কারণগুলোকে ধামা চাপা দিতে সাহায্য করে। বৈষম্যকে দরদি পরিভাষার মোড়কে ঢেকে রেখে শুদ্ধভাষীরা এক ধরনের ‘হোলিয়ার দ্যান দাও’ গোছের মনোভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ান। নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের এই দাবি তো আসলে দ্বিচারিতা! তাহলে কি সংবেদনশীল ভাষাকে সমাজ বদলের ছোট একটা পদক্ষেপও বলা যাবে না? যাঁরা তথাকথিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন, এলিট নন, ভাষার কচকচানিতে পড়ার মতো সময় যাঁদের নেই— শহর-গ্রামে ছড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ তাঁরা— পারেন কি পরিশীলিত ভাষায় কথা বলতে? উচ্চবর্গের সুচারু ভাষা কি বৈষম্যের আরও একটা স্তর তৈরি করে না? ঠিকই, কিন্তু সংবেদনশীল ভাষার প্রসঙ্গ ছাড়াও শ্রেণি, বর্গ, জাত, লিঙ্গ, ধর্মভেদে ভাষা তো সবসময়েই অনুক্রমিক। চাষাভুসো আর বাবুদের মুখের কথার দাম তো এক নয়!
মানুষ অত ভেবেচিন্তে কথা বলে না সবসময়ে। বার বার অন্যের বোনের শয্যাসঙ্গ লাভের আশায় তো আর কথায়-কথায় ‘শালা’ বলা হয় না! এমন কষ্ট-কল্পনা বাঙালির ফ্যান্টাসিকে অহেতুক চাপে ফেলে দিতে পারে! চুরি-চামারি বলার সময়ে কি কোনও বিশেষ জাতের কথা মনে রাখি? আমরা জানি প্রেমই আসল; যার যেখানে মজে মন কী-বা মুচি কী-বা ডোম— জাতফাত কোনও ব্যাপারই না! বার বার জাতপাতের প্রসঙ্গ উঠে আসলেও আমরা বলি— ও কিছু না, কথার কথা। সমাজ যেমন বদলায় শব্দের মানে, তার অভিঘাতও বদলে যেতে থাকে। একদিন যা ছিল বৈষম্যচিহ্নিত, আজ তার ব্যবহার প্রায় আপামর। আবার, কাল যে ‘মাগী’ স্বছন্দে ঘুরে বেড়াত, আজ সে পরিণত হয়েছে খিস্তিতে! চারদিকে যা কিছু ঘটছে, যেভাবে ঘটে আসছে, তারই প্রেক্ষিতে তৈরি হয় আর বারংবার বদলে যায় ভাষা। কিন্তু চুনকামের পরেও পুরনো দেওয়ালে যেমন একটু-একটু করে ফুটে ওঠে কবেকার নোনাধরা, শ্যাওলার সবুজ আভা, ঠিক তেমন শব্দের ইতিহাসও সহজে মুছে ফেলা যায় না। শব্দের গায়ে-গায়ে প্রাচীন শৈবাল— সময়ের প্রলেপের তলায় লেগে থাকে নানান অনুষঙ্গ, সামাজিক ব্যবহারের ছাপ। আমাদের কথা, ভাবনা, স্বপ্ন, কবিতা, গানে সেই ছাপ কখনও আবছা-কখনও প্রকট হয়ে ওঠে।
ভেবে দেখি না, ভাষার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে কীভাবে কাজ করে জাত্যাভিমান, ধর্মান্ধতা, বর্ণবিদ্বেষ, বিত্তমনস্কতা, সমকামভীতি, যৌন হিংসা, নারীবিদ্বেষ। হাসি-তামাশা, গালি-গালাজ, প্রবাদ-প্রবচন, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও ঘুরেফিরে সেই সব অপমানকর, আক্রমণাত্মক নির্দেশ। চলতি ভাষার টানে আহ্লাদে-আনন্দে, রাগে-দুঃখে বলে ফেলি এমন সব কথা, আর তা উচ্চারণ করতে গিয়ে পুনঃস্থাপন করি তার ভিতরকার না-বলা ইঙ্গিত, যা হয়তো অনেক সময়ে আমরা করতে চাই না। ছোটলোক-ইতর, কুত্তা-জানোয়ার, মা-মাসি, মেয়েলি-শরীরী, ডাইনি-লক্ষ্মী, শাড়ি-চুড়ি, তালি-খিস্তি, খোট্টা-মেরো, মোল্লা-উজবুক, কাফের-বজ্জাত, কাটা-গোটা, খোজা-বাঁজা, নাচ-মুজরা ছাড়াও কত আপাতশান্ত, শাশ্বত নদ-নদী, লতা-মহীরুহ, ঐক্য-একতা, সূচক-ব্যঞ্জক, ঋণ-ভর্তুকি, রাষ্ট্র-সন্ত্রাস, প্রথম বিশ্ব-তৃতীয় বিশ্ব, দুনিয়াদারির শব্দে-শব্দে গ্লানি-অপমান। ভাষার মধ্যেকার অবমাননা, অসাম্য কি তবে অবরুদ্ধ করে মুক্তির পথ? মুক্তিকামী মানুষ তাহলে কোন ভাষা ব্যবহার করবেন? সমস্যাটি গভীর, তাই চটজলদি কোনও উত্তর নেই। এক্ষেত্রে চটজলদি সমাধানের প্রয়োজনও নেই যে! তার চেয়ে একটু ভেবে দেখার বা ভেবে বলার সময় নিই।
ভাষা নিয়ে আমরা ভাবি না— স্বাভাবিক বা নিশ্চিত বলে ধরে নিই, গুরুত্ব দিই না তার নির্মাণ-প্রক্রিয়ায়, প্রশ্ন করি না— জানতে চাই না বৈষম্যের আকরগুলি মুখে-মুখে বয়ে বেড়াব আর কতদিন! সংবেদনশীল ভাষার কিছু সমস্যা আছে বলে কি তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করব? সে-কথায় যাওয়ার আগে কয়েকটা আপত্তিকর শব্দ নিয়ে একটু ভাবা যাক। বেশ্যা বা প্রস্টিটিউট শব্দটি পতিতাবৃত্তির ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, যেখানে নারীদের কেনা-বেচার পণ্য হিসেবে দেখা হয় তার সাথে জড়িয়ে আছে। তবে বেশ্যা বলতে আমরা শুধু দেহোপজীবিনীকে বুঝি না। যে-মানুষ ব্যক্তিগত লাভের জন্য তার নীতি বা মূল্যবোধ বিক্রি করে আমরা তার কাজকেও বেশ্যাতি বলি। যে-মানুষকে কেনা যায় সে যে পতিতারও অধম! বেশ্যার সব প্রতিশব্দই এই বিদ্বেষ বহন করে। অথচ যৌনকর্মী শব্দটিতে যৌন বিনিময়কে একটি কাজ হিসেবে ধরা হচ্ছে যার কোন নির্দিষ্ট লিঙ্গ পরিচয় নেই। যৌন বিনিময়কে অপরাধ, অপকর্ম বা পাপ না ভেবে পেশা ভাবলে এর সঙ্গে নিযুক্তরা হয়ত তাদের কাজের অবস্থা, পারিশ্রমিক ও সুরক্ষার অধিকারের দাবিগুলি করতেও সক্ষম হবেন।
যদি আপনি দারিদ্র্য নিয়েই খুশি থাকেন, তাহলে মনে রাখবেন শয়তান হল আপনার বন্ধু। অন্যদিকে, যে দরিদ্রের প্রতি দানশীল, যে দরিদ্র-নারায়ণকে চিনতে পারে, সেই বড়লোক কিন্তু মহান। অর্থাৎ এটা ধরে নেওয়া থাকে যে, সমাজে কিছু মানুষ নিজেদের অকর্মণ্যতায় গরিব হয়ে থাকবে। দরিদ্রের কাছে তার দারিদ্র্য লজ্জার, গ্লানির। আর মহানুভবের দাতব্যই দারিদ্র্য দূরীকরণের একটা বেশ পাকাপাকি উপায়।
সমকামী বা হোমোসেক্সুয়াল শব্দগুলি শুধুমাত্র যৌন আচরণের ওপর ভিত্তি করে একজন মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করে। এসব শব্দের মূলে রয়ে গেছে (প্রজননভিত্তিক বিসমকামিতাকে আদর্শ মেনে) সমকামীর মানসিক বা শারীরিক বিকারের ক্লিনিকাল, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আখ্যান। এই আখ্যান আমাদের মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত। খুব সহজে তা ঝেড়ে ফেলা সম্ভব না। সাধারণ সমাজে সমকামী ব্যক্তিদের প্রতি যে তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, আক্রোশ, অস্বস্তি, অবিশ্বাস আর ভয় কাজ করে, তার কোনও সীমা নেই। বেশ্যার মতো ‘হোমো’ শব্দটিও গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই হোমোসেক্সুয়ালের বদলে গে বা লেসবিয়ান শব্দগুলি হয়তো একই লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিদের বর্ণনা করার জন্য কিছুটা সম্মানজনক।
গৃহবধূ হিসেবে কাউকে পরিচয় করাতে গেলে অবধারিতভাবে বলা হয়, ‘উনি কিছু করেন না, উনি একজন গৃহবধূ।’ এখন গৃহবধূরা কিছু না করলে, সকাল-সকাল পেট ভরে খেয়ে, পাটভাঙা শার্ট-প্যান্টুল পরে আপিসবাবুরা কীভাবে কাজে বেরোতেন আর ফিরে এসে কীভাবেই বা ‘আন্ডা বাচ্চা লইয়া গুষ্টিসুখ’ অনুভব করতেন তা বলা মুশকিল। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বাড়ির কাজকে মোট-জাতীয় পণ্য থেকে বাদ দেওয়ার একটা বৃহৎ-কাঠামগত দিক থাকলেও দৈনন্দিন কথোপকথনে এই বহিষ্করণের সংকেত পেতে অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে ‘গৃহিণী’ শব্দটিও লিঙ্গগতভাবে সীমাবদ্ধ; এই ভূমিকাটি যেন মহিলাদের জন্যই নির্ধারিত। অথচ সংসার সামলানো যে একটা কাজ আর লিঙ্গ-নির্বিশেষে যে তা করা যায়, ‘হোম মেকার’ শব্দটিতে তার আভাস আছে।
স্বামীকে নিয়ে বিশেষ কিছু বলার থাকে না। যার উৎপত্তিতে মালিক বা প্রভুর অবস্থান, সে তো তার আইনত বিবাহিত স্ত্রীরও মালিক। পুরুষের আধিপত্যের ইঙ্গিতবাহী ‘স্বামী’ শব্দটি নারীর স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রকে সীমিত করে। অন্যদিকে জীবনসঙ্গী বা সঙ্গী লিঙ্গ, যৌন অভিমুখ ও বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে প্রেমের সম্পর্কে থাকা যে-কাউকে বর্ণনা করতে পারে।
‘দারিদ্র্য’ শব্দটি অনেক সময়ে একটু ব্যাপক অর্থে একটা সাধারণ ঘাটতি বা অভাব রূপে ব্যবহার করা হয়; যেমন চিন্তার দারিদ্র্য, মানসিকতার দারিদ্র্য। এই ঘাটতির দায় অনেকটাই বর্তায় ব্যক্তির ওপর। খেয়াল করব গরিব শ্রেণির প্রতিও অনেক সময়ে এমন ধারণাই পোষণ করা হয়। ‘গরিব’ বা ‘দরিদ্র’ শব্দগুলির মধ্যে একটা নেতিবাচক দিক থাকে, যা কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-সম্পর্কিত স্টিরিওটাইপগুলিকে আরও বদ্ধমূল করে তোলে। অভাব যখন দরজায় এসে দাঁড়ায়, ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে পালায়। অভাবে যে স্বভাব নষ্ট হয়, এ তো সবার জানা! যদি আপনি দারিদ্র্য নিয়েই খুশি থাকেন, তাহলে মনে রাখবেন শয়তান হল আপনার বন্ধু। অন্যদিকে, যে দরিদ্রের প্রতি দানশীল, যে দরিদ্র-নারায়ণকে চিনতে পারে, সেই বড়লোক কিন্তু মহান। অর্থাৎ এটা ধরে নেওয়া থাকে যে, সমাজে কিছু মানুষ নিজেদের অকর্মণ্যতায় গরিব হয়ে থাকবে। দরিদ্রের কাছে তার দারিদ্র্য লজ্জার, গ্লানির। আর মহানুভবের দাতব্যই দারিদ্র্য দূরীকরণের একটা বেশ পাকাপাকি উপায়। নিম্নবিত্ত বা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ শব্দগুলি অপেক্ষায় নিরপেক্ষ, কারণ এগুলির মধ্যে একটা ইঙ্গিত থাকে যে, অর্থাভাব ব্যক্তিগত ত্রুটির চেয়ে বরং একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোগত সমস্যা।
আরও অনেক শব্দ নিয়ে বলা যেতে পারে আরও অনেক কথা— বাছতে-বাছতে হয়তো ভাষা উজাড় হবে তবু শেষ হবে না। সমাজে বিদ্বেষ-বৈষম্যরও যে শেষ নেই! প্রত্যেকটা শব্দ বদলে ফেলার অবাস্তব কর্মসূচি নয়, প্রয়োজন ভাষাকে অধরা না রেখে সামাজিক বৈষম্য প্রকাশের মাধ্যমরূপে চিহ্নিত করা। ওপর-ওপর শব্দ বদল নয়, সচেতনভাবে আপত্তিজনক শব্দগুলোকে ধীরে-ধীরে বর্জন করে বিকল্প শব্দের ব্যবহার হয়তো বৈরিতা কিছুটা হ্রাস করতে পারে। কথায়-কথায় জাত, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ, শ্রেণি, শিক্ষা, যৌন অভিমুখ, শারীরিক-মানসিক অ/ক্ষমতা বা আকৃতির ভিত্তিতে যে অপরকে বাদ দিচ্ছি আমরা, অনুভূতিশীল ভাষার প্রয়োগে তাদের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সম্মানসূচক সম্বোধন পাওয়ার অধিকার আমাদের সবার। তুই-তামারির দিন শেষ। পাঠক বুঝবেন, মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে আপাতদৃষ্টিতে যতটা লিবারাল দেখায়, আদপে তা নাও হতে পারে। ভেবে দেখুন, দু-কূল বাঁচিয়ে যে-মূলস্রোত বয়ে চলেছিল ধীরে-ধীরে, অন্য অনেক চোরা, ভাঙাচোরা স্রোত যদি তার সাথে মিলে যায় কী হবে? পাড় ভেঙে, কূল ভেসে যাবে না? লিবারাল দাবির মধ্যেও কি এক ধরনের র্যাডিকাল সম্ভাবনা নিহিত থাকে না? যে-মানুষ নিজেকে মানুষ বলেই চিনতে শেখেনি চেয়ারে না বসে, মেঝেতে বসতে গেছে বার বার, সেই মানুষটির অস্তিত্ব আর তার কাজের প্রতি ন্যায্য মর্যাদা কি বৈষম্য কাঠামোতে কোনও পরিবর্তন আনবে না? মুখের কথা কি মর্যাদা প্রকাশের অন্যতম উপায় নয়? ভাষার সচেতন প্রয়োগ সমাজ বদলের জরুরি পদক্ষেপ তো বটেই! আর সর্বশিক্ষার মধ্যে দিয়ে সর্বস্তরে সঞ্চারিত হতে পারে বিদ্বেষ-বিরুদ্ধ ভাষার ধারণা।
পূর্ববর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook