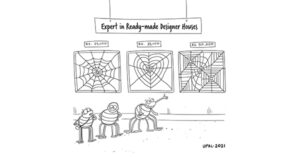দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাসে হ্যারড-ডমার গ্রোথ মডেলের সূক্ষ্ম সালোকসংশ্লেষ আর মিহির রক্ষিত মহাশয়ের ডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়ামের উন্মাদনার বিভাজনরেখা বরাবর, হঠাৎ, বর্শার মতো এসে গেঁথে গিয়েছিল একটি বই। তখনও প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের রিডিং রুমে হাতে হাতে ঘোরে— ‘সাতটি তারার তিমির’, ‘বিপন্ন বিস্ময়’ আর ‘কোয়েলের কাছে’; পাশাপাশি। কেবল কবিতাই লিখি তখন, এবং অবসরে মুক্ত গদ্য, নিয়মিত গল্প লেখার আরও কয়েক বছর বাকি।
মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’ এসেছিল ঝড়ের প্রবল কড়া-নাড়া হয়ে। ব্রতীর মায়ের চিহ্নবিহীন শোক ছিঁড়ে-উপড়ে দিয়েছিল সমঝোতাপরায়ণ এক উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবারের চরম স্বার্থপরতা আর ভণ্ডামি, আর ব্রতীর হত্যার মধ্য দিয়ে এক নষ্ট সমাজের সুবিধাবাদী স্তব্ধতাকে।
“কোথায় পালাবে, আবার পালাবে ব্রতী? ব্রতী কোথায় পালাবে? কোথায় ঘাতক নেই, গুলি নেই, ভ্যান নেই, জেল নেই?
আরও পড়ুন : দুর্গম তাওয়াং-এও পৌঁছে গিয়েছিলেন নবনীতা দেবসেন…
…এই মহানগর— গাঙ্গেয় বঙ্গে— উত্তরবঙ্গের জঙ্গল ও পাহাড়— বরফ ঢাকা অঞ্চল—রাঢ়ের কাঁকর-খোয়াই-বাঁধ— সুন্দর বনের নোনাগাং— বন— শস্যক্ষেত্র— কলকারখানা— কয়লাখনি— চা-বাগান কোথায় পালাবে ব্রতী? কোথায় হারিয়ে যাবে আবার? পালাস না ব্রতী। আমার বুকে আয়, ফিরে আয় ব্রতী, আর পালাস না।”

ছবি সৌজন্য: পিটিআই
নিভে গেছে দেওয়াল-লিখন, অজস্র মৃত্যু, কাস্টডিয়াল টর্চার, বিনা আইনে জেলের ভেতর অবরুদ্ধ তরুণ তরুণীদের দুর্মর স্বপ্ন— কেউ কোনও কথা বলে না কেন, কেউ লেখে না কেন এই সময়ের কথা? মহাশ্বেতার কণ্ঠ ব্রতীর মায়ের স্বর হয়ে আমাদের নির্বিকার শান্তির স্থিতাবস্থা-কে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মহাশ্বেতা, যিনি অজস্র মায়ের আবেগ, শোকের আগুনে দগ্ধ হতে হতে, সমাজ ও পরিবারের অসহনীয় নিস্পৃহতার মধ্যে ব্রতীর মৃত্যুর বিনির্মাণে নিমজ্জিত হলেন, তিনিই আবার অননুমেয় পদসঞ্চারে ‘হাজার চুরাশির মা’ প্রকাশের তিন বছরের মধ্যে চলে গেলেন আদিবাসী বিদ্রোহের পুনর্নিমাণে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক থেকে দেশ ও ইতিহাসে।
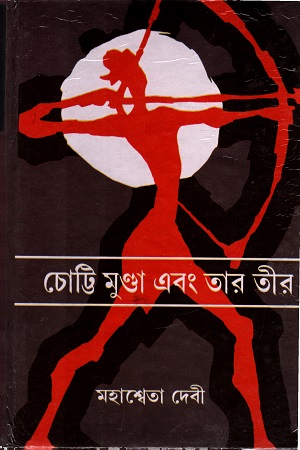
১৯৭৭-এ এল ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘বেতার জগৎ’-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর বই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি-তে অনুবাদ করলেন প্রবীণ অনুবাদক জগৎ শঙ্খধর, ‘জঙ্গল কে দাবেদার’। তারপর অন্য সব ভারতীয় ভাষায়, ‘অরণ্যের অধিকার’-এর সেই পরাক্রম আজও অব্যাহত। ‘অরণ্যের অধিকার’ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের লেখকদের লেখকের আসনটি দীর্ঘ সময়ের জন্য মহাশ্বেতার হয়ে গেল। ‘অরণ্যের অধিকার’-এর মধ্য দিয়ে কাছে-পিঠে থাকা, অথচ অচেনা এক দেশ টান দিয়েছিল আমাদের চেতনাকে, যেন কোন নৃত্যপর ওঁরাও যুবকের পাঞ্জা! বদলে গিয়েছিল সাহিত্য নিয়ে ভাবনার প্রকার। ‘অরণ্যের অধিকার’-এর ত্রিশতম সংস্করণের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ২০০৬ সালে মহাশ্বেতা লিখছেন, উপন্যাসটি লেখার সময় আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার লুণ্ঠিত হওয়ার কালানুক্রমিক নিরবচ্ছিন্নতা তাঁর চিন্তাকে অধিকার করেছিল। ব্রিটিশ শাসকের হাতে যার সূচনা, স্বাধীনতার পর ভারত সরকার ও নানা রাজ্য সরকারও সে পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি। জনজাতিদের গোষ্ঠীবদ্ধ অস্তিত্বে অরণ্য একটি প্রধান স্বর। কিন্তু পরবর্তীকালে আদিবাসীদের নিজস্ব জমি ও ভূমি থেকে উচ্ছেদের বিষয়টি নিয়েও মহাশ্বেতার কাজ চলেছে। কুমার সুরেশ সিং-এর ‘ডাস্ট স্টর্ম অ্যান্ড হ্যাংগিং মিস্ট’ বইটি ‘অরণ্যের অধিকার’-এর রচনাকে প্রাণিত করেছিল, মহাশ্বেতা নিজেই লিখেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছিল তাঁর আদিবাসী জীবন ইতিহাসের সন্ধান। ভ্রমণ, আর গেজেটিয়ারে লিপিবদ্ধ গবেষণা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল এক দূরবর্তী পথে।

১৯৭০-এর সেই আগুনঝরা বেলায় নকশাল আন্দোলনের বিস্তার বাংলায় এক দশক পুরনো। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ছোটানাগপুরের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস জানে না। বরং বাবু সাহিত্যিকদের ‘সুলভা’ আদিবাসী রমণীর সন্ধানে রোমান্টিক অভিযানের কাহিনি তাদের কাছে বেশি চেনা। অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যদি বলি, ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ বেরিয়েছে ১৯৬৭-তে। সেই উপন্যাসের ভিত্তিতে সত্যজিৎ রায়ের ছবি ১৯৭০-এ। মধ্যবিত্তের দৃষ্টিকোণ যখন সাহিত্যের কপালে ত্রিনয়ন এঁকে দিচ্ছে, আর বাণিজ্যিক সংবাদপত্র হয়ে উঠছে তার অভিভাবক, সেই সময় মহাশ্বেতা আমাদের চেনাচ্ছেন ভারতবর্ষকে, মেলে ধরছেন অরণ্যনির্ভর জনগোষ্ঠীর বিপুল শোষণ ও প্রতিরোধের ইতিহাস, বিরসা-কে তুলে আনছেন লোক-ইতিহাসের পাতা থেকে, স্মৃতি, ইতিহাস বাস্তবের মন্থনে নির্মাণ করছেন এক নতুন সাহিত্যরূপ।
গত শতকের ছয়ের দশকে মহাশ্বেতার বারবার পালামৌ-এ যাওয়া। অরণ্য, অরণ্যজীবী মানুষদের কাছে। সেখানে দারিদ্র ও বঞ্চনা তখন ভয়াবহ। পরে, গত শতকের আটের দশকে বন্ধুয়া মজদুর মুক্তি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন মহাশ্বেতা। প্রান্তিক মানুষের প্রতি তাঁর অভিনিবেশ ক্ষণজীবী ছিল না।
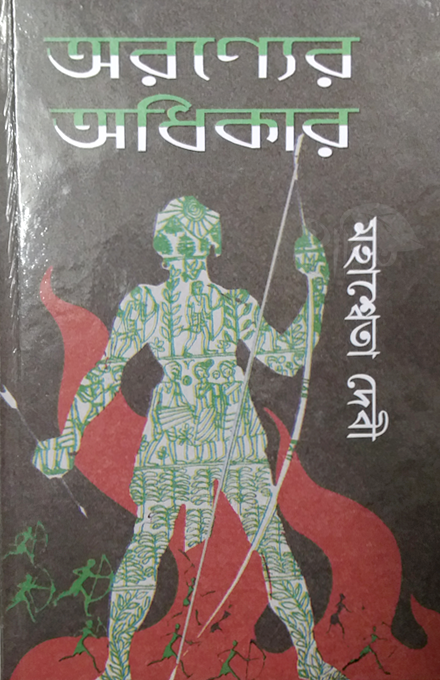
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যর ইতিহাসের সন্ধানে যাত্রা আরম্ভ হয়েছে অবশ্য অনেক আগে। নিজের দেশটিকে যেন হাতের তালুতে রেখে উল্টেপাল্টে দেখতে ভালবাসেন তিনি। মহাশ্বেতা দেবী নিজেও বলেছেন, তাঁর লেখা ভাল করে জানতে হলে সাতের দশকের আগে লেখা আখ্যানগুলিও পড়তে হবে। ‘লায়লী আসমানের আয়না’, ‘তিমির লগন’, ‘অমৃত সঞ্চয়’ ইত্যাদি আপাত-সাধারণ নাটকীয়তা-রঞ্জিত উপন্যাসের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে পরবর্তীকালের মহাশ্বেতা দেবীর প্রবহমানতা । ১৯৬৭-এ প্রকাশিত ঝাঁসির রানি অবশ্য সর্বকালের মানদণ্ডেই এক ব্যতিক্রমী উপন্যাস, অলিখিত ইতিহাসকে ইতিহাসে বুনে দেওয়ার মৌলিকতায়। আমরা যাঁরা তাঁকে পরবর্তী সময়ে ‘হাজার চুরাশির মা’, ‘চোট্টি মুণ্ডার তীর’ ও ‘গল্প সংগ্রহ’ থেকে চিনেছি— অনেক আগেই অন্তরে শুনেছি, এক ভারতবর্ষের কণ্ঠস্বর, যা কলকাতাকেন্দ্রিক নাগরিক রোমান্স থেকে আমাদের মন উঠিয়ে দিয়েছিল লেখালিখির আদিকালেই।
তরুণ বয়সেই তাঁর বাংলার মধ্যযুগের লোক-ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ ছিল, পরে তিনি বাহির হয়েছেন আদিবাসী বিদ্রোহের শিকড়ের সন্ধানে। আরম্ভ হয়েছে ভ্রমণ, লোক-ইতিবৃত্ত সঞ্চয় করে এনে লেখা। একে একে এসেছে ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘চোট্ট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর’, ‘বসাই টুডুর উপাখ্যান’, এবং একই মাত্রার পদসঞ্চারে বহু গল্প— যেগুলি আজ সাহিত্যের ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে শাশ্বত হয়ে গেছে। ‘শিকার’, ‘বেহুলা’, ‘বান’, ‘বিছন’, ‘নুন’, ‘বায়েন’, ‘দ্রৌপদী’-র মতো গল্প পরবর্তীকালে অনূদিত হয়ে মহাশ্বেতা দেবী-কে বিশ্বের পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এই গল্পগুলিতে মহাশ্বেতা অন্ত্যেবাসী সমাজকেই কেবল নিবিড় সহমর্মিতায় দেখেছেন, তা নয়, লোকবিশ্বাসের সঙ্গে জড়ানো তাদের দৈনন্দিনতাকে বুঝতে চেয়েছেন। ওঁরাও, সাঁওতাল, মাল, পাখমারা, বাগদি, ডোম— এদের সামাজিক অস্তিত্ব ও প্রতিরোধের কথা আগে এই তীব্রতায় বাংলা গল্পের সীমিত পরিসরে আসেনি। তাঁর কাছে বাস্তব কোনও দ্বিমাত্রিক ছবি নয়, ইতিহাসের ক্রিয়ান্বয়তা তাদের করেছে চলমান। তাঁর গল্প সংগ্রহের ভূমিকায় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, ‘ইতিহাস মানে এখানে কেবল অতীতের উৎস বা উত্তরাধিকারের উদ্ঘাটন নয়, বরং অতীত থেকে ভবিষ্যতের যাত্রাপথের ইংগিতও বটে। তাতেও অবশ্য আশাবাদী ভবিষ্যৎ দর্শনের সহজ উত্তরণ নেই। বরং বর্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যতের বীজের উদ্গমের পুরাকথাসম উদ্ভাস আছে।’
তিনি জানতেন, উপাদান হিসেবে বাস্তব জরুরি। কিন্তু কেবল বাস্তব দিয়ে মহৎ সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়। বাস্তবের সঙ্গে মিশবে সৃজনশীল কল্পনা, লোক-ইতিহাস, স্মৃতি, মিথ, দেশের অলিখিত ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে যেসব উপাদান, তার মিশেল না হলে সাহিত্যের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না।
মহাশ্বেতার আগেও বৃহৎ পরিসরে বাস্তবকে কথাসাহিত্যে ধারণের এক প্রবহমানতা ছিল। সতীনাথ ভাদুড়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দেশের সন্ধানে গিয়েও মহাশ্বেতা তাঁদের চেয়ে স্বতন্ত্র। ‘অরণ্যের অধিকার’-এর ৩০ বছর পর একটি সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা বলছেন, সেই ‘literature is not enough’, যে ‘literature’ বাস্তবতার সঙ্গে কোনও পরিচয় করায় না। বলছেন, জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকার শিক্ষা তিনি পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন থেকে—
‘আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নামজাদা লোকেদের এমনকি পরিবর্তনকামীদেরও, তোমরা কি কখনো সেখানে গেছ, যেখানে মানুষ বছরে একদিন ভাত খায়? সেখানে কি গেছ যেখানে রোদে জল শুকিয়ে যায় বলে মেয়েরা সন্ধের সময় কুয়ো কেটে রেখে আসে? সমস্ত রাত্তির ধরে বিন্দু বিন্দু জল জমে আর মেয়েরা সূর্য ওঠার আগে জল নিয়ে আসে? কখনও কি সেসব জিনিস দেখেছ? Share করেছ?’
তিনি জানতেন, উপাদান হিসেবে বাস্তব জরুরি। কিন্তু কেবল বাস্তব দিয়ে মহৎ সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়। বাস্তবের সঙ্গে মিশবে সৃজনশীল কল্পনা, লোক-ইতিহাস, স্মৃতি, মিথ, দেশের অলিখিত ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে যেসব উপাদান, তার মিশেল না হলে সাহিত্যের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অথচ, নিজের ঘরে নিজের টেবিল-চেয়ারে বসে লেখা হয় না। তাই মহাশ্বেতাকে বারবার চলে যেতে হয়েছে মানবজীবনের অন্তহীন রহস্যের কাছে, এবং চোখের দেখাকে কল্পনা ও ইতিহাসের মিশ্রণে ভেঙে-গড়ে নিয়েছেন তিনি। এইভাবেই তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে নতুন বাংলা কথ্যভাষা। বিরসার ভাষা থেকে ‘বান’ গল্পে ষোড়শ শতকের নদিয়ার বাগদি সমাজের ভাষা। নিহত সন্তানের দেহখণ্ডকে বিছন বানানোর ভয়াল চেষ্টায় নিযুক্ত ভূমিহীন মজদুরের মুখের ভাষা। এর যাথার্থ, এর গঠন-তত্ত্ব নিয়ে ভাষাবিদরা আলোচনা করতে থাকুন, মহাশ্বেতা পৌঁছে গেছেন মানবজীবন কথকের অনন্ত যাত্রায়।
‘অরণ্যের অধিকার’-এর নতুন সংস্করণের ভূমিকায় মহাশ্বেতা লিখছেন, অরণ্যের লুন্ঠন, পরিবেশের ওপর উন্নয়নের আঘাত, অরণ্যের রক্ষাকারী আদিবাসীদের উচ্ছেদ দেখে দেখে তিনি হতাশ, ক্লান্ত। ওই সময়ে, ২০০৬ সালেই, এসেছিল অরণ্য অধিকার আইন, তা সম্পূর্ণ রূপায়িত না হলেও দেশের বহু অঞ্চলে আদিবাসী ও বনবাসীদের দিয়েছিল অরণ্যভূমির ব্যক্তি-মালিকানা। গড়চিরোলিতে গোণ্ডরা পেয়েছিল অরণ্য পরিচালনার সামূহিক অধিকার। মহাশ্বেতার স্বপ্ন সাকার হতে চলেছিল। এখন আবার পরিকাঠামো-মুগ্ধ উন্নয়নের জোয়ারে আইনটিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। রথের চাকার দু-পাশে পড়ে আছে তারা, এই মৃত্তিকার আদি সন্তান ও অরণ্যের রক্ষক আদিবাসীরা।
মানুষ আর লেখক হিসেবে সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। একেবারে শুরু থেকেই। পাঠক কী ভাববে, পছন্দ করবে কী করবে না, তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কোন লেখা কীভাবে লিখলে অমরত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে, তা নিয়ে ভাবতেন না। কোথায় লেখা ছাপা হচ্ছে— তাই নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। ‘বেতার জগৎ’, ‘প্রসাদ’, ‘নবকল্লোল’-এর মতো জনপ্রিয় পত্রিকায় ছাপা হত তাঁর অসাধারণ সব লেখা। টাকার জন্য অল্প বয়সে লিখতে হয়েছে, একথা নিজেই স্বীকার করেছেন। প্রথম দিকের সেসব লেখার মধ্যে কোনও অনন্যতা খুঁজে পাননি আলোচকরা। কিন্তু লেখার মধ্যে যে জোর লুকিয়ে থাকত, তা তাঁর একেবারে নিজস্ব। বড় বাণিজ্যিক পত্রিকায় নভেলা লেখার ডাক পাওয়ার আশায় যেসব তরুণ লেখক হাপিত্যেশ করে যৌবন কাটিয়ে দেন, তেজস্বিনী মহাশ্বেতা তাঁদের আদর্শ হতে পারেন। পাঠক সর্বত্র অনুসরণ করেছে মহাশ্বেতা দেবীকে। যে পত্রিকাতেই তাঁর লেখা বেরক না কেন, সেই পত্রিকা খুঁজে বের করে তাঁর লেখা পড়েছে। আসলে মহাশ্বেতা দেবী আমাদের শিখিয়েছিলেন, লেখকের স্বাধীনতা একেবারেই তার নিজের অর্জন। এই স্বাধীনতা তাকে কেউ উপহার দিতে পারে না।
এই স্বাধীনচিত্ততা তাঁর অন্য কাজেও দেখেছি। গুজরাতে গোধরার নৃশংস ঘটনার পর যখন আহমেদাবাদে রায়ট আরম্ভ হল, সরকারি নিস্পৃহতায় জীবন ও সম্পত্তি হারালেন হাজার হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, কোনও দিক থেকে কোনও সরকারি সহায়তার ঘোষণা হওয়ার আগেই শুনলাম, মহাশ্বেতা দেবী ট্রেনে চলেছেন, সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার ও সংগ্রহ করা পাঁচ হাজার টাকা। শুনে মনে হয়েছিল, এ তো সমুদ্রে শিশির বিন্দু। মহাশ্বেতা দেবী আরও টাকা সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর কাছে মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছনো জরুরি ছিল। পরে শুনেছিলাম, ওই টাকা ও খাবারই ছিল বিপন্ন শহরে বাইরে থেকে এসে পড়া প্রথম সাহায্য।
নিজের শর্তে বাঁচা এবং লেখা। মহাশ্বেতা নিজের জীবন দিয়ে এই দুই পন্থা অনুসরণ করেছেন। সামাজিক চণ্ডীমণ্ডপ তাঁকে যে সর্বদা মার্জনা করেছে, এমন নয়। বিশ্ববিখ্যাত হলেও যে লেখক বা শিল্পী জন্মসূত্রে মহিলা— তাঁকে বাধ্য স্ত্রী আর ‘ভাল’ মা হওয়ার সামাজিক পরীক্ষায় পাশ করতে হয়।

গত শতকের নয়ের দশকের গোড়ায় বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে বাড়ির প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে প্রথম তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, একটি অনুবাদ গল্পের জন্য অনুমতির তদ্বিরে। মহাশ্বেতা তখনই কিংবদন্তি। ঈষৎ তিরস্কার-সহ তিনি আমাকে দিতে বলেছিলেন ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ওপর একটি নোট। কার কাছে কী কাজ পাওয়া যায়, খুব ভাল জানতেন। টেবিলে বসে বিডিও, থানা, অফিসার, হাসপাতালে ফোন ঘোরাচ্ছেন— আমার মতো অনেকেই দেখেছেন। বিপ্লবের ব্যাখ্যাতা মহাশ্বেতা মনে করতেন, সরকারের কাছে কাজ দাবি করা যে কোনও নাগরিকের কর্তব্য। তিনি সেটাই করতেন। বিক্রির নামে বান্ডিল করা বর্তিকা নিয়ে গিয়ে উপহার দিয়েছি আর টাকা ফিরিয়েছি মহাশ্বেতাদির সমিতিকে। স্নিগ্ধ, মধুর বন্ধুত্বে তিনি লালন করেছেন আমাদের প্রজন্মের বেশ কয়েকজন তরুণতর লেখককে। কিন্তু যখন অনুবাদের মাধ্যমে তিনি বিশ্ববিখ্যাত, পেয়েছেন ম্যাগসাইসাই, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার— তখনও নিজের লেখা নিয়ে, সমাজের ওপর তাঁর লেখার বিষয়ে কোনও উপদেশ বা জ্ঞানের কথা তাঁর মুখে শুনিনি। লেখাকে জীবনের থেকে আলাদা করে কখনও দেখেননি, তাই এই নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনও বিশেষ সচেতনতা ছিল না। আমার অনুরোধে ‘রূপকলা কেন্দ্র’-তে এসেছেন, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে। তাঁতশিল্পীদের আবদারে একবার কলকাতায় কাপড়ের প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে এলেন। প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে যে রেশম শাড়ি উদ্বোধককে দেওয়া হত, মহাশ্বেতাকে তা দেওয়া যায় না। ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত জগৎসিংহ পুরের হাতে বোনা মোটা তাঁতের শাড়ি কয়েকটি দেওয়া হল তাঁকে। অনুমেয়, সে শাড়ি কোথায় গিয়েছিল। কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার পর গল্ফগ্রিনের বাড়িতে গেলে প্রণাম করে ওঠার সময় বলেছিলেন, তোমার মাথায় খুব ধুলোর গন্ধ। সপ্তাহে দু-দিন চুল ধুয়ে নিলে ওটা চলে যাবে। মুখে মৃদু হাসি দেখেছিলাম। ধুলে যে ওই গন্ধ যায় না, তাঁর চেয়ে ভাল আর কে জানত।
জীবনের শেষ পর্বে হয়তো অনেকটা আবেগ ও দ্রোহের বশেই বামপন্থা থেকে সরে এসে অন্যরকম রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে দিয়েছিলেন তাঁর নাম। নন্দীগ্রাম পর্বের পর থেকেই এর সূচনা। এই সিদ্ধান্তে তাঁর পুরনো বন্ধু ও পাঠকরা দূরে চলে গিয়েছিলেন, নতুন বন্ধু-সংসর্গ সে-দূরত্ব পূর্ণ করতে পারেনি। ২০১৪-তে আমার প্রবন্ধের বই ‘দেশের ভিতর দেশ’ মহাশ্বেতা দেবীকে উৎসর্গ করার পর যে বন্ধুদের মুখে ঈষৎ হাসি দেখেছিলাম, তাঁরা কি জানতেন, লেখকের লেখক মহাশ্বেতা দেবীর শিকড় আমাদের মন থেকে তুলে দিতে পারেনি কোনও ঘটনাক্রম। তিনি একটি বজ্রবাণ, যা বুকের ভেতর গেঁথে গেছে চিরতরে।
যে ভারতবর্ষ চেনার মন্ত্র তাঁর কাছে পেয়েছিলাম, তাই আজও আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন মালকানগিরির উদ্বাস্তু বসতে, নিয়মগিরি পাহাড়ের নিচে ঘন অরণ্যের মধ্যে বক্সাইট খনির কনভেয়ার বেল্টের কাছে, খরাক্লিষ্ট মারাঠওয়ারার আখ-শ্রমিক মেয়েদের ছাউনিতে, ছত্তিশগড়ের বস্তারের গোণ্ড গীতকুড়িয়ার ঘরে, গড়চিরোলির নদী-কল্লোলিত গ্রামে দেবাজী তোফার কাছে ‘অরণ্যের অধিকার’ হস্তান্তরের কাহিনি শুনতে শুনতে অনুভব করি, মহাশ্বেতা দেবী একটি বড় শিরীষ গাছের মতো আমার ধুলোর গন্ধমাখা মাথায় ছায়া ফেলে জেগে আছেন।