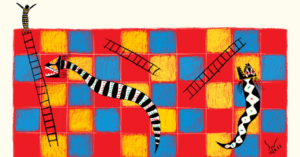দাদু ছাড়া দুনিয়া অন্ধকার
একটা নীল কেটলি! আমার শুধু এটাই মনে আছে। আমার জীবনের প্রথমতম স্মৃতি হচ্ছে ওটাই, একটা গোলগাল, বেঁটে, ভালমানুষের মতো দেখতে নীল রঙের কেটলি। আজ আর বলা যাবে না সেটা পোর্সিলিনের, না কলাই করা জিনিস। কলাই করা কেটলি হয় কি? না হলেও আমার যেন মনে হয় ওটা কলাই করা কেটলিই ছিল। না-ও হতে পারে। তবে তখন আমি এতই ছোট যে, জিনিসপত্র সম্পর্কে কোনও বিচারবোধ জন্মায়নি। কোনটা কেন বা কী, সে সব বড়রা জানে। আর কোথায় যে দেখেছিলাম, সেই জায়গাটার কথাও আমার মনে নেই।
তখন আমার দু’ভাগ, খানিকটা ময়মনসিংহে, আর খানিকটা কলকাতায়। ময়মনসিংহে আমি বেশির ভাগ সময়েই থাকতাম কারও না কারও কোলে। কত লোক! এক তো মা, তার পর দাদু, ঠাকুমা, জেঠিমা, চার জেঠতুতো দাদা, আরও সব দাদা-দিদিরা। সবচেয়ে বেশি অবশ্য দাদু। দাদু ছাড়া দুনিয়া অন্ধকার। সকাল থেকে রাত অবধি দাদুর সঙ্গে সেঁটে থাকতে চাইতাম। সেটা হত না, কারণ, দাদু অতি ব্যস্ত একজন মোক্তার, তাঁর কাছারি আছে, মক্কেলদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কতবার হয়েছে, আমার বায়নায় দাদু কাছারি কামাই করেছেন, মক্কেলদের ভুজুংভাজুং দিয়ে বিদেয় করে দিয়েছেন। দাদুর হাতেই স্নান, খাওয়া, শেষে ঘুম অবধি পাড়িয়ে কোলে করে মায়ের জিম্মায় দিয়ে আসতেন। বাবাকে চিনতাম বটে, কিন্তু বড্ড দূরের মানুষ। লম্বা, ছিপছিপে, অতিশয় সুপুরুষ একটা লোক মাঝে মাঝে আসে যায়, কখনও আমাকে একটু কোলেও নেয়, কিন্তু ওই এসোজন-বোসোজনের মতোই একজন মাত্র। হবে না-ই বা কেন। এম.এ., বি.এ., ল পাশ লোকটা তখন ওকালতি করে, টেনিস খেলে, হকি খেলে, ফুটবল পেটায়, আর ব্রিজ খেলায়ও ভারি পটু। তার ওপর আছে হারমোনিয়াম বাজিয়ে রাগাশ্রয়ী গান গাওয়া, বই পড়ার নেশা এবং আড্ডা। পরে বড় হয়ে দেখেছি, লোকটার সংগ্রহে কত না বই! কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ শেক্সপিয়র, কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ অস্কার ওয়াইল্ড, কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ জর্জ বার্নার্ড শ, ডেকামেরন থেকে শুরু করে আগাথা ক্রিস্টি, কী যে ছিল না। বেশ একটু বড় হয়ে শেক্সপিয়র বাদে আর সব বই আমি পড়েও ফেলেছিলাম। কিন্তু সে তো পরে। সেই চেতনার প্রথম উন্মেষকালে বাবা নিতান্তই একজন উটকো লোক। মনে আছে, লোকটা ঘামাচি মারতে খুব ভালবাসত। তাই গ্রীষ্মকালে যখন আমার গা-ভর্তি ঘামাচি হত, তখন লোকটা মাঝে মাঝেই আমাকে তার কোলে উপুড় করে ফেলে মহানন্দে নখ দিয়ে পুটপুট করে ঘামাচি মারত। সেটা আমার কাছে মোটেই সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু গম্ভীর, রাশভারী, আধচেনা লোকটাকে আদ্যন্ত ভয় পেতাম বলে আপত্তিও করতে পারিনি। বাবা বলতে তখন ওইটুকুই। তবে আমার চুপচাপ, স্নেহময়ী, ধর্মপ্রাণা নম্রকন্ঠ মা-কে আমার বড্ড ভাল লাগত। কিন্তু সারা দিন অত বড় সংসারের নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে মা এমন ভাবে হারিয়ে যেত যে, দেখাই পাওয়া যেত না।
তখন আমার আর আমার রোগাভোগা বায়নাদার, ছিঁচকাঁদুনে দু’বছরের বড় দিদির সারা দিনের আশ্রয় ছিলেন দু’জন। দাপুটে মোক্তার দাদু রাজকুমার মুখোটি, আর আমার দাপুটে ঠাকুমা হেমলতা দেবী। আমি আবার দাদুর বেজায় নেই-আঁকড়া। অথচ বড় হয়ে শুনেছি, দাদু তাঁর সন্তানদের বা অন্যান্য নাতি-নাতনিদের একেবারেই প্রশ্রয় দিতেন না। অত্যন্ত রাগী এবং রাশভারী বলে তারাও কদাচিৎ দাদুর নিকটবর্তী হতে পেরেছে। তাঁর চার মেয়ে আর দুই ছেলের সন্তানসন্ততি বড় কমও ছিল না। কিন্তু দাদু কেমন করে যেন তাঁর এই নাতিটির কাছে বশ হয়ে গিয়েছিলেন। আর সেটা এতটাই যে, আমার আবদার রাখতে দাদু অন্যায্য কাজ করতেও পিছপা ছিলেন না। তাঁর এই চূড়ান্ত পক্ষপাত দেখে আমার তুতো-ভাইবোনেরা আমাকে বেজায় হিংসে করত। একবার আমার এক জ্ঞাতিভাই আমাকে হয়তো একটা গাঁট্টা বা চিমটি বা চুল ধরে টানা গোছের একটা কিছু করেছিল। সেটা শুনে দাদু রেগে গিয়ে তাকে দা নিয়ে তাড়া করেছিলেন।
বড় হয়ে শুনেছি, দাদু তাঁর সন্তানদের বা অন্যান্য নাতি-নাতনিদের একেবারেই প্রশ্রয় দিতেন না। অত্যন্ত রাগী এবং রাশভারী বলে তারাও কদাচিৎ দাদুর নিকটবর্তী হতে পেরেছে। তাঁর চার মেয়ে আর দুই ছেলের সন্তানসন্ততি বড় কমও ছিল না। কিন্তু দাদু কেমন করে যেন তাঁর এই নাতিটির কাছে বশ হয়ে গিয়েছিলেন।
আমাদের দেশ হল ঢাকা, বিক্রমপুর। মুন্সিগঞ্জের অন্তর্গত টঙ্গিবাড়ি থানার অধীন বাইনখাড়া গ্রাম। খুব সম্পন্ন গৃহস্থ নয়, তবে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবার। আমার দাদুর পরের ভাই চন্দ্রকুমার ছিলেন শিক্ষক, ছোট অশ্বিনীকুমার তেমন কিছু করতেন না, সম্ভবত চাষবাস দেখতেন।
এটা চর্চিত সত্য যে, বিক্রমপুর বানভাসি অঞ্চল বলে সেখানে চাষের ওপর নির্ভরতা ছিল কম। বছরের ছ’মাস গোটা পরগনা জলের তলায় চলে যেত বলে চাষের অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতা ছিল। তাই বিক্রমপুরের পুরুষেরা লেখাপড়া শিখে রুজি-রোজগার করতে অন্যত্র যেত। আমার দাদু তেমনই একজন। তখন ময়মনসিংহ ছিল ফৌজদারি মামলার পীঠস্থান। একজন আমাকে বলেছিল, ময়মনসিংহের জমি অতি সরেস বলে, এখানে চাষিদের তেমন গা ঘামাতে হয় না। লাঙল দিয়ে বীজ ছড়ালেই বহুত। তাই চাষিদের হাতে অনেক বাড়তি সময় থাকে। আর সে-জন্যই ময়মনসিংহের চাষিরা এই বাড়তি সময়ে আর কিছু না পেয়ে মারদাঙ্গা বাধিয়ে নেয়। তাই এই জেলায় এত বেশি ফৌজদারি মামলা। এটা রসিকতাই হবে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ময়মনসিংহে প্রচুর ফৌজদারি মামলা হত।
মুক্তাগাছার জমিদার বীরভদ্রবাবুকে এক সময়ে আমার দাদু প্রাইভেট পড়াতেন। শিক্ষকের প্রতি বীরভদ্রবাবু এতটাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, নিজে বড় হয়ে কর্তৃত্ব পাওয়ার পর, দাদুকে শহরের অভিজাত এলাকায় অনেকটা জমি বসবাস করার জন্য দেন। আমাদের বাড়ির দু’দিকে দুটো জমিদারবাড়ি। এক দিকে গোলোকপুরের জমিদার, অন্য পাশে ভবানীপুরের জমিদার। মাঝখানে আমাদের বাড়ি। বাড়ি বলতে একটা বড়সড় উঠোন ঘিরে চারটে টিনের ঘর। মাটির মেঝে। গোটা বাড়িটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বাইরের দিকে অনেকটা ফাঁকা জমি এবং মাঠ, সেখানে দাদুর কাছারিঘর। অনেক মক্কেল জড়ো হত বলে ঘরখানা ছিল বেজায় বড়। বাকি জায়গাটা ছিল রাজ্যের ছেলেপুলেদের খেলবার জায়গা। বাড়ির পিছনে ছিল একটা পুষ্করিণী। উঠোনের এক কোণে ছিল পাতকুয়া, আর বাইরের মাঠের ধারে একটা টিউবওয়েল, তার পাশে গোয়ালঘর।
একমাত্র দাদু-ঠাকুমার ঘরটার মেঝেই ছিল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো, আর ওপরে ছিল লোভনীয় একটি পাটাতন, যেটাকে আমরা বলতাম ‘কার’। এই কারে উঠলে টিনের চালের গরমটা খুব টের পাওয়া যেত, আর রহস্যময় আলো-আঁধারিটা ছিল ভীষণ আকর্ষক। একটা সরু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে নানা বর্জিত জিনিসপত্র আর ট্রাঙ্ক-বাক্সের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো ছিল নেশার মতো।
যে-কথাটা বলাই হয়নি, তা হল একটি নদীর কথা, যে-নদীর কাছে আমার অপরিসীম ঋণ। ব্রহ্মপুত্র। বেশ চওড়া নদী, বিপুল জলের ঢল নিয়ে নিশিদিন বয়ে যেত। পাট, মুলিবাঁশ আর কত কী নিয়ে অগুনতি নৌকোর চলাচল। আর নদীর ধারে গেলেই পাট পচানোর কটু গন্ধ আসত নাকে। ও-পাড় ছিল শম্ভুগঞ্জ। সে এক রহস্যময় জায়গা। সন্ধেবেলা দেখা যেত আলেয়ার আলো। লোকে বলত আলেয়াভূত। সেই নদীর সঙ্গে আমার আশৈশব সখাভাব। কত জায়গা ছুঁয়ে আসত নদীর বিবাগী জল। উদাস স্রোত কোথা থেকে এসে কোন নিরুদ্দেশে চলে যায় কে জানে। সাঁতার শেখার পর ওই ব্রহ্মপুত্র ছিল আমার সবান্ধব জলক্রীড়ার তীর্থক্ষেত্র। দিনে ঘণ্টাটাক বা তার বেশি দাপদাপি না করলে শান্তি ছিল না। সে শুধু অবগাহন তো নয়, যেন মিশে যাওয়া। আজও সেই জলের পুণ্যস্পর্শ আমার সর্বাঙ্গে লেগে আছে।