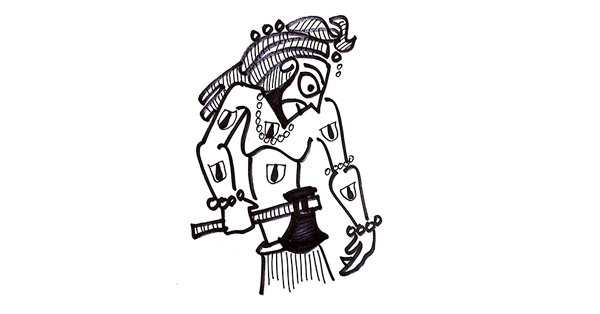হিয়া টুপটাপ, জিয়া নস্টাল : পর্ব ২৭

 শ্রীজাত (August 2, 2023)
শ্রীজাত (August 2, 2023)আজাদ হিন্দ পাঠাগার
আমরা যখন ছোট, তখন পাড়ায়-পাড়ায় লাইব্রেরি থাকত। হয়তো খুব বড় নয়, হয়তো বেশ সাদামাটাই তার সংগ্রহ, তবু, থাকত। কারণ হয়তো এই যে, তখনও বাড়িতে-বাড়িতে পড়াশোনার চলটা ভাল রকম জারি ছিল। অবসরে অভিভাবকরা যেমন বই মুখে করে বসে থাকতেন, স্কুলের পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে বাচ্চারাও ডুবে থাকত গল্পের বইয়ে। টেলিভিশন দেখার অনুমতি হয়তো হপ্তায় দু’দিন, খেলার অনুমতি কেবল বিকেলবেলাটুকু। বাকি রইল স্কুলের পড়া। সেও যখন শেষ, তখন কচিকাঁচারা কী করবে? এর উত্তর ছিল একটাই। গল্পের বই। কেননা সে ছাড়া অবসরের আর কোনও বন্ধু তখনও পৃথিবীতে আসেনি। সত্যি বলতে কী, আজ, এই প্রযুক্তির মুঠোভর্তি রমরমার যুগে দাঁড়িয়ে সেই সময়টাকে কল্পনা করাও খুব কঠিন। আমরা নেহাত বড় হয়েছি তেমন একটা সময়ে, তাই এসব লিখতে পারি। নইলে সেইসব চলে যাওয়া সময় আসলে ডাইনোসরদের মতোই, যাদের কঙ্কাল দেখার জন্য জাদুঘরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই কোনও।
এত কথা বলছি, তার কারণ একটাই। আমাদের ছোট্ট মধ্যবিত্ত পাড়াতেও ছিল একখানা লাইব্রেরি। আর সে নেহাত ছোটখাটো ছিল না, তখনকার তুলনায়। তার নাম ছিল আজাদ হিন্দ পাঠাগার। গড়িয়া অঞ্চলের যাঁরা বাসিন্দা, অন্তত সে-সময়ের, তাঁদের সকলের কাছেই এই নামটা ভীষণ চেনা। কেননা প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই এক-দু’জন করে অন্তত ছিলেন, যাঁরা এই পাঠাগারের সদস্য। তাই সকাল থেকে রাত, লাইব্রেরির কাউন্টার কখনও খালি যেত না। যখনই যাই না কেন, কয়েকজনের পিছনে দাঁড়াতে হতো।
আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেক হেঁটে, আদিগঙ্গার উপর সরু একটা সাঁকো পার হয়ে, বাঁ-হাতে পড়ত আজাদ হিন্দ পাঠাগারের দরজা। ভিতরে ঢুকেই প্রথমে মস্ত এক মাঠ, ফি বছর সেখানে নানা অনুষ্ঠান হয় তখন। কখনও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, কখনও বিজয়া সম্মিলনী, আবার কখনও গণনাট্য সংঘের উৎসব। বাবা-মা’র হাত ধরে খুব ছোট থেকেই সেসব অনুষ্ঠান দেখতে বা শুনতে যেতাম, আর ভাবতাম, কবে আমিও এই পাঠাগারের সদস্য হয়ে উঠতে পারব। না-পড়া বইয়ের প্রতি যে-আকর্ষণ ওই বয়সে টের পেতাম, তার তুলনা আর বড় হয়ে কিছুর প্রতি পাইনি।
সে যা হোক, একবার আমার জন্মদিনের উপহার হিসেবেই বাবা পাইয়ে দিলেন আজাদ হিন্দ পাঠাগারের অমূল্য সদস্যপদ, নামমাত্র বিনিময়ে। সে যে কী আশ্চর্য আনন্দের সময়, আজ আর লিখে বোঝাতে পারব না। কাউন্টারে এক গম্ভীরমতো কাকু থাকতেন বেশির ভাগ সময়ে, তাঁর দৌলতেই আমার হাতেখড়ি ঘটল সেখানে। মনে আছে, দু’খানা কার্ড ছিল। একটা গোলাপি রঙের, সেটা থাকবে সদস্যদের কাছে, আরেকটা হালকা সবুজ রঙের, সেটা থাকবে লাইব্রেরির জিম্মায়। কত তারিখে কী বই ইস্যু হচ্ছে আর কবের মধ্যে তা ফেরত দিতে হবে, সব হিসেব হাতের লেখায় ধরা থাকত ওই দুই কার্ডেই। একটা থাকত লাইব্রেরির আপিসের দেরাজে, অন্যটা সদস্যের নেওয়া বইয়ের মলাটের সঙ্গে সাঁটা। এভাবেই লেনদেন চলত তখন।
আমি যেন এক ধাক্কায় গিয়ে পড়লাম অথৈ সমুদ্রে। বাড়িতে গল্পের বই আছে ঠিকই। সেসব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বহুবার পড়াও হয়ে গেছে আমার। কিন্তু হাতের সামনে এত-এত ছোটদের বই দেখতে পেয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। কোনটা দিয়ে শুরু করব? আগে কী পড়লে ভাল হবে? এইসব ভেবেই কেটে গেল হপ্তাখানেক। আমাদের বাড়িতে গল্পের বই বিষয়ে কোনও গাইডলাইন ছিল না, বরং ছাড় ছিল অনেকটাই। যা ইচ্ছে পড়তে পারো, নেহাত খুব বড়দের বই না হলেই হল। পাঠাগারে অবশ্য বড়দের বই পর্যন্ত পৌঁছনোর কোনও উপায়ও ছিল না, সে-বিভাগ সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের জন্যে ছিল আলাদা অনেকগুলো তাক, তাতে থরে-থরে বই রাখা। রংবেরঙের মলাট তাদের, আর হরেকরকম নাম। কিছু শোনা, বেশির ভাগই না-শোনা। ভিতরে ঢুকলেই মনে হত সোনার খনিতে নেমেছি বুঝি। দু’হাত ভরে কুড়িয়ে নেবার আগেই চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। যেতও তাই।
পাঠাগারে অবশ্য বড়দের বই পর্যন্ত পৌঁছনোর কোনও উপায়ও ছিল না, সে-বিভাগ সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের জন্যে ছিল আলাদা অনেকগুলো তাক, তাতে থরে-থরে বই রাখা। রংবেরঙের মলাট তাদের, আর হরেকরকম নাম। কিছু শোনা, বেশির ভাগই না-শোনা। ভিতরে ঢুকলেই মনে হত সোনার খনিতে নেমেছি বুঝি।
কোন বই দিয়ে শুরু করেছিলাম, আজ আর মনে নেই। কিন্তু ওই একখানা ছোট্ট আর চৌকো গোলাপি রঙের কার্ড আমার সামনে এক নতুন পৃথিবী খুলে দিয়েছিল। বইয়ের পৃথিবী। একদিকে যেমন পড়ছি ‘কাউন্ট অফ মন্টেক্রিস্টো’ বা ‘দ্য হাঞ্চ অফ নোতরদম’, অন্যদিকে তেমনই পড়ছি দস্যু মোহন বা রঘু ডাকাতের গল্প। আর দেখতে-দেখতে, নিজের অজান্তেই, বই দিয়ে তৈরি এক ঘন অরণ্যে প্রবেশ করছি ছোটবেলার আমি। যেখানে কেবল ভিতরদিকেই যাওয়া যায়, যেখান থেকে বেরোনোর রাস্তা জানা নেই কারও। সত্যি বলতে, নেশা যে কী মারাত্মক হতে পারে, সেটা ওই বয়সে বুঝতাম না, আজাদ হিন্দ পাঠাগার না থাকলে।
স্কুল যখন খোলা, তখন হপ্তায় একটা করে বড় বই পড়া হত। সে নাহয় একরকম। নেশাটা চাগাড় দিয়ে উঠত গরমের ছুটি বা পুজোর ছুটিতে। দু’দিনে একখানা করে বই শেষ করছি তখন। জোগান দিতে-দিতে লাইব্রেরির গম্ভীরকাকুও হাঁপিয়ে উঠছেন রীতিমতো। একের পর এক পড়ে যাচ্ছি টারজানের অ্যাডভেঞ্চার, সেসব শেষ হতে না হতেই গোয়েন্দা গণ্ডালু আমার প্রিয় হয়ে উঠছেন। কেবল তাতেই রক্ষে নেই, পাড়ার বন্ধুদের মধ্যে চলত পড়ার প্রতিযোগিতা। ছুটির দুপুরে যে যার লাইব্রেরি কার্ড বার করে মিলিয়ে দেখতাম, কে কতগুলো বই পড়েছি। তাতে পড়বার জেদ আর তাড়া, দুটোই বেড়ে যেত অনেকখানি। চুরিবিদ্যাও চলত একটু-আধটু। কোনও বন্ধুর মা হয়তো ‘কোয়েলের কাছে’ পড়ে শেষ করেছেন সদ্য, বইটা ফেরত দেওয়া হয়নি। সে-বই একরাতের জন্য চলে এল আমাদের হাতে। কখনও দু’খানা দুপুরের জন্য আমরা ধার পেলাম ‘যুবক যুবতীরা’। বই আমাদের একটু একটু করে কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, ওই দুপুর আর রাত মিলিয়ে। এখন মনে হয়, আজাদ হিন্দ পাঠাগারের ছোটদের বিভাগের সব বই-ই বোধহয় পড়ে শেষ করে ফেলেছিলাম, এত বেশি ছিল পড়ার তেষ্টা, জানার খিদে। এখন কোনও লাইব্রেরি এমনভাবে টানে কি? না মনে হয়। কোনও নতুন বই যখন হাতে আসে, পড়ি ঠিকই, কিন্তু রাত জেগে, কাজ বাদ দিয়ে পড়ে ফেলবার যে-তাগিদ, তা সেই ছোটবেলার সঙ্গেই চলে গেছে কোথায়।
এই লেখাটা লিখলাম একটাই খেদ থেকে। সেদিন খবর পেলাম, আজাদ হিন্দ পাঠাগার আর নেই। বন্ধ হয়ে গেছে। কথাটা শুনে স্বজন বিয়োগের চেয়ে কিছু কম কষ্ট পাইনি। কেননা সারা বছর ওই লাইব্রেরিই ছিল আমাদের বন্ধুমহল, আমাদের আশ্রয়, আমাদের অভিভাবকও বটে। তা মৃত্যু মানে আমাদের ছোটবেলারও অনেকখানি অংশের বিদায়। খোঁজ করলাম, কেন বন্ধ হল ওইরকম একখানা পাঠাগার? জানা গেল, শেষ কয়েক বছর আর কোনও সদস্যই হচ্ছিল না লাইব্রেরির। বইগুলোয় ধুলো আর মাকড়সার জাল জমছিল, গোলাপি আর সবুজ কার্ড পাশাপাশি পড়ে থাকছিল মলিন দেরাজে। ঘরের আলো জ্বালাবার মতো টাকাও উঠত না চাঁদা থেকে, কর্মীদের মাইনে তো দূরস্থান। তাই শেষমেশ বন্ধ করে দিতে হল তার দরজা। আর ওই দরজার ওইপাশে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে, অনেক-অনেক পুরনো, ধূসর বইয়ের ফাঁকে বন্ধ হয়ে রইল আমাদের ছোটবেলা। যা, ওইসব বইদের মতোই, বাতিল আর অপ্রয়োজনীয় আজ।
ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook