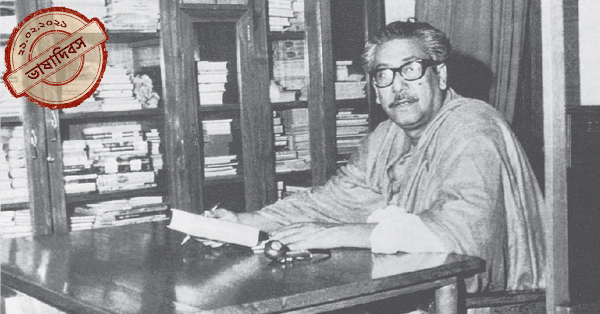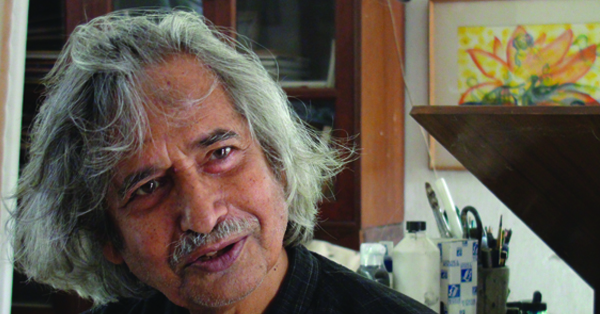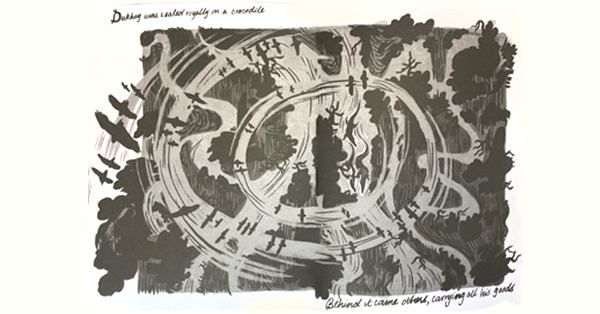ছায়াবাজি: পর্ব ১৫

 চন্দ্রিল ভট্টাচার্য (July 8, 2023)
চন্দ্রিল ভট্টাচার্য (July 8, 2023)নায়িকার ভূমিকায়
কয়েকটা ছবি শুধু নায়ক বা নায়িকার ওপর নির্ভর করে থাকে। তারকা নয়, ছবির নায়ক বা নায়িকা, যাঁকে প্রায় কেউ চেনে না, নতুন বা অখ্যাত, কিন্তু যিনি অভিনয়ের গুণে গোটা ছবিটাকে উতরে দেবেন। অভিনয় অসামান্য হতে পারে, নাও পারে, কিন্তু এই শুধু অভিনয়ের ওপর নির্ভর করাটার মধ্যে একটা চিন্তাগত দারিদ্র আছে। এতে কোনও সন্দেহই নেই যে অভিনয় একটা ছবিকে বহুদূর নিয়ে যেতে পারে, কারণ সেটাই ছবির প্রকাণ্ড জরুরি উপাদান, কিন্তু ছবির চিত্রনাট্য যদি নড়বড়ে হয়, তবে শুধু অভিনয় বা শুধু ক্যামেরা বা শুধু গান দিয়ে সেই দুর্বলতা ঢাকা যায় না। ‘টু লেসলি’ (চিত্রনাট্য: রায়ান বিনাকো, পরিচালনা: মাইকেল মরিস, ২০২২) সম্পর্কে অবশ্য খুব কর্কশ কথা বলা যায় না। কারণ চিত্রনাট্য এখানে বিরাট কায়দা ফলাতে চায়নি, শুধু লেসলি নামে এক মহিলার সোজসাপ্টা গল্প বলতে চেয়েছে— যে কিনা লটারিতে বিরাট টাকা জিতেছিল, তারপর মদ ও ড্রাগ খেয়ে সব উড়িয়ে দেয়, এমনকি এই নেশার ঘোরে নিজের ছেলেকে অবধি ছেড়ে চলে যায়। ছেলের বয়স তখন ছিল ১৩। এখন, ছ’বছর পরে, লেসলি কপর্দকশূন্য, তার পরিবারের কেউ তাকে দেখতে পারে না, বন্ধুরাও এড়িয়ে চলে। তার থাকার জায়গা নেই, এখানে লাথি সেখানে ঝ্যাঁটা খায়, রাস্তার ধারে দিন কাটায়, একটা সুটকেসে কিছু জামাকাপড় আছে, আর আছে তার ছেলের সঙ্গে কয়েকটা ছবি। কোথাও না থাকতে পেয়ে সে ছেলেকে ফোন করে, ছেলে এখন রাজমিস্ত্রির কাজ করে, সে মা’কে নিজের কাছে এনে রাখে, কিন্তু শর্ত দেয় যে মা মদ ছুঁতে পারবে না। লেসলি বলে, মদ সে ছেড়ে দিয়েছে। তারপর ছেলে আর ছেলের রুমমেটের জামাকাপড় ঘেঁটে, আলমারি ঘেঁটে টাকা চুরি করে এবং তাই দিয়ে মদ খায়। ব্যাপারটা গোপন থাকে না এবং ছেলে তাকে বের করে দেয়, লেসলি অন্যের কাছে থাকতে যায়। সেখানেও একই শর্ত, সেখানেও সব প্রতিজ্ঞা ভেঙে মদ খাওয়া এবং সেখান থেকেও বহিষ্কার। এই পর্যায়ে লেসলির অসহায়তা, বিষাদ, ক্ষোভ এবং নেশার ওপর প্রবল নির্ভরতা ভয়ানক ভাল ফুটিয়েছেন অভিনেত্রী অ্যান্ড্রিয়া রাইসবরো। লেসলিকে সারা পৃথিবী প্রত্যাখ্যান করেছে, অতখানি টাকা সে নষ্ট করে ফেলেছে বলে তাকে নিয়ে বিস্ময় ও হাসাহাসির অন্ত নেই, এখন পাঁড় মাতাল বলে লোকে তার প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য নিয়ে তাকায়— পুরোটাই সে বুঝতে পারে এবং মাঝেমাঝে চোখের জল চেপে রাখতে পারে না। তবু এই গর্তে, এই ঢাল বেয়ে, তার জীবনের চলাটা যেন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, এ থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা তার নেই। যতগুলো আবেগ— নিজের প্রতি মায়া, নিজের ভাগ্যের প্রতি ক্রোধ, ছেলে যে কোনওদিনই আর আপন হবে না সেই উপলব্ধি, ভিখিরির অধিক জীবন যে আর কখনও আয়ত্ত হবে না সেই বোধ, যে লোকগুলো তাকে নিয়ে সর্বক্ষণ ঠাট্টা করছে তারা কেউ তার চেয়ে খুব উন্নত নয় সেই ধারণা এবং তাদের সপাটে মেরে ফেলার প্রকাণ্ড ইচ্ছে আর তা না পারার গ্লানি— সবই এই নায়িকার মুখে চোখে দেহভঙ্গিতে দুরন্ত ফুটে উঠেছে। গল্পের পরের দিকটা, যেমন হয়, দ্বিতীয় সুযোগের। শাপমুক্তির। লেসলিকে ভবঘুরে বলে তাড়িয়ে দেওয়া একটা লোক অন্যের কাছে তার জীবনের গল্প শুনে একটু নরম হয় এবং নিজের মোটেল-এ তাকে চাকরি দেয়। ঘর ঝাড়পোঁছ করার কাজ। কিন্তু সে অনিয়মে এবং অকর্মণ্যতায় দীক্ষিত হয়ে গেছে, দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে, রোজ মদ খায় ও রাত করে ফেরে। মোটেলের লোক শেষমেশ তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু এবার লেসলি কথা দেয়, সুরাসক্তি-মুক্ত হবে। যদিও উইথড্রয়াল এফেক্টে তার খুবই দুরবস্থা হয়, কিন্তু সে কদিন প্রবল মনের জোরে লড়ে নিজেকে মদ-নির্ভরতা থেকে ছাড়িয়ে নেয়। তারপর তার একটা নিজের খাবার-দোকান খোলার গল্প। ছেলের সঙ্গেও পুনর্মিলন হয়, ছবির শেষে লেসলি ঘর বর সন্তান ব্যবসা, সবই পায়। আমরা প্রথম থেকেই নায়িকার প্রতি সমব্যথী হয়ে উঠি, কিন্তু যেহেতু তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারগুলো খুবই এক-গোত্রীয় এবং পেল্লায় অনুমানযোগ্য, তাই আমাদের একটা সময়ের পর ‘এ বাবা, ফের মদ খাচ্ছে, তার মানে তো আবার অপমানিত হবে গো’ গোছের ভয় ছাড়া বিশেষ কিছু ঘটে না, অনুভূতি একরঙা বলেই ভোঁতা হয়ে যায়। এছাড়া বহুক্ষণ ধরে একটা লোকের নিরুপায়তা দেখিয়ে, তারপর একটা মন্তাজে তার মদ ছেড়ে দেওয়ার আখ্যান (বমি আর কাঁপুনি আর দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া কিন্তু ফের ফিরে আসা) দেখিয়েই তাকে ভাল-র পথে রওনা করে দেওয়া, এর মধ্যে একটু বেশিমাত্রায় সরলতা আছে। একটা লোকের মদাসক্তি কেটে গেলেই সে চমৎকার হয়ে উঠবে, কাজে দিব্যি নিষ্ঠাবতী ও অধ্যবসায়ী হয়ে উঠবে: এও বড্ড সরল ভাবনা। কিন্তু ছবিটা দেখতে খুব খারাপ লাগে না, একজন পূর্ণ পরাজিত লোকের সঙ্গে কে না আত্মসম্বন্ধ পাতাতে পারে? যখন লেসলি ছেলেকে বলে ‘আরে জামাকাপড়ের দাম আমি দিচ্ছি, ছেলের কাছে কেউ অন্তর্বাস কেনার টাকা নেয় না কি’, আর তারপর ব্যাগ হাতড়াতে শুরু করে, যেন মানিব্যাগ আছে কিন্তু সে খুঁজে পাচ্ছে না, সে দৃশ্য মর্মস্পর্শী। মাতাল অবস্থায় কিংবা অপমানের তুঙ্গমুহূর্তে, যখন একটা লোকের হারাবার কিছু থাকে না (এবং সে অতিরেকের লাইসেন্স পেয়ে যায়), অ্যান্ড্রিয়া খুব ভাল অভিনয় করেছেন। বহুবার তাঁর কান্না, চিৎকার, এবং গালাগাল দুর্ধর্ষ প্রদর্শন করেছেন, আনমনা মুদ্রাদোষও, কিন্তু ছবিটা পুরোটাই তাঁর ঘাড়ে হেলে আছে। ছবিটা যে দেখা যায়, তা তাঁরই গুণে, আর তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই বোধহয় পরিচালক ঠিক করেছেন, তিনি যখন প্রায় প্রতিটা ফ্রেমে আছেন তখন একমেটে গল্প বললে ক্ষতি নেই।

কিন্তু ছবিটা দেখতে খুব খারাপ লাগে না, একজন পূর্ণ পরাজিত লোকের সঙ্গে
কে না আত্মসম্বন্ধ পাতাতে পারে?‘রিটার্ন টু সোল’ (Return to Seoul) (চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: ডেভি চাউ, ২০২২) ছবিটাও নায়িকার মুখের ওপর প্রায় সারাক্ষণ নজর নিবদ্ধ রাখে, কিন্তু অভিনেত্রীকে বোধহয় বলে দেওয়া হয়েছে কোনও অভিব্যক্তি প্রদর্শন না করতে। তা একটা স্টাইল হতেই পারে, কিন্তু তাহলে তো চিত্রনাট্যে খুব একটা আবেগ থাকলে চলে না। এদিকে ছবির গল্প দাঁড়িয়ে আছে মা-বাবার প্রতি মেয়ের ভালবাসার ওপর। নায়িকা ফ্রেডি জন্মগত ভাবে কোরিয়ান, কিন্তু তার প্রকৃত বাবা-মা তাকে দত্তক-কেন্দ্রে দিয়ে দিয়েছিল, সে ফ্রান্সের এক দম্পতির কাছে মানুষ হয়েছে। এখন বড় হয়ে কোরিয়ায় এসেছে, জন্মদাতা মা-বাপকে খুঁজতে। দত্তক-কেন্দ্রের বার্তা পেয়ে মেয়েটির বাবা দেখা করতে উৎসাহী হয়, কিন্তু মা কোনও সাড়া দেয় না। বাবা রোজ রাতেই নাকি মদ খেয়ে তার কথা ভাবে ও কান্নাকাটি করে। বাবা আর মা বহুকাল একসঙ্গে থাকে না, বাবা ফের বিয়ে করেছে, তার দুই মেয়েও এখন অনেকটা বড়। গোটা পরিবার ফ্রেডির সঙ্গে দেখা করে, ফ্রেডির ঠাকুমা বলেন যে দারিদ্রের চোটে তাঁরা ফ্রেডিকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফ্রেডি পরে বাবার পরিবারের কাছে থাকতেও আসে দিনতিনেকের জন্য, সেখানে তার বরং একটু সহানুভূতি হয় বাবার এই পক্ষের স্ত্রীর জন্য, যে মুখ বুজে সারাদিন সংসারের জন্য খেটে চলেছে। বাবা আবেগপ্রবণ, কিন্তু ফ্রেডি তার প্রতি বেশ নিষ্ঠুর, বাবার গাদা গাদা মেসেজের কোনও উত্তরও দেয় না, বাবার দেওয়া সস্তা জুতো সে পার্কে ফেলে দেয়। আবার ফ্রেডির সঙ্গে একরাতের যৌনতা হয়েছিল যে কোরিয়ান ছেলেটির, সে প্রেম জানাতে ফ্রেডি হেসে ওঠে এবং তার উপহারটাও প্রত্যাখ্যান করে। মনে হয় কোনও কিছুই তার হৃদয়ে খুব দাগ কাটে না। তার এক বান্ধবী বলে, তুমি খুব বিষণ্ণ লোক। তারপর ছবিতে হঠাৎ বলা হয়, দু’বছর কেটে গেছে। আমরা দেখি ফ্রেডি কোরিয়াতেই থাকে, একটা চাকরি করে, তার প্রচুর বন্ধুবান্ধব আছে, একজনকে দেখে তো মনে হয় প্রেমিক, কিন্তু ফ্রেডি টিন্ডার-এ ডেটও করে। তার জন্মদিনের পার্টিতে ক্লাবে গিয়ে নাচানাচি হয়, আবার সে মাঝেমাঝে বিষণ্ণও হয়ে পড়ে, কারণ তার মা জানিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চায় না। দত্তক-কোম্পানির টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছে মা, ২২ শব্দে। টিন্ডারে ডেট করতে গিয়ে ফ্রেডি বলে, সে রোজ ভাবে মা তার কথা ভাবে কি না। আবার হট করে বলা হয়, আরও ক’বছর কেটে গেছে। তখন ফ্রেডি তার ছেলেবন্ধুকে নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যায়, আমরা জানতে পারি ফ্রেডি এখন মিসাইল বেচছে। বাবা তার জন্য পিয়ানো বাজিয়ে একটা সুর তৈরি করে মোবাইলে রেকর্ড করে এনেছে। গাড়িতে ফেরার সময়ে সে একেবারে অকস্মাৎ, কোনও কারণ ছাড়াই দুম করে প্রেমিককে বলে ওঠে, আমি তুড়ি মেরে তোমাকে আমার জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারি। প্রেমিক স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী বললে? ফ্রেডি কথাটার পুনরাবৃত্তি করে। আবার কিছুক্ষণ পর জানা যায়, আরও এক বছর ( না কি দু’বছর, সত্যি গুলিয়ে গেছে) কেটে গেছে। ফ্রেডির মা দেখা করতে রাজি হয়েছেন। ফ্রেডি দত্তক-কেন্দ্রে (সেখানেই দেখা হবে) গিয়ে চেয়ারে বসে কাঁদতে থাকে, মা এসে তার গায়ে হাত বোলাতে থাকে। মা একটা মেল আইডি দেয় যোগাযোগের জন্য। তারপর আবার এক বছর কেটে গেছে। ফ্রেডি বোধহয় কোথাও একা ট্রেক করছিল, হোটেলে বাথরুমে গিয়ে সে মা’কে মেল করে, কিন্তু মেল ডেলিভারি হয় না, ফেলিওর দেখায়। শেষে ফ্রেডি সেই হোটেলের পিয়ানোয় বসে সুর তুলতে থাকে। মানে, চলতি আর্ট ফিলিম মার্কা ছবি। গল্পটা ঘনবদ্ধ নয়, এদিকে গল্প-গল্প ভান আছে, ‘ধুর গল্পই বলব না’ চলন নেই। ‘ইমোশন আবার কী’ ঢং আছে, ওদিকে ইমোশনের ওপরেই পুরোটাকে হেলান দেওয়া আছে। চিত্রনাট্যটা ছড়ানো ও ছ্যাৎরানো। মাঝে মাঝেই লাফাতে লাফাতে এক-পাঁচ-দুই বছর কেটে যায়, জন্মদিন দিয়ে একটা সূত্র বোনার চেষ্টা হয়, কিন্তু তার ওপরেও খুব জোর নেই। কী হচ্ছে তার যুক্তি বা কার্যকারণ স্পষ্ট করা হয় না, ফ্রান্সে মানুষ হয়ে আচমকা একটা লোক কোরিয়ায় এসে কাজ করছে কেন তার উত্তরে বলা হয়, সে উত্তর কোরিয়ার হাত থেকে দক্ষিণ কোরিয়াকে রক্ষা করতে চাইছে। যদি ধরে নিই, ছবিতে বলতে চাওয়া হয়েছে, একটা মেয়েকে তার বায়োলজিকাল মা-বাবা অন্যের কাছে দিয়ে দিয়েছিল, তাই সে আর আজীবন কাউকে ভালবাসতে পারে না— যে প্রেম জানাচ্ছে তাকে না, যে প্রেমিকের সঙ্গে আছে তাকে না, যে দেশে মানুষ হয়েছে তাকে না, শুধু শেকড়ের কাছে ফিরতে চায়: নিজের মা, নিজের মাতৃভূমি— তাহলে সেই ন্যাকা বক্তব্যের উপযোগী জবজবে ছবি হয়নি। নায়িকার প্রতি আমাদের মায়া ভালবাসা সমবেদনাও তৈরি হয় না। কারণ তার চরিত্রটাকে গড়েই তোলা হয়নি তেমন ভাবে, শুধু ভাসমান একটা কচুরিপানার মতো রাখা হয়েছে প্রায় সব ফ্রেমে। অভিনেত্রী জি-মিন পার্ক প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছেন, মোটামুটি গম্ভীর থেকেছেন, নাইটক্লাবে গানের সঙ্গে খুব নেচেছেন (আধুনিক গোলমালাক্রান্ত জীবন দেখাতে গেলে প্রচণ্ড উচ্চগ্রামে ধক্কাস-ধক্কাস গানের সঙ্গে নাচ দেখাতে হয়), বাসে যেতে যেতে আচমকা ‘ড্রাইভার, গাড়ি ফেরাও, সোল-এ ফেরত চলো’ অবাস্তব চিৎকার ও ছোটাছুটি অবধি করেছেন, কিন্তু তাতে তো ছবির আবেদন তৈরি হয় না। সিনেমায় গল্প থাকতে হবে তার কোনও মানে নেই, বহু আধুনিক ছবিতে বরং কোনও গল্প থাকে না এবং একেবারে কিছুই ঘটে না, কিন্তু সেখানে আবার নায়িকা মা’র জন্য ককিয়ে সারা ছবি কাটিয়ে দেয় না। সেখানে মূল সুরটাই হচ্ছে আবেগহীনতা এবং কোনও কিছুকেই বিরাট আবেগের যোগ্য না ভেবে ওঠা। বুঝতে হবে, নায়িকা এই জন্মদাত্রীকে কখনও চোখে দেখেনি, তার কাছে এই মা একটা থিওরিটিকাল অস্তিত্বমাত্র। তাহলে আধুনিক একটা ফরাসি মেয়ের এত তনছট আদিখ্যেতা কেন, তার কোনও কারণ উপস্থিত করা হয় না। মা বললেই কান্না পেয়ে গেলে, আধুনিক ছবি করা শক্ত, অন্তত আউটসাইডার-উত্তর যুগে। এই মাঝামাঝি-কাটিং ছবি বলেই বোধহয় খুব বিখ্যাত হয়েছে এই ফিল্ম, এবং সেজন্যেই আরও সন্দেহের চোখে দেখা উচিত যে কোনও মাঝ-আকাঙ্ক্ষী প্রয়াসকে।
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook