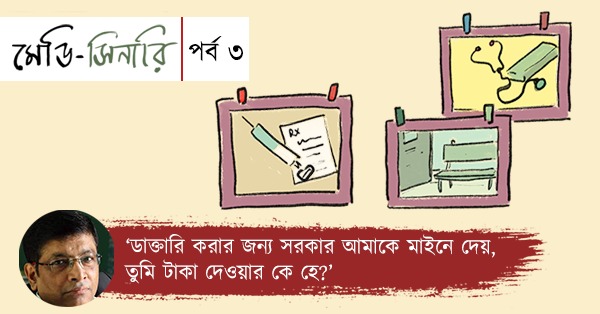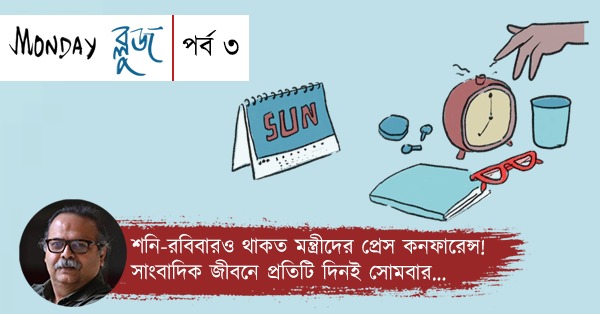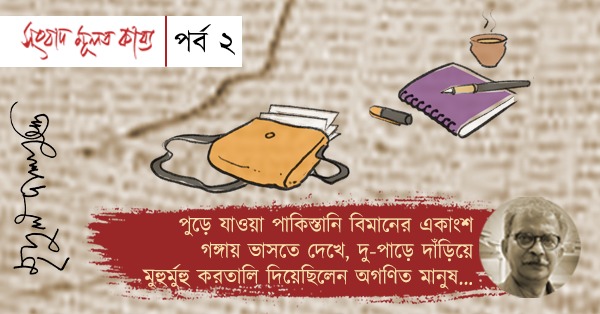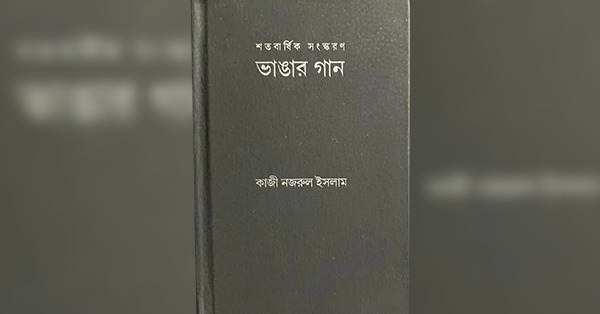কনিষ্ঠ আঙুল

 অর্ণব চক্রবর্তী (August 26, 2022)
অর্ণব চক্রবর্তী (August 26, 2022)কাট’। পরিচালক প্রমোদকান্তি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিগারেট ধরালেন। তারও কয়েক সেকেন্ড বাদে ধীরে-ধীরে উঠে বসল সুমন। আগেরবার কাঁধ, এবার কনুই। কাঁধের ব্যথাটা খুব বেশিক্ষণ থাকবে না বোধহয়, কিন্তু কনুইয়ের ব্যথাটা মনে হচ্ছে ভোগাবে। সে হাত ঘুরিয়ে কনুইয়ের অংশটা দেখার চেষ্টা করে। ইশ, এর মধ্যেই ফুলে গেছে! তাও হাড় যে ভাঙেনি তাই রক্ষে! সুমন দু’একবার হাত ভাঁজ করে, সোজা করে, অন্য হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ব্যথার উগ্রতা পরখ করে নিতে চায়। তারপর ব্যথা কিছুটা ধাতস্থ হলে সে অভিমানী মুখ তুলে তাকায় সামনের দিকে।
ঘরভর্তি লোক তাকে দেখছে। ফাঁকে-ফাঁকে আড়চোখে পরিচালকের দিকেও তাকাচ্ছে কেউ-কেউ। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে সুমনও পরিচালকের দিকে তাকায়। প্রমোদকান্তি ভীষণ বিরক্ত হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে দেখছেন। জানলায় কাচ দেওয়া। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি এক্ষুনি ঘুষি মেরে কাচটা ভেঙে ফেলবেন। সুমনের অভিনয়ে যে তিনি খুশি নন তা আর বলে দিতে হয় না। অথচ শুধুমাত্র একটা পড়ে যাওয়ার দৃশ্য দিয়ে একজন অভিনেতাকে বিচার করা কি ঠিক? সংলাপ দিয়ে দেখুন! ক্রোধের সংলাপ, কান্নার সংলাপ, এমনকী সংলাপহীন অভিব্যক্তির গূঢ় ভাষাও সুমনের আয়ত্তে আছে। কিন্তু প্রমোদকান্তি পড়ে আছেন ওই একটা দৃশ্য নিয়েই। আগের বার কাঁধে ব্যথা পাওয়ার পর সুমন তাঁকে বলেছিল, ‘এই দৃশ্য দিয়ে কি অভিনয় যাচাই করা ঠিক?’
প্রমোদকান্তি কড়া গলায় বলেছেন, ‘ভাত সেদ্ধ হয়েছে কি না একটা চাল টিপেই বোঝা যায়। হাঁড়ি উপুড় করে দেখতে হয় না।’
সুমন প্রমোদকান্তির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ‘হয়নি, না?’
প্রমোদকান্তি কটমট করে তাকালেন। ‘জিজ্ঞেস করছেন? আপনি তো একজন অভিনেতা। একটা সিন উতরোল কি না অভিনয় করে বুঝতে পারেন না?’
‘না, পুরোপুরি ইয়ে করে তো করা যাচ্ছে না!’
‘কিয়ে করে করা যাচ্ছে না? কী চাই আর আপনার?’
‘আসলে কাপড় যেটা পেতে রাখা হয়েছে, সেটা খুব পাতলা। লাগছে খুব।’
‘আপনি একজন অভিনেতা হয়ে এত আতুলে কেন বলুন তো? ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান!’
‘না মানে, সেফটিটা দেখতে হবে না?’
‘এইটা আমার ফোর্থ ফিল্ম, বুঝলেন? আপনার সাথে প্রথম কাজ করছি না আমি। এমন কিছু করতে বলছি না যে আপনি মরে যাবেন।’
‘ও! তাহলে আরেকবার চেষ্টা করে দেখব?’
‘আর কতবার চেষ্টা করবেন বলুন তো! চেষ্টা করেও তো হবে বলে মনে হয় না। আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেই বোঝা যায়।’
‘কী বোঝা যায়?’
‘বোঝা যায় আপনি একটা ভিতুর ডিম! নিন, করুন এবার ঠিক করে। বাপ রে বাপ! সংলাপ নেই কিছু নেই, তাতেই এই!’
সুমন আবার ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ায়। দৃশ্যটি সহজ। গুলির শব্দ হবে এবং সুমন ছিটকে পড়বে। পরিচালকের একটাই দাবি— পড়ে যাওয়ার দৃশ্য স্বাভাবিক হওয়া দরকার। সুমন আমতা-আমতা করে বলেছিল, ‘ইনডিরেক্টলি দেখানো যায় না ব্যাপারটা?’
প্রমোদকান্তি কটমট করে তাকিয়েছিলেন। ‘আমাকে জ্ঞান দেবেন না। আপনি আপনার কাজটা করুন, আমি আমার কাজটা করব।’
সুমন লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকাল।
‘রেডি?’
‘হ্যাঁ।’
হ্যাঁ বলার পরই সুমন বুঝল যে সে রেডি নয়। তার ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটা কাঁপছে।
এটা প্রথমবার নয় অবশ্য। আগেও বহুবার তার কনিষ্ঠ আঙুল কেঁপেছে। তার দৃঢ় ধারণা, কনিষ্ঠ আঙুলটা তাকে ঠিক সময়ে সতর্ক করে দেয়। আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে।
না, বিপদ তেমন কিছু এখনও হয়নি তার। কারণ প্রতিবারই সে আঙুলের কথা শুনেছে। কিন্তু কনিষ্ঠ আঙুলের কথা না শুনলে ভয়ানক গোলযোগ কিছু একটা যে ঘটবেই, এ-বিশ্বাসে সন্দেহের ছায়া কখনও পড়েনি। আর পড়বেই বা কেন? ব্যাপারটা তো তার ক্ষেত্রেই প্রথম হচ্ছে না! ঠাকুমার যেমন ভুরু নাচত, বাবার যেমন কান চুলকাত, সেরকমই তার কনিষ্ঠ আঙুল থরথর করে কাঁপে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে একটা ব্যাপার আছে না? না, সবার অবশ্য নেই। কিন্তু কিছু-কিছু মানুষের আছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কখনও তাদের প্রতারণা করে না। বাবা বলত, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হচ্ছে শরীরের কম্পাস। এই পৃথিবীতে গুটিকয় মানুষ শরীরের মধ্যে কম্পাস নিয়ে জন্মায়। সেটা ঠিক সময়ে তাদের পথ দেখিয়ে দেয়।
বাবার বিশ্বাস ছিল ব্যাপারটা জেনেটিক। তাদের বংশের সবার মধ্যেই নাকি এই শক্তিটা বর্তাবে! স্ত্রী-পুত্রের চেয়েও সংসারে তাকে বেঁধে রেখেছিল এই ঐতিহ্য। ফলে সুমনের বারো বছর বয়স অবধি যখন কিছুই পাওয়া গেল না, তখন বাবা মুষড়ে পড়েছিল কিছুটা। সুমনকে মাঝে মাঝে ডেকে শরীরের বিভিন্ন অংশে চাপ দিয়ে বলত, ‘এখানটা সুড়সুড় করে মাঝে মাঝে? এখানটা করে? এখানটা?’ তারপর একদিন কথা নেই-বার্তা নেই সুমনকে বেত দিয়ে বেধড়ক পেটাল। পেটাতে-পেটাতে চিৎকার করছিল, ‘এখনও বল, কিচ্ছু হয় না? কিচ্ছু টের পাচ্ছিস না তুই? মেরেই ফেলব তোকে আজকে…’ মা আর ইসমাইল কাকা দু’দিক থেকে ছুটে এসে থামিয়েছিল। ইসমাইল কাকা তখন ইরাক থেকে এসেছিল এক মাসের ছুটিতে। সুমনকে মারধোর করার পরদিন বাবাকে ডেকে বলল, ‘শুনো গা, ইখানে থাইক্যা তুমার মাথা আউলা হয় যাইব। ইরাক যাবা?’ তারপর হুটোপুটি করে ভিসা করা, জুতো কেনা, জামা কেনা… যুদ্ধ লাগার বছর তিনেক আগের কথা। যুদ্ধের আগে বাবার কান চুলকেছিল কি না, তা সুমনরা কেউ জানে না।
‘অ্যাকশন!’
সাথে-সাথে ক্যাপ ফাটানো বন্দুকের শব্দ হল। এখন সুমনের পড়ে যাওয়ার কথা। অথচ সে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে।
‘কাট।’
‘আমার একটা কথা বলার ছিল প্রমোদবাবু। একটু প্রাইভেটলি বলতে পারলে ভাল হত।’
প্রমোদকান্তি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখে হতাশা আর রাগ। উত্তর দিলেন না। সুমন এগিয়ে এল তাঁর কাছে। ‘প্লিজ!’
সে একটা অজুহাত খুঁজছিল, প্রথম যেটা মাথায় এসেছে সেটাকেই ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে নিচ্ছে। যে-ঘরে শুটিং হচ্ছিল, সেখান থেকে মাঝের চাতালে যেতে যতটা সময় লাগে তারই মধ্যে সে একটা কাল্পনিক গল্প দাঁড় করিয়ে ফেলেছে।
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে একটা ব্যাপার আছে না? না, সবার অবশ্য নেই। কিন্তু কিছু-কিছু মানুষের আছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কখনও তাদের প্রতারণা করে না। বাবা বলত, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হচ্ছে শরীরের কম্পাস। এই পৃথিবীতে গুটিকয় মানুষ শরীরের মধ্যে কম্পাস নিয়ে জন্মায়। সেটা ঠিক সময়ে তাদের পথ দেখিয়ে দেয়।
চাতালে এসে প্রমোদকান্তি সিগারেট ধরালেন। তিনি সুমনের দিকে তাকাচ্ছেন না। তাকিয়ে আছেন দূরে দিগন্তের দিকে আর সিগারেটে লম্বা-লম্বা টান দিয়ে খানিকটা দীর্ঘশ্বাসের মতো ধোঁয়া ছাড়ছেন। সুমন শুরু করবে কি না বুঝতে পারে না। প্রমোদকান্তি কি তাকে নিজে থেকে বলতে বলবেন, না কি সুমনেরই শুরু করা উচিত?
‘বলুন কী বলবেন।’ প্রমোদকান্তির সিগারেট অর্ধেকটা শেষ হয়েছে, গলাও আগের তুলনায় স্বাভাবিক। যেন তেমন গুরুতর কোনো সমস্যাই হয়নি, মানুষটা রাগতেই জানে না! যেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কাজ খুব সুচিন্তিত; হঠকারী কোনও সিদ্ধান্ত তিনি আজ অবধি কখনও নেননি।
সুমন আসল অভিনয় এবার শুরু করে, ‘আমার ঠাকুরদা বত্রিশ বছর বয়সে স্ত্রী আর দুই সন্তান রেখে মারা যান। স্নান করতে গিয়েছিলেন কুয়োতলায়। ফেরার সময় পা পিছলে পড়েন সিমেন্টের বাঁধানো চাতালের ওপর। হাতে বালতি আর সাবান থাকার জন্য হাতের সাপোর্ট পাননি। মাথায় চোট পেয়েছিলেন। সেখান থেকে ব্রেনে ইন্টারনাল হেমারেজ হয়ে মৃত্যু। আশ্চর্য ব্যাপার হল, ঘটনাটা ঘটার তিনদিন আগে এক স্থানীয় সাধু আমাদের বাড়িতে খেতে এসেছিলেন। ঠাকুরদা ধার্মিক মানুষ ছিলেন, মাঝে মাঝেই সাধুসন্ন্যাসীদের ধরে এনে খাওয়াতেন। তো সেই সাধু খেতে বসে নাকি ঠাকুরদাকে বলেছিলেন, তিনদিন স্নান না করতে। স্নান করলে ভাগ্যে দুর্যোগ আছে। ঠাকুরদা শুধু ধার্মিকই ছিলেন না, শুচিবায়ুগ্রস্তও ছিলেন। ফলে স্নান না করলে তাঁর চলত না। তাই পুকুরে না গিয়ে তিনি ভোর-ভোর স্নান করতে যান বারোয়ারি কুয়োতলায়। তারপরে ওই ঘটনা। শ্রাদ্ধের দিন সাধু আবার এসে হাজির। তাঁর নোঙরা বসন দেখে আর মাথার জটায় উকুন-টুকুন থাকতে পারে ভেবে, ঠাকুমা আলাদা ঘরে বসিয়ে শ্রাদ্ধের ভোগ খাইয়েছিলেন। খেতে-খেতে বার বার তিনি বলছিলেন, ‘বার বার বারণ করলাম, তোরা শুনলি না? শুনলি না তোরা?’ খাওয়ার শেষে যাবার সময় ঠাকুমা তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। তিনি আশীর্বাদ করার বদলে বললেন, ‘সাবধান, এই ফাঁড়া তোদের বংশের সাথে রয়ে গেছে। এই ফাঁড়া থেকে তোদের নিস্তার নেই।’ জ্যোতিষী ডেকে তাবিজ-টাবিজ করিয়ে ঠাকুমা ফাঁড়া কাটানোর অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই সাধু মাঝে মাঝেই আসতেন। আর ফাঁড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে যেতেন। সেই কারণেই আমি এই সিনটা স্বাভাবিক ভাবে করতে পারছি না! কেন যেন মনে হচ্ছে, ঠাকুরদার মতো মাথায় চোট পেয়ে মারা যাব।’
বানিয়ে-বানিয়ে গল্পটা বলতে তার এতটুকু গলা কাঁপে না। একবারও থামে না, তোতলায় না, ঘটনাপ্রবাহ গুছিয়ে নেওয়ার জন্য থামে না। যেন প্রতিটি শব্দ সে বিশ্বাস করে, যেন প্রতিটা বাক্যের মধ্যে আর যাই থাক না থাক, মৌলিকতার অভাব নেই। মুখের অভিব্যক্তির সাথে ফাঁড়ার ভয় ও অযৌক্তিকতাকে আলাদা করা যায় না, হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অথচ প্রমোদকান্তির মুখে হালকা হাসির রেখা ফুটে ওঠে। তিনি সুমনের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলেন, ‘ভাই একটা কথা বলব?’
‘নিশ্চয়ই, বলুন।’
‘কিছু মনে করবেন না ভায়া, আমার মনে হয় কি জানেন, আপনার ঠাকুমা আর সন্ন্যাসীর মধ্যে ইয়ে… মানে এক্সট্রা-ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার ছিল।’
এরকম কথা যে কোনও ভদ্রলোক বলতে পারেন, তা সুমনের কল্পনার অতীত। এখন তার রেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু বানিয়ে বলা গল্প তাই রাগ অত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জাগছে না। বরং ঘটনার আকস্মিকতায় সে বেশ ঘেঁটে গেছে। তার মধ্যে যোগ হয়েছে প্রমোদকান্তির হাসি। ভদ্রলোককে কিছুক্ষণ আগেও সে ভেবেছিল অতিশয় গম্ভীর, আঁতেল গোছের মানুষ। এখন দেখা যাচ্ছে মুখোশের নীচে লোকটা এক নম্বরের ফক্কর! তা ফক্করের এত পারফেকশনিস্ট হবার কী দরকার? একটা গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়ার সিন নিয়ে এত ফ্যাকরা!
প্রমোদকান্তির হাসি দেখে সে একটু আশ্বস্ত হয়েছিল। ভেবেছিল, এবার হয়তো তিনি গুলি খাবার দৃশ্য থেকে বেরিয়ে সংলাপের দৃশ্যে আসবেন। কিন্তু ভদ্রলোকের হাঁটাচলা দেখে তো সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না। সুমনের সাথে একই দৃশ্যে যারা অভিনয় করবে, তারা কেউ এখনও আসেনি। আসবে কি না তাও সে জানে না। প্রমোদকান্তি চাতালের মধ্যে হাঁটছেন আর ফোনে কার সাথে কথা বলছেন। গলার স্বর মৃদু, সাবধানী। উত্তেজনার চিহ্ন নেই।
‘সুমন, আপনি আজকে বাড়ি যান। রাতে ফোন করে বলে দেব।’ মিনিট কুড়ি পর ফোন রেখে প্রমোদবাবু বললেন।
‘পরের ডেটটা…’
‘ফোনে। ফোনে কথা হবে। যান।’
সুমন বাইরে বেরিয়ে এল। মনটা ভাল নেই। তার ওপর কিছু একটা খচখচ করছে। মেসের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ে। এ-মাসেও সে মা’কে দেখতে যেতে পারেনি। যাবে কী করে? গত তিন মাস সে মামার হাতে এক পয়সাও দিতে পারেনি। নিজের বোন বলে আর কতদিন মামা থাকতে দেবে? এক বছর ধরে মামা ঘ্যানঘ্যান করছে। ঘ্যানঘ্যানানির মধ্যে অবশ্য যুক্তিও আছে। মামার বাড়িতে সে গোটা কৈশোর কাটিয়েছে। ইসমাইল কাকার সাথে সুমনের বাবা কাজ করতে গিয়েছিল ইরাকে। ইরাক থেকে টাকা আর খেজুর আসত তিন মাস অন্তর। শুরুর দিকে টাকার পরিমাণ নেহাত মন্দ ছিল না। তারপর লাগল যুদ্ধ। সেই সময় হা-পিত্যেশ করে খবরের জন্য বসে থাকত সবাই। সুমনও করত। যতখানি না দুশ্চিন্তায়, তার চেয়ে বেশি যুদ্ধের রোমাঞ্চে। সারাদিন ধরে টিভি খোলা থাকত বাড়িতে। ইংরেজি চ্যানেল, কেউ কিচ্ছু না বুঝলেও চলত। তারপর একদিন সন্ধেবেলা মুড়ি খেতে-খেতে মা হুট করে চ্যানেল পালটে দিল। মামিকে বলল, ‘ভাল লাগে না বাপু খালি-খালি এই যুদ্ধের কথা। বাংলা সিরিয়ালগুলো দেখে এবার একটু শরীর জুড়োই।’ মামা-মামি উল্লাসে সায় দিয়ে উঠল, যেন মড়ক-মহামারী পেরিয়ে অনেকদিন পর পার্বণ লেগেছে; কী আনন্দ, কী আনন্দ! সন্ধেগুলোতে সিরিয়াল ফিরল, কিন্তু সুমনের বাবা আর ফিরল না। টাকা আসাও বন্ধ হয়ে গেল।
মামা-মামির সাথে মায়ের কোনও বিবাদ ছিল না। মামার থেকে তো মামির সাথেই মায়ের বন্ধুত্ব বেশি ছিল। সারাদিনের গুজুর-গুজুর দেখে সত্যিই মনে হত দুই বোন। মামা ঠাট্টা করে বলত, ‘বাবা গো, দুই মেয়ে মিলে আমার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে সারাদিন। এদের একটা মরলে আমার হাড় জুড়ায়!’
গত বছর কালবৈশাখীর সময় পাশের মাঠে আম কুড়োতে গিয়ে মামি বজ্রপাতে মারা যায়। হাড় জুড়াল কি না বলা যায় না, তবে এক সপ্তাহ পর মামা অফিসে রেজিগনেশন দিয়ে চলে আসে। তার নাকি আর কাজে মন বসে না! তারপর একটা ঘরে মা, একটা ঘরে মামা ভূতের মতো থম মেরে বসে থাকে! সেবার কৃষ্ণনগরে একটা থিয়েটার করে ফিরলে মামা সুমনকে ডেকে বলল, ‘তোকে মানুষ করলাম, তুই এবার একটু রোজগার করে আমাদের দেখ! আমার আর কাজ কারবার করতে ভাল লাগছে না।’
সুমন থিয়েটার করত তখন। পরিচিতি হয়নি। মফস্সলের গ্রুপ, শোও পেত খুব কম। পয়সাকড়ি নেই। মামার কথা শুনে ভাবল সিনেমায় টাকা বেশি, চেষ্টা করে দেখা যাক। কয়েকদিন সোজা পথে চেষ্টা করে বুঝেছে ওভাবে এগোলে চিড়ে ভিজবে না। মানসম্মান বিসর্জন দিয়ে সে এবার প্রমোদকান্তির হাতে-পায়ে ধরেছিল। তাতে কাজ হয়েছে। স্ক্রিপ্টটাও ভাল। ‘থ্রিলার কিন্তু থ্রিলার নয়’ গোছের। অর্থাৎ দর্শকও টানব, আঁতলামিও করব টাইপ। কিন্তু এ কী? কোথায় প্রথম দিন ভাল একটা সিন করবে তা না, ক্যাপ ফাটানোর বন্দুকের শব্দ শুনে ‘স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে’ পড়ে যেতে হবে!
ইসমাইল কাকার সাথে সুমনের বাবা কাজ করতে গিয়েছিল ইরাকে। ইরাক থেকে টাকা আর খেজুর আসত তিন মাস অন্তর। শুরুর দিকে টাকার পরিমাণ নেহাত মন্দ ছিল না। তারপর লাগল যুদ্ধ। সেই সময় হা-পিত্যেশ করে খবরের জন্য বসে থাকত সবাই। সুমনও করত। যতখানি না দুশ্চিন্তায়, তার চেয়ে বেশি যুদ্ধের রোমাঞ্চে।
তবু সুমন হাল ছাড়ে না। বাড়ি এসে সে মাটিতে মোটা কম্বল বিছায়। তারপর পড়ে যাওয়ার দৃশ্য অভ্যাস করতে থাকে। হাজারবার মনকে বোঝানো সত্ত্বেও ভয়টাকে সে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তাছাড়া কনিষ্ঠ আঙুলটি অবুঝ বাচ্চার বায়নার মতো প্রবলভাবে নড়তে থাকে, যেন মাথা নাড়িয়ে বলতে চায়— না, না, না…
সেদিন রাতে প্রমোদকান্তি ফোন করলেন না। পরেরদিন সকালেও না। মনের মধ্যে টেনশন নিয়েই মামাবাড়ি চলে এল সুমন। উঠোনের বাইরে মামা সানগ্লাস পরে দাঁড়িয়ে আছে। রোদ খুব বেশি নেই। সানগ্লাস পরার দরকার হয় না। কিন্তু মামি মারা যাবার পর থেকে সানগ্লাস তার প্রিয় সঙ্গী। হয়তো চোখের কোনা যখন-তখন সজল হয়ে ওঠে বলেই…
সুমনকে দেখে মামা আরও গম্ভীর হয়ে গেল, ‘দু’মাস আসিসনি কেন?’
সুমন উত্তর না দিয়ে প্রণাম করে। মামা আশীর্বাদ করে বলে, ‘রোজগারপাতি হয়েছে কিছু?’
‘এখনও কিছু করে উঠতে পারিনি।’
‘তাই জন্যই আসিসনি দু’মাস? রোজগার না হলে বাড়ি আসবি না? এটা কোনও কথা হল?’
‘না মামা, একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম। একটা সিনেমায় চান্স পেয়েছি।’
‘বাহ। তাহলে তো রোজগার হচ্ছে। শোন, পরের মাসে টাকা না নিয়ে ঘরে ঢুকবি না, বুঝেছিস? যা, ভেতরে যা।’
সুমন বাড়ির ভেতরে ঢুকল। কোনও জানলা খোলা নেই, আধো অন্ধকার, পরিত্যক্ত বাড়ির মতো নিঃসাড়। আর স্যাৎসেঁতে। আর মেঝেভর্তি ধুলো। মায়ের ঘরে ঢুকল সুমন। মা বিছানার ওপর বসে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে।
‘মা! আলো জ্বালাওনি কেন?’
‘আলো জ্বালাস না, আলো জ্বালাস না।’
‘কেন? অন্ধকার হয়ে আছে তো!’
‘আজকাল আলো খুব চোখে লাগে। সূচের মতো ফোটে।’
‘কবে থেকে হচ্ছে বলো তো এটা?’
‘এই তো, মাস কয়েক ধরে। তোর খবর কি বাবা? ঠিকঠাক খাওয়া-দাওয়া করছিস?’
‘হ্যাঁ, একটা সিনেমায় অভিনয়ের কাজ পেয়েছি মা। সেটা নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি।’
‘ও বাবা! সিনেমায় পাট করবি তুই! পয়সাকড়ি দেবে ভাল?’
‘শুরুতেই কি আর ভাল হয় মা? কয়েকটা সিনেমা করার পর কদর বাড়ে, তখন টাকা বাড়ে। তাছাড়া এটা ছোট রোল। তবে ইমপর্টেন্ট।’
‘ও। মামার জন্য মিষ্টি এনেছিস?’
মিষ্টি আনা হয়নি। উচিত ছিল। এই পড়ন্ত সংসারে আরেকটু খুশির হাওয়া, আরেকটু উৎসবের ছোঁয়া দেওয়া উচিত ছিল তার। মা বুঝতে পারে, তড়িঘড়ি করে বলে, ‘আর মিষ্টি এনে কী হবে? তোর মামার সুগার। আমারও আর মিষ্টি মুখে রোচে না। মিষ্টি খেত কিছু তোর বাবা!’
‘আচ্ছা মা, বাবার যে ওই ব্যাপারটা ছিল না, ওই কান চুলকানো, ওটাতে ঠিক কীরকম হত বলো তো!’
‘কীরকম হত আমাকে কি খুলে বলেছে কখনও? মাঝে মাঝে কোনও কাজ করতে গিয়েও করত না। ফিরে আসত। বলত, কান চুলকাচ্ছে। আমি প্রথম-প্রথম বুঝতাম না। একদিন মা’কে, মানে তোর ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কী, মা তখন খুলে বলল। ওদের বংশে নাকি সবারই এটা থাকে!’
‘ঠাকুমার বাবারও ছিল?’
‘ছিল।’
‘তাঁর কী হত?’
‘হিসি পেত বার বার। হঠাৎ ঘন-ঘন হিসি পেলে বুঝতে হত বিপদ আসছে।’
‘তুমি এসব বিশ্বাস করো?’
‘ধুর! ওদের সামনে ভাবটা দেখাতাম যেন করি। আসলে তো এক রকমের মানসিক রোগ! আজকাল কত রকমের রেয়ার রোগের নাম দেখি কাগজে। এটাও হয়তো তেমনই। নিজের মনেই একটা ব্যাখ্যা বানিয়ে নিত। তারপর সেটাকে বিশ্বাস করে-করে তিল থেকে তাল করে তুলত। এর জন্য যে কত কাজ তোর বাবা করতে পারেনি! আমাদের অবস্থা কি এরকম হয় না কি নইলে? তোর বাবার যা ক্ষমতা ছিল, তুই ঘরে বসে খেতে পারতি। বানানো ভূতে ভয় পেয়ে সে জীবনটাই নষ্ট করল। তুইই বল না, ইরাকে যাবার আগে কেন তার কান চুলকাল না? বুঝতে পারল না যে, এই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া?’
‘যুদ্ধ তো লেগেছিল ইরাকে যাওয়ার দেড় বছর পর!’
‘তা হোক। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকলে তাও ধরা পড়ার কথা। আসলে ওসব ভুজুংভাজুং। সব মানসিক সমস্যা। আমার ভাগ্য ভাল যে, তোর মধ্যে ওসব বর্তায়নি।’
সুমন মুখ নীচু করে। কড়ে আঙুল কাঁপার কথা সে মা’কে জানায়নি কখনও। ক্লাস নাইনে পড়তে একদিন স্কুলে যাবার সময় কড়ে আঙুল কাঁপল। সে হাত মুঠো করে থাকল সারাক্ষণ, মুঠো খুললেই কেবল ওই একটা আঙুল থরথর করে কাঁপছে। দুপুরে পাশের স্কুলের সাথে ফুটবল ম্যাচ। গোটা স্কুল ভেঙে পড়েছে খেলা দেখতে, দু’তরফের চিৎকারে রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। এরকম একটা ম্যাচে খেলা পাঁচ মিনিট গড়াতে-না-গড়াতে একটা কড়া ট্যাকেলে হাত ভেঙে হাসপাতাল গেল সুমন। সেই শুরু। সেই থেকে তার বদ্ধমূল ধারণা যে, কড়ে আঙুল কাঁপা মানেই…
আসলে ব্যাপারটা হয়তো উলটো। মনের মধ্যে ভয় থাকলেই বরং কড়ে আঙুল কাঁপে। তাহলে একটা অন্ধবিশ্বাস চার-পুরুষ ধরে বটের শিকড়ের মতো ছড়াতে থাকল! ইশ! প্রমোদকান্তি তাহলে ঠিকই বলেছে। সে একটা ভিতুর ডিম।
‘তোকে একটা কথা বলা হয়নি বাবা।’
‘বলো মা।’
‘আমার দিন ফুরিয়ে এল।’
‘এসব কি বলছ? তোমারও কি কান চুলকাচ্ছে না কি?’ সুমন ঠাট্টা করার চেষ্টা করে।
‘তোকে বলা হয়নি বাবু। আমার ক্যানসার হয়েছে রে!’
ঠাস করে চড় খেল যেন সুমন। মায়ের মুখে অর্ধেক হাসি অর্ধেক অন্ধকার; ক্যানসার স্নানভেজা চুল থেকে জলের মতো ঝরছে। নদী হয়ে বইছে। সেই নদী এসে মিশছে অনুশোচনার সমুদ্রে। সুমন সমুদ্রের মধ্যে একক ডুবুরি হয়ে সাঁতরে চলে, মার্বেলের গুলির মতো ভারী নিঃশ্বাসের বুদবুদ ওঠে আর প্রকাণ্ড হাঙরের মতো সে পাশ দিয়ে যেতে দেখে মৃত্যুকে। তিনমাস সে মা’কে দেখতে আসেনি। এই তিনমাসে এমন পরিবর্তন হয়ে যাবে সে কি ভাবতে পেরেছিল? এই ধুলোময় অন্ধকার ঘর আসলে মায়ের শরীর। প্রাণ নেই, শুধু হাড়ের কাঠোমাটা ঠান্ডা বাতাসে ঠক ঠক করে কাঁপছে।
বেশিক্ষণ বসে না সুমন। সে যখন বাড়ি ফিরছিল, তখন কয়েক ফোঁটা জল চোখের কোণ থেকে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। হাতের চেটো দিয়ে জল মুছে সুমন ভাবল, এবার একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। প্রমোদকান্তিকে ফোন করে জানাতে হবে যে, সিনটা সে করতে পারবে। নিখুঁত, একদম স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। আর না, কনিষ্ঠ আঙুলকে প্রশ্রয়ের দিন শেষ। শৌখিনতার দিন শেষ। এবার সে যেমন-তেমন পার্টও নিয়ে নেবে। শিল্পের জন্য নয়, রোজগারের জন্য অভিনয়টা করবে এবার থেকে। কিন্তু এই ভাবনাগুলি চাউমিনের এক-একটা লম্বা সুতোর মতো পরস্পর জট পাকিয়ে পড়ে রইল। সুমন কাঁটা চামচে জড়িয়ে যখন মাথার মধ্যে তাদের গোল করে ঘোরাচ্ছিল, তখনই ফোনটা বেজে ওঠে। প্রমোদকান্তি ফোন করেছেন।
‘হ্যালো প্রমোদবাবু, বলুন।’
‘একটা খারাপ খবর আছে সুমন।’
‘কী খবর?’
‘সোজাসুজিই বলি, আপনার অভিনয়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। ফলে আপনাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। তার জায়গায় আরেকজনকে ঢোকানো হল। আই অ্যাম সরি। ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা রইল।’
ফোন কেটে পকেটে ঢোকানোর আগেই সুমন অজ্ঞান হয়ে বাসের সিট থেকে গড়িয়ে পড়ল।
কনিষ্ঠ আঙুলকে প্রশ্রয়ের দিন শেষ। শৌখিনতার দিন শেষ। এবার সে যেমন-তেমন পার্টও নিয়ে নেবে। শিল্পের জন্য নয়, রোজগারের জন্য অভিনয়টা করবে এবার থেকে। কিন্তু এই ভাবনাগুলি চাউমিনের এক-একটা লম্বা সুতোর মতো পরস্পর জট পাকিয়ে পড়ে রইল। সুমন কাঁটা চামচে জড়িয়ে যখন মাথার মধ্যে তাদের গোল করে ঘোরাচ্ছিল, তখনই ফোনটা বেজে ওঠে।
বাসের মধ্যে অজ্ঞান না হয়ে ঘরে অজ্ঞান হলে হয়তো অস্বস্তি একটু কম হত, কিন্তু মানুষের সাহায্য ও আন্তরিকতা কিছুই পাওয়া যেত না। ঘরের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে তাই ভাবছিল সুমন। জনাদশেক লোক তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়া উপেক্ষা করে, বাস থামিয়ে, তার চোখে-মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরাল; তারপর গরজ করে ঠিক স্টপেজে শুধু নামিয়েই দিল না, বাসস্টপের ধারে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ছোলা খেতে থাকা বুনোপাগলার হাতে কুড়ি টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বলল, ‘তুই একটু বাবুর সাথে মিত্রপাড়া অবধি যা তো। বাবুর শরীর খারাপ হলে রিক্সা ডেকে হাসপাতালে নিয়ে যাবি।’
বুনোপাগলার বয়স বেশি নয়। হবে সুমনের চেয়ে বছর সাতেক বড়। ভাল ফুটবল খেলত বলে পাড়ার সবাই একডাকে চেনে। পড়াশুনাতেও কিন্তু মন্দ ছিল না। সুমনের বাড়িওয়ালার ছেলে অন্তুই বুনোপাগলার কাছে টিউশন পড়েছে এক সময়। তখনও বুনোপাগলা স্কুলের ছাত্র, সবাই তাকে বুনো বলে ডাকত। ‘বুনো’ তার ডাকনাম না কি গায়ে রোমের বাহুল্যের কারণে প্রাপ্ত, তা অন্তুও বলতে পারেনি। তবে সে যখন টিউশন পড়েছে, তখনও পাগলামির কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। সেটা শুরু হয় তারও বছর দেড় বাদে। বাঁকুড়ার কোনও কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে সে পাগল হয়ে ফেরে। যখন প্রথম জানা যায়, গোটা এলাকায় হইহই পড়ে গিয়েছিল। সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে নাকি জানলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ত! বলাবলি করত, কপালের দোষ বেচারার। ভাগ্যে না থাকলে এমন কারও হয়? এসবই অন্তুর কাছে শোনা। কেউ-কেউ বলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের র্যাগিং সহ্য করতে না পেরে সে পাগল হয়ে গেছে। কেউ বলে নারীঘটিত ব্যাপার। বুনোপাগলা নিজে আর কিছু বলে না। সে যেন কথা বলতে ভুলে গেছে। আপনমনে ঘুরে বেড়ায় আর হাসে।
আজ সে একটা কাজ পেয়ে খুব খুশি। উত্তেজিত হয়ে সুমনের হাত চেপে ধরেছে। প্রথম কিছুক্ষণ হাত ছাড়াবার চেষ্টা করেছিল সুমন। কিন্তু তাতে বুনোপাগলা সাঁড়াশির মতো কব্জিখানা এমন চেপেছে যে, সে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠেছিল।
হাঁটতে-হাঁটতে সুমন বলল, ‘বুনোপাগলা, তুমি কি দুঃখ পেয়ে পাগল হয়েছিলে?’
বুনোপাগলা উত্তর দেয় না, হাসে।
‘আমারও খুব দুঃখ জানো তো, আমিও পাগল হয়ে যাব।’
বুনোপাগলা আরও এক প্রস্থ খিলখিলিয়ে হাসে।
‘তুমি সবসময় হাসো কেন বুনোপাগলা? তোমার কান্না পায় না?’
বুনোপাগলা জোরে-জোরে ওপর-নীচ মাথা নাড়ায় আর হাসে।
সুমন অবাক হয়ে দেখে, বুনোপাগলা তার বাসা চেনে। ঠিক বাসার সামনে এসে হাত ছেড়ে দিল। গেট খুলে ঢোকার মুখে সুমন এক মুহূর্ত থামল। তার কি কিছু একটা দেওয়া উচিত? খাবার বা টাকা? বাসের লোকেরা যদিও কুড়ি টাকা দিয়ে দিয়েছে… এই সময়ই অন্তু বেরিয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে। খুব মাঞ্জা মেরেছে। শ্বশুরবাড়ি যাবে হয়তো! অন্তুর বউ দু’মাস হল কনসিভ করেছে। এখন কোন্নগরে আছে, বাপের বাড়ি। অন্তু নির্ঘাত বউয়ের কাছেই যাচ্ছিল, হঠাৎ গেটের সামনে বুনোপাগলাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।
বুনোপাগলা অন্তুর দিকে তাকিয়ে হাসছে। ছোটবেলার মাস্টারমশাই। হোক না প্রাইভেট টিউশন, তবু তো স্যার বলে ডাকত এক সময়! এখন কি তাহলে…
‘এই যা যা, যা এখান থেকে।’ অন্তু বুনোপাগলাকে গেটের সামনে থেকে তাড়িয়ে দেয়, তারপর সুমনের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘গেট খুলে রাখিস না, মালটা ঢুকে পড়বে।’
সুমন আর বুনোপাগলার দিকে তাকাতে পারে না। মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকে আসে। কিন্তু দশ ফুট বাই বারো ফুটের ড্রয়িংরুম, প্লাস্টিকের চেয়ার, প্লাস্টিকের টেবিল, দেওয়ালের পাশে জড়ো করা প্লাস্টিকের বোতল, একদিকে কাত হওয়া বুড়ো ফ্যান, পুরু ওষ্ঠের মতো দেওয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা একচিলতে শেল্ফ, তার মধ্যে তারা মায়ের জিভ বের করা মুখ— এসবের কিছুই সে চিনতে পারে না। এ যেন অন্য কারো বাড়ি। যেন কিছু ধরার আগে, চেয়ারে বসার আগে, জুতো খুলে ঘরে ঢুকে পড়ার আগে গৃহস্থের অনুমতি প্রয়োজন। সুমন চোখটা-মুখটা ভালো করে ঘষে, চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে ডলে-ডলে ঘষে, সারা গা চুলকায়… বুনোপাগলা তার হাত ধরে কি পাগলামো ঢুকিয়ে দিল না কি? সুমন কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? নইলে তার সারা গায়ে এমন অসম্ভব অস্বস্তি হচ্ছে কেন? ভাবনাগুলো আঁকাবাঁকা সড়কপথে না চলে হঠাৎ খাদের গা বেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে কেন? সে কি আবার অজ্ঞান হয়ে যাবে? শরীরে প্রবল অস্বস্তি নিয়ে সুমন অনুভব করে, তার কড়ে আঙুল কাঁপতে শুরু করেছে। সে কি বিপদে পড়েছে আবার? মরে যাচ্ছে? মায়ের আগেই কি সে মরে যাবে?
সুমন আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ল।
অজ্ঞান হয়ে বোধহয় পড়ে ছিল কয়েক ঘণ্টা। মুখের মধ্যে জলের ছিটে পড়তে জ্ঞান ফিরল। সুমন চোখ মেলে দেখল, বুনোপাগলা হাসছে। বড় মিষ্টি হাসি। বড় উষ্ণ আর সুন্দর।
সুমন চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে দেখল বুনোপাগলা এখনও বসে আছে। সুমনকে দেখে হাতের আঙুলগুলো জড়ো করে মুখের কাছে এনে দেখাল তার খিদে পেয়েছে। খিদে কি সুমনেরই কম পেয়েছে? কিন্তু তাও খেতে ইচ্ছে করছে না। সে পকেট থেকে কুড়ি টাকা বার করে বাড়িয়ে দেয়। বুনোপাগলা নেয় না, জোরে-জোরে দু’হাত দিয়ে মাটিতে চাপড় মারে। তারপর আবার মুখের কাছে হাত তুলে দেখায়।
সুমন রান্নাঘরে ঢুকে এসে দুজনের পরিমাণমতো চাল নিয়ে বসিয়ে দিল। সঙ্গে মুসুর ডাল আর বেগুনভাজা। রান্না করতে-করতে সে বার বার করে দেখতে লাগল কনে আঙুলটাকে। কী নিরীহ ভালমানুষের মতো বসে আছে! লাস্ট বেঞ্চে বসে থাকা গোবেচারা ছেলেটার মতো; পড়া করে আসেনি বলে সারাক্ষণ বুকে ভয় নিয়ে চুপ হয়ে আছে। হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই বুড়ো আঙুল। তারপর তর্জনী আর মধ্যমা। কড়ে আঙুলটাই বরং সবচেয়ে কম ব্যবহৃত হয়। বাদ গেলেও কোনও অসুবিধা হয় না।
ভাত আর ডাল হয়ে গেছে। তেল গরম করতে বসিয়ে চপার দিয়ে তাড়াতাড়ি কয়েকটা বেগুন কেটে ফালি করে নেয়। সাথে সাথে কতগুলো নতুন চিন্তা ভাজা হতে থাকে মাথার মধ্যে। মা-ই কি তাহলে ঠিক? এই কড়ে আঙুলের জন্যই কি সে, তার বাবা, তার ঠাকুমা বার বার হেরে গেছে, পিছিয়ে গেছে? গোটা শরীরের ভয় এসে জমেছে কড়ে আঙুলের মধ্যে। তখন এই অকর্মর্ণ্য আঙুলটাই হয়ে উঠেছে পথের কাঁটা। এখন পিঠ ঠেকে গেছে সুমনের। পথের কাঁটা ঠিক সময়ে সরিয়ে ফেলতে না পারলে…
ইশ, বেগুনভাজাগুলো পুড়ে গেল খানিকটা। সুমন একটা থালায় অনেকটা ভাত, বেগুনভাজা আর বাটিতে করে অর্ধেকটা ডাল নিয়ে এসে দেখল বুনোপাগলা মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।
‘বুনোপাগলা, ও বুনোপাগলা!’
বুনোপাগলা উঠে বসে অল্প হাসে। ভাতের থালার দিকে জুলজুল করে তাকায়। সুমন ভাতের থালাটাকে কিছুটা দূরে রেখে বলে, ‘ভাত খাবে বুনোপাগলা?’
বুনোপাগলা মাথা নাড়িয়ে জানায়, হ্যাঁ।
‘তাহলে একটা কাজ করে দিতে হবে যে!’ সুমন কড়ে আঙুলটাকে মেঝেতে রেখে বাকি আঙুলগুলো গুটিয়ে নেয়। তারপর চপারটা এগিয়ে দেয় বুনোপাগলার দিকে। ‘কাটো’।
বুনোপাগলা প্রথমে বুঝতে পারে না। সুমন ঈঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে তার হাসি থেমে যায়। ভয়ের চোখে সুমনকে দেখে।
‘কাটো বুনোপাগলা, কাটো। তুমি ভাত খাবে না? গরম ভাত, ডাল আর বেগুনভাজা। তোমার খিদে পেয়েছে না?’
বুনোপাগলা একবার ভাতের দিকে দেখে একবার আঙুলের দিকে। তার মুখের চিরকালীন হাসি উধাও হয়ে গেছে। তার বদলে নেমে এসেছে দ্বন্দ্ব, নেমে এসেছে কষ্ট, নেমে এসেছে চিৎকার। আর স্মৃতি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের র্যাগিং-এর স্মৃতি। তার বুকের পাঁজর হাপরের মতো ওঠে আর নামে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বের হয়। তারপর হঠাৎ চপার তার মাথার ওপর ওঠে। সুমন চিৎকার করে ওঠে। বন্যার জলের মতো হু হু করে রক্ত বেরিয়ে মেঝেটাকে যেন ভাসিয়ে দিতে চায়।
অসহ্য যন্ত্রণা নিয়েও ভাল করে দেখতে চায়, এ কি শুধুই রক্ত? না কি আরও কিছু? তিরিশ বছর ধরে জমিয়ে রাখা ভয়? দুয়েরই রং বোধহয় লাল। সে আলাদা করতে পারে না।
শেল্ফ থেকে ফার্স্ট-এইড বক্সটা বার করে বুনোপাগলাই তুলো নিয়ে আসে। আর ডেটল। কিন্তু প্রায় এক বান্ডিল তুলো শেষ হয়ে যায়, রক্ত থামে না। সুমন মনে-মনে ভাবে, এত ভয়? এত ভয় জমে ছিল তার শরীরে?
ঠিক এই সময়েই ফোন বেজে ওঠে। স্ক্রিনে প্রমোদকান্তির নাম। অন্য কেউ হলে হয়তো সে ফোন ধরত না, কিন্তু প্রমোদকান্তির ফোন সে ধরে ভয়টাকে পরীক্ষা করার জন্য। দাঁত দিয়ে যন্ত্রণা চেপে ধরে বলে, ‘হ্যাঁ প্রমোদবাবু, কী ব্যাপার?’
‘একটু কনফিডেনশিয়াল কথা ছিল আপনার সাথে।’
‘বলুন।’
‘আপনি ওই সিনেমাটায় অভিনয় করতে এখনও রাজি আছেন? ওই সিনটা করতে হবে না। ওটা আমরা ইনডিরেক্টলি নেব।’
‘কিন্তু অন্য একজন করছে বললেন?’
‘অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে। সিনটা করতে গিয়ে ওর মাথায় চোট লাগে। তারপর ইন্টারনাল হ্যামারেজ হয়। আমরা হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এক্সপায়ার করে গেল। ওই অনেকটা… আপনার দাদুর যেমন হয়েছিল।’
‘ও!’
‘আপনাকে আমরা একটা মোটা টাকা অফার করব সুমন। আপনি যে আমাকে ব্যাপারটা নিয়ে সাবধান করেছিলেন, সেটা কাউকে বলবেন না প্লিজ। পার্টটা আপনিই করবেন। কনফার্মড।’
‘আচ্ছা।’
সুমন ফোন রেখে দিয়ে কাটা আঙুলটার দিকে তাকায়। লাস্ট বেঞ্চে বসা ছেলেটাকে হেড মাস্টার এবার ক্লাসের বাইরে বার করে দিয়েছেন। পড়া না করে আসা কোনও দুর্বল ছাত্র এখন আর ক্লাসে নেই। সুমন নিজের হাতের দিকে তাকায়। তারপর ধরা গলায় ডাকে, ‘বুনোপাগলা!’
রক্তের ওপর বসেই কী অনায়াসে বেগুনভাজা চটকে ভাত খাচ্ছে বুনোপাগলা! সুমনের ডাক শুনে মুখ তুলে হাসে। বড় মিষ্টি সেই হাসি। বড় উষ্ণ। শুধু কি উষ্ণ? না কি একটু পরিহাসের ছিটেও তার সাথে মিশে আছে?
ছবি এঁকেছেন চিরঞ্জিৎ সামন্ত
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook