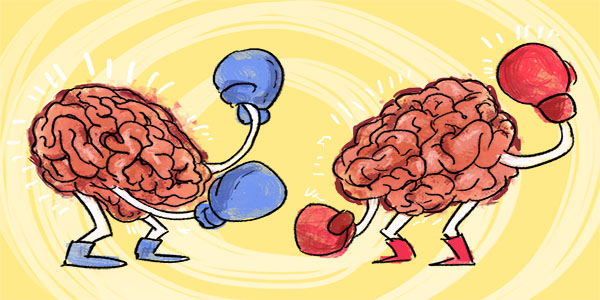১.
চিন্তা ও বুদ্ধিচর্চার জগতে যাঁরা বাস করেন তাঁরা একটা অদ্ভুত দ্বৈত জীবন যাপন করেন। তার একটা দিক হল তন্ময় নির্জনতা – পড়াশোনা করা, নিজের ভাবনাচিন্তা আর সৃজনশীল অভিব্যক্তির (তা সে যে আকারই নিক না কেন – শিল্প, সাহিত্য, বা গবেষণা) বিবর্তনের নির্জন পথ ধরে একাকী পথচলা। আবার অন্যদিক হল সামাজিক যূথচারীতার – যেখানে নিজস্ব বিষয় ও তার সাথে সম্পর্কিত অন্য নানা বিষয় নিয়ে যাঁরা আগ্রহী বা সহপথচারী তাঁদের সাথে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নানা মঞ্চে মতের আদানপ্রদান – যার মধ্যে বক্তৃতা, আলোচনাসভা, আবার নিছক আড্ডা সবই আছে। অর্থাৎ, একই সাথে তীব্রভাবে একক আবার আবশ্যকভাবে সামাজিক দুই বৃত্তের মধ্যে সর্বদা আমাদের যাতায়াত।
এই যে সামাজিক বৃত্ত সেখানে মতের আদানপ্রদান অনেকভাবে হয়। এখন প্রশ্ন হল, আড্ডা আর আলোচনা, আলোচনা আর বিতর্ক, বিতর্ক আর ঝগড়া এদের মধ্যে সীমারেখাগুলো কী? বক্তৃতা বা আলোচনাসভা বা বিতর্কসভার নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক আঙ্গিক এবং বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের পূর্বনির্ধারিত ভূমিকা থাকে। তার মানে যে সবসময় তা মানা হয় তা নয় (ভাবুন পরশুরামের ‘বদন চৌধুরীর শোকসভা’ গল্পটির কথা) — কিন্তু তাহলেও ধারণাগুলো নিয়ে অন্তত একটা স্পষ্টতা আছে। আড্ডা-আলোচনা-বিতর্ক-ঝগড়া এদের কোন ধরাবাঁধা আঙ্গিক নেই, খানিকটা অনানুষ্ঠানিক বা আটপৌরেভাবে হওয়াটাই চল। তাই একটা থেকে আরেকটায় খুব সহজেই চলে যাওয়া যায়। আর কিছু ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে আর আসলে যা হচ্ছে সেদুটো আলাদা হতে পারে – আপনি ভাবছেন আড্ডা বা আলোচনা হচ্ছে কিন্তু তলায় তলায় বিতর্কের একটা চোরাস্রোত বইছে এটা হতেই পারে।
আড্ডার মূলে যদি থাকে একটা খেয়ালখুশি ব্যাপার – তার আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু একেবারেই ধরাবাঁধা ছাঁচের বাইরে – আলোচনার লক্ষ্য কিন্তু খানিকটা নির্দিষ্ট। প্রত্যাশা থাকে কোনো বিষয়ের পরিধির মধ্যে তার প্রবাহ বইবে এবং কথাবার্তা তার বাইরে চলে গেলে তাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করা হবে।
আড্ডার মূল উদ্দেশ্য বিনোদন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতের আদানপ্রদান। এর মধ্যে একটা নিতান্ত সামাজিক দিক আছে – আড্ডা থেকে কিছু শিখি না শিখি বা অন্য কোন উদ্দেশ্যসাধন হোক না হোক (যেমন, কারোর সাথে আলাপ হওয়া বা কারো বাড়িতে ভালো চা বা চানাচুর খাওয়ার লোভ) – মানুষ স্বভাবত যূথচারী আর তাই তার ধমনীতে বইছে সহমর্মীদের সাথে বেঁধে বেঁধে থাকার অমোঘ আকর্ষণ ।
আড্ডার মূলে যদি থাকে একটা খেয়ালখুশি ব্যাপার – তার আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু একেবারেই ধরাবাঁধা ছাঁচের বাইরে – আলোচনার লক্ষ্য কিন্তু খানিকটা নির্দিষ্ট। প্রত্যাশা থাকে কোনো বিষয়ের পরিধির মধ্যে তার প্রবাহ বইবে এবং কথাবার্তা তার বাইরে চলে গেলে তাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করা হবে। আলোচনার মূল উদ্দেশ্য জানা, সে কোনো বিষয় নিয়ে বা কারোর মতামত নিয়ে হোক। বিতর্কের গোড়ার কথা হল একটা নির্দিষ্ট মতপার্থক্য আছে, এবার যুক্তি-তথ্য, ব্যক্তিগত পছন্দ বা রুচি, অথবা কোন মতাদর্শ বা নীতির (সে নৈতিক হোক বা নান্দনিক) নিরিখে নিজেদের অবস্থানগুলো প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা – সে যার সাথে বিতর্ক তার কাছেই হোক, বা অন্য কেউ যদি উপস্থিত থাকেন, তাদের কাছে। বিতর্কে অধিকাংশ সময়েই হারজিতের নিষ্পত্তি করা যায়না কিন্তু মতভেদের কারণ খানিকটা পরিষ্কার হয়। আর ভালো বিতর্কের একটা ফল হল ভিন্ন মতের স্বপক্ষে যুক্তি এবং তথ্যগুলো জানলে নিজের বক্তব্য আরো জোরালো করার সুযোগ পাওয়া যায়। আর ঝগড়া, অর্থাৎ উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় যার ফলে মতান্তর থেকে মনান্তর শুধু নয়, মনোমালিন্য হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল? ঝগড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করা। যতক্ষণ না কারো দম বা গলার জোর বা সৌজন্যবোধে টান পড়ছে —বা, অন্য কেউ পরিস্থিতি সামলাবার এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে হস্তক্ষেপ না করছেন — তরজা চলতেই থাকে, কারণ থামা মানেই হারস্বীকার।
আগেই বলেছি, আড্ডা, আলোচনা, বিতর্ক, আর ঝগড়ার মধ্যে সম্পর্ক কোনও সরল জ্যামিতির নিয়মে বাঁধা থাকেনা, কথাবার্তার ধরন একটা থেকে আরেকটায় গড়িয়ে যেতে পারে অনায়াসে – ঠিক যেমন উষ্ণতার ফারাকে একই জিনিস বরফ, জল ও বাষ্পের রূপ নিতে পারে।
সংঘাত সর্বদাই ক্ষতিকারক, তাই সংঘাতের সম্ভাবনা থাকলে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। জেনেবুঝে ঝগড়া করার কোনও অর্থ হয় না। যদি জানি কারোর সাথে মতের গভীর অমিল, তাহলে তার সাথে আলোচনা – এবং বাধ্য হলে সংশ্রব— এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। রুচি বা মতাদর্শ নিয়ে মৌলিক পার্থক্য থাকলে, সেখানে তর্ক করার খুব একটা অর্থ হয় না। বুদ্ধদেব বসু ১৯৪০ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, যে খাওয়া-পরা, আমোদ-প্রমোদের রুচিবৈষম্যে খুব একটা কিছু এসে যায় না – এই সব ক্ষেত্রে মতান্তর থেকে বিতর্কের বা মনান্তরের সম্ভাবনা কম।১ কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে রুচি বা মতাদর্শগত বৈষম্য এত মৌলিক যে সেখানে বিরোধ এবং মনান্তর অবধারিত আর তাই এসব ক্ষেত্রে পরস্পরকে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। তাঁর একটি উদাহরণ হল সাহিত্যের জগত থেকে। তাঁর কাছে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কেউ না হলে, তাঁর সাথে আলোচনার অর্থ নেই, “কেননা রবীন্দ্রনাথকে যিনি অবজ্ঞা করেন, তিনি আমার অস্তিত্বসুদ্ধু অস্বীকার করেন, যেহেতু রবীন্দ্রনাথের ভিত্তির উপরেই আমি দাঁড়িয়ে আছি।’’ আবার আমরা রাজনৈতিক মতাদর্শের জগৎ থেকে যদি উদাহরণ নিই, তাহলে কোন রাজনৈতিক নেতাকে কেউ যদি মহান বলে মানেন আর কেউ ভাবেন স্বেচ্ছাচারী একনায়ক, সমাজের কোন অংশের প্রতি কেউ যদি বৈষম্যমূলক ভাব পোষণ করেন (যেমন, ধর্মের ভিত্তিতে) আর কেউ মনে করেন আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো আপোষ করা যায় না, সেখানে খুব বেশি আলোচনার জায়গা নেই। দুই ভূখণ্ডের মধ্যে কোনও সেতু বা যানপরিবহনের ব্যবস্থা না থাকলে যেমন যাতায়াত অসম্ভব, সেরকম মৌলিক মতভেদ থাকলে তা নিয়ে বিতর্কের কোনও সমাধান নেই। তাই, রুচি আর মতাদর্শ নিয়ে মৌলিক পার্থক্য থাকলে, সেখানে তর্ক করার খুব একটা অর্থ হয় না। আলোচনা হলে শুধু তিক্ততাই হয়।২
যে মতভেদের কোনো মিলনবিন্দু নেই, তা নিয়ে বিতর্ক লেগে যাবার একটা কারণ হতে পারে, একে অন্যের মতামত সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত না থাকা এবং কথাপ্রসঙ্গে মতভেদগুলো উন্মোচিত হওয়া। কিন্তু মৌলিক কিছু বিষয়ে বন্ধুদের মতামত সম্পর্কে একেবারে অবহিত না থাকার সম্ভাবনা কম। তবে সময়ের সাথে মানুষের ধ্যানধারণা পাল্টাতে পারে এবং সেটা হলে বন্ধুদের মধ্যেও অপ্রীতিকর মতভেদ এবং বন্ধুবিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে
কিন্তু তার মানে আরো অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপারের মতো যা করা উচিত বা উচিত না, আর যা হয় সেদুটো সবসময় এক হবে এমন আশা করা যায়না। বন্ধুদের মধ্যেও সবসময় উত্তপ্ত বিতর্ক কী এড়ানো যায়? যে মতভেদের কোনো মিলনবিন্দু নেই, তা নিয়ে বিতর্ক লেগে যাবার একটা কারণ হতে পারে, একে অন্যের মতামত সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত না থাকা এবং কথাপ্রসঙ্গে মতভেদগুলো উন্মোচিত হওয়া। কিন্তু মৌলিক কিছু বিষয়ে বন্ধুদের মতামত সম্পর্কে একেবারে অবহিত না থাকার সম্ভাবনা কম। তবে সময়ের সাথে মানুষের ধ্যানধারণা পাল্টাতে পারে এবং সেটা হলে বন্ধুদের মধ্যেও অপ্রীতিকর মতভেদ এবং বন্ধুবিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে ।
তবে সব তর্ক রুচি বা মতাদর্শ নিয়ে নয়। কিছু উঠে আসে কোনও কিছু সম্পর্কে আলাদা ব্যাখ্যা থেকে। তথ্য বা প্রমাণ যেহেতু সচরাচর সীমিতই হয় – সে সাংস্কৃতিক জগতে হোক বা রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয় হোক, এমনকি ক্রীড়াজগৎ — তাই কে ঠিক সেটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় না। এক্ষেত্রে আলোচনা বা বিতর্ক কিন্তু বিভিন্ন মতামতের পেছনে যুক্তি ও তথ্য উদ্ঘাটনে একটা বড় ভূমিকা নিতে পারে। বিদ্যাচর্চা বা গবেষণার জগতে এরকম বিতর্ক সবসময়েই চলে—এর উদ্দেশ্য আমাদের যুক্তি বা তথ্যের যেগুলো দুর্বলতা সেগুলো বুঝে তাদের আরও জোরদার করা। সেখানে বিতর্কের শেষে সবাই একমত হবেন আশা করা যায় না, কিন্তু পরস্পরের অবস্থান নিয়ে ধারণাটা খানিক পরিষ্কার হওয়ার কথা। আসলে সবাই একমত হওয়া সম্ভব শুধু নয়, কাঙ্ক্ষিতও নয়। আমাদের নিজেদের চিন্তাভাবনার বিবর্তন, জীবনের অভিজ্ঞতা এইসব মিশে যে মতামত তৈরি হয়, তা শুধু আমাদের কাছে মূল্যবান নয়, অন্যদের কাছেও তার মূল্য আছে। সেই জন্যেই আমরা নানা বই পড়ি, নানা লোকের বক্তব্য শুনি। তার উদ্দেশ্য শুধু আমাদের নিজস্ব জগৎদর্শনের স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করা না, বিপুল এবং বিচিত্র এই জগৎসংসারে নানা বিষয় নিয়ে আমরা কতটা জানি, কতটা জানি না, এবং কতটা জানা সম্ভব তার এক মানসিক মানচিত্র তৈরি করা। বেড়াতে গিয়ে কোনও জায়গা ভালো লাগলে সেখানে বসবাস শুরু করতে হবে তা যেমন নয়, সেরকম বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হওয়া মানেই সেগুলো সার্বিকভাবে গ্রহণ করার কোন আবশ্যকতা নেই। বরং, মতভেদ স্বাস্থ্যকর কারণ সবাই সবার সাথে সব কিছু নিয়ে একমত হলে আর কথাবার্তার কোনো বিষয় থাকবে না যে!
কিন্তু সবাই কি এই বহুমতের বহুত্ববাদে বিশ্বাস করেন? বা তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বাস করলেও নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করেন? বিবাদে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা আমাদের সবার মধ্যে আছে, যদিও আমরা জানি যে কাউকে প্রভাবিত করা বা কারো মত পরিবর্তন করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে আক্রমণ করাটা কখনোই কার্যকর হয় না। এ কি মানুষের এক আদিম হিংস্র সত্তার প্রতিফলন যাতে উপলব্ধি ও জ্ঞানের আলোর স্বচ্ছতার বদলে আগ্রাসনের উত্তাপ আমাদের অন্ধ করে দেয়, যখন “মারের জবাব মার” হয়ে ওঠে বাকযুদ্ধের মূলমন্ত্র ?
অনেক সময় আমরা এ ধরনের সংঘাত এড়িয়ে উঠতে পারি না। এখন প্রশ্ন হল, যে সামাজিক আদানপ্রদানে সমৃদ্ধ হবার এবং একমত না হয়ে বহুমতের বহুত্ব উদযাপন করার অবাধ সম্ভাবনা, সেখানে কোন মনোভাব থেকে আমরা মেতে উঠি শব্দের রণযুদ্ধে, যতই থাকনা তার বৌদ্ধিক বা নান্দনিক ধার?
মতান্তর যখন মনান্তরে পরিণত হয়, তার ফলে চিরতরে বন্ধুবিচ্ছেদ অবধি হতে পারে। কখনোই তা কাম্য নয়, কারণ কারো সাথে যদি বন্ধুত্ব থাকে তার মানে তার সাথে অনেক বিষয়ে মতের ও মনের মিল আছে বলেই সে বন্ধু। আগে না জানা থাকলে আর তর্কের ফলে এই ফাটলরেখাগুলো উন্মোচিত হলে, এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ায় ভালো – যাকে বলে হয় “দ্বিমত হওয়া নিয়ে একমত হওয়া” (agreeing to disagree)।
কিন্তু তা সত্ত্বেও, অনেক সময় আমরা এধরনের সংঘাত এড়িয়ে উঠতে পারি না। এখন প্রশ্ন হল, যে সামাজিক আদানপ্রদানে সমৃদ্ধ হবার এবং একমত না হয়ে বহুমতের বহুত্ব উদযাপন করার অবাধ সম্ভাবনা, সেখানে কোন মনোভাব থেকে আমরা মেতে উঠি শব্দের রণযুদ্ধে, যতই থাকনা তার বৌদ্ধিক বা নান্দনিক ধার? বিতর্কে শেষ কথা বলার লোভে, কোন বর্বর জয়ের উল্লাসের আশায় আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কে আঘাত হানি?
আমাদের সবার মধ্যে একটা অপরিণামদর্শী দিক আছে যার থেকে মুহূর্তের তাড়নায় আমরা অনেক কিছু করে ফেলি — বেশি কথা বলি, বেশি খাই, বেশি সময় নষ্ট করি – আর তারপর মনে হয় না করলেই হত। তাই সমস্যাটা কি আত্মসংযমের, যার অবধারিত ফল হল পরে পস্তানো ?
নাকি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে দলাদলির বা গোষ্ঠীতন্ত্রতার প্রবণতা ? সব বক্তব্যকেই আমরা অতিসরলীকৃত কিছু শ্রেণিতে যতক্ষণ না ঠেসে ঢোকাতে পারছি, আরাম নেই – সে বাম বা ডান, প্রতিষ্ঠানপন্থী বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী যাই হোক না কেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে যা হারিয়ে যায় তা হল ব্যক্তিমতামতের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এবং তার সাথে সমষ্টিগতভাবে মতামতের বহুত্ববাদের সম্ভাবনাটাই ।
নাকি এর জন্যে আসলে দায়ী আমাদের যূথচারীতা তলায় তলায় সদাপ্রবহমান অহমিকার চোরাস্রোত? আমি-ই ঠিক, বাকি-রা ভুল; আমি-ই সৎ, বাকি-রা মতলবি; আমি-ই আদর্শনিষ্ঠ, বাকিরা আদর্শভ্রষ্ট; আমি-ই বিদ্বান, বাকিরা অজ্ঞ; আমি-ই বুদ্ধিমান, বাকিরা নির্বোধ। এদিকে মানুষ তো স্বভাবগতভাবে আশ্রয়ভিখারি। তাহলে কী এক আত্মঘাতী অহংবোধে তাড়িত হয়ে, এ ‘আমি’-র সুতীক্ষ্ণ তরবারিতে ছিন্ন করে ফেলে সম্পর্কের আশ্রয়জাল, যার অবধারিত ফল হল একাকিত্ববোধ?
চিন্তা ও বুদ্ধিচর্চার জগতের দুই আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী দিকের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম – সংক্ষেপে যাকে আমাদের তন্ময় ও বাঙ্ময় দিক বলা যেতে পারে। এই দুটি দিক আসলে সম্পূরক হলেও, অনেক সময়েই আমাদের নিজস্ব কিছু প্রবণতার জন্যে এদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব এসে যায়, যাতে হয় আমাদের একাকীত্ববোধ আরো গভীর হয়ে বিচ্ছিন্নতাবোধে পরিণত হয়, নয়তো যৌথজীবনের মঞ্চগুলো কন্টকাকীর্ণ হতে থাকে, যা অস্বস্তি, আঘাত এবং মলিনতার জন্ম দেয়।
এই দ্বন্দ্বের থেকে কি মুক্তির কোন পথ আছে?
২.
যেকোনো কথোপকথনের একটা অংশ হল শোনা, অন্যটা হল বলা। অথচ ভালো করে শোনার ক্ষমতা খুব অল্প লোকেরই আছে। ১৯৩৫ সালে একটি লেখায় আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তরুণ লেখকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন: “যখন কেউ কথা বলবে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কী বলতে যাচ্ছ ভাববেনা। অধিকাংশ লোক কখনো শোনে না।” ৩
শোনা মানে শুধু চুপ করে অন্যকে কথা বলতে দেওয়া না – যা সৌজন্যবোধ থেকেও আসতে পারে। শোনা মানে অন্যকে কথা বলতে দিয়ে তারপর নিজের মতামত সজোরে ঘোষণা করা নয়। ভালোভাবে শোনা মানে কেউ কী বলছে এবং কেন বলছে সেটা বুঝতে চেষ্টা করা, এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার বক্তব্যকে বুঝতে চেষ্টা করা। তার মানে তার সাথে একমত হওয়া নয়, বরং নিবিড় কৌতূহলে তার চিন্তাধারা বুঝতে চেষ্টা করা।
মন দিয়ে শোনার প্রধান সুফল হল, এতে বক্তার আস্থা অর্জন করা যায়। যিনি বলছেন তিনি যত গভীরে গিয়ে এবং বিশদে তাঁর বক্তব্য বলবেন, এই মতামত কেন একজন পোষণ করেন সেটা অনেক ভালো বোঝা যায় এবং বিষয়টি নিয়ে আমাদের বোঝার গভীরতা বাড়ে। বোঝা মানেই একমত হওয়া নয় – অন্যপক্ষের মতের আলোয় আমরা নিজেদের মতকে আরো ভালো করে যাচাই করতে পারি, এবং তার স্বপক্ষে যুক্তি আরো ভালো করে শানিয়ে নিতে পারি।
এখন একথা ঠিক যে সবার সব কথা শুনলে সব সময় যে নতুন উপলব্ধি হয় তা না, কিন্তু শোনার ধৈর্যটুকু না থাকলে যে যে ক্ষেত্রে বুঝলে লাভ হত সেই সুযোগগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়। আরেকভাবেও দেখা যায় —উত্তপ্ত বিতর্ক থেকেও তো কিছু শেখা যায়না, বরং তাতে মনোমালিন্য হলে তার ভার আমাদের বহন করতে হয়। তার থেকে মন দিয়ে শোনার অভ্যেস করা অনেক শ্রেয়।
ফিরে আসি বিতর্কের কথায়।
একটা উদাহরণ দিই। কার কবিতা ভালো লাগে এই আলোচনায় একবার কবি শঙ্খ ঘোষের সাথে একটি আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা আমার অহেতুকরকম দুর্বোধ্য লাগে এবং অভিধান নিয়ে না বসলে পড়াই যায় না এই মর্মে কিছু বলেছিলাম। এটি একটি পরিচিত অভিযোগ। উনি একমত হলেন যে কিছু কবিতায় এমন শব্দের ব্যবহার আছে, যেগুলো পরিচিত নয় এবং অনভ্যস্ত পাঠক হোঁচট খেতেই পারেন। কিন্তু তার সাথে উনি কিছু কবিতার উদাহরণ দিলেন যাতে মানতেই হয় ওঁর অনেক কবিতাই আছে যেগুলো কিন্তু অত খটোমটো নয়। শুধু তাই নয়, সেই কবিতাগুলো নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বুঝতে পারলাম বিদগ্ধ একজন পাঠকের কেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কিছু কবিতা ভালো লাগে।
আমরা নিজেরাও যেমন বদলে যাই, সেরকম বাইরের পৃথিবীও নিত্য পরবিবর্তনশীল আর তাই কোন বিতর্কেই আমি যা ভাবছি সেটা সম্পূর্ণ নির্ভুল এটা ভাবার অর্থ হয় না। কিন্তু যেহেতু কল্পবিজ্ঞানের সময়যান আয়ত্তে নেই, বিভিন্ন সময়ের “আমি”-র সাথে কথোপকথন অসম্ভব। তাই অন্যদের সাথে আড্ডা-আলোচনা এবং বিতর্ক ছাড়া আমাদের চিন্তার বিবর্তন হতে পারে না, আমরা বাঁধাধরা চিন্তার একটা রুদ্ধদুয়ার কক্ষে আটকা পড়ে যেতে বাধ্য।
এই উদাহরণ থেকে যেটা শেখার সেটা হল, উনি মন দিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আমার কথা না শুনলে, কী বলছি, কেন বলছি বোঝার চেষ্টা না করে “তুমি বোঝোনা” বা “আমি বলছি, শোন” বলে উড়িয়ে দিলে ওঁর মতো বিদগ্ধ একজনের কাছে আমি কবিতা নিয়ে আমার মতামতই প্রকাশ করতাম না। শুধু তাই না, উনি আমার কথা উড়িয়ে না দিয়ে যেভাবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সেটা তাঁর বৈদগ্ধের জোর দিয়ে নয়, আমাকে ব্যাপারটা নিজেই আরো ভালো করে ভেবে দেখার দিশা দিয়ে। আর আমি যেটা শিখলাম যে, বিদগ্ধ একজন পাঠকের কেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কিছু কবিতা ভালো লাগে – যেমন, তাঁর কবিতায় ছন্দের প্রয়োগ — তার একটা আভাস পেলাম। এতে আমার প্রাথমিক পছন্দ-অপছন্দ না পাল্টালেও, কবিতার রসাস্বাদন করার ক্ষমতা সমৃদ্ধ হল। উৎকর্ষ ও ভালো লাগার তো অনেকগুলো মাত্রা থাকে এবং ব্যক্তিবিশেষে সেগুলোর গুরুত্ব আলাদা হতেই পারে, তাই আলোচনা করলে যে মাত্রা গুলো নিয়ে আমরা অতটা সচেতন নই, সেইগুলো সম্পর্কে আমাদের চেতনা সমৃদ্ধ হয়।
জীবনচক্রের অমোঘ আবর্তনে কিছু কিছু ধ্যানধারণা, ভালো লাগা পাল্টে যেতে বাধ্য। আগের “আমি”-রা আর পরের “আমি” সবাই যদি একজায়গায় জড়ো হতাম – খানিক পরশুরামের ‘ভুশণ্ডীর মাঠে’-র মতো – তাহলে হয়তো প্রবল বিতর্ক লেগে যেতো! আমরা নিজেরাও যেমন বদলে যাই, সেরকম বাইরের পৃথিবীও নিত্য পরবিবর্তনশীল আর তাই কোন বিতর্কেই আমি যা ভাবছি সেটা সম্পূর্ণ নির্ভুল এটা ভাবার অর্থ হয় না। কিন্তু যেহেতু কল্পবিজ্ঞানের সময়যান আয়ত্তে নেই, বিভিন্ন সময়ের “আমি”-র সাথে কথোপকথন অসম্ভব। তাই অন্যদের সাথে আড্ডা-আলোচনা এবং বিতর্ক ছাড়া আমাদের চিন্তার বিবর্তন হতে পারে না, আমরা বাঁধাধরা চিন্তার একটা রুদ্ধদুয়ার কক্ষে আটকা পড়ে যেতে বাধ্য।
আর সেটা খেয়াল না রাখলে এবং আরেকজন কেন কোনো কথা বলছে সেটা না ভাবলে অবধারিত ফল হল দুই কঠিন বস্তুর পরস্পরের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগার মতো। সেখানে কে ছিটকে পড়ল আর কে দাঁড়িয়ে থাকল, সেটাই মূল বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমার জিৎ মানে তোমার হার, আর তোমার জিৎ মানে আমার হার – এক শূন্য অংকের খেলা ।
এর বিকল্প আছে।
প্রথমত, আমরা যদি বিতর্ককে যুদ্ধ বা প্রতিযোগিতা না ভেবে অভিযান বা অন্বেষণ ভাবি, যেখানে কোনো কিছুর গভীরে গিয়ে বোঝাটাই মূল উদ্দেশ্য, তখন যাদের সাথে আলোচনা বা তর্ক হচ্ছে তারা আর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সহপর্যটক হয়ে ওঠে। সেই প্রক্রিয়ায় পরস্পরের মতবিনিময় ছাপিয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়ায় আমাদের নিজস্ব চিন্তার বিবর্তন।
দ্বিতীয়ত, আমাদের নিজস্ব ভাবনাচিন্তার বিকাশের যে প্রক্রিয়া তা অন্তঃসলিলা নদীর মতো আমাদের চেতনার মধ্যে দিয়ে সর্বদা বহমান। এই প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রাখার অর্থ হল, যে বিষয় নিয়ে মতভেদ, সেটার তক্ষুনি একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে, এরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের যৌথ কৌতূহল এবং অনুরাগকে মূলধন করে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা সময়সীমা ছাড়াই চলতে পারে এই কথোপকথন। অনেকসময় দেখা যায় পরে আমাদের মত কাছাকাছিই শুধু আসতে পারে তা না — কিছুক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান পাল্টেও যেতে পারে। তাই প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত না করে বরং তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন, কিছু সংশয় জাগিয়ে দিলে তা তাঁর মতপরিবর্তনের সম্ভাবনা অনেক বেশি বাড়িয়ে দিতে পারে। মনে আছে, কলেজজীবনে আমার উগ্র-বামপন্থী চিন্তাধারায় গণতান্ত্রিক অধিকার বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এগুলো খানিক বুদ্ধিজীবীদের বিলাসিতা মনে হতো। এই অধিকারগুলো যে কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর স্বত্ত্বাধিকার (entitlement) নয়, এদের শিকড় যে আরো অনেক গভীর এবং সেখানে গলদ থাকলে গোটা ব্যবস্থাটাই নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে, সেটা তখন যাঁরা বলেছিলেন সবসময় একমত হতে পারিনি। কিন্তু বলাই বাহুল্য, ১৯৮৯ সালের আগে হওয়া সেই সব আলোচনায় কে ঠিক ছিলেন তা নিয়ে আজ দ্বিমত হবার অবকাশ খুব কম।
এই প্রক্রিয়া নিয়ে আরো তলিয়ে ভাবলে ফিরে আসতে হয় সেই “আমি”-র ধারণায়। শঙ্খ ঘোষ তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে লিখছেন : “আমার তো মনে হয়, সমস্ত শিল্পই এই নিজেকে জানার শিল্প। কেননা, এক হিসেবে, নিজেকে জানার সম্পূর্ণতাই সকলকে জানার পাথেয়।” ৪ এখানে শিল্প শুধু নয়, আরো বৃহত্তর অর্থে সমস্ত বৌদ্ধিক চর্চার ক্ষেত্রেও এই যুক্তি প্রযোজ্য। আর এই যুক্তি মানলে, বিতর্কে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অনন্ত সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে তুচ্ছ বালির প্রাসাদের দখল নিয়ে যুদ্ধ করার মতই অসার। প্রসারিত অর্থে আমাদের জ্ঞানান্বেষণের যাত্রাপথও বালিতে পদচিহ্ন রাখতে রাখতে হাঁটার মতো। তার অনেকটাই একক যাত্রা, অনেকটা অন্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ, আর খানিকটা একসাথে কিছুটা পথচলা। পদচিহ্ন ধুয়ে যেতে পারে, পরস্পরের সাথে মিশে যেতে পারে, কিন্ত পথচলা অনন্ত।
———————————-
* অম্লান দত্ত সম্পাদিত শঙ্খ ঘোষকে নিবেদিত নগ্ন অক্ষরের গায়ে (পরম্পরা, ২০২২) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত “অসংখ্য শঙ্খ” প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত সংস্করণ।
পাদটীকা:
১. “মতান্তর ও মনান্তর” (উত্তরতিরিশ , নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৫)।
২. এই বিতর্ক বিষয়ে আমার “তর্কে বহুদূর” (অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা, ২০১৯) প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা আছে।
৩. Ernest Hemingway, “Monologue to the Maestro – A High Seas Letter”, Esquire, October, 1935.
৪. শঙ্খ ঘোষ, “মর্ত্য কাছে স্বর্গ যা চায়”, এ আমির আবরণ, ১৯৮০।
ছবি এঁকেছেন: অনুষ্টুপ সেন