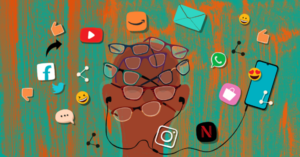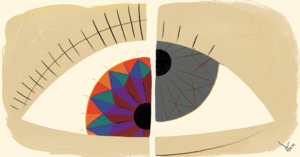তরুণ মজুমদার চলে যাওয়ার দিন রাতে খেতে-খেতে আমার মা ‘পলাতক’ ছবিটার কথা বলছিল। ১৯৬৩ সালে বানানো ছবি। যাত্রিকের পরিচালনায়। ফলত তার কৃতিত্ব শুধুমাত্র তরুণবাবুকে দেওয়া সম্ভবত উচিত নয়। কিন্তু ছবির চিত্রনাট্যটি তরুণ মজুমদারের লেখা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দেখলাম তিনি বলেছেন, উত্তরবঙ্গে তাঁদের মেটেলির বাড়িতে লন্ঠনের আলোয় তিনি ‘পলাতক’-এর চিত্রনাট্য লেখেন। অতএব ধরে নিতেই পারি এই ছবিটির কল্পনাজগৎটি মূলত তারই। সম্ভবত আমার মা কলেজে পড়াকালীন সেই ছবিটি দেখেছিল। ছবিটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মা’র চোখমুখ চকচক করছিল। বহুদিন আগের সেই অভিজ্ঞতার রেশ যে এখনও অমলিন রয়ে গেছে সেটা টের পাচ্ছিলাম। আমার ‘পলাতক’ দেখা ছোটবেলায়, দূরদর্শনে। তার স্মৃতি খুব একটা স্পষ্ট নয়। সেই অভিজ্ঞতা যাচাই করার তাগিদে ছবিটি সম্প্রতি আবার দেখলাম।
‘পলাতক’ একটি অদ্ভুত বাণিজ্যিক ছবি। শুরু হয় এই বাক্য দিয়ে: ‘একটি অবাস্তব অতিনাটকীয় কাহিনী।’ এইরকম একটা ঘোষণা দিয়ে একটি বাণিজ্যিক ছবি শুরু করার মধ্যে স্পষ্টতই এক ধরনের অভিপ্রায় লুকিয়ে থাকে। সেই অভিপ্রায়ের লক্ষণগুলি বুঝতে গিয়ে মিশ্র অভিজ্ঞতা হল।

‘বাণিজ্যিক’ শব্দটি সচেতনভাবেই ব্যবহার করলাম। ছবিটির গান, সংলাপ ও অভিনয়ের ভঙ্গি প্রায় পুরোটাই দর্শক-অভিমুখী। এক ধরনের আটপৌরে ফ্যামিলিয়ারিটি ছবিটির ছত্রে-ছত্রে সচেতনভাবে বুনে দেওয়া হয়েছে। সেই পরিচয়ের স্বাদ দর্শককে আহ্বান করে। তাতে গুরুগম্ভীর গভীরতার কোনো ছদ্ম-চিহ্ন নেই। সেখানে অসিতবরন, ভারতী দেবী, জহর রায়, জহর গাঙ্গুলি, রবি ঘোষ, অনুভা গুপ্ত, রুমা গুহ ঠাকুরতা, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি এবং অবশ্যই অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায় অধ্যুষিত যে সময়-চিহ্নহীন গ্রামবাংলা, তা একটা অতি-পরিচিত চালচিত্রের মতো। এই পরিচয় তৈরি হয় মূলত সংলাপ ও অভিনয়ের ভঙ্গিতে। যেমন জহর রায় কিংবা জহর গাঙ্গুলি তাঁদের স্ব-স্ব চরিত্রের বাইরেও তাঁদের নিজস্ব ম্যানারিজম নিয়ে সেই সময়কার বাংলা বাণিজ্যিক ছবির একটি অতি-পরিচিত জগতের মধ্যে খুব সহজে দর্শকদের টেনে নিয়ে যেতে পারেন। এই সুবিধার ব্যবহার সচেতন এবং নিশ্চিতভাবে বাণিজ্যিক। এই অভিনয়-ভঙ্গির আরাম ২০২২ সালে বসে কল্পনা করা আমাদের পক্ষে একটু দুষ্কর। আমরা দূরবিন দিয়ে এই অভিনয় দেখি এবং অবশ্যই আমাদের পরিবর্তিত রুচির নিরিখে এগুলি এখন অনেকটাই অতিনাটকীয় লাগে। প্রত্যেকটা চরিত্র এক-একটি টাইপ, এবং সেই টাইপগুলি একেবারেই বাণিজ্যিক থিয়েটার ও সিনেমার ভঙ্গিতে মাত্র কয়েকটা আঁচড়ে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয় মাত্র। সেখানে স্তরায়ন বা লেয়ারিং এক ধরনের বোকা বিলাসিতা। প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র ভাল। সবাই সবাইকে ঘিরে বেঁধে থাকে, সবাই যেন এক মায়াময় জগতের অলস বাসিন্দা। যেটুকু খলতা প্রকাশ পায় তাও প্রায় কমেডির ধার ঘেঁষে। তাকে বড়জোর দুষ্টামি বলা যায়। অন্ধকারের কোনও চিহ্ন তাতে নেই।
অবশ্যই এটা কাল্পনিক জগৎ। দেশভাগ-পরবর্তী ছিন্নমূলদের স্রোতে আক্রান্ত, খাদ্য-সংকট ও রাজনৈতিক হিংসায় জর্জরিত বাংলায় এই জগৎটি শুধুমাত্র মানুষের কল্পনায় থেকে গেছে। কিন্তু কল্পনাটি কাল্পনিক নয়। এই টাইমলেস, মিঠে, সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকার গ্রাম— মানুষের কল্পনায় তখনও বৈধ। তাতে প্রবেশ করতে গেলে রিয়ালিজমের ধুয়ো ধরতে হয় না। তরুণ মজুমদার সেখানে অনায়াসে হেঁটে বেড়ান। এবং তাতে প্রবেশ করতে তাঁর এন্ট্রি-পাস হল গান। সেই গানের ব্যবহারবিধি যাত্রার মতো। তা সংলাপের ঠিক মাঝখান থেকে অতর্কিতে শুরু হয়ে যায়। তা লোকসংগীতের মতো, কিন্তু ঠিক লোকসংগীত নয়। তাতে আধুনিক সংগীতায়োজন থাকে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাগরিক কণ্ঠ থাকে, যেগুলিকে সম্ভবত সচেতন সাঁকো হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যা ওই রূঢ় কঠিন বর্তমানের সঙ্গে ওই কল্পনার জগতের এক অলক্ষ্য যোগ অবচেতনে তৈরি করে। এগুলি সচেতন বাণিজ্যিক জনপ্রিয় ছবির নির্মাণকল্প।

এই পরিচিত জগতের আবেগগুলোও অত্যন্ত পরিচিত। মা, ভাই, সন্তান, বন্ধু, আত্মীয়, পড়শি— এদের প্রত্যেকটি আবেগের প্রোটোটাইপ খুব স্পষ্ট। এখনকার হিসেবে সম্ভবত একটু মোটা দাগের। কিন্তু এই ফ্যাব্রিকটি খুব কাজের। কাউকে কিছু বলে দিতে হয় না। সবাই নিশ্চিন্তে এই চেনা জগতের মায়ার কোলে মাথা রাখতে পারে।
কিন্তু এই অতি-পরিচিত সামূহিক কল্পনার চালচিত্রে পরিচালক যে মূল গল্পটি বলেন, সেটি এই চালচিত্রের ঠিক বিপ্রতীপে অবস্থিত। ছবিটি অনুমান করি সবাই দেখেছেন, তাই তার গল্পের পুনরাবৃত্তি করছি না। কিন্তু আংটি চাটুজ্জের ভাই, বসন্ত চাটুজ্জে (অনুপকুমার) ছবিতে মিষ্টি হেসে, গান গেয়ে, কখনও রেগে কখনও হেসে, কখনও নিতান্ত ভাঁড়ামো করে যে-কাণ্ডটি করেন, সেটি আদপে বড় মায়াবী রকমের নিষ্ঠুর। তা এই চালচিত্র ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। মানুষের গভীর শোক ও মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই নিষ্ঠুরতা প্রায় প্রাকৃতিক। তাতে এক ধরনের আত্মবিধ্বংসী নৈর্ব্যক্তিকতা আছে, যা মানুষ প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তার হিসাব বুঝে উঠতে না পেরে বিহ্বল হয়ে যায়। বসন্ত চাটুজ্জে (বসন্ত নামটা নেহাত কাকতালীয় বলে এখানে ভাবতে অসুবিধা হয়) আসে এবং যায়। সে ভালবেসে আঁকড়ে ধরে, এবং অন্য কেউ ভালবাসতে শুরু করলেই বিনা নোটিশে পালিয়ে যায়। নির্দয় ভাবে পালায়। এবং এই নির্দয়তা পরিশেষে তাকেও রেহাই দেয় না। সে প্রকৃতির মতোই নির্লিপ্ত ও মায়াময় এবং এই দ্বন্দ্বই তাকে শেষে ধ্বংস করে।
এই মায়া, স্থিতি ও ধ্বংসের সহাবস্থান সেই সময়কার বাঙালি দর্শকের অবচেতনে জ্বলজ্বল করছে। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের সময় শস্য-শ্যামলা প্রকৃতির মধ্যে কঙ্কালসার মানুষের লাশ বাঙালি সদ্য দেখে এসেছে। তাকে প্রায় চুপিসারে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও তরুণ মজুমদার দু’হাত ধরে সেই দ্বন্দ্বটির মাঝখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন। আর তাঁদের সঙ্গত করে বংশী চন্দ্রগুপ্তের আর্ট ডিরেকশন ও সৌম্যেন্দু রায়ের চিত্রগ্রহণ। সত্যজিৎ রায়ের হাত দিয়ে তৈরি হওয়া রিয়ালিজমের যে নতুন ঘরানা বাংলা ছবিতে তৈরি হয়েছে, তাকে এই জনপ্রিয় কল্পনার পরিসরে এক দ্বান্দ্বিক অবকাশে পরিচালক জড়িয়ে নেন। সেটা কাকতালীয় ধরাটা অনুচিত। এই সহাবস্থানই সম্ভবত এই ছবির মূল উদ্দেশ্য।

এত কিছু তরুণবাবু সচেতনভাবে করেছিলেন কি না, জানি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রকল্প সচেতনভাবে করলে তাতে যে চেষ্টার অতি-কষ্টের চিহ্ন থাকে, তা এই ছবিতে নেই। এই পরিচালক সম্ভবত তাঁর দর্শকদের মতোই এই জগৎটি অচেতনে বয়ে বেড়াতেন। এবং দর্শকদের পাশে বসে সেই গল্পটি শোনাতে শোনাতে তিনি এবং তাঁর দর্শকমণ্ডলী একত্রে এই অজানার পাড়ে গিয়ে বসেন।
সম্ভবত সেই কারণেই প্রায় ৫০ বছর পরেও আমার মায়ের স্মৃতিতে এই ছবিটি বিচরণ করতে থাকে। সাম্প্রতিক বাংলা বাণিজ্যিক ছবি নিয়ে আমাদের যে সামূহিক হা-হুতাশ, তার সমাধানের কোনো একটা গোপন চিরকুট এই ছবির মধ্যে হয়তো লুকিয়ে আছে। আমাদের পরিচালকেরা আর লণ্ঠনের আলোয় চিত্রনাট্য লেখেন না। তাতে অবশ্য অনাবশ্যক নস্টালজিয়ায় ভোগার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু লণ্ঠনের আলো-আঁধারি যে অবচেতন জগতের সাঁকোটি তৈরি করে, সেই সাঁকোটি আমরা বহু অহংকার ও অযত্নে ধ্বংস করে ফেলেছি।
সেই ট্র্যাজেডি সম্ভবত বসন্ত চাটুজ্জের আত্মধ্বংসের চেয়েও করুণ।