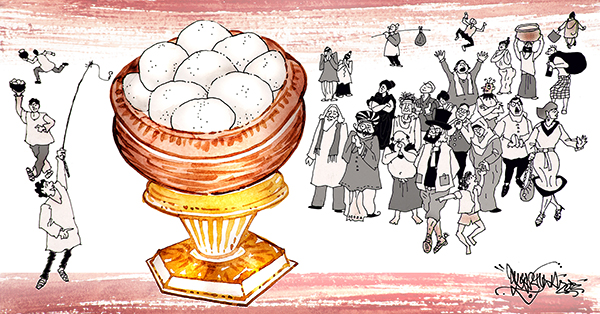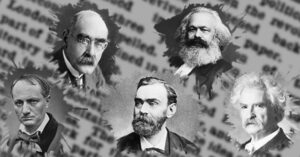মিষ্টান্ন মিতরে জনা: দ্বিতীয় পর্ব
আগের কিস্তিতেই বলেছি যে, শুধু রসগোল্লার ইতিহাস নিয়েই পূর্ণাঙ্গ গবেষণা-গ্রন্থরচনা সম্ভব। বস্তুত সে-ইতিহাসের সঙ্গে কলকাতার আইডেনটিটির ওতপ্রোতকরণ এক সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব হলেও রসগোল্লার আদি জন্মভূমি নিয়ে গ্রাম-শহরের ছাড়াও একাধিক জেলা ও একাধিক রাজ্যের পুরনো ঝগড়া রয়েছে। আমাদের খাদ্যরীতির প্রথম ইতিহাসবিদ কে টি আচাইয়ার মতে সতেরো শতকে হুগলি জেলা নিবাসী পর্তুগিজরাই ছানার সঙ্গে মিষ্টি মিশিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, ছানাকে চিনির রসে ডোবানোর পবিত্র কর্তব্যটির প্রথম সম্পাদনও তাঁদের হাতেই। তবে বাঙালির ইতিহাসের এই ক্রান্তিকারী মুহূর্তটি সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাসবিদরা একমত নন। তাঁদের অনেকেই মনে করেন যে, রসগোল্লার জন্মমুহূর্তটি শহর কলকাতার ‘বাবু’-সংস্কৃতিরই এক নির্ভুল মাইলফলক। ‘বাংলার খাবার’ নামে একটি অসামান্য নাতিদীর্ঘ গ্রন্থের প্রণেতা প্রণব রায়ের মতে বাগবাজারের নবীনচন্দ্র দাশের হাতে ১৮৬৮ সালে স্পঞ্জ রসগোল্লা সৃষ্টির বছর দুয়েক আগেই বেনিয়াটোলার সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের দীনু ময়রার পূর্বপুরুষ ব্রজ ময়রা হাইকোর্টের কাছাকাছি এক দোকানে রসগোল্লা আবিষ্কার করেন। অন্যদিকে, ওই বইটিতেই রসগোল্লার উপর নদিয়া জেলার দাবির এক বর্ণনা পাওয়া যায় বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণী থেকে, যেখানে সাহিত্যিক পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ‘রসগোল্লার প্রত্নতত্ত্ব’ সম্পর্কে দাবি করেন যে, মধ্য-উনিশ শতকের কোনও একদিন কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামের হারাধন ময়রা ক্রন্দনরত শিশুকন্যাকে ভোলানোর জন্য রসে ছানা ডুবিয়ে খেলাচ্ছলেই বানিয়ে ফেলেন এক ‘উৎকৃষ্ট সামগ্রী’, তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাণাঘাটের জমিদার পালচৌধুরীরা সেই সৃষ্টির নাম দেন রসগোল্লা। আবার সম্প্রতি বাংলাদেশের খাদ্য-গবেষক শওকত ওসমান এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন যে, বরিশালের পটুয়াখালি বা পিরোজপুর অঞ্চলের হিন্দু ময়রারাই রসগোল্লার আদি নির্মাতা। অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে, এই বিতর্ক আসলে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যেরই রকমফেরতা, যার মাধ্যমে জমে ওঠে রসগোল্লার একান্ত বাঙালিয়ানার উপর এক স্থানিক অভিজ্ঞান দেগে দেবার চেষ্টা। বুদ্ধিমানের পক্ষে এই জন্ম-বিতর্কে কোনও বিশেষ পক্ষ অবলম্বন না করাই শ্রেয়, তাই সারা দুনিয়ার ডেজার্টের এক বিশ্ব-ইতিহাসের (Sweet Invention: A History of Dessert, ২০১১) প্রণেতা মার্কিন খাদ্য-ইতিহাসবিদ মাইকেল ক্রন্ডল সে-পথে হাঁটেননি। শুনলে অবাক হবেন যে, কে টি আচাইয়া যেমন তাঁর A Historical Dictionary of Indian Food গ্রন্থে সারা ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলার মিষ্টিকেই স্থান দিয়েছিলেন, ২০১৫ সালে প্রকাশিত মিষ্টান্ন-মহাকোষগ্রন্থ The Oxford Companion to Sugar and Sweets-এও ঠাঁই পেয়েছে রসগোল্লা, কিন্তু জন্ম-বিতর্ক সেখানেও অমীমাংসিত।
এই বাগধারায় ওড়িশাবাসীদেরও এক বিপ্রতীপ, প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বর অধুনা সংযোজিত হয়েছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের উপর একাধিক বইয়ের লেখক জগবন্ধু পাধির মতে তিনশো বছরেরও বেশি আগে রসগোল্লা বানান ওড়িয়া ময়রারা, বছরওয়াড়ি রথযাত্রায় ঠাঁই না মেলায় রুষ্ট লক্ষ্মীদেবীকে তুষ্ট করার জন্য। এই মত যে নিছক কলিঙ্গকপোলকল্পিত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় তা নয়, কারণ দ্বাদশ শতকের দক্ষিণ ভারতে কন্নড় চালুক্য বংশের রাজা তৃতীয় সোমেশ্বরের লেখা সংস্কৃত কোষগ্রন্থ ‘মানসোল্লাস’-এ খানিক বাঙালি পান্তুয়ার স্টাইলে ছানার গোলককে ভেজে চিনির রসে ডোবানোর কথা আছে। দক্ষিণ ভারত থেকে সেই ঘরানা আগে ওড়িশায় পৌঁছবে, ‘ক্ষীরমোহন’ নামে সেখানে প্রতিষ্ঠা পাবে, আর উনিশ শতকে সেখান থেকে তীর্থভ্রমণ সেরে ঘরফেরতা বাঙালিরা— অথবা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কারণে হৃতসর্বস্ব বাংলায় পরিযায়ী ওড়িয়া শ্রমিকরা— সম্ভব করবেন সেই রসসুধামঞ্জরীর ‘টেকনোলজি ট্রান্সফার’, এমনটা নিতান্ত অসম্ভব নয়, যদি অবশ্য পুজো ও প্রসাদের উপচারে ছানার মিষ্টির ব্যবহারে ওড়িশাবাসীদের কোনও আপত্তি না থেকে থাকে। এইসব ধোঁয়াশার জন্যই বাংলা-ওড়িশার এই রসসিঞ্চিত বিতর্ক আপাতত অমীমাংসিত বলেই ধরতে হবে, কারণ বিপুলা এই পৃথিবীতে দুই রসগোল্লা-ঐতিহ্যেরই জায়গা রয়েছে, আর সেই দুই ঐতিহ্যই এখন জিআই ট্যাগের অস্ত্রে বলীয়ান।
পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের উপর একাধিক বইয়ের লেখক জগবন্ধু পাধির মতে তিনশো বছরেরও বেশি আগে রসগোল্লা বানান ওড়িয়া ময়রারা, বছরওয়াড়ি রথযাত্রায় ঠাঁই না মেলায় রুষ্ট লক্ষ্মীদেবীকে তুষ্ট করার জন্য। এই মত যে নিছক কলিঙ্গকপোলকল্পিত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় তা নয়, কারণ দ্বাদশ শতকের দক্ষিণ ভারতে কন্নড় চালুক্য বংশের রাজা তৃতীয় সোমেশ্বরের লেখা সংস্কৃত কোষগ্রন্থ ‘মানসোল্লাস’-এ খানিক বাঙালি পান্তুয়ার স্টাইলে ছানার গোলককে ভেজে চিনির রসে ডোবানোর কথা আছে।
রসগোল্লার জন্মের স্থান-কাল-পাত্র বিষয়ক তর্কে অহেতুক সময় নষ্ট না করেও মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, কলকাতার এই মিষ্টিকে জাতে তোলেন হুগলির ময়রা ‘রসগোল্লার কলম্বাস’ নবীনচন্দ্র দাস, যিনি সম্পর্কে ছিলেন রসিক কবিয়াল ও ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি’ খ্যাত ভোলা ময়রা, অর্থাৎ ভোলানাথ মোদকের নাতজামাই। ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় পাড়ি দিয়ে ১৮৬৬ সালে বাগবাজারে একটি দোকান খুলে টুকটাক মিঠাই বিক্রিবাটা করতেন তিনি, বছর দুয়েক বাদে একদিন থোড়বড়িখাড়া থেকে খদ্দেরদের রেহাই দেওয়ার জন্য বানিয়ে ফেলেন বাংলার নবজাগরণের গৌরবময় ইতিহাসে তাঁর অতুল অবদান ‘স্পঞ্জ রসগোল্লা’, আর তাই খেয়ে চমৎকৃত হয়ে যান সে-আমলের ধনাঢ্য মাড়োয়াড়ি ব্যবসায়ী ভগবান দাস বাগলা আর তাঁর কিশোর পুত্র। সীমাহীন হর্ষ আর কয়েক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে পিতাপুত্র সেদিন বাড়ি ফেরার পর নবীনচন্দ্রকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। তাঁর সুযোগ্য পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র আর পৌত্র সারদাচরণ দ্রুত এই এই ক্ষুদ্র দোকানটিকে আস্তে-আস্তে এক পরিব্যাপ্ত উদ্যোগের পর্যায়ে নিয়ে যান, যার পরিণতিতে ১৯৪৬ সালে সারদাচরণের উদ্যমে কে সি দাস প্রাইভেট লিমিটেডের সূত্রপাত, আর ‘স্টিমিং’, ‘ভ্যাকুয়াম প্যাকিং’, কৌটো-বন্দিকরণ ইত্যাদি প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে রসগোল্লার বিশ্বায়নেরও শুরু। ‘কলম্বাস’-এর দেখানো রাস্তায় তার পরে হেঁটেছেন আরও কতই না অভিযাত্রিক— ১৯০৭ সালে শ্যামবাজারের চিত্তরঞ্জন থেকে শুরু করে হাল আমলের হলদিরাম অব্দি। বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে লেখা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের বেস্টসেলার ‘মিষ্টান্ন-পাক’-এ রসগোল্লা ঠাঁই পেয়েছে বটে, কিন্তু তার ‘লেবার-ইনটেনসিভ’ রেসিপি পড়লে মনে হয় না স্বদেশি আর বয়কট আন্দোলনের মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে-ঘরে রসগোল্লা জ্বাল দেওয়া হত। আরেকটু ‘আপার ক্রাস্ট’ বাঙালি আর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাঠকদের জন্য ১৯২৬ সালে লেখা শ্রীমতী জে. হালদারের লেখা ইংরিজি রান্নার বই Bengal Sweets-এও পড়ি যে, সত্যিকারের খোলতাই রসগোল্লা বানাতে গেলে জ্বাল দেওয়ার পরেই গোল্লাগুলিকে ফেলতে হবে ‘in a series of syrup reservoirs of gradually decreasing temperatures’। তাই বাঙালির মনন, ধীশক্তি, আর পরিশ্রমের অনেকটা রসগোল্লার পরিচর্যায় ব্যয়িত হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই।
তবু বলতেই হয় যে, সেই মনন আর সৃষ্টিশীলতার সর্বোত্তম উদ্ভাসের প্রতীক সন্দেশ, যাকে কানাডীয়-মার্কিন খাদ্য-ইতিহাসবিদ কলিন টেলর সেন বলেছেন ‘the emblem of Bengaliness’। চিনির ডেলার রকমফের হিসেবে সন্দেশের ইতিবৃত্ত অনেক পুরনো হলেও ছানা ও চিনি বা গুড়ের রাজযোটকে তার নবজন্ম বাংলার নবজাগরণের উন্মেষকালের পুণ্যলগ্নে। ১৮২৩ সালে রাজা রামমোহন রায় যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জোরালো দাবিতে বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লিখছেন, তার কাছাকাছি সময়ে হুগলি জেলার জনাই গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে বৌবাজারে একটি ছোট মিষ্টির দোকান খোলেন প্রাণচন্দ্র নাগ, আর অল্পকালের মধ্যেই বিশেষত সন্দেশের কারিকুরিতে সেই দোকানকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেন তাঁর পুত্র ভীমচন্দ্র নাগ। ছানার সন্দেশের কল্লোলিনী তিলোত্তমা হয়ে ওঠার ইতিহাস অতঃপর প্রবাহিত হল ধর্ম ও সমাজসংস্কার, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের উত্থান, এবং অবশেষে জাতীয়তাবাদের স্ফুরণের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অল্প কিছুকাল আগে জমিদারবাড়ির জামাইষষ্ঠীর ভোজে জামাইকে চমকে দেওয়ার উপযোগী মিষ্টি বানানোর বরাত পেয়ে চন্দননগরের সূর্যকুমার মোদক বানালেন গোলাপগন্ধী নির্যাসকে গর্ভে নিয়ে সগৌরবে দণ্ডায়মান জলভরা সন্দেশ, আর তাঁর পৌত্র ললিতমোহন সেই তুলনাহীন সৃষ্টিকে অবয়ব দিলেন তালশাঁসের। ১৮৮৫ সালে, অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠালগ্নে উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে ঝাঁপ খুললেন দ্বারিকানাথ ঘোষ, আর ভবানীপুরে ভাই বলরাম মল্লিকের নামে দোকান খুলে মিষ্টির বেসাতি শুরু করলেন কোন্নগরের গণেশচন্দ্র মল্লিক। আর সেই ১৮৪৪ সাল থেকে সন্দেশকেই পাখির চোখ করে যাঁরা নিরঙ্কুশ তপস্যা করে চলেছেন, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সেই শ্বশুর-জামাতার জুটি গিরিশচন্দ্র দে ও নকুড়চন্দ্র নন্দীর দ্বৈতসাধনার কথা আলাদা করে বলতেই হয়। চিনির ডেলার একাধিপত্য থেকে সন্দেশকে মুক্তি দিয়ে তাকে বস্তুত চারুকলার স্তরে নিয়ে যাওয়ার মহাযজ্ঞে, অন্যদের অবদানকে তিলমাত্র খাটো না করেও, গিরিশ-নকুড়কেই অগ্রপুরোহিত বলে গণ্য করতে হবে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে সন্দেশের ‘সংস্কৃতায়ন’-এ সহায়ক হয়েছিল গন্ধবৈচিত্র্যের এক নিবিড় অন্বেষণ, আম কাঁঠাল কামরাঙা পাতিলেবু কমলালেবু নতুন গুড় দিয়ে তার শুরু, মোগলাই মসলা, যেমন ছোট এলাচ দারচিনি জয়িত্রী পেস্তা বাদাম কেসর কিসমিস গোলাপজল আতর দিয়ে তাতে নতুন মাত্রার সংযোজন, অতঃপর পাশ্চাত্যের প্রভাবে ভ্যানিলা চকোলেট স্ট্রবেরি কিউয়ি ফ্লেভারের আগমন, আর সাম্প্রতিক অনুপ্রবেশ উৎকৃষ্ট ব্র্যান্ডি আর হুইস্কির। আজও ‘নকুড়’-এর দোকানটির সন্দেশের বহুবিচিত্র সমাহারের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি অতি ক্ষীণজীবী, তাদের ‘শেল্ফ লাইফ’ বারো ঘণ্টার বেশি নয়। তাঁদের প্রধান কারিগর, বিহারের আদি বাসিন্দা সার্থকনামা উচিত নারায়ণকে বাংলার সন্দেশব্রহ্মাণ্ডের যথোচিত নারায়ণ আখ্যা দিলে অন্য শিল্পীদের খুব আপত্তি হবে বলে মনে হয় না।
তবে ‘একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুই জনে’, তাই স্রষ্টাদের পাশাপাশি ভোক্তাদের কথা হবে না, তাও কি হয়? স্থানাভাবে আমজনতার কথা ছেড়ে দিচ্ছি। বাংলার মহাপুরুষদের ‘সুইট টুথ’ নিয়েই ছোটখাটো একখানা মহাকাব্য লেখা বিলক্ষণ সম্ভব। চৈতন্যদেবের কথা তো আগেই হয়েছে, এক ঝাঁপে উনিশ শতকে এসে পড়লে দেখি ঝাঁ-চকচকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রত্যেক দিন আনা হচ্ছে দু’হাঁড়ি মিষ্টি, একটি দেবী কালীর জন্য, আরেকটি থেকে হাসিমুখে ভক্তদের বিলোবেন শ্রীরামকৃষ্ণ, নিজেও গালে ফেলবেন দু’চারটি। কুলপিবরফ ভালবাসতেন, এবং নিয়মিত খেতেন বলে তাঁর গলক্ষত বা ডিপথিরিয়া হয়েছিল, এমনও শোনা যায়। তাঁর শিষ্য এবং তার পর স্বামীজি হয়ে ওঠার আগে যৌবনদৃপ্ত নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘যদি আমাকে রসগোল্লা খাওয়াতে পারে তো ভাল, নইলে কান মলে দেব।’ আর বিবেকানন্দের বাড়ি থেকে নকুড় নন্দীর সন্দেশের দোকান মাত্র তিন মিনিটের হাঁটা পথ, তাই অলমতি বিস্তরেণ। তরুণ ছাত্র বিদ্যাসাগর তো তাঁর শিক্ষকের বাড়ির সরস্বতী পুজো উপলক্ষে দেবীবন্দনা করেছিলেন ‘লুচি কচুরী মতিচুর শোভিতং / জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্’ ইত্যাদি শ্লোক রচনা করে, আন্দাজ করি পরিণত বয়সে দেশের মিষ্টান্ন-রাজধানীর প্রাচুর্যে অবগাহন করতে তাঁর কুণ্ঠা হয়নি। ভীমচন্দ্র নাগ নাকি নিয়মিত খদ্দের স্যার আশুতোষের জন্য স্পেশ্যালি বানিয়েছিলেন আশুভোগ সন্দেশ, আর নেহরু সন্দেশ নিবেদন করা হয়েছিল মতিলাল নেহরুকে, ১৯২৭ সালে কলকাতা সফরের সময়। শোনা যায় লর্ড রিপনের নামেও তৈরি হয়েছিল সন্দেশ, আর লেডিকেনির বিধুর ইতিহাস তো আমরা সবাই জানি। এক ঘরোয়া আড্ডায় বনফুলের স্ত্রীর হাতে বানানো সন্দেশ খেয়ে চমৎকৃত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘উদ্বেগ’ প্রকাশ করেন যে, বাঙালি-জীবনে দ্বারিক ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর এক তৃতীয় রসস্রষ্টার আবির্ভাব হল। বিশ্বকবি মনে করতেন, সন্দেশ খেয়ে কেউ যদি বুঝতে না পারেন সেটি নকুড় নন্দীর না কি ভীমনাগের, তা হলে তিনি বাঙালি নন। এ-ব্যাপারে নিজের বাঙালিয়ানার নির্ভুল স্বাক্ষরও তিনি রেখেছেন। একবার চিকিৎসক ও সাহিত্যিক পশুপতি ভট্টাচার্যের কাছে রবীন্দ্রনাথ নবীন ময়রার দোকানের স্পঞ্জ রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলে ব্যস্ত পশুপতি অন্য দোকানের রসগোল্লা কিনে কবির কাছে হাজির করেন। কিন্তু সেই ‘ফাঁকিবাজি’তে কাজ হয়নি, মুখে দেওয়ামাত্রই কবি সেই রসগোল্লার ‘অথেন্টিসিটি’ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সেই রবীন্দ্র-ঐতিহ্য বেশ কিছু বঙ্গসন্তান এখনও ধরে রেখেছেন। তাই প্রণব রায়ের ‘বাংলার খাবার’-এ যখন পড়ি, ভীমনাগের দোকানে সন্দেশ খেয়ে এক রসিক বলে দিয়েছিলেন যে, সন্দেশের পাক হয়েছিল তেঁতুল কাঠের জ্বালে এবং তার নির্মাণকালে কারিগর কারখানায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন, সেই কাহিনির ‘অথেন্টিসিটি’ নিয়ে অন্তত কোনও সন্দেহ জাগে না।
এক ঘরোয়া আড্ডায় বনফুলের স্ত্রীর হাতে বানানো সন্দেশ খেয়ে চমৎকৃত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘উদ্বেগ’ প্রকাশ করেন যে, বাঙালি-জীবনে দ্বারিক ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর এক তৃতীয় রসস্রষ্টার আবির্ভাব হল। বিশ্বকবি মনে করতেন, সন্দেশ খেয়ে কেউ যদি বুঝতে না পারেন সেটি নকুড় নন্দীর না কি ভীমনাগের, তা হলে তিনি বাঙালি নন। এ-ব্যাপারে নিজের বাঙালিয়ানার নির্ভুল স্বাক্ষরও তিনি রেখেছেন।
আমার মতো ডায়াবেটিকদের জন্য আবার পৌষ মাসই সর্বনাশের সময়, আর সেই মাসের এই সংক্রান্তির সময় বাংলার পিঠেপুলির কথা উল্লেখমাত্র না করলে মহাপাতক হতে হবে। পিঠে বানানো আর খাওয়া প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির অভ্যেস, আর মধ্যযুগের বিবিধ মঙ্গলকাব্যে আর চৈতন্য-চরিতসাহিত্যে তো যে কোনও খাওয়ার বর্ণনার অছিলা পেলেই, প্রায় ইষ্টকবর্ষণের মতোই, পিষ্টকবর্ষণ। ‘ঠাকু’মার ঝুলি’তে সুচারু পিঠে বানানোই প্রকৃত রাজমহিষীর ‘লিটমাস টেস্ট’, উচ্চাভিলাষী ছদ্ম-রানি কিন্তু আদতে দাসী কাঁকনমালাকে দিয়ে দক্ষিণারঞ্জন ‘আস্কে পিঠে, চাস্কে পিঠে, ঘাস্কে পিঠে’ বানিয়েছেন, কিন্তু নিম্নবর্গের লোকজীবনের প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক সেই অকরুণ অনুপ্রাস অন্তত পূর্ববঙ্গের পিষ্টক-ঐতিহ্যের প্রতি সুবিচার করেনি। আস্কে পিঠে আসলে চালের গুঁড়ো জলে মিশিয়ে স্টিম করে বানানো ক্ল্যাসিক ‘চিতই পিঠে’, দেখতে দক্ষিণ ভারতের আপ্পম বা ইডলির মতো হলেও ভুরভুরে নতুন খেজুর গুড় মাখিয়ে খাওয়ার মধ্যেই তার অনন্যতা। আর বিপরীতে আসল রানি কাঞ্চনমালা প্রকৃত রাজমহিষীসুলভ নৈপুণ্যে বানিয়েছিলেন উচ্চবর্গের সমৃদ্ধির নির্ভুল সিগনেচার সব পিঠে— চন্দ্রপুলি, ক্ষীরমুরলী, মোহনবাঁশি, চন্দনপাতা— যার কিছু এখনও পৌষপার্বণের সময় বঙ্গের কিছু ঘরে বানানো হয়, আর কিছু হয়ে ওঠে বাংলার কাঁথা বা গয়নাবড়ির মতোই বহুবিচিত্র ‘নকশি পিঠে’, যার শিল্পসৌকর্য ঢাকা বা ময়মনসিংহের মতো জায়গায় বার্ষিক ‘পিঠা-উৎসব’-এ দৃশ্যমান। ধানভিত্তিক কৃষি-অর্থনীতির বাংলায় পালিত হবে নবান্ন বা পৌষ-পার্বণের মতো উৎসব, আর তার খাদ্য-সংস্কৃতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নেবে পিঠেপুলি, সেই মধুর সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না।
মাইকেল ক্রন্ডলের হিসেব অনুযায়ী, ২০০৩ সালে সারা ভারতে বানানো হয়েছিল ষোলোশো কোটি টাকার মিষ্টি, যার অর্ধেকই গেছে বাঙালির পেটে। প্রায় কুড়ি বছর পরে এই ব্যবসার অর্থমূল্য কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তার হিসেব আমাদের নেই, কিন্তু অচিরে সে-হিসেব করা প্রয়োজন। ২০২০-’২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতর আর ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের দুর্গাপুজোকে ঘিরে গড়ে উঠেছে যে পরিব্যাপ্ত ‘সৃষ্টিশীল অর্থনীতি’ বা ‘ক্রিয়েটিভ ইকনমি’, তার অর্থমূল্য বত্রিশ হাজার কোটি টাকারও বেশি। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে দুর্গাপুজোকে মানবসভ্যতার অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ‘ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ’-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত করার আগে ইউনেস্কো যে প্রতিবেদনগুলির সমীক্ষা করেছিল, তার মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। তাহলে আমাদের মিষ্টান্ন-সংস্কৃতির অতুল ঐশ্বর্যের জন্য কেন হবে না একই রকম বিশদ সমীক্ষা, নিবিড় ডকুমেন্টেশন, তালিকাভুক্তির অপ্রতিরোধ্য আবেদন? ইনট্যাক, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর আর্ট অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ সদ্য কে সি দাস, নবীনচন্দ্র দাস, ভীমচন্দ্র নাগ, আর গিরিশচন্দ্র দে-নকুড়চন্দ্র নন্দীর চারটি দোকানকে ‘হেরিটেজ’ তকমা দিয়েছে বটে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দুতে আমাদের মহাসিন্ধুর প্রতিফলন অসম্ভব। আজারবাইজান যদি তার ‘দোলমা’ রন্ধনশৈলীর জন্য ইউনেস্কোর ঐতিহ্যতালিকায় ওঠে, কোরীয়রা যদি ‘কিমচি’র জন্য খিমচে নিয়ে আসতে পারে সেই মহাগৌরবের তকমা, মিষ্টান্ন-মহিমায় আচ্ছন্ন আমরা তাহলে কম কীসে, অ্যাঁ? তাই এক কল্পনাসম্ভব উত্তর-অতিমারী পৃথিবীকে বাংলার নিজস্ব মধুর রসের সংযোগে আরেকটু বাসযোগ্য করে যাওয়াই হোক না আমাদের নতুন বছরের নতুন অঙ্গীকার! অপেক্ষায় থাকো ইউনেস্কো, আমরা আসছি, আবারও।
ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র