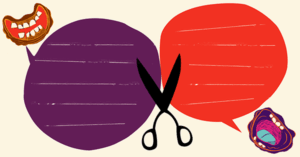মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। ‘Sapiens’, অর্থাৎ যে চিন্তা করে। আকাশের তারা দেখে সে সন্তুষ্ট থাকে না, সে জানতে চায় তাদের উৎস, তাদের দূরত্ব। ঝড়-বৃষ্টি থেকে পালিয়েই সে বাঁচে না, সে অনুসন্ধান করে সেসবের কারণ। ক্রমান্বয়ে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাকে সে বিচ্ছিন্ন ভেবে ভুলে যায় না, তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করবার চেষ্টা করে। আবার সে প্রাণীও তো বটে! তাই আর পাঁচটা প্রাণীর মতোই সে বেঁচেবর্তে থাকতে চায়। বংশগতির মাধ্যমে তার জিন সন্তানের মধ্যে সঞ্চার করে দিতে চায়। হয়তো চূড়ান্ত বোধের সম্মুখীন হয়েও সে তাই বলে ‘মরিতে চাহি না আমি…’।
কিন্তু জিজ্ঞাসা আর জিজীবিষা— এই দুই পথ প্রকৃত বিচারে বিপরীতমুখী। বাঁচবার তাগিদে বহু শতাব্দীর বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কে উৎকীর্ণ হয়েছে এক ধরনের জগৎচিত্র। পথে খানাখন্দ দেখলে সে এড়িয়ে যায়, রাস্তা পার হওয়ার সময় নিখুঁত হিসেবে মেপে নেয় ধাবমান গাড়ির দূরত্ব ও গতিবেগ, ধোঁয়া দেখে আঁচ করে নেয় আগুন, বিপদ। যাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, কমন সেন্স। এই কাণ্ডজ্ঞান তার চলার পথকে সহজ করে, তাকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু এই কাণ্ডজ্ঞান নির্মিত যে-জগৎচিত্র, তাই কি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ? না কি তা সত্যের এক বিকৃত ছবি? এক ভ্রান্তি? তাই যদি হয়, ভ্রান্তির ওপারে তবে কী? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পারে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণায় বা মহাকাশের বিশাল ব্যাপ্তিতে নিহিত কী সেই সৎবস্তু? কীভাবেই বা তার ধারণা করা সম্ভব?
বিজ্ঞানের জটিল ও দুরধিগম্য তত্ত্বের অনুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁর আগ্রহ নয়। তিনি চেতনান্বেষী, মানবমনের বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। বিজ্ঞানের ইতিহাসকে প্রেক্ষাপটে রেখে তিনি প্রবেশ করেন তাঁর চরিত্রদের মনের গভীরে। জ্ঞানতত্ত্বের অভিমুখ এবং মানবসমাজের গতিপথ চিরকালের মতো বদলে দেওয়া এই মানুষগুলির জীবনের নির্ণায়ক কিছু মুহূর্তের হদিশ দেন আমাদের।
আমাদের অধিকাংশের জীবন এইসব প্রশ্নকে না ছুঁয়েই অতিবাহিত হয়। কিন্তু কেউ-কেউ ভাবেন, অনুসন্ধান করেন। ভাবেন শিল্পীরা, কবি-সাধক-দার্শনিকেরা। আর ভাবেন বৈজ্ঞানিক। এঁদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের পথই হয়তো সবচেয়ে কঠিন। কারণ তাঁর অনুসন্ধানকে শৃঙ্খলিত রাখতে হয় যুক্তিবুদ্ধির নিয়মে, গণিতের কাঠামোয়। খেয়ালখুশির আশ্রয় নেওয়ার তাঁর উপায় নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের সীমা কতদূর? তার সীমাবদ্ধতাই বা কোথায়? কী উপায়ে সত্যে উপনীত হন বিজ্ঞানী? কোন মূল্যে?
এইসব প্রশ্নকে কেন্দ্রে রেখেই আবর্তিত হয় বেনহামিন লাবাতুতের উপন্যাস ‘When We Cease to Understand the World’।
*****
উপন্যাস তো বলে ফেললাম, কিন্তু এই বইয়ের অবয়ব ঠিক চিরায়ত উপন্যাসের মতো নয়। এই কাহিনীর কোনো plot বা সংক্ষিপ্তসারও বলা দুষ্কর। প্রচলিতার্থে গল্প বলে যাওয়ার চেয়ে গভীর পাঠে পাঠকের মনোজগতে কিছু নকশা তৈরি করাই এই বইয়ের লেখকের অভিপ্রায় বলে মনে হয়। পাঁচটি পৃথক অংশে বিভক্ত এই বইটির একমাত্র শেষের কাল্পনিক গল্পটি বাদ দিলে বাকি প্রত্যেকটি অংশেরই কেন্দ্রে রয়েছে ইতিহাসনির্ভর বাস্তব। বইটিকে বরং প্রবন্ধোপন্যাস বলা যেতে পারে। ইংরেজিতে যাকে বলে ‘essayistic novel’। ইদানীংকালে ওলগা তোকারজুক বা জুলিয়ান বার্নসদের কাছ থেকে আমরা এই ধরনের উপন্যাস পেয়েছি। কিন্তু এই বই যেন তাদের থেকেও কিছুটা আলাদা। এর আখ্যানশৈলী বরং খানিকটা docu-feature গোত্রের— কখনও তথ্যভিত্তিক ইতিহাস পরিবেশিত হচ্ছে লেখকের ভাষ্যে, কখনও আবার দৃশ্যায়নের মাধ্যমে তিনি আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন চরিত্রদের নিভৃত অন্তর্জগতে।
তবে এই চরিত্ররা কাল্পনিক নয়, প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। জার্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রিৎজ হাবর যেমন। নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া সংশ্লেষের পদ্ধতি আবিষ্কার করে যিনি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ। বা জ্যোতির্বিদ কার্ল শোয়ার্জশিল্ড। মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ময়দানে রুশ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়তে-লড়তে যিনি আইনস্টাইনের সাধারণ ক্ষেত্র সমীকরণের সমাধান বের করেন। কৃষ্ণগহ্বরের আভাস দিয়ে মহাকাশের অবয়ব তো বটেই, আমাদের স্থান-কালের ধারণাও আমূল বদলে দেন তিনি। রয়েছেন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ, আলেক্সান্ডার গ্রোথেন্ডিক— যিনি তার দূরপ্রসারী কল্পনা ও তীক্ষ্ণ মেধার সাহায্যে গণিতের বিভিন্ন শাখাকে একীভূত করেছেন, বীজগণিত জ্যামিতির সাহায্যে নির্ণয় করে দিয়েছেন গণিতচর্চার অভিমুখ। আর রয়েছেন বিবদমান দুই বিজ্ঞানী— এরভিন শ্রোডিঙ্গার ও ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ, পদার্থের অভ্যন্তরীণ যে-কোয়ান্টামজগৎ (ক্ষুদ্রাংশিক), তার চরিত্র অন্বেষণ করতে গিয়ে যাঁরা শুধু একে অপরের সঙ্গে নয়, লড়ছেন নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধির সঙ্গে, সমগ্র বৈজ্ঞানিকমহলের সঙ্গেও।
উচ্চতর বিজ্ঞানের সঙ্গে অনতিপরিচিত পাঠক এঁদের নাম শুনে খানিকটা সন্ত্রস্ত হতে পারেন। বইটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তাঁর বোধগম্য নাও হতে পারে কিন্তু লাবাতুতের কাহিনিতে এগুলি অনুষঙ্গমাত্র, উপজীব্য নয়। তিনি বৈজ্ঞানিক নন, সাহিত্যিক। বিজ্ঞানের জটিল ও দুরধিগম্য তত্ত্বের অনুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁর আগ্রহ নয়। তিনি চেতনান্বেষী, মানবমনের বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। বিজ্ঞানের ইতিহাসকে প্রেক্ষাপটে রেখে তিনি প্রবেশ করেন তাঁর চরিত্রদের মনের গভীরে। জ্ঞানতত্ত্বের অভিমুখ এবং মানবসমাজের গতিপথ চিরকালের মতো বদলে দেওয়া এই মানুষগুলির জীবনের নির্ণায়ক কিছু মুহূর্তের হদিশ দেন আমাদের। অন্তর্জ্বালায় জাজ্বল্যমান এবং অনন্তের দ্যোতনাবাহী এই মুহূর্তগুলির সম্পূর্ণ অর্থ অনুধাবন করা হয়তো তাঁদেরও সাধ্যের অতীত ছিল, পাঠকের তো বটেই। অনুমানে, আভাসে তার ধারণা করা যেতে পারে মাত্র।
*****
সেরকমই একটা মুহূর্ত আমরা দেখি হাইজেনবার্গের জীবনে। বছর তেইশের যুবক হাইজেনবার্গ হেলিগোল্যান্ডের নির্জন দ্বীপে প্রায় এক বদ্ধোন্মাদ দশায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা, মলমূত্র ত্যাগ করে ফেলছেন যত্রতত্র, দিনের পর দিন অর্ধভুক্ত, অস্নাত, বিনিদ্র। যেন মরণপণ করেছেন যে, গণিতের মাধ্যমে উদ্ঘাটন করবেন কোয়ান্টামজগতের রহস্য। কিন্তু তা দুঃসাধ্য প্রায়। পাতার পর পাতা অঙ্ক কষে নিজেই ছুঁড়ে ফেলছেন সেসব। শেষমেশ যখন শয্যাশায়ী, হাতে আসে একটি কবিতার বই— গোয়েথের অনুবাদে হাফিজের কবিতা। চতুর্দশ শতাব্দীর ফারসি কবি হাফিজ, যিনি আহারনিদ্রা ত্যাগ করে খর মরুভূমির মাঝখানে অবিরাম ৪০ দিন মৌন সাধনা করেছিলেন আল্লাহ্র আভাস পাওয়ার আশায়। প্রায় মৃত্যমুখে এসে পৌঁছানো হাফিজকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন তিনি আর সেই আগের মানুষটি নন, তাঁর মধ্যে তখন আবির্ভূত হয়েছে এক দ্বিতীয় চেতনা, যে-চেতনার চালনেই হাফিজ লিখেছেন প্রায় শতাধিক কবিতা। প্রায় ৬০০ বছর পর, হাইজেনবার্গ জ্বরের ঘোরে আউড়াচ্ছেন সেই কবিতা। শুষ্ক গদ্যভাষা, গণিতের বিমূর্ত ভাষা যেন রূপান্তরিত হচ্ছে কাব্যের মরমিয়া ভাষায়। না হয়ে তার উপায় কী! একটি ধূলিকণার মধ্যে যদি এক কোটি অণুর অবস্থান হতে পারে, তাহলে সেই আণবিক জগতের বর্ণনায় বিজ্ঞানের চিরায়ত ভাষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রয়োজন উপমার, সুদূরপ্রসারী কল্পনার, স্বপ্নভাষ্যের।
সেই স্বপ্নভাষ্যই যেন পথ বাতলে দিচ্ছে শ্রোয়ডিঙ্গারকেও। তিনি হাইজেনবার্গ অপেক্ষা বর্ষীয়ান, স্থিতধী। ক্ষয়রোগ আর ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্য থেকে সাময়িক স্বস্তি পেতে ডাক্তার হেরউইগের নির্জন ক্লিনিকে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে ডাক্তারের কিশোরী কন্যার ছোঁয়ায় মুগ্ধ বিজ্ঞানী শরীরে-মনে আবিষ্কার করছেন যৌবনচাঞ্চল্য। কিন্তু যে-বৌদ্ধিক অনুসন্ধান নিয়ে তিনি জুরিখ ছেড়েছিলেন, তার কোনও কূলকিনারা পাচ্ছেন না। তাঁরও তো উদ্দেশ্য কোয়ান্টামজগতের তিমির বিনাশ করা, চিরায়ত ভৌতবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে তার ব্যাখ্যা করা। কিন্তু তাঁর সমীকরণে চলে আসছে কল্পসংখ্যা— যার অর্থ, কোয়ান্টাম-তরঙ্গ আমাদের এই ত্রিমাত্রিক দুনিয়াকে অতিক্রম করছে। বহুমাত্রার মধ্যে দিয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে সে পৌঁছচ্ছে এক বিচিত্র-বিমূর্ত জগতে, যে-জগৎ আমাদের সাধারণ যুক্তি, বুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞানের অতীত। শরীর-মনের প্রস্ফুটিত আন্দোলনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে তাঁর এই বৌদ্ধিক আলোড়ন। প্রাচ্য দর্শনে সুপণ্ডিত শ্রোডিঙ্গার স্বপ্নে দেখছেন এক দেবীমূর্তি— কৃষ্ণা, অসি-ধরা, মুণ্ডমালা-পরিহিতা এই দেবীর স্তন থেকে দুগ্ধচ্ছটা বেরিয়ে এসে তাঁকে স্নাত করছে, আবার অসির এক কোপে ছিন্ন করছেন তাঁর উন্নত লিঙ্গ, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক।
এইসব অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই হাইজেনবার্গ-শ্রোডিঙ্গারদের মনোজগতে ঘটাচ্ছে এক গূঢ়তর সত্যের উদ্ভাস, এবং তা যখন বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদ্যের আকার নিচ্ছে, তখন সেই বৈপ্লবিক তত্ত্বপ্রস্তাব মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই, যাদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং আইনস্টাইন। হোক না অণু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, কিন্তু তাকে বুঝতে চিরাচরিত যৌক্তিক বনেদটুকুও বিসর্জন দিতে হবে? এ তো সত্যের হেঁয়ালিতে পর্যবসিত হওয়া! কিন্তু তাঁর আস্ফালনই সার। কোয়ান্টামজগৎ আদতে স্বতঃসত্তারহিত— তাকে কণারূপে দেখলে সে কণা, তরঙ্গরূপে দেখলে তরঙ্গ। তা আছে আবার নেই। তার গতিবেগ নির্দিষ্ট তো অবস্থান অনির্দেশ্য, শক্তি পরিমেয় তো কাল দুর্জ্ঞেয়। তাকে ধারণা করতে গেলে কাণ্ডজ্ঞান ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই! ওরহান পামুকের ‘My Name is Red’ উপন্যাসে যেমন শিল্পী ওসমান নিজেকে অন্ধ করছেন আল্লাহ্র দৃষ্টির আন্দাজ পাওয়ার জন্য, বা মহাভারতের কৃষ্ণ যেমন বিশ্বরূপ দর্শন করানোর পূর্বে অর্জুনকে সতর্ক করছেন, ‘ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা…’।
*****
কিন্তু এই সর্বভেদী, সর্ববৈনাশিক উপলব্ধির মূল্য কী? মানবসভ্যতাকেই বা তা কোন পথে চালিত করবে? এর উত্তর খুব স্পষ্ট নয়। তবে এইটুকু নিশ্চিত যে, ব্রহ্মাণ্ডের উপর নিক্ষিপ্ত বিজ্ঞানের আলো যত তীব্রতর হচ্ছে, ততই দীর্ঘতর হচ্ছে তার ছায়া। স্টিভেন ওয়েনবার্গ তাঁর ‘To Explain the World’ বইতে লিখেছেন, ‘মহাবিশ্ব যতই বোধগম্য হয় আমাদের, ততই সবকিছু অর্থহীন লাগে আমার।’ লাবাতুতের কাহিনি জুড়েও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এক অদ্ভুত নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতার ইঙ্গিত। হাবের এবং শোয়ার্জশিল্ড-এর শেষ চিঠিতে নইলে কেন একই রকম হতাশা ও ভয় ধরা পড়বে? কেন এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের আভাস কুরে কুরে খাবে তাদের শেষ দিনগুলি? কেনই বা স্বয়ং শ্রোডিঙ্গার পরবর্তীকালে তাঁর নিজেরই তত্ত্বকে অলীক প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন! গণিতের অভিমুখ চিরতরে বদলে দেওয়া মহামেধা গ্রোথেন্ডিক শেষ জীবনে কেন বেছে নেবেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর যাপন, জ্বালিয়ে দিতে বলবেন তাঁর জীবনের সমস্ত কাজ, তরুণ ছাত্রীর উৎসাহের উত্তরে কেবল হাসিমুখে বলবেন, ‘গণিতে আমার আর কোনও আগ্রহ নেই’?
উত্তর দেন না লেখক। কেবল কাহিনির প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করেন ইতিহাসের এক অমোঘ ইঙ্গিত। বিশ্বযুদ্ধ। বইয়ের চরিত্রেরা পৃথক দেশের, তাদের জীবন আবর্তিতও হয় ভিন্ন-ভিন্ন অক্ষপথে। কিন্তু যুদ্ধ-থরথর কাল তাদের কোথাও যেন মিলিয়ে দেয়, একসূত্রে গাঁথে লাবাতুতের কাহিনি। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবিষ ক্লোরিন গ্যাসের আমদানি হাবেরের হাত ধরেই, যে-বীভৎসতা সহ্য করতে না পেরে ভরা পার্টিতে নিজের মাথায় গুলি করেন তাঁর স্ত্রী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হয়ে প্রাণপাত করা ইহুদি শোয়ার্জশিল্ডের পুত্রকেই এক সময় আত্মহত্যা করতে হয় জার্মানি ছেড়ে পালতে না পেরে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাতে বাধ্য হন আজীবন শান্তিকামী শ্রোডিঙ্গার। আবার বালক গ্রোথেন্ডিককে দেখতে হয় কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে তাঁর বাবার মৃত্যু। মায়ের হাত ধরে কোনওক্রমে তিনি পালিয়ে বাঁচেন। যুদ্ধবিক্ষুব্ধ ইউরোপ শুধুমাত্র প্রেক্ষাপট নয়, দেখা দেয় এই কাহিনির পরিণাম হিসেবে। মনে পড়ে যায় ওপেনহাইমারের ভবিষ্যদ্বাণী, ‘পদার্থবিজ্ঞানীরা পাপের সন্ধান করে ফেলেছেন। এই জ্ঞান থেকে এখন আর তাঁদের মুক্তি নেই।’
*****
বইয়ের একদম শেষ অংশে এসে যখন এক রহস্যময় উদ্যান-পরিচারকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, যিনি গল্পচ্ছলে বলেন লেবুগাছের কথা, কীভাবে গাছটি মৃত্যুর পূর্বে প্রচুর ফল দেয়, তা যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম— ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্বেই এক বহুপ্রজ প্রাচুর্য্য। বর্তমান মানবসভ্যতার দিকে তাকিয়ে পাঠক ক্ষণিকের জন্যে হলেও শিউরে উঠতে বাধ্য হন। জ্ঞানের পরিণাম কি তবে ধ্বংস?
ওই যে শুরুতেই বলেছিলাম, জিজ্ঞাসা আর জিজীবিষার পথ বিপরীতমুখী।
When We Cease to Understand the World
লেখক: বেনহামিন লাবাতুত
(মূল স্প্যানিশ: ‘Un Verdor Terrible’)
ইংরেজি অনুবাদ: আদ্রিয়ান নাথান ওয়েস্ট
প্রকাশক: পুশকিন প্রেস