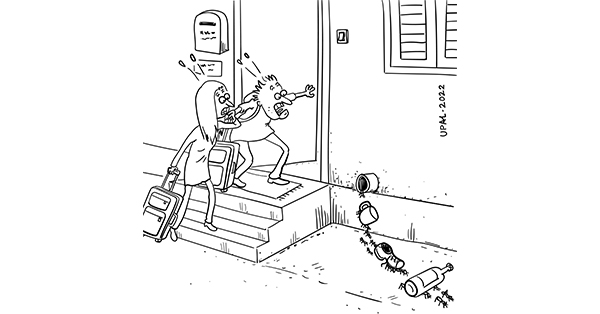রবীন্দ্রনাথ ও রামকিঙ্কর

 ঋষি বড়ুয়া (May 29, 2021)
ঋষি বড়ুয়া (May 29, 2021)রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে রামকিঙ্কর যখন বাঁকুড়া থেকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছলেন, তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর— সেটা ১৯২৫ সাল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বাঁকুড়ায় ওঁদের প্রতিবেশী। কলকাতায় দুটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। বাংলার সংস্কৃতি-জগতের সঙ্গে তাঁর একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র ছিল। রামকিঙ্করের ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়ার প্রতি নিষ্ঠা দেখে উনিই উদ্যোগ নিলেন ওঁকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ভর্তি করার ব্যাপারে। শোনা গেছে, নন্দলাল রামকিঙ্করকে দেখে উক্তি করেছিলেন— ‘এই তো, হয়ে গেছে, আর কেন?’ তারপর একটু ভেবে বলেছিলেন— ‘ঠিক আছে, ২/৩ বছর থাকো।’
সেই ‘২/৩ বছর’ হয়ে গিয়েছিল তাঁর শান্তিনিকেতনে আজীবন থাকা। এখানকার পাট চুকিয়ে আর্থিক কারণে চাকরি খোঁজা শুরু হল। মাঝখানে দু’এক বছর আসানসোল এবং দিল্লির মডার্ন স্কুলে চাকরির পর, ১৯৩৪-এ স্থায়ীভাবে যোগ দিলেন কলাভবনে।
শান্তিনিকেতনে তখন রবীন্দ্রনাথের নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মুক্তচিন্তার পরিবেশ। সমস্ত সাবেকি শিক্ষাব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে শান্তিনিকেতন মডেল তখন সাড়া ফেলেছে দেশে ও বিদেশে। ইংরেজদের আমদানি করা চার দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার উল্টোপথে চলেছেন তিনি।
ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নামকরণ হয়েছে ‘বিশ্বভারতী’। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেয়েছে। তার মধ্যে কলাভবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কিন্তু এখানে নন্দলালের নেতৃত্বে চলছে আর এক শিল্পচিন্তার অনুসন্ধান।

শিক্ষক নন্দলাল বসু ও ছাত্র রামকিঙ্কর বেইজ
ছবি ঋণ: ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্টঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ই বি হ্যাভেল-এর চেষ্টায় মৌলিক ভারতীয় শৈলী খুঁজতে গিয়ে সৃষ্ট হয়েছে আর এক নতুন ধারা— যাকে আমরা ‘বেঙ্গল স্কুল’ বলে জানি। অবনীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন নন্দলালকে তাঁর যথার্থ উত্তরসূরি হিসেবে ‘ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি’-তে যোগদান করাতে। কলাভবনের অধ্যক্ষ তখন অসিত হালদার। কিন্তু নন্দলালকে এখানে সপ্তাহে একবার আসতে হত ক্লাস নিতে। রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টির অভাব ছিল না। উনি বুঝলেন নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে আনতে পারলে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। মৌলিক ভারতীয় শৈলী আরোপ করতে গিয়ে এক ধরনের ‘ম্যানারিজম’ চলে এসেছিল ওই বেঙ্গল স্কুল ধারায়। যদিও নন্দলালও বেঙ্গল স্কুল-এর শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁর মধ্যে একটা ধারণার বিস্তৃতি আর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। গুরুদেবের কথায়, ১৯২১-এ নন্দলাল অধ্যক্ষ হলেন কলাভবনের।
রামকিঙ্কর যখন ছাত্র হিসেবে এলেন, আলাদা ‘বিভাগ’ বলে কিছু ছিল না। প্রাথমিক ভাবে সব বিষয়েই চর্চা করানো হত— ছবি আঁকা— ওয়াশ, টেম্পারা, ফ্রেস্কো ইত্যাদি; আল্পনা, তাঁতের কাজ, বাটিক এবং অল্পস্বল্প মূর্তি গড়া। গুরুদেবের আমন্ত্রণে দুই মহিলা শিল্পী এসেছিলেন— লিজা ভন পট এবং মার্গারেট মিলওয়ার্ড। তাঁদের কাছেই ছাত্রছাত্রীরা প্রথম মাটির কাজ (‘ক্লে মডেলিং’) এবং প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে কীভাবে ছাঁচ নিতে হয় তা শিখল।
বাঁকুড়ায় ছোটবেলায় ছবি আঁকা ছাড়াও, মূর্তিকারদের সাথে মাটির মূর্তি করার একটা অভ্যাস ছিলই। সুতরাং কলাভবনে ওইসব নতুন টেকনিক দেখার পর তাঁর বেশি সময় লাগেনি ওগুলো আয়ত্ত করতে।
১৯৩৪-এ যখন স্থায়ীভাবে যোগ দিলেন শিক্ষক হিসেবে, তখন থেকেই শুরু হল মূর্তি বিভাগের জন্য নতুন উদ্যোগে আয়োজন। প্লাস্টার অফ প্যারিস ছিল দুষ্প্রাপ্য— যা সামান্য মাইনে পেতেন তা দিয়ে বড় মূর্তি বানানো সম্ভব ছিল না। এদিকে বড় কাজ করার জন্য মনটা উসখুস করছে। সিমেন্ট আর কাঁকর দিয়ে তৈরি হল ‘সুজাতা’। কিন্তু ‘সুজাতা’ নামকরণ অনেক পরে হয়েছে।

‘সুজাতা’, ডাইরেক্ট কংক্রিট, ১৯৩৫ রবীন্দ্রনাথ ওই সময়ে মাঝেমাঝে আশ্রমে ঘুরতে আসতেন। একদিন ওই মূর্তিটা চোখে পড়াতে, নন্দলালের কাছে জানতে পারলেন যে ওটা কিঙ্করের করা। পরের দিন তলব হল— গুরুদেব ডেকেছেন। বকুনি খাওয়ার আশঙ্কায় ভয়ে-ভয়ে হাজির হলেন গুরুদেবের কাছে। বকুনি দূরের কথা— আদেশ দিলেন, আশ্রম ভরিয়ে দিতে হবে ওই রকম বড়-বড় মূর্তি দিয়ে!
এই ঘটনাটা ছোট হলেও, রামকিঙ্করের জীবনে এর মাহাত্ম্য বিশাল। একদিন সাহস করে গুরুদেবকে প্রস্তাব দিলেন একটা পোর্ট্রেট করবেন বলে। প্রথমে একটু আপত্তি ছিল— ক্যালিপারস (কম্পাসের মতন একটা যন্ত্র) ব্যবহার করাটা খুব বিরক্তিকর, এই বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন আশ্বস্ত হলেন যে ওটা ব্যবহার করা হবে না, তখন রাজি হলেন।
প্রথমে যে মূর্তিটা হল, তার শৈলীটা ছিল বেশ রিয়ালিস্টিক। দু-তিনজন ছাত্রদের নিয়ে সেটাকে প্লাস্টারে পরিণত করা হল। মাস্টারমশাই নন্দলাল খুব খুশি মূর্তি দেখে।
পরের দিন দেখা গেল তাঁর স্টুডিওর দরজা বন্ধ, এবং বেশ জোরে কিছু ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দরজা খোলার পর দেখা গেল মূর্তি ভেঙ্গে চৌচির! এরপর মন থেকে যে দ্বিতীয় সংস্করণটি করলেন, সেটাই সেই চিরপরিচিত, বিখ্যাত আবক্ষ মূর্তি, যার সংস্করণ দেশে এবং বিদেশে অনেক জায়গায় রাখা আছে।

‘রবীন্দ্রনাথ’, প্লাস্টার, ১৯৩৮
ছবি ঋণ: ‘রামকিঙ্কর বেইজ: স্কাল্পচার্স’, দেবীপ্রসাদতাঁর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মুখেই শুনেছি, স্টুডিওতে ক্লাস চলাকালীন কারও কাজ যদি পছন্দ না হত উনি বলতেন ‘ভেঙে আবার করো’— কারওরটা আবার নিজেই ভেঙে দিতেন। নান্দনিক গুণমানের সঙ্গে আপোস করা চলে না। ওই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজকে ভেঙে দেওয়ার সাহস তাঁরই ছিল!
‘সুজাতা’-র পর আশ্রমে গড়ে উঠল ‘সাঁওতাল পরিবার’, ‘মিল কল বা কলের বাঁশি’, ‘ধান ঝাড়াই’ এবং আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ— ‘বাতিদান’। ১৯৪০-এ ‘শান্তিনিকেতন গৃহ’র সামনে কাঠের কাঠামো বানিয়ে ডাইরেক্ট সিমেন্টে (সঙ্গে মার্বেল পাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে ফিনিশিং হল) যে কাজটা হল, সেটিকে বলা হয় ভারতের প্রথম বিমূর্ত ভাস্কর্য। কিন্তু বিমূর্ততা (‘অ্যাবস্ট্রাকশন’) সম্বন্ধে তাঁর গভীর ধারণা ছিল; নিছক খেলার ছলে ওইরকম ফর্ম তৈরি হয়নি। এ ব্যাপারে তাঁর খুব স্বচ্ছ ধারণা ছিল। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, ‘মহেঞ্জোদারোর আমল থেকেই শিবলিঙ্গ প্রচলিত। আমাদের মিথোলজিতেও আছে। ওটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট তো। কোনও রূপ নেই। ভেবে নিতে হয়। দেখতে পাচ্ছেন না কিছু। ওটাকেই যদি একটু-আধটু রূপ দেওয়া যায়, ব্যস, ফর্ম এসে গেল। ভিসুয়াল ফর্ম।’

‘সাঁওতাল পরিবার’, ডাইরেক্ট কংক্রিট, ১৯৩৮
ছবি ঋণ: ‘রামকিঙ্কর বেইজ: আ রেট্রোস্পেকটিভ (১৯০৬-১৯৮০)’, আর. শিবকুমারসৃষ্টিশীলতা এবং প্রতিভা অনেকের মধ্যেই থাকে, কখনও সুপ্ত, কখনও তার বিকাশ ঘটে। রামকিঙ্করের মধ্যে ছিল একটা আগ্নেয়গিরি। যেখানেই থাক, তার অগ্ন্যুৎপাত হতই। শান্তিনিকেতনে মুক্তচিন্তার পরিসর তাঁর সৃষ্টিশীলতার বিকাশের আদর্শ জায়গা ছিল। রবীন্দ্রনাথের পরিষ্কার নির্দেশ ছিল, ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে কাজ করার সময়। নন্দলালও সে-কথার অমান্য করেননি। সুতরাং শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁর সমস্ত রকম এক্সপেরিমেন্টেশনে সাহায্য করেছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
রামকিঙ্কর ছিলেন বোহেমিয়ান, non-conformist— অনেকটাই সামাজিক দায়বদ্ধতার ধার-না-ধারা একজন মানুষ। তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের তোয়াক্কা করতেন না। কিন্তু তার জন্য খোলাখুলি অসামাজিক আচরণ করতে কেউ দেখেননি। তিনি ছিলেন আত্মভোলা, দিলদরিয়া, স্বচ্ছ মনের মানুষ।
অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ প্রখর একজন ব্যক্তিত্ব— তাঁর মেধা, দর্শন, শিল্প চেতনাকে ছোঁয়া কারও সাধ্য ছিল না। এহেন একজন ব্যক্তিত্বের, তাঁর বিপরীত চরিত্রের রামকিঙ্করের সঙ্গে কোন মানসিক স্তরে যোগাযোগ হয়েছিল, তা বোঝা মুশকিল। কিন্তু বাঁকুড়ার এই সাদামাটা, আড়ম্বরহীন যুবকটির মধ্যে যে একটা স্ফুলিঙ্গ আছে, সেটা গুরুদেবের ধরতে দেরি হয়নি। তাই এই স্বাধীনতা এবং প্রাণের আনন্দে কাজ করার আহ্বান জানাতে দ্বিধা করেননি।

ভাস্কর্য নির্মাণে মগ্ন শিল্পী রামকিঙ্কর
ছবি ঋণ: ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্টরামকিঙ্করকে একটি সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ওঁর কাজে রবীন্দ্রনাথের কোনও প্রভাব আছে কি না। তার উত্তরে বলেছিলেন, ‘আছে এবং নেই’। কথাটার ব্যাখ্যা করেছিলেন এই বলে যে, সরাসরি প্রভাব না থাকলেও, গুরুদেব যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তাঁকে কাজ করার— সেটাই সবচেয়ে বড় প্রভাব।
শান্তিনিকেতন গৃহ এবং উপাসনাগৃহের কাছে যখন ‘ল্যাম্প স্ট্যান্ড’ বা ‘বাতিদান’ কাজটা করা হচ্ছিল, অনেকের মনেই প্রশ্ন ছিল এই কাজটার বিষয়টা নিয়ে এবং বিরাট সংশয় ছিল কাজটার ‘মানে’ নিয়ে। অনেকেই ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারেননি যে, মন্দিরের কাছে যে-কাজটা রাখা হবে সেটা নিরাকার ব্রহ্মকে একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা— বিমূর্ত, অ্যাবস্ট্র্যাক্ট— একটি ধারণার বিমূর্ত রূপ। আসলে তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের থেকে বহু বছর এগিয়ে ছিলেন রামকিঙ্কর, এটা তারই একটা নিদর্শন।
গুরুদেব যখন অনুমতি দিলেন তাঁর পোর্ট্রেট করার জন্য, ব্যবস্থাটা এরকম হল যে, গুরুদেব নিজের মতন বসে লেখালিখি করবেন, আর রামকিঙ্কর একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর modelling stool-এর উপর কাজটা করবেন। একদিন কাজের ফাঁকে, যখন আশেপাশে কেউ নেই, রামকিঙ্করকে বললেন, ‘যেটি দেখবে বাঘের মতন ঘাড় মুচড়ে ধরবে। শেষ করে আর পেছনে তাকাবে না। আবার নোতুন ধরবে।’
‘বাঘের মতন ঘাড় মুচড়ে’ ধরা একটি প্রতীকি কথা। রামকিঙ্করের কাজে subtlety কম, dynamic force বেশি। তাঁর অসংখ্য ছবি ও মূর্তিতে ছন্দটা lyrical না বলে forceful বলাটা ভালো। হয়তো গুরুদেবের ওই কথাটাই তাঁর কাজের মূল মন্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছিল।
ঋণ স্বীকার:
১। ‘রামকিঙ্কর বেইজ:আ রেট্রোস্পেকটিভ (১৯০৬-১৯৮০)’, আর. শিবকুমার
২। ‘চিত্রকথা’, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
৩। ‘রামকিঙ্কর:অন্তরে বাহিরে’, সম্পাদনা:প্রকাশ দাসকভারের ছবি ঋণ: ‘রামকিঙ্কর বেইজ: আ রেট্রোস্পেকটিভ (১৯০৬-১৯৮০)’, আর. শিবকুমার
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook