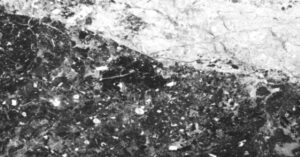সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে হাজার হাজার পাতা লেখা হয়ে গেছে। তাঁর জীবন আর কাজ নিয়ে এমন কোনও ক্ষেত্র বোধহয় বাকি নেই যেটা ছোঁয়া হয়নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, কী নিয়ে লিখব সেটা নিয়ে একটা দুর্মদ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়লাম। তারপর ভাবলাম সবার যেমন একটি করে নিজস্ব রবীন্দ্রনাথ আছেন, তেমনি একটা করে ব্যক্তিগত সত্যজিৎ রায় আছেন। আমারও আছে। তিনি সুপ্ত আছেন অবচেতনে, মননে, বিবেকে। তিনি সত্তার গভীরে এমনভাবে স্থাপিত আছেন যে, আমি চাই বা না চাই তিনি এসে আবির্ভূত হন জাগরণে, নিদ্রায়, স্বপ্নে। সেই একান্ত আপন সত্যজিৎ কীভাবে ধীরে ধীরে ভেতরে শিকড় গেড়েছেন, সেই রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।
ওঁর সব ছবি যেমন একাধিকবার দেখেছি, ওঁকে নিয়ে অনেক দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়েছি, এক-একটি ছবি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ পাঠ করেছি, এব সেই সঙ্গেই জন্ম নিয়েছে নিজের ভেতরে এক শৈল্পিক এবং ব্যক্তিগত নির্ভরতা। এক চিরকালীন ভরসা, আশ্বাস, সমবেদনার জগৎ। ভীষণ আনন্দে, বা নিদারুণ বিষাদে, বা অস্থির দ্বিধা-দ্বন্দ্বে তিনি উদ্ভাসিত হয়েছেন দৈনন্দিনতার জীবনচরিতে। তাঁর বিপুল দৃশ্য-শব্দের ভাণ্ডার থেকে ভেসে এসেছে নানা সঙ্কেত, যা মনকে দিয়েছে বাস্তবের ভূমি, কল্পনার উড়াল। আমি প্রথম সত্যজিতের ছবি দেখি আমাদের শিবপুরের বাড়ির সামনে ধোপার মাঠে— খোলা আকাশের নীচে, বাঁশ দিয়ে টাঙানো পর্দার ওপর। ‘ব্যাটলশিপ পটেমকিন’ আর ‘পথের পাঁচালী’ পর পর দু’দিন দেখানো হয়েছিল। সেই যে শৈশবে উনি হৃদয়ে-বুদ্ধিতে বীজ হয়ে ঢুকে পড়লেন, এখন সেটা সারা শরীর জুড়ে বটবৃক্ষের আকার পেয়েছে। সারা জীবনে এখনও পর্যন্ত নাট্যে এবং চলচ্চিত্রে যা কাজ করেছি, নেপথ্যে নানাভাবে কাজ করে গেছে তাঁর অভিভাবকত্ব। শৈল্পিক উৎকর্ষের এমন এক মানদণ্ড উনি তৈরি করে দিয়ে গেছেন, সেই নিরিখে যেমন পেয়েছি এক সমতা, তেমনই বুঝেছি নিজের অক্ষমতা, দৈন্য।
মনে পড়ে, ‘নন্দন’ যখন তৈরি হল, সেই লগ্নে একদিন ‘অপু ট্রিলজি’ প্রদর্শিত হয়েছিল। সেটা ১৯৮৫ সাল হবে। দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ি। মনে মনে গভীর সাধ— থিয়েটার-সিনেমা করব। সারাদিন ধরে তিনটি ছবি দেখেছিলাম। সেই প্রথম যুবক-মনে, যখন মগজ একটা পরিণতির আন্দাজ তৈরি করতে চাইছে, তখন ‘অপু ট্রিলজি’ একটা প্রবল অভিঘাত ঘটিয়েছিল। সেই উৎকর্ষের এভারেস্টের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কাছেই প্রশ্ন রেখেছিলাম যে, বাংলা চলচ্চিত্রের শৈল্পিক মান যদি এইখানে পৌঁছে গিয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম এমন কী করতে পারে, যাতে অন্তত সেটা দেখতে শিমূলতলার লাট্টু পাহাড়ের মতো লাগে, বা নিতান্ত দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্নে পাহাড়! কিন্তু এরকম একটা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার পাওয়ার যেমন ভাল দিক আছে, তেমন উল্টোদিকও আছে। ভাল দিকটা হল— আগামী প্রজন্ম বুঝে নেয় তার ভার, দায়িত্ব, অনুশীলনের ভূমি। আর খারাপটা হল— এই মহাত্মাদের প্রভাব সমাজ-সংস্কৃতিতে এতটাই গভীর হয় যে পরবর্তীর শিল্পীদের নাভিশ্বাস ওঠে সেখান থেকে নিজেদের মুক্ত করতে বা জনমানসকেও নতুন কোনও বিকল্পে স্থাপন করতে।
রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী বঙ্গদেশে, পঞ্চাশ-ষাটের দশক জুড়ে নাট্য-জগতে শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্ত, চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক ঘটক এমন এক আকাশচুম্বী সাংস্কৃতিক মিনার নির্মাণ করলেন যে, তাঁদের পাশে সব কিছুকেই ছোট লাগছিল। তাই সত্যজিতের প্রতিভার ছায়া এবং তাঁর নির্মাণস্থাপত্যের দর্শন থেকে বেরিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র এখনও পর্যন্ত কোনও ভিন্ন মাত্রার বিকল্প দিতে পারেনি। ফ্রান্সের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যেমন জাঁ রেনোঁয়া, এবেল গান্স, জাঁ ভিগোকে সম্মান জানিয়েও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে হেঁটেছিলেন ফরাসি নিউ ওয়েভের চলচ্চিত্রকাররা। সত্যজিতের সমকালে পশ্চিমবঙ্গে বহু উচ্চমানের চলচ্চিত্র হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর চিত্রভাষের বিপরীতে একটা সংহত সাংস্কৃতিক চিহ্ন গড়ে ওঠেনি। ঋত্বিক ঘটক একমাত্র ব্যতিক্রম। কিন্তু আমরা ওঁদের দুজনকে লড়িয়ে দিয়েছি আমাদেরই স্বভাবগুণে। একজন শিল্পসুষমায় সংযমের প্রতিভূ, অন্যজন ভাববিহ্বল আত্মহারা ‘ম্যাভেরিক’। কিন্তু আসলে একটা বহুমুখী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এই দুই মহান প্রতিভা যে দুজন দুজনের পরিপূরক, সেটা কি ভেবে দেখার কোনও অবকাশ আছে? কোনও উপরতলের সাদৃশ্যে বা বৈসাদৃশ্যে নয়, কিন্তু সিনেমার আত্মা যেখানে প্রাণের উৎস নির্দিষ্ট করছে— সেই উৎসমুখে দুজনের সাক্ষাৎ মিলতে পারে একই ভূমিতে। বাংলা চলচ্চিত্র আজ হয়তো সেই ভূমি আবিষ্কারে সচেষ্ট হতে পারে। সত্যজিতের সমকালে মৃণাল সেন নিশ্চয়ই একটা অন্য মাত্রা দিয়েছেন। আরও পরে গৌতম ঘোষ এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ভিন্ন নান্দনিকতার পথ খুঁজেছেন। কিন্তু অপর্ণা সেন বা ঋতুপর্ণ ঘোষ বারবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন সত্যজিৎ ঘরানায়। ঋতুপর্ণ তাঁর স্বন্তন্ত্র দক্ষতায় বিরাজ করলেও সত্যজিৎ-এর প্রকাণ্ড ছায়াতেই লালিত হয়েছেন। তারপর থেকে বাংলা চলচ্চিত্র খালি সংখ্যায় বেড়েছে, আড়ম্বরে উজ্জ্বল হয়েছে, কিন্তু নিরন্তর চিত্রভাষের অন্বেষণ, তীক্ষ্ণ সমাজবীক্ষণের যে পরম্পরা সত্যজিৎ এবং তাঁর সমসাময়িকরা তৈরি করেছিলেন, সেখান থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। তার কারণ খোঁজার জায়গা এটা নয়।
যে ব্যক্তিগত সত্যজিতের কথা বলছিলাম, সেখানে ফিরে গিয়ে বলি, আমার অনেক শৈল্পিক বাধাবিপত্তি ওঁর কারণে সহজেই পার করা গেছে। যেমন ধরা যাক কেউ আমাকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি ‘অরিজিনাল’ ছবি বানান না কেন?’ আমি হয়তো পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘অরিজিনাল’ মানে?’ তাতে প্রশ্নকর্তা বললেন, ‘এই ধরুন, আপনার সব ছবি কোনও উপন্যাস বা গল্পের ভিত্তিতে তৈরি। আপনি নিজের গল্প লেখেন না কেন?’ এই ফাঁদ থেকে বেরোনোর রাস্তা আমার জানা সত্যজিৎবাবুর দয়ায়। আমি বললাম, ‘আপনি কি ‘পথের পাঁচালি’-কে অরিজিনাল ছবি বলবেন না? ওটা তো বিভূতিভূষণের উপন্যাসের ভিত্তিতে করা।’ সব ক্ষেত্রেই দেখেছি প্রশ্নকর্তা এরপর নীরব হয়ে যান। সেই নীরবতার সুযোগ নিয়ে আরও ক্ষুরধার করে তুলি পাল্টা-প্রশ্নের ধার। ‘আপনি নিশ্চয়ই সত্যজিৎ রায়কে একজন মৌলিক চলচ্চিত্রকার বলে মনে করেন?’ মনে মনে ভাবলাম— কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে এই বিষয়ে বিতণ্ডা করবে? ‘তাহলে আপনার যুক্তি অনুযায়ী উনি তো অরিজিনাল হচ্ছেন না। কারণ ২৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবির মধ্যে ২১টি কোনও না কোনও গল্প-উপন্যাসের অবলম্বনে সৃষ্ট। তার মধ্যে ওঁর সব শ্রেষ্ঠগুলি রয়েছে।’ অবশ্যই এর বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি খাড়া করা মুশকিল, ফলে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আর কোনও সংলাপ থাকে না। আসলে ‘মৌলিক-অমৌলিক’, ‘স্বদেশি-বিদেশি’ এই বিপরীত যুগ্মপদের তাত্ত্বিক পরিসর অনেকদিনই তামাদি হয়ে গেছে। এখনও কিছু মানুষ এসব নিয়ে ভাবিত এক সেকেলে ভঙ্গিতে।
কিন্তু আসল প্রশ্নটা হচ্ছে চলচ্চিত্রের ভাষার বিস্ফার ঘটছে, না কি সাহিত্যের অনুকরণ হচ্ছে! সত্যজিৎ সেই প্রশ্নের নিরসন করে দিয়ে গেছেন তাঁর চিত্রকল্পের বিন্যাসে। আবার দৈনিক যাপনে সত্যজিতের চরিত্রেরা বার বার নিষ্ক্রমণ দিয়েছে নানা ব্যক্তিগত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে। আনন্দ, বিষাদ, যন্ত্রণা, আপসের নানা মুহূর্তে তারা স্মরণে এসেছে, অবলম্বন দিয়েছে, ভাবনার অভিমুখ দিয়েছে। মাঝে মাঝে রহস্যের মতো লাগে— সত্যজিৎ এসব চরিত্র দেখলেন কোথায়? গ্রামের হোক বা নগরের হোক, তাঁর ছবিতে যে-সব মানুষ উঠে এসেছে তাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে, সেসব তিনি জীবন্তে কি দেখেছেন? না কি এরা তাঁর অনন্য কল্পনার নির্মাণ? আমরা যৌবনে যখন এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে নানা শুঁড়িখানায় যাতায়াত করতাম— সে মেট্রো গলির ছোট ব্রিস্টল হোক বা বারদুয়ারি— মাঝেমাঝে দেখা হয়ে যেত সত্যজিতের চরিত্রদের সঙ্গে। জানতাম যে ওঁর এসব অঞ্চলে কোনও দিন গতায়াত ছিল না। তাহলে কি উনি ছদ্মবেশে আসতেন এইসব মানুষদের সন্ধানে? তা যদি না-ই হবে, এমন রক্তমাংসের জ্যান্ততায় কী করে ধরতেন তাঁদের? তবে সত্যজিৎবাবুর ব্যক্তিগত আসা-যাওয়া যেসব স্থানে ছিল, তার একটি আমি জানি। কারণ আমি নিজে সাক্ষী। ‘জগন্নাথ’-এর অভিনয় দেখতে এসেছিলেন সত্যজিৎবাবু সত্তরের দশকের শেষে। আমার তখন বয়স ১৪-১৫ হবে। অ্যাকাডেমির সাজঘরে সেই বোধহয় খুব কাছ থেকে দেখা ওঁকে। একটা গ্রুপ-ছবিও তোলা হয়েছিল, সেটাতে আমি আছি। তারপরে একটা অদ্ভুত ঘটনায় ওঁকে কাছ থেকে দেখি। আমি তখন থাকি রেসকোর্সের পাশে হেস্টিংসে সরকারি আবাসনে। সবে ধূমপান শুরু করেছি। আমাদের আবাসনের অকালপক্ব ধূমপায়ীদের দলটির একটা গোপন আস্তানা ছিল, আবাসন থেকে বেরিয়ে দূরে একটা ছোট রাস্তায়। হেস্টিংস অঞ্চলটা বেশ অভিজাত জায়গা, বিশাল মাপের পুরনো বাংলো বাড়িগুলোই তার প্রমাণ। সেই শান্তিপূর্ণ আভিজাত্যের ছত্রছায়ায় একটা নিরিবিলি ডেরা আবিষ্কার করা হয়েছিল। একদিন আমরা বেশ গোটা দশেক ছেলে সিগারেট ধরিয়ে বিকেলের মৌজে আবিল, হঠাৎ একটা সাদা আম্বাস্যাডর এসে দাঁড়াল একটু দূরে, পাশের বাড়ির গেটে। গাড়ি থেকে নেমে এলেন সত্যজিৎ রায়। আমরা সবাই এক মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে সটান উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেট হাতের আড়ালে লুকিয়ে ফেললাম। এক স্থির নীরবতা। উনি আমাদের দিকে ঘুরে তাকালেন না। হয়তো ১৫ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ছিলেন বড় লোহার দরজা খোলার অপেক্ষায়। তারপর ঢুকে গেলেন। আমি সহ দু’একজন সিগারেট ফেলেও দিয়েছি। আমাদের এই আচরণ আমাদেরকেই অবাক করেছিল, নিজেদেরকে নিয়ে মস্করাও করেছিলাম। কিন্তু মনে মনে জানতাম এই মান্যতা, সম্মান উনি আমাদের অবচেতনে খোদাই করে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে পাশের বাড়ির বড় জানলা দিয়ে ভেসে এল একটি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রেশ। পরে জেনেছিলাম, উনি ওই বাড়িতে আসতেন সঙ্গীত শুনতে। কিন্তু কোনওদিন আর দেখা পাইনি। এরপরে সত্যজিৎবাবুকে শুধু দূর থেকেই দেখেছি। ঘুরপথে ওঁর কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নিমাই ঘোষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে কাজ করার সুবাদে। সেদিন আবার বহুবছর বাদে আমার চোদ্দো বছরের পুত্রকে নিয়ে সারাদিন পরের পর ‘অপু ট্রিলজি’ দেখলাম। ফিরে গেলাম সেই যৌবনের দিনে, নন্দনে একসঙ্গে তিনটে ছবি দেখার দিনটাতে। সেদিন ছিলাম অপুর কাছাকাছি, আজ অনেকটাই হরিহরের দিকে ঝুঁকেছি।