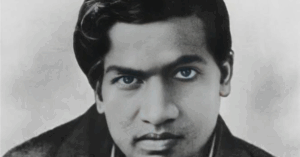আর. শিবকুমার আধুনিক চিত্রকলার একজন প্রখ্যাত গবেষক, সমালোচক এবং শিল্প-ইতিহাসবিদ। সোমনাথ হোরের জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর সৃষ্টিশীল জগতের নানান দিক নিয়ে কথা বললেন ডাকবাংলা.কম-এর এই সংখ্যায়। কথোপকথনে মালবিকা ব্যানার্জি।
সোমনাথ হোরের কাজের সঙ্গে ১৯৪৩-এর বাংলার মন্বন্তর সমার্থক। আপনার কি মনে হয়, এই ঘটনার প্রভাব ও অনুরণন তাঁর শিল্পজীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে?
হ্যাঁ, বাংলার মন্বন্তর সোমনাথ হোরের জীবনে গভীর অর্থবহ ঘটনা, যা তাঁর চেতনা এবং শিল্পকে জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি তাড়িয়ে ফিরেছে। প্রথম জীবনের একটিমাত্র অভিজ্ঞতা একজন শিল্পীর সমগ্র শিল্পচিন্তাকে এভাবে প্রভাবিত করেছে, প্রায় ‘অবসেশন’-এর পর্যায় কাজ করে গেছে, এটা খুবই বিরল। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, উনি শুধুমাত্র একটা ঘটনা হিসাবে তেতাল্লিশের মন্বন্তরকে দেখেননি, তার দরুন জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছিল, সেই পটভূমিকায় কাজ করেছেন। আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিকাঠামোর কারণে যে দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল, এবং যা আবার ঘটতে পারে, সেই অমানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন, সৃষ্টি করে চলেছিলেন। এই সময়ের যন্ত্রণা ছাড়াও, এই দর্শন তাঁর ভিতর আঘাত ও ক্রোধের যে অনুভূতি জাগায়— তা সোমনাথ হোরের শিল্পে সর্বত্র প্রতিধ্বনিত।
ওঁর সামাজিক এবং রাজনৈতিক সচেতনতা— বিশেষত মন্বন্তর এবং তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে ওঁর সংযোগ— প্রিন্টমেকার সোমনাথ হোরের দক্ষতা এবং উদ্ভাবনের মূল্যায়ন থেকে কি আমাদের কিছুটা বিচ্যুত করে? এই ক্ষেত্রে ওঁর অবদান সম্বন্ধে আপনার কী মত?
না, আমার তা মনে হয় না। বরং আমার মনে হয় উল্টোটাই ঠিক— এই সচেতনতা ওঁকে উদ্ভাবনশীল হতে প্রায় বাধ্য করেছিল। সোমনাথ হোর একই বিষয়ে আটকে থাকা এক্সপ্রেশনিস্ট ছিলেন না; মতবাদে সমর্পিত শিল্পী ছিলেন। উনি অনেক আগেই এটা বুঝেছিলেন যে ভাবাবেগ স্থায়ী হয় না এবং একটা দীর্ঘ সময় ধরে দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য তা যথেষ্ট নয়। এমনকী, নিজের ভিতরের আবেগকে বাঁচিয়ে রাখতে উনি বারংবার তা বিভিন্ন ভাবরূপে প্রকাশ করেছেন— অসাধারণ উদ্ভাবনীক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, নানা মিডিয়ামে কাজ করে যাওয়াটা এই পদ্ধতিরই অঙ্গ।
ওঁর অবদান দু’ভাবে দেখা যেতে পারে— শিল্পী হিসাবে, এবং শিক্ষক হিসাবে। দুই ক্ষেত্রেই উনি অনন্যসাধারণ। একজন প্রিন্টমেকারের পক্ষে মিডিয়াম এবং টেকনিকের ক্ষেত্রে যা-যা চর্চা করা সম্ভব, উনি পুরোটাই গবেষণা করেছিলেন। এমনকী একেবারে নতুন একটা পদ্ধতি যোগ করেন— পেপার-পাল্প প্রিন্টিং— যা প্রিন্টমেকিং এবং রিলিফ ভাস্কর্যের সেতুবন্ধন হিসাবে দেখা যায়। শিক্ষক হিসাবেও ওঁর প্রভাব দৃষ্টান্তমূলক, সমসাময়িক শিল্পীদের তুলনায় অনেক বেশি প্রিন্টমেকার ছাত্রছাত্রীকে উনি লালন করেছিলেন।

ছবি সৌজন্য গ্যালারি ৮৮
কলাভবনের অত্যন্ত সৃষ্টিশীল একটা সময়ে সোমনাথ হোর শান্তিনিকেতনে পড়াতে শুরু করেন; কে.জি. সুব্রহ্মণ্যন এবং রামকিঙ্কর বেজ তখন তাঁর সমকালীন শিল্পী। তাঁদের সহযোগিতা কেমন ছিল? এই অসামান্য সময়কে তাঁরা কীভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন?
সোমনাথ হোর শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ১৯৬৭-এ, কিন্তু শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই। মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদের গণ্ডি যথেষ্ট সীমিত, এবং নন্দলাল এবং বিনোদবিহারীর মতো শিল্পীরা একটা মডার্নিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রিন্টমেকিং-এর জগতে নতুন সম্ভাবনা অনুসন্ধান করছিলেন, যা অনেক বেশি ফলপ্রসূ ছিল। আমার মনে হয় প্রধানত এটাই শান্তিনিকেতনের প্রতি ওঁকে আকর্ষণ করে।
কিন্তু সোমনাথের কলাভবনে শিক্ষক হিসাবে যোগদান এবং শান্তিনিকেতনে উঠে আসার আগের ইতিহাস একটু অন্যরকম ছিল। ১৯৬৭-র গোড়া থেকেই সোমনাথ হোর দিল্লির শিল্পজগৎ থেকে সরে আসেন, দিল্লি কলেজ অফ আর্ট থেকে পদত্যাগ করেন। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে শান্তিনিকেতন হয়তো চিরকালই মডার্ন আর্ট জগতের কিনারায়, কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কলাভবন তখনও শিল্পভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। বিনোদবিহারী এবং রামকিঙ্কর তখনও শান্তিনিকেতনে। তাঁরা সোমনাথের কাছে আদর্শ শিল্পীর জীবিত নিদর্শন ছিলেন— শিল্প ও জীবনের প্রতি গভীরভাবে নিমজ্জিত, কিন্তু প্রদর্শশালা এবং শিল্পের ব্যবসায়িক দিক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আরও কিছু বছর পর কে.জি. সুব্রহ্মণ্যনও শান্তিনিকেতনে ফেরত চলে আসেন। উনিও শিল্প এবং জীবনের ক্ষেত্রে প্রশস্ত দর্শনে বিশ্বাসী একজন শিল্পী ছিলেন। আদর্শগত ফারাক থাকলেও, সোমনাথ এবং সুব্রহ্মণ্যনও একে অপরকে সহযাত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দেন। শিল্পকে বৃত্তি রূপে দেখার যে দর্শন, সেই ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে ঘটতে থাকে অপার আদান-প্রদান।
‘উন্ড’ সিরিজটা এখন পৃথিবী-বিখ্যাত; সোমনাথ হোরের এই সময়ের কাজ প্রসিদ্ধ। ব্যক্তিগত জীবনে উনি ভীষণভাবে একাকী ছিলেন, নিজের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। এই আদর্শবাদ, যা ওঁর শিল্পকে সমৃদ্ধ করে এসেছে, উনি কীভাবে ধরে রাখতে পেরেছিলেন, বিশেষত যখন গ্যালারি এবং শিল্প-বিক্রেতারা তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছে?
গ্যালারিদের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক চিরকালই বেমানান, অস্বস্তিকর ছিল। ১৯৫৬ এবং ১৯৬৮-এর মাঝে, বারো বছরে উনি আটটা একক প্রদর্শনী করেন; এই সময় তিনবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। বলা যায় উনি শিল্প, তার প্রদর্শনী এবং ব্যবসা, এই সব কিছুর সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন, কিন্তু যেমন আমি বললাম, ওঁর মনে হত যে, ওঁর আদর্শ এবং শিল্পভাবনার সঙ্গে এই সব কিছুরই একটা সংঘাত রয়েছে। মার্ক্সিস্ট হিসাবে ওঁর মনে হত, প্রদর্শশালার পদ্ধতি ওঁর আদর্শের বিরোধী, এবং এসব থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। একই সঙ্গে, এই সিদ্ধান্ত ওঁকে পেশাদার সমালোচক বা আর্ট মার্কেটের পরোয়া না করে সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠার স্বাধীনতা দিয়েছিল। এই মার্কেট সিস্টেমে গ্যালারিদের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু দর্শক ছাড়া শিল্পীর কদর নেই, এবং বর্তমান যুগে দর্শক ও শিল্পীর সংযোগস্থল হিসাবে গ্যালারিকেই দেখা হয়। শিল্পজগতের সঙ্গে উদ্বেগজড়িত সম্পর্ক সত্ত্বেও, শিল্পপ্রেমীদের উৎসাহে ১৯৯০-এর পর থেকে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে উনি ওঁর কড়া নীতি একটু শিথিল করেন।

আনটাইটেল্ড, উড এনগ্রেভিং
ছবি সৌজন্য গ্যালারি ৮৮
সোমনাথ হোরের ভাস্কর্য আজ পৃথিবী-বন্দিত। অপূর্বরূপে গঠিত তাঁর ভাস্কর্যে ক্ষীণকায়, চোখ বসে-যাওয়া কিছু মূর্তি যেন মানুষের অবস্থার প্রতীক। ওঁর কিছু বিখ্যাত ভাস্কর্যের মূল্যায়ন কীভাবে করবেন আপনি?
ষাটের দশকের শেষ থেকে ওঁর প্রিন্টের কাজে স্পর্শের অনুভূতি প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ওঁর ইন্ট্যাগ্লিও প্রিন্টে উপরের স্তরটা স্পৃশ্য হতে শুরু করে; রিলিফ স্কাল্পচার-এর ধরনে তৈরি হতে থাকে পেপার-পাল্প প্রিন্ট। এগুলোর শুরুর কাজগুলো মাটির ট্যাবলেট বা মোমের শিট-এ তৈরি হত, যেগুলো তারপর সিমেন্টে ঢালাই করা হত এবং পাল্প-প্রিন্টের ম্যাট্রিসে পরিণত করা হত। ওঁর প্রথমদিকের ভাস্কর্যগুলো এই মোমের শিট থেকেই তৈরি হয়েছে; কেটে, নিপুণভাবে হাতে নাড়াচাড়া করে ফর্ম তৈরি করে, ব্রোঞ্জে ঢালাই করা হত।
সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা ভাস্কর্যে বস্তুধর্ম বজায় রাখার চাহিদা এবং পদ্ধতি, দুই-ই বিদ্যমান। অদ্ভুত ভাবে, এই পদ্ধতি সোমনাথ হোরকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের ভয়ঙ্করভাবে বিকৃত শরীরের ফর্মে ফেরত নিয়ে যায়। ত্বকের মতো কুঁচকে যাওয়া মোমের শিট, যা তার উপরে কাটা ক্ষতকে নিখুঁতভাবে মানুষের শরীরের মতোই ধরে রাখতে পারে, এবং ব্রোঞ্জ, যা দিত স্থায়িত্ব, স্মৃতির ওই ছবিগুলোতে আবার অসামান্য জীবনীশক্তির সঙ্গে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। ওই প্রাণশক্তির প্রতিফলন ড্রয়িং এবং প্রিন্টিং-এ সম্ভব নয়। শারীরিকতা ছাড়াও, ওঁর স্কাল্পচারের ছোট সাইজ— মানুষের হাতের মুঠোয় ফিট করে এমন— তাদের স্পর্শ করে অনুভব করার জন্য আদর্শ। ওঁর ভাস্কর্যে মানুষের যন্ত্রণা এবং ভঙ্গুরতা অন্তরঙ্গ ভাবে প্রকাশ পায়, অসাধারণ সংবেদনশীলতায়।

আপনার সঙ্গে সোমনাথ হোরের গভীর পরিচয় ছিল। আপনার কাছে মানুষ এবং কর্মরত শিল্পী সোমনাথ হোরের চিরন্তন স্মৃতি কী?
সোমনাথ হোর সব বিষয়ে প্যাশনেট মানুষ ছিলেন, তা নিজের বিশ্বাসই হোক বা কাজ। এটা উনি একটা যুক্তির প্রলেপে ঢাকতে চাইতেন, কিন্তু সব সময় সফল হতেন না। বহির্ভাগের অন্তরালে সব সময় একটা অস্থিরতা কাজ করত, যেন বিক্ষুব্ধ থাকার যথেষ্ট কারণ সবসময় বজায় ছিল। আদর্শগত অবস্থান থেকে হতভাগ্যের প্রতি সমবেদনা ছিল, এবং তা প্রকাশ করতে কোনও দ্বিধা বোধ করতেন না। অত্যন্ত উদার শিক্ষক ছিলেন, প্রতিভা চিনে ফেলতেন এবং মতাদর্শে ফারাক থাকলেও তার মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করতেন না। এবং, প্রিন্টমেকার হিসাবে ছিলেন অক্লান্ত গবেষক ও নিরীক্ষক। সব কাজই কমন স্টুডিওতে করতেন এবং ওঁর কাজ একটা আইডিয়া থেকে ফাইনাল প্রিন্টে উত্তীর্ণ হচ্ছে— এটা দেখা, মুদ্রণের পর মুদ্রণ দেখা, ওঁর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে স্টুডিওতে তন্ময় হয়ে কাজ করা শিল্পী সোমনাথ হোরের ছবিটাই আমার সবচেয়ে কাছের স্মৃতি।
দুঃখের বিষয়, সোমনাথ হোরের শতবর্ষ এমন একটা সময় হচ্ছে, যখন একটা ভোট হচ্ছে, যা মেরুকরণে বিশ্বাসী, এবং যা ওঁর বিশ্বভাবনা এবং রাজনীতির বিপরীতধর্মী। বিশ্বভারতীতে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে ওঁর শতবর্ষের পরিকল্পনা কী?
এখন চারদিকে যা ঘটছে, তা দেখলে উনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়তেন। পার্টি সদস্যপদ ১৯৫৬-এ ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি ওঁর প্রবৃত্তি পুরোপুরি সোশ্যালিস্ট রয়ে গিয়েছিল, ছিল সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি গভীর, সহজাত সমবেদনা। এইসব মেরুকরণ, বা মানুষকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা— সোমনাথ হোরের গোটা সংস্কৃতি, সত্তা, বিশ্বাসের বিপরীতমুখী। এসব দেখলে সত্যিই উনি খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়তেন।
যদিও আমরা এখনও অতিমারীর মাঝে, কলাভবনে আমার সহকর্মীরা সোমনাথ হোরের শতবর্ষ উপলক্ষে কিছু ছোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করছেন, যার মধ্যে থাকছে একটা প্রদর্শনী। ওঁর উপরে লেখা একটা বই তক্ষশীলা ফাউন্ডেশন থেকে বেরোচ্ছে বলেই জানি, যা সম্পাদনা করছেন ভাস্কর কে এস রাধাকৃষ্ণণ। ওঁর অসামান্য কেরিয়ারের উপরে একটা
বইও বেরোনোর কথা ছিল, কিন্তু তা বেরোয়নি, খানিকটা ওঁর নিজের নীরবতার কারণেই।
সোমনাথ হোরের শতবর্ষ উদযাপন হচ্ছে, ভাল কথা— যদিও ওঁর মাপের শিল্পীর পক্ষে এই উদযাপন একটু দেরি করেই হল। আমি নিশ্চিত এই শতবর্ষ উপলক্ষে আরও বহু প্রদর্শনী, অনুষ্ঠান এবং প্রকাশনা আমরা দেখতে পাব।